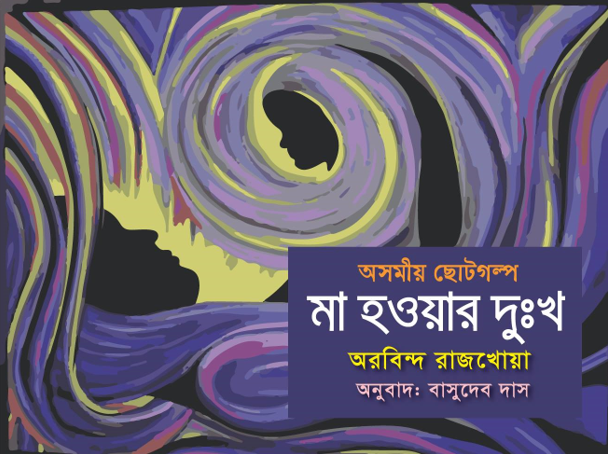মোজাম্মেল হক যখন পাকাপাকি গ্রামে ফিরে যান তখন স্বপ্নীলের বয়স সাত। শহরের বড় স্কুল, সারি সারি দোলনা, পিছলে পড়ার স্লাইড, সমান্তরাল করে কাটা ঘাস বিছিয়ে রাখা মাঠ আর পরিস্কার জামা জুতো পরা বন্ধুদের মায়া কাটিয়ে চলে আসার সময় ছেলেটা টু শব্দও করেনি। এটা অবশ্য খুব একটা অবাক করার মত কিছু নয়। স্বপ্নীল তখন থেকেই শব্দ করা বন্ধ করে দিয়েছে যখন আবিদা জরায়ুর ক্যান্সারে শয্যাশায়ী হলো। কয়েক বছর খুব লড়াই করে কঙ্কালের মত হয়ে যাওয়া আবিদা যখন চলে গেল, কেউ আশ্চর্য হয়নি। আশ্চর্য হয়েছিল এটা দেখে যে স্বপ্নীল শেষ সময়ে মায়ের কাছে যাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিল, এমনকি লাশটাও দেখল না। মোজাম্মেল হক তাকে দিয়ে কবরে একমুঠ মাটি দেয়ালে সে তাও দিয়েছিল অন্যদিকে তাকিয়ে। কোনো কান্না নেই, জিজ্ঞাসা নেই, যেন বোধই নেই। স্বপ্নীলের খালা এসে বলেছিল, “দুলাভাই, আপনি অহেতুক কিছু ভাববেন না। সবার প্রকাশের ক্ষমতা তো এক নয়, আপনার ছেলেটা ইন্ট্রোভার্ট।”
ইন্ট্রোভার্ট – অন্তর্মুখী — শব্দটা প্রথম ওইদিনই শুনেছিলেন তিনি। যারা নিজেদের অনুভব, অনুভূতি সব নিজেদের মধ্যেই চেপে রাখে, তারাই এরা। মাকে মাটি দিয়ে এসে খুব সুন্দর করে আশেপাশের বাড়ি থেকে দিয়ে যাওয়া ভাত, মুরগির মাংস, বোম্বাই মরিচ দেয়া মসুরির ডাল দিয়ে মেখে ভাত খেলো স্বপ্নীল। বড়মানুষদের মতই, অবাক হয়ে দেখল সবাই, বলাবলিও করল, ভীষণ ঝাল খেতে পারে, অন্য বাচ্চারা তো ডাল খেতেই পারেনি। দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেল পার করে দিল, আত্মীয় ভরা বাড়ি, সবাই টেনে টেনে নিতে চাইলেও কারো কাছেই গেল না ছেলেটা। মোজাম্মেল হক সেদিনই ঠিক করলেন গ্রামে চলে আসবেন, পাকাপাকিভাবে। শহরের যান্ত্রিকতার মধ্যে থাকলে ছেলেটা হয়ত আরও চুপচাপ হয়ে যাবে। আর আবিদা নেই, অন্য কাউকে সে জায়গাটা দেবারও ইচ্ছা নেই যেহেতু, শহরের জীবন ঝঞ্ঝাট হয়ে যায় ভীষণ ভাবতে গেলে। সকালে উঠে গোসল করে অফিসের জন্য তৈরি হওয়া বাদে আর তো কোনো কাজ ছিল না একসময়। আবিদার শেষ বছরগুলোতে সেই কাজ বেড়ে চারগুণ হলো। যদিও মেয়ের দেখাশোনা করতে স্বপ্নীলের নানী বা খালাও প্রায়ই এসে থাকত, কিন্তু তাই বা কয়দিন। দিনের বেলা আবিদার দেখাশোনার জন্য কাজের লোক, রাতের বেলা তিনি নিজে। কেমন যেন গুমোট হয়ে গিয়েছিল ঘরটা, চারিদিকে যেন আটকে আছে বাতাস, ঘরে যারা আছে সবার যেন কোষ বিভাজন থেমে গেছে। জমানো টাকা, আবিদার গয়না আর পৈতৃক সম্পদের ওপর ভরসা করে গ্রামে চলে এলেন তিনি। জমি বর্গা চাষীদের দিলেন, বাগানে সুপারি গাছ লাগালেন, পুকুরে মাছ ছাড়লেন, কিনলেন মুরগী – হাঁস – দুটো গরুও, আর স্বপ্নীলকে ভর্তি করিয়ে দিলেন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে, ক্লাস থ্রিতে।
জীবনটা সত্যিই অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল তখন। বাড়ির আশেপাশের আত্মীয় – স্বজন – প্রতিবেশী থেকে শুরু করে গ্রামের মোটামুটি সবার সাথেই হৃদ্যতা, সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাবা – মা মারা যাওয়ার পর থেকে গ্রামে প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা আসেননি তিনি। কিন্তু এখানে বাস শুরু করার পর মানুষের আচরণে একবারের জন্যও মনে হয়নি তিনি কখনো এখানে ছিলেন না। কিন্তু সমস্যা স্বপ্নীলকে নিয়ে রয়েই যায়। সেই চুপচাপ থাকা, নিজের মনে পড়াশোনা করা, খেলার সময়ে উঠানে একা হাঁটাহাঁটি করা — এমনকি স্কুলে খোঁজ নিয়ে শুনেছিলেন ও নাকি টিফিনের সময় হেডমাস্টারের রুমে গিয়ে বসে থাকে, খবরের কাগজ পড়ে।
স্বপ্নীলের ছোটবেলাটা এমনই ছিল। তাই যখন আন্দোলনের সময় স্বপ্নীল চুপচাপ বাড়ি ফিরে এসে ঘরের দরজা আটকে দিল তখন মোজাম্মেল হকের কিছুই মনে হয়নি। এই ছেলে তো আর আন্দোলন করার ছেলে না। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ছাত্রজীবনে তিনি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। নারিকেলের খোসা দিয়ে বোমাও বানিয়েছেন। তার ছেলে এতবড় আন্দোলন ফেলে ঘরে এসে দুয়ার দিয়েছে। তাও আবার এমনভাবে দুয়ার দিয়েছে মনে হচ্ছে ভেতরে বসে কান্নাকাটিও করছে। সারাজীবন এমনভাবে খবরের কাগজ পড়ে গেছে এই ছেলে যে দেখলে মনে হত বিরাট রাজনৈতিক বোদ্ধা। এখন মনে হচ্ছে না হয়েছে এ কোনো বোদ্ধা, না হয়েছে যোদ্ধা! হয়েছে এক ভীতুর ডিম, যা থেকে এখন কাপুরুষতা ফুটে বের হচ্ছে।
মোজাম্মেল হকের চোখে স্বপ্নীলের একমাত্র সাহসিকতা ছিলো দক্ষিণাকালী মন্দির ধারের শ্মশানে বসে শকুন দেখা। শ্মশানটা স্বপ্নীলের স্কুল থেকে বেশি দূরে ছিল না। মোজাম্মেল হক নিজেই স্বপ্নীলকে শ্মশান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্মশানে গিয়ে একপাল শকুন বসে থাকতে দেখা গেল, আর কিছু আকাশে উড়তে। একটা শকুন পাল থেকে আলাদা একটু দূরে বসে ছিল, একটা আধভাঙা পাথরের ওপর, গিন্নি শকুন, স্বপ্নীলকে তিনিই চিনিয়েছিলেন। শকুনদের রানী ওই গিন্নি শকুন। গিন্নি শকুন এসে ঠোকর না দেয়া অব্দি অন্য শকুনরা মৃতদেহে ঠোঁট ছোঁয়ায় না। উবু হয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে স্বপ্নীল শকুন দেখেছিল। কালো – সাদা – বাদামী মেশানো পালক, ঝুলে থাকা চামড়া, শক্ত তীব্র বাঁকানো চঞ্চু — আর বিন্দুর মত গোল কালো চোখের মণিতে কি ভয়ানক বিরোধী চাহনি! নারকেল গাছের শুকনো ডালের মত বিরাট ডানা ঝাঁকিয়ে মাঝেমধ্যেই আশেপাশের বাতাসে আরেকটু করে নোংরা ছড়িয়ে দিত।
তারপর থেকে প্রায়ই স্বপ্নীল শকুন দেখতে যেত। কিছুদিন শকুনদের মুড়ি খাওয়াবার চেষ্টা করলো, তারপর পাতা খাওয়াবার, তারপর হঠাৎ একদিন বাদও দিয়ে দিল, বলল দুঃস্বপ্ন দেখছে, শকুন নিয়ে বিশ্রী সব স্বপ্ন, খুব একটা খুলে বলেনি, মোজাম্মেল হকও আগ্রহ দেখাননি, ছেলের শকুনপ্রীতি তার খুব যে ভালো লাগছিল এমন তো নয়। তারপর স্বপ্নীল বড় হয়ে গেল, স্কুল – কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেল। শকুনের কাহিনি ওখানেই শেষ, আর স্বপ্নীলের প্রথম ও শেষ সাহসিকতাও অতটুকুই।
আন্দোলনের খবর জানতে প্রতিদিনই খবরের কাগজ সংগ্রহ করছিলেন তিনি। বাজারের ঔষধের দোকানে বলে রেখেছিলেন তাদের খবরের কাগজের সাথে যেন তার জন্যও একটা রাখে। ওরা রেখে দেয় প্রতিদিনই। সব পত্রিকায় সঠিক সংবাদ আসেও না, দীর্ঘদিনের শক্ত কবজার ফল। স্বপ্নীলকে দেখে মনে হয় যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। নাস্তার টেবিলে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছেলেটাকে দেখেন। উদভ্রান্তের মতো মুখ, চোখের নিচে দাগ হয়ে গেছে বাড়ি আসার এই দুই তিনদিনেই। নাকি আগে থেকেই ছিল? যেদিন বাড়িতে এল ছেলেটা সেদিন ঠিক করে ওর মুখটাই দেখতে পাননি, মাথা নিচু করে ছিল, চোখ দেখা তো দূরের কথা যেন পিঠের ওপর কেউ ভারী তিনমণি বস্তা চাপিয়ে দিয়েছে এতটাই কুঁজো হয়ে ঢুকেছিল ঘরে।
– তোর কি শরীরটা খারাপ?
– না বাবা।
– মুখটা তো ভালো লাগছে না।
– ঘুম হচ্ছে না বাবা। দুঃস্বপ্ন দেখছি খুব, ভয়ানক সব দুঃস্বপ্ন।
– কী দেখিস?
স্বপ্নীল কিছুক্ষণ ওভাবেই মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে। তারপর মাথা তোলে।
– শকুন দেখি বাবা।
মোজাম্মেল হক ভয় পান না, কিন্তু কোথাও যেন একটা নাড়া খান। কপাল কু্ঁচকে যায় তার। স্বপ্নীল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আবার মাথা নামিয়ে ফেলে।
– মাঝখানে দেখিনি বাবা। কত কত বছর যে গেল, একদম দেখিনি।
যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে। মায়া লাগে মোজাম্মেল হকের। মা মরা তার ছেলেটা, কত দূরে দূরে থাকে, সামান্য স্বপ্ন দেখে কেমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছে।
– ঘুমানোর আগে আজ একটু দুধ গরম করে দেব, খেয়ে ঘুমাবি।
স্বপ্নীল মাথা কাৎ করে সম্মতি দেয়। বিকেলে ছিপ নিয়ে পুকুর ঘাটলায় গিয়ে বসে। আটায় সামান্য পানি গুলে দলা বানিয়ে বরশিতে গেঁথে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। ফলাফল একটা সরপুঁটি, একটা ফলি আর তিনটা কচ্ছপ। রাতের খাবারে দুটো মাছই সুন্দর করে মশলা দিয়ে ভেজে দেন মোজাম্মেল হক। স্বপ্নীল বেছে ফলি মাছটা নেয়।
– সরপুঁটিটাও নে।
স্বপ্নীল দুপাশে মাথা নাড়ে।
– বেশ, ফলিটাই খা। ঢাকায় তো এসব ভালো পাওয়া যায় না।
ঢাকায় অবশ্য খুঁজলে সবই পাওয়া যায়, বাঘের দুধও। হাতে টাকা লাগে, আর লাগে কোথায় যেতে হবে সেটা জানা। স্বপ্নীল চুপচাপ খেয়ে ওঠে। সিংকে পানি ছেড়ে আস্তে আস্তে প্লেটটা ধুয়ে নেয়, তারপর তোয়ালেতে হাত মুছে ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর বাবা দুধ নিয়ে এলে চুপচাপ খেয়ে শুয়ে পড়ে। একটু পর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বাবা তখনো দাঁড়িয়ে।
– যাও, আমি ঘুমাচ্ছি।
মোজাম্মেল হক মাথা নেড়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে আসেন। সবকিছু গুছিয়ে মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর প্রস্তুতি নেন। মশারি তোশকের নিচে গুজে দিতে দিতে তার আবিদার কথা মনে পড়ে। ও থাকলে এত চিন্তা করতে হতোনা। ছেলেরা মায়ের যত কাছের হয়, বাবার তত কাছাকাছি কখনোই পৌঁছাতে পারে না। মাছের সাথে পানির যেমন সম্পর্ক, হাঁসের সাথে ততটা কখনোই নয়।
গভীর রাতে আচমকা তার ঘুম ভেঙে যায়। পিঠের কাছে একটা স্পর্শ অনুভব করে। ফিরে দেখে স্বপ্নীল গুটিশুটি মেরে তার পাশে শুয়ে আছে। সে পাশে সরে গিয়ে আরেকটু জায়গা করে দেয়। স্বপ্নীল ফিরে তাকায়।
– ভয় পেয়েছি বাবা।
মোজাম্মেল হক কথা বলেন না। আস্তে আস্তে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। হয়ত ওই হাতে আস্থা রেখেই ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ে।
সকালে উঠতে স্বপ্নীলের বেশ একটু দেরীই হয়। পুকুর ঘাটলায় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছিলেন মোজাম্মেল হক। ওকে আসতে দেখে তিনি ওর দিকে খবরের কাগজ এগিয়ে দেন। স্বপ্নীল চরম বিতৃষ্ণায় খবরের কাগজের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। মোজাম্মেল হক বিষয়টা লক্ষ্য করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলেন না। কিই বা বলবেন, পাতাজুড়ে লাশের ছবি, রক্ত, সংঘাত, সংগ্রাম। বিপ্লবের প্রসব বেদনা।
– তুই কি স্বপ্ন দেখিস বল তো।
স্বপ্নীল প্রথমে চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দেয়।
– একটা লাশ দেখি বাবা। লাশটা ঘিরে অনেক শকুন। আর দূরে বসা একটা গিন্নি শকুন। গিন্নি শকুন এসে ঠোকর দেয় না বলে অন্য শকুনরা লাশটা খায় না। হঠাৎ লাশটা চোখ খোলে, গিন্নি শকুনটার দিকে আঙুল তুলে কি যেন বলতে চায়। তখন অন্য শকুনেরা নখ দিয়ে ওকে চেপে ধরে, আঁচড়ায়, ওর চোখ তুলে নেয়, ওর সারা শরীরে ক্ষত। এইসবের মধ্যেও ওই গিন্নি শকুনটা ওভাবেই চুপচাপ বসে থাকে।
মোজাম্মেল হক পুরোটা শোনে। তারপর মুখ খোলে।
– লাশটা কার?
– একটা ছেলের, বাবা। রাস্তায় দেখা হয়েছিল, আন্দোলনের সময়, নামটাও জিজ্ঞেস করিনি। আমার পাশেই দৌড়াচ্ছিল, হঠাৎ পায়ে গুলি লাগে। মরেনি, পড়ে গেছে শুধু। আমি গিয়ে টেনে তুলেছি। হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম একটু দূর অব্দি নিয়ে গেলেই অন্য অনেক মানুষজন পাব, হাসপাতালে পাঠাতে পারব। কিন্তু কেউ থামলো না, বাবা। আমি এত হাত তুলে বললাম গুলি না করতে। ছেলেটা আমার হাতের মধ্যেই মরে গেল। নয়টা গুলি, বাবা। আমি গুনেছি।
বলতে বলতে স্বপ্নীল কেঁদে ওঠে। মোজাম্মেল হক অবাক হন। স্বপ্নীলকে সে কবে কাঁদতে দেখেছিলেন মনে করতে পারেন না। উনি উঠে ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান, মাথায় হাত রাখেন। কিন্তু কি বলবেন ভেবে পান না।
– মানুষের মৃত্যুর জন্য কষ্ট দেখতে ভালো লাগে না, বাবা। ছেলেটা অনেক কষ্ট পেয়েছে। মুখ হা করে ছিলো, নিশ্বাস নিতে পারছিল না, চোখ উলটে যাচ্ছিল। আমি সহ্য করতে পারিনি, বাবা। ওর লাশটা ফেলে আমি পালিয়ে এসেছি।
মোজাম্মেল হক এবার কথা বলেন।
– সবাই তো সমান সাহসী হবে না, বাবা।
– আমি শকুন দেখতে যেতাম কেন বাবা, শকুনগুলো দেখতে মায়ের মতন লাগত। ক্যান্সারে ভুগে মায়ের চেহারাও একদম এমন হয়ে গেছিল, না বাবা? পরে বুঝলাম, শকুন কি কখনো মায়ের মত হয়?! শকুন কখনো মা হয় না। মায়ের কত কষ্ট হচ্ছিল, না বাবা? আমি তোমাকে দোষ দিই না, বাবা। আমি দেখেছি তুমি মাকে কি করেছ। কিন্তু তোমাকে দোষ দিই না, বাবা। মাকে ওভাবে দেখতে আমারও ভালো লাগত না। মার মরে গিয়ে শান্তি হয়েছে। তুমি মেরে ফেলছ বলে হয়ত মার একটু দুঃখ হবে, হয়ত হয়েছে, কিন্তু কত কষ্ট কমে গেল মায়ের, বলো বাবা, কত কষ্ট কমে গেল!
স্বপ্নীল উন্মাদের মত কথাগুলো বলে যায়, আর পুকুরের স্থির পানির দিকে তাকিয়ে মোজাম্মেল হক স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

দিলশাদ চৌধুরী
জন্ম ১৯৯৯ সালে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত। অনুবাদ ও কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন।