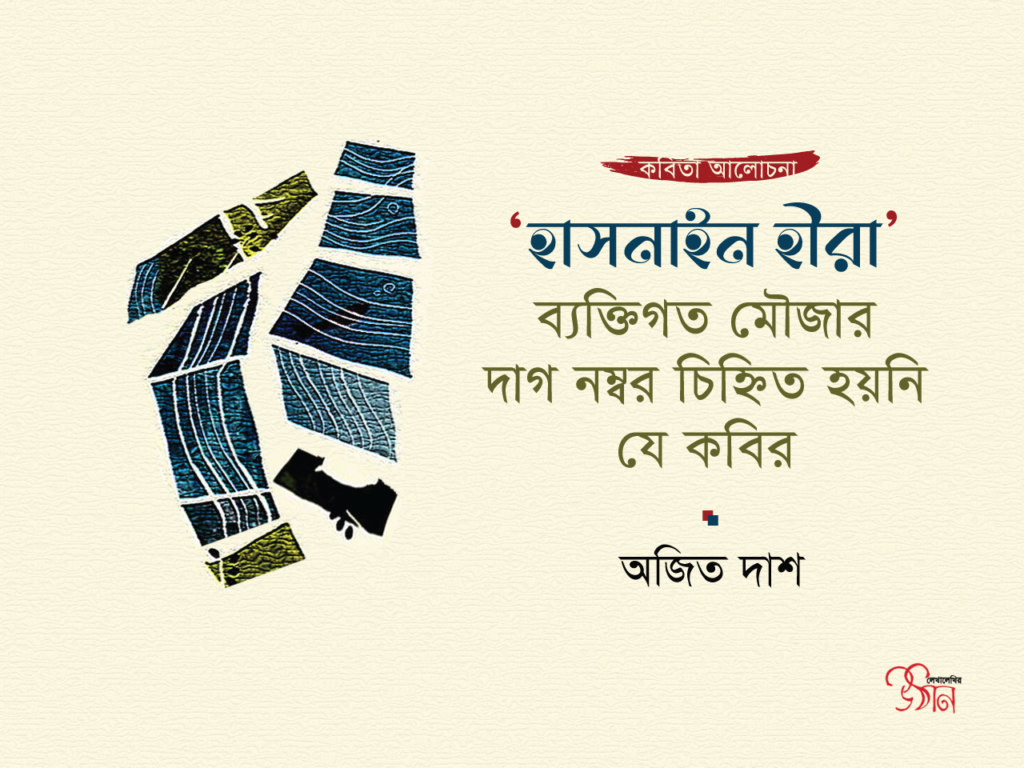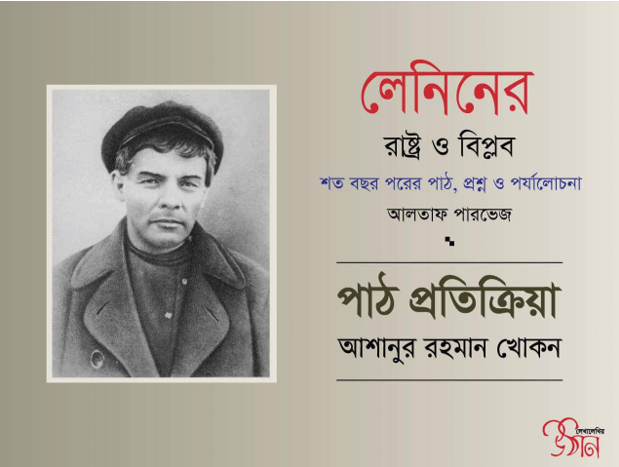‘…ঘড়িতে সাঁতার কেটে বয়স্ক পৌষমাস এলিয়ে পড়ে ঘুমবালিশে। জন্মের কাছাকাছি, মৃত্যুর পাশাপাশি খুব বেশি বড় করার মতো হাতে কোনো চানরাত নাই। ফের সকালে তবু জুঁইফুলের প্রেমে পড়ে যাই। বিষাদ ও বিষ্যুদবার এড়াতে এড়াতে মোহ থেকে পাঁচহাত দূরে সরে আসি। অবসর যেন ছুঁয়ে ফেলতে না পারে দীর্ঘতম হাসির কারণ। প্রেম ও প্রার্থনার পরিপূরক উত্তীর্ণ হাসিটাকেও ভালোবাসি।’
– শরীর একটা উত্তীর্ণ পাতার বিবরণ / বাঁক বাচনের বৈঠা
হাসনাইন হীরা’র কবিতা নিয়ে দু-চার কথা লিখতে চাওয়া আমার জন্য যতটা সহজ আবার ঠিক ততটা কঠিন। সহজ কারণ তাঁর কবিতার পঙক্তি আমাকে অপহরণ করে। কবির সহজিয়া বোধের প্রস্রবণে আমি আক্রান্ত হই। আর কঠিন কেননা ‘যথার্থ কবিতার’ তন্দ্রা থেকে বের হতে না পারলে অনর্গল বলতে চাওয়ার প্রবণতা ঠিক প্রয়োজনীয় কথাটাও কখনো কখনো আড়াল করে দেয়।
যথার্থ শব্দটা আমি সচেতনভাবেই উল্লেখ করেছি। আশির দশক পরবর্তী বাংলা কবিতার জৌলস সংকুচিত হতে হতে নব্বই পরবর্তী এখন এমন এক জায়গায় এসে মাথা ঠুকেছে যেখানে কবিতার পাঠকের নাগাল পাওয়া বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। বলতে দ্বিধা নেই, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিষয়টি এখন নিতান্তই ব্যক্তিচর্চা বা আত্মতৃপ্তির জায়গায় এসে ঠেকেছে। আমাদের প্রচলিত সামাজিক কাঠামোতে কবিতা কিংবা ফিকশন রচনার এখন আর তেমন কোনো মূল্য নেই। কবিতা লেখা এখানে তাসের ঘর নিয়ে খেলা করার মতো একটি বিষয়। কবিতার এই দুরূহ পথ তৈরি করার ভূমিকায় যেমন সমাজের ‘কালেক্টিভ টেস্ট’ এর অবদান রয়েছে তার চেয়ে বেশি অবদান লিটল ম্যাগাজিন ও দৈনিক পত্রিকার সিন্ডিকেট সাহিত্য। এই সিন্ডিকেটে বহু বিচিত্র প্রতিভার সেলিব্রিটি কবিরা থাকলেও নেই কোনো কবিতা। তাই এমন সিন্ডিকেটের পর্দা সরিয়ে যথার্থ কবিতার নাগাল পাওয়া কিংবা চিনতে পারার ধাপটি পাঠকের জন্য দূর্ভাগ্যের।
কবি হাসনাইন হীরা ঠিই এমনই সময়ে দাঁড়িয়ে তার স্বভাবের অনুকূল তার আত্মউপলব্ধির পথে হাঁটতে হাঁটতে লিখছেন-
১.
‘যাওয়া’ না থাকলে ঠিকই ফিরে আসতো হাওয়া
টবের ভেতর বড় হওয়া ফুলগাছটাও
বেরিয়ে পড়তো প্রসন্ন জানালার দিকে।
২.
রেলগেটের পাশে হাত পেতে ছিল সদ্য ফোটা ফুল
অনেকটাই মানুষের মতো;
হাতে হাত রেখে বললাম, দাঁড়িয়ে আছ কেন?
ভেতরে আসো, ভেতর থেকেও বাহির দেখা যায়।
৩.
সুদূরতার মতো তাকানোর টি-শার্ট পড়ে
মানুষের জায়গা নিয়েছে টাকা
টাকার জায়গা নিয়েছে মানুষ
ভালো থাকার জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে;
৪.
কফিনের ধাঁচে বেজে চলেছে একা একটি গিটার
সুর নেই, যতটুকু আওয়াজ সবটুকুই অন্ধকার।
– আয়নাতে যা দেখা যায় না / বাঁক বাচনের বৈঠা
নিজে কবি হলে, কবিতা নিয়ে আলোচনা করার কিছু চমৎকার সুবিধা আছে। সেটা হলো, কবির ভাবনাকে কিংবা কবিতাকে বিশ্লেষণের ঠিক কাছাকাছি পথটাতে যাওয়া যায়। মানে চিহ্নিত করা যায়।
পুজির ক্লেদযুক্ত বিচ্ছিরি প্রকান্ড মূর্তির সঙ্গে প্রতিযোগী জীবনের সেলাই খুলতে খুলতে কবি যখন সদ্য ফোটা ফুলকে বলেন, ‘দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে আস, ভেতর থেকেও বাইরে দেখা যায়’ তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না এই কবির ঝোঁক আমাদের ‘স্বরূপ-সন্ধানের’ ডাক দেয়।
কথা, শব্দ, অক্ষর, এই জগত সংসার আমাদের কি দেয়? এক মায়ায় আচ্ছন্ন করে রাখে। এইখানে একজন বড় কবির সার্থকতা হলো তারা আমাদের এই মায়ার জগতে ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে ডাক দেন। বাহির থেকে ভেতরে ডাক দেন যেখানে জগত সংসারের দ্বার খুলে যায়। কবি হাসনাই হীরার কবিতায় খুব সুস্পষ্টভাবে এই ডাক পাওয়া যায়। তিনি নিজের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও ডেকে নিয়ে যান। যে পথে আমরা ভাল থাকার পথটুকু কুড়োতে কুড়োতে যেতে পারি। আনায়াসে পথ হাঁটি। কবি এই সহজ কাজটিই করেন নিজেকে ভাঙ্গিয়ে কবিতায় বিছিয়ে দিয়ে। আমি মনে করি এটাই সহজ কবিতা, সহজিয়া কবিতার বৈশিষ্ট্য।
কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ বাঁক বাচনের বৈঠায় এমন টুকরো টুকরো ভাবনা আর কথার তরঙ্গ পাঠকের দিকে তীব্রভাবেই সঞ্চারিত হবে।
ত্রিপিটকে ভাগ করা কবির এই কাব্যগ্রন্থের তিনটি পিটকের নামই ভীষণ মনকাড়া, শব্দ এবং ভাবনায়। পুরো কাব্যগ্রন্থটিতে যদিও আমার সবচেয়ে প্রিয় অংশ হয়ে উঠেছে, ‘পাখি ও পাতার টেলিপ্যাথি’ কিন্তু শুরুর অংশ ‘বিনুনিবিতা’ আর শেষের অংশ ‘পরিব্রাজক সাবানের ফেনা’ কবির শব্দ, ভাষা, চিত্রকল্প, মেটাফোর ইত্যাদি নিয়ে এক ভিন্ন রকমের স্পন্দন, আবহ আর জগত তৈরি করবে পাঠকের মনস্তত্ত্বে। লাল পিঁপড়ের মতো পাঠক ভীড় করবেন ‘শিল্পের দোকানে।’
কবিতার এক্সপেরিমেন্টের নামে, এই সময়ে ঢাকার গোষ্ঠীবদ্ধ পিঠ চাপড়ানো কবিরা যে বর্জ্য নিষ্কাশন করেন সেখানে কবিতার কমপ্লিট কোনো ভাবনা থাকে না। খুবলানো শব্দ আর বাক্য জোড়াতালি দিয়ে তারা সাঁতার কাটতে চান মূলত নিশ্চিত ভারহীন জ্ঞাতিজনদের সুইমিংপুলে। বিপরীতে হীরার মতো কবি ভারহীন জ্ঞাতিজনের সুইমিং পুলে সাঁতার না কেটেও এক্সপেরিমেন্ট করেন কবিতায় ‘কমপ্লিট ভাবনা’ তৈরির মাধ্যমে। অখন্ড ভাবনার সঙ্গে শব্দ, বাক্য আর চিত্রকল্পকে কোনো প্রত্যন্ত পাহাড়ি আদিবাসীর হাতের আঙ্গুলের মিহি কৌশলে তৈরি ঝুড়ির মতো বুনে ফেলেন। ফাঁকি নেই, প্রতিনিয়ত চেষ্টা আছে। কেন? কারণ চিবিয়ে খাওয়া অর্ধেক জীবনে এই বুনন তার নিত্য প্রয়োজনীয় সংসারের জিনিসের মতো। ফলে সেটাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলেও সেখানে পাঠকদের ভীড় করার মতো বাতাসা পাওয়া যায়।
‘…স্বপ্নের দামে এক প্যাকেট জোছনা কিনে খাই। প্রার্থনার ঝালফ্রাই কিংবা কিসমিস দানার ভোর নাগালে না পেলে চিবিয়ে খাই অর্ধেক জীবন। অর্ধেক কান্নাকাটি আরো বেশি মাতাল করে তোলে, হেসে ওঠে মদিরতার গেলাস। বিষাদের বিদ্যুৎ চমকানো দুপুরে কৃচ্ছতার ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে এলে জানা যায় অন্ধসময়ে মৃতরাই বীর্যবান, জাদুর বাক্সো খুলে দংশনের ভয় দেখায়।’
– শূন্যতার রূপক/ বাঁক বাচনের বৈঠা
সম্প্রতি এই সময়ে বেশ কিছু পপুলার তরুন কবিদের কাব্যগ্রন্থ পড়ার সুযোগ হয়েছে। প্রথম দশ-পনেরটি কবিতা ছাড়া বইয়ের প্রায় কবিতাগুলোই যেনো সেই কবিতাগুলোর পুনর্ভাঙ্গন। একঘেয়ে। পড়তে পড়তে ক্লান্তি চলে আসে। কিছু কবিদের দেখা যায় নির্দিষ্ট কিছু শব্দ আর সংস্কৃতির মোহে পড়ে পঙক্তির পর পঙক্তি লিখে চলছে। একই ভাবনাকে ভিন্ন অনুষঙ্গে নিয়ে এসে চমক দেখানোর চেষ্টাও করছেন কেউ কেউ। নির্দিষ্ট কিছু শব্দকে ভাঙ্গিয়ে লেখার প্রবণতাও হাল আমলের অনেক কবিদের মধ্যে দেখা যায় আর সিরিজ নামের কবিতা দিয়ে তো যা ইচ্ছে তাই লিখছে। এর একটা কারণ অবশ্য সহজেই কবিতা (কবিদের) যাপিত জীবনের মধ্যে ধরা না দিলে, সেটিকে অস্বীকার করে জোড় করে লিখতে চাওয়ার প্রবণতা। এই বৈশিষ্ট্যটি গদ্য রচনার ক্ষেত্রে যতটা সহযোগী কবিতার ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত। অবশ্য, আমাদের যা দিনকাল তাতে এই লেখাটুকুও যেনো থেমে না যায় তাই উৎসাহ না দিয়ে থাকা যায় না। পাশাপাশি যথার্থ কবিতা খুঁজে বের করার অভিযানও চালিয়ে যাওয়া চাই। যে অভিযানের সফলতায় পাওয়া যেতে পারে এমন ‘সহজ কথামালা’
ভেতরে গিরিখাত, লাবণ্যে নদী
স্থল ও জলে তুমি একাকার…।
আমি সকালের সমার্থক অনুভূতিশীল
শব্দ ও শিশিরের দ্রবণ।
পালক ছড়ানো পরাগের বিলে
নির্জনতার আলো হয়ে সাঁতরাই
অনাবৃত আনন্দের ধারায়।
সাঁতারের শ্বাস থেকে মূহু মূহু
আঁছড়ে পড়ে চাঁদ,
চাঁদেরা বিছা খুলে ঝরনা হয়ে যায়…।
-সহজ কথামালা/ বাঁক বাচনের বৈঠা
কবিতায় একটা পূর্ণ ছবি, দৃশ্যকল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবনার ছন্দোবদ্ধ না হলে সে কবিতায় প্রাণ থাকে না। কবিতা নিয়ে এই কথাগুলো যখন লেখার চেষ্টা করছি ঠিক তার আগেই হাসনাই হীরার কবিতা এইসব তোয়াক্কা না করেই দ্রুতগামী এক যানে উঠে বসেছে দীর্ঘপথ পাড়ি দেবে বলে। আমি আটকে দিয়ে বলার চেষ্টা করি আরে ভাই কোথায় যাও একটু থামো ঠিক তখন বাঁক বাচনের বৈঠা থেকে কবি আমাকে বলেন-
হাসি-খুশি, জন্ম-মৃত্যু, ধার-দেনা আর
প্রেম ও ঘৃণার মতো সমযোতাহীন
পৃথিবীটা ঘুরছে আমার মাথার ভেতর।
বিন্দু থেকে বিস্মৃতি
প্রতিদিনকার সংবাদ প্রতিদিন
পড়ি, ছিঁড়ি আর উড়িয়ে দেই দূর্লভ হাওয়ায়।
একটা আলাপের হাত থেকে
আরেকটা আলাপের হাতে গিয়ে গল্পটা
রেললাইনের মতো আরো বেশি দীর্ঘ হতে থাকে…।
-লাইফ ইজ ট্রাভেল ওয়ার/ বাঁক বাচনের বৈঠা
আমি বুঝতে পারি, কবি এই দীর্ঘ পথে বিনা সংকোচ কাউকে তোয়াক্কা না করে চলতে থাকবেন শূন্যতার দিকে স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে। যে শূন্যতায় সব মিলিয়ে গিয়ে থাকবে এক অসীম পাওয়া কারণ তিনি ‘মার্বেল রঙের ছোটখাট একটা পৃথিবী নিয়ে ভাবেন। জোড় করে নয়, কিংবা কবি হওয়ার জন্যও ভাবেন না। তার এই ভাবনা মজ্জাগত, তাই কবি এখানে আফসোসের স্বরে বলেন, ‘আহা শেখার যদি কোনো আলাদা বয়স থাকতো।’
কবিতাকে ছিঁড়ে, খুঁড়ে সমালোচনার মাধ্যমে কবিকে রাজ-আসনে তোলা কিংবা ঘর ছাড়া করার মতো তত্ত্বজ্ঞান আমার নেই। সাধারন একজন পাঠক হিসেবে মনে হয় কবিতা যে পুনর্পাঠের দাবি করে ফিরে ফিরে কবির ভাবনার কাছে নিয়ে যেতে চায় সেটাই একজন কবির উল্লেখযোগ্য সার্থকতা। পাঠক এই কবির কবিতা পাঠ করে তার কাব্য ভাবনার কাছে ফিরে আসবেন এই আশ্বাসটুকু তাদের দিতে পারি।
আরেকভাবে বলা যেতে পারে, পরিধিকে বৃত্তের বাইরের অংশ ভেবে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হওয়ার যে গতি পরিধির স্বকীয়তা বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীভূত হতে চায় সেখানে বৃত্তের আসল অবয়বটি নিশ্চিতভাবেই বাধাগ্রস্থ হয়, তলিয়ে যায়। বাঁক বাচনের বৈঠা হাতের কবি সচেতনভাবেই সেই কাজটি এড়িয়ে গিয়ে আটপৌরে শব্দ আর ভাবনা নিয়েই স্বতঃস্ফূর্তভারে তাঁর কবিতার বৃত্ত তৈরি করেছেন কোনো নির্দিষ্ট চূড়াকে কেন্দ্র না করেই। পাঠক খুঁজতে চাইলে এমন অসংখ্যা পঙক্তি খুঁজে পাবেন কবির চলন দেখে মনে হবে যেনো সদানিড়া আর সেখানে তরতর করে ভেসে চলছেন কবি নিজেই। ফলে কাব্যগ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কবির যে ভেসে চলা তাতে বিন্দু পরিমাণ একঘেয়েমী নেই। বরং কবির চরাচর ব্যাপ্তি তাকে ক্লিশে না করে দিয়ে বরং পাঠকের জন্য নতুন নতুন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দিয়েছে। কবির বহমান ধারা কবির গন্তব্যে
পৌঁছুলেও এমন কবিতার ক্ষেত্রে পাঠকের সবচেয়ে বড় অর্জন বা সুবিধে হলো পাঠক সেখান থেকে নিজের ঘাট খুঁজে নিতে পারেন সহজেই।
‘…বিস্ময় ও বিষাদের চশমা খুলে হেঁটে আসবে সাঁকোপাতাঘুম। বৃক্ষের মোড়কে এই নীরবতা একদিন মানুষের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। আপনি কার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হে অ্যানড্রয়েড মেঘের পুরাণ!…
…কথার ভেতর কথা ঠুকলে অঙ্ক ভুলে যাই। ভুল অঙ্কে ফণা ভাঙে সর্পিলসময়। জানেন তো, এই সকল জীবন ওই সকল সময়ের ফটোকপি! কোনো আওয়াজ নেই, অমরতা নেই; সমরতার পাশে নিজ নিজ ইশকুল খুলে ভেবে দেখুন, আপনার জুতো আপনার চেয়ে ছোট না বড়?’ – (টকশো/ বাঁক বাচনের বৈঠা)
‘রঙহীন দুপুরের ছায়া কুড়াতে গিয়ে পেয়ে যাই মেঘফুলের ধারণা। আকাশমাতার বুকের ভেতর পাথরবেলা ডুকরে ডুকরে ওঠে। ছায়া দেখিয়ে নদীও সমুদ্র হতে চায়; হেসে ওঠে পালকবাদী হাওয়া।’ – (ট্রাম কার্ড/ বাঁক বাচনের বৈঠা)
‘জামপাতার মতো নির্ধারিত কোনো ঠিকানা নেই আমার। কামারশালার জীবন নিয়ে তাই গড়িয়ে যায় ঋতু। বিস্মৃতি মোড়ানো সেতুর উপর শ্বাশত রোদ বুক খুলে দাঁড়ায়। চাঁদের ভাষায় মুখ তুলে বলি চোখ খোল সামুরাই! আমিই তোমার একমাত্র টিপসই ঊর্ধ্বকমার ভেতর সরলতার মোম জ্বেলে রাখি। কোটি কোটি বছরের হ্রেষাধ্বনি ধরে আছি বুকের মাজারে। দাগ নম্বর চিহ্নিত হলে ধরে নিও, পথের পাশে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত কাঁচলই আমার ব্যক্তিগত মৌজা।’ – (ব্যক্তিগত মৌজা/ বাঁক বাচনের বৈঠা)
উপরোক্ত কবিতাগুলোর উদ্ধৃতি থেকে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে কবির ভাষাস্রোত কিভাবে আমাদের কাব্যস্রোতের দিকে ঠেলে দেয়। আর মনযোগী হয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেখানে জাদু-বাস্তবতার এক পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই জাদুবাস্তবতা কোনো ধার করা জাদুবাস্তবতা নয়, নয় কোনো রেপ্লিকা। এখানে আছে আমাদের নিজস্ব আধুনিকতার ভিত্তি। যাকে আমরা একান্ত দেশীয় বলতে পারি। কেননা এই দেশীয় আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যই হলো তার ধারাকে আটকে রাখা যায় না। তার চলমান যাত্রা তাকে কিছুতে সরিয়ে দিতে পারে না গন্তব্য থেকে।
আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ইউরোপীয় আধুনিকতার ধারাকে আমাদের সাহিত্যে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া হয় কিন্তু সেটা যে সত্য নয় তা আরও স্পষ্ট হয় আমাদের নিজস্ব আধুনিকতার পথটুকু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে। সে আধুনিকতার হাত ধরে আমাদের জীবনে, যাপনের পথ বেয়ে এগিয়ে গেলে কত বিচিত্র দর্শন আর জীবন আমাদের সমৃদ্ধ করবে সেগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। আপাত বিজ্ঞপ্তি প্রিয় মনকে শুনাতে পারি-
‘ঘোষণা ছাড়াই উল্টে গ্যাছে পথ। পথের পাশে শপথের পরিত্যাক্ত হাড় বাজাতে গিয়ে আমি লাই দিয়ে ফেলেছি নদীর স্রোত, উদীয়মান আকাশের মন। সকালের সাথে মেলাতে চেয়েছি ফুল ফোটার আওয়াজ। অতঃপর হাতের উপর সূর্যদয় নিয়ে হেসেছি, খেলেছি, তামাশাও করেছি। মূলত লুকাতে চেয়েছি অন্ধকার।’ – (জরুরী বিজ্ঞপ্তি/ বাঁক বাচনের বৈঠা)
কবি হাসনাই হীরার সঙ্গে আমার পরিচয় ২০১৩-১৪’র দিকে। এরপর আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক, আজকে পর্যন্ত এগিয়েছে। কবির বাঁক বাচনের বৈঠা কাব্যগ্রন্থটি জেমকন তরুন পুরস্কার প্রাপ্তির আগে ২০১৮ অথবা ২০১৯ এর বই মেলায় বের করার একটা প্রস্তুতিও তিনি নিয়েছিলেন। সে বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত আলাপও হয়েছিলো। আমার মনে পড়ে, হীরা ভাই আমাকে এক রাতে ফোন করে দীর্ঘ আলাপ শেষে বলেছিলেন, ‘পুরস্কার পাওয়া তো আমার উদ্দেশ্য নয় অজিত ভাই, আপনি সেটা জানেন। আমি এও জানি হয়তো তেমন কিছুই হবেই না। বইটা তো আসছে মেলায় কোনো না কোনো প্রকাশনী থেকে বের করবোই। যদি এখানে নির্বাচিত হয়ে যায় তাহলে প্রকাশ করার খরচটা অন্তত আমার বেঁচে যাবে। প্রকাশনী খোঁজ করার ঝামেলা পোহাতে হবে না।’ কিন্তু কবির প্রত্যাশার বাইরে গিয়ে সেটা হয়েছে। তিনি পুরস্কারটি পেলেন। তার কবিতাকে পুরস্কৃত করার মধ্যে দিয়ে নির্বাচকরা মূলত বাংলা কবিতার ধারাকে এই দুঃসময়ে আরও একধাপ এগিয়ে দিলেন।
আমাদের পুরস্কার সংস্কৃতি পাঠকের নজড় কাড়ার সঙ্গে কখনো কখনো ব্যক্তির সৃষ্টিশীল কাজকে সীমাবদ্ধ একটি গ-িতে আটকে দেয় এবং এমনভাবে চিহ্নিত করে যা সৃজনশীল যেকোনো লেখক, সাহিত্যিকদের জন্য বিড়ম্বনার ও পীড়াদায়ক।
আক্ষরিক অর্থে হাসনাইন হীরা পুরস্কারটি পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমি তাকে মোটেও পুরস্কার প্রাপ্ত কবি, কিংবা বাঁক বাচনের বৈঠা পুরস্কার প্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ এমন ট্যাগ লাগিয়ে চিহ্নিত করতে নারাজ। কারণ এই কাব্যগ্রন্থটির অবস্থান আমার দৃষ্টিতে ‘পুরস্কার ট্যাগ’ ছাপিয়ে আরও একধাপ এগিয়ে। আমি এই কবিকে গন্ডির ভেতরে আটকে রাখতে চাই না কারণ তার কবিতা প্রস্রবণের মতো। আমার বিশ্বাস তিনি নিজেও সেটিকে অতিক্রম করে গেছেন ইতিমধ্যে। কারণ তিনি নিয়ত পুরাতনকে ভেঙ্গে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, শব্দ, মেটাফোর নিয়ে কবিতায় উপস্থিত হন। সম্প্রতি সাহিত্য সাময়িকী ‘কালের খেয়ায়’ প্রকাশিত হওয়া তার একটি কবিতা পড়লে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে কবি তার চলমান সময়, জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকেও কিভাবে কৌশলে তার শব্দে ক্রিয়াশীল করে তুলেছেন-
‘মেঘেদের কেককাটা উৎসবে মেতে আছে আর্দ্র বাতাসের ছুরি। দড়ি ছেঁড়া বাছুরের মতো এই মেঘেদের মনেও আত্মসমালোচনার ভয় নেই। তোমার তুড়ি বাজানো শহরে কদম ফোটার আয়োজন এখন আরোপিত মনে হয়। বর্ষার ধারাবাহিকতাও অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক নদীনিভর। বর্ধিত বৃষ্টির বিরহ তাই ভারী করে তুলেছে তোমার মুখ। অথচ হালকা হওয়ার অনেক গল্পই গড়িয়ে গেছে নিজেদের দিকে …।
হ্যাশট্যাগ লাগিয়ে আর শিথিল করা যাচ্ছে না ভাঙনের বৈভব। চেপে যাওয়া অনেক ঢেউ অসন্তোষের অভিযোগ করে আছে। আঞ্চলিক আন্তরিকতায় বড় কোনো ঘটনা নেই বলে সম্পর্কের সমুদ্রগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর আমি নির্বিবাদ রোদের মতো বেল আইকন চালু রেখে অনুবাদ করে চলেছি তোমার ভিজা যাওয়া পৃষ্ঠাগুলো।
-বিরাগী বর্ষার অনুবাদ / সমকাল, ২৪ জুন ২০২২
আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রম উন্নয়নে অভাবনীয়ভাবেই বদলে যাচ্ছে আমাদের ভাষা ও প্রকাশ। স্বাভাবিকভাবে কালের নিয়মে আমাদের চলমান বাস্তবতা যখন অনেকটা দ্রুত গতিতেই বাঁক নিচ্ছে তখন ভাষার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকা একজন কবি সেই কবিতাটিই লিখবেন যা তার সময়ের চৌহদ্দির ভেতর দিয়ে ধরা দেয়। এই ভঙ্গুর সময় যখন অন্ধকারে পরিবৃত কোথাও কোনো আশার আলো দেখি না, শুভের চিহ্ন নেই হাসনাই হীরা তখন পালক খসিয়ে খসিয়ে উড়ছেন আলোর দিকে। এই পালক খসানো তার কাব্যে এক পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে বদলে যায় ক্রমশ নতুনের দিকে।
আমি চাইলেই তার কাব্যগ্রন্থের শুরু থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত যেকোনো কবিতার প্যারা কিংবা বাক্য নিয়ে সহজে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারি যা হয়তো খুব সহজেই এই সময়ে অন্য কারো কাবগ্রন্থ নিয়ে হয়ত সম্ভব নয়। কেউ থাকতে পারেন এবং আছেন। সুযোগ পেলে তাদের নিয়েও আমার মূল্যায়ণ থাকবে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করার মতো যে, ভাষার প্রতি আবেগপ্রবণতা একজন কবির সহজাত বিষয় কিন্তু এই আবেগপ্রবণতা অনেক কবিকেই লক্ষচ্যুত করে। কিন্তু এই কবি তার আবেগপ্রবণতাকে এদিক-ওদিক টলতে দেননি ফলে তা হয়ে উঠেছে কবিতায় যথাযথ। ‘উপলব্ধির চন্দ্রবিন্দুর’ শেষে দেখা যায় কবি লিখছেন-
‘মানুষ’ বুঝতে গিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে যায় মানুষ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায় রাষ্ট্র। আমিও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাবি, রাষ্ট্র ও মানুষের মাঝে যে ফাঁকা জায়গায়টা, ওটা এখন কার বাড়ি?
এমন করেই কোথাও কোথাও কবিকে দেখা যাবে তিনি শুধু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই থেমে থাকেননি বরং প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত কবি ধাওয়া করে চলছেন একটা আলোক বিন্দুকে। মলাট বন্ধি বইয়ের পৃষ্ঠার মতো এক বাস্তবতা থেকে আরেক বাস্তবতায় কবির অগ্রসর হওয়া কোনোভাবেই একরৈখ নয়।
এ পর্যন্ত উদ্বৃত কবিতাগুলোর ভেতর দিয়ে পাঠকের এটুকু বুঝতে নিশ্চই অসুবিধা হবে না যে তিনি জোড় করে পাঠকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করতে চান। অথবা বলতে চান, ‘এই দেখ আমি কবি, আমি সত্যদ্রষ্টা। আমি সময়ের অনুলিপি তৈরি করি, তোমরা জোড় করে পড়ে তা বুঝে নাও, শিল্পের স্বাদ নাও। কবিতা বরাবরই বিমূর্ত! আস বিমূর্তরে কর নমস্কার।’
কিন্তু কবিতার সেই বিমূর্ততা কি? কবিতার বিমূর্ততা মূলত তার নিরাভরণ ভাষা, প্রকাশ এবং সহজাত বোধের বিচিত্র ভঙ্গিমায় বলা ছবির ক্যানভাসে এক চিরন্তনের দিকে। সেখানে কবির জন্ম এবং জন্মান্তর গেঁথে যায় এক সূত্রে আর পাঠক সেখানে হাত বাড়াতে পারেন। পাঠকের অধিকার তৈরি হয়।
আমার নানামুখী কাজের চাপে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ঠিক আলোচনা না লিখলেও নিজের অনুভূতির ভিত্তিটুকু লিখতে চাইলেও হয়ে উঠে না। হাসনাইন হীরার কবিতা নিয়ে দীর্ঘদিন কিছু লেখার ইচ্ছে থাকলেও সেটি হয়ে উঠেনি কিন্তু সম্পাদক পুলক হাসান নাছোড়বান্দা। খেয়ার এই সংখ্যার জন্য কবির নির্বাচিত কিছু কবিতা সহ কবির কবিতা নিয়ে দু-চারটি কথা লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। সেজন্য কবি ও সম্পাদক পুলক হাসানের কাছে আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।
সর্বশেষ যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলাপ করে এই লেখাটি শেষ করতে চাই তা হলো, কেন এই কবির ‘ব্যক্তিগত মৌজার দাগনম্বর চিহ্নিত হয়নি?’ তার উত্তর কবি নিজেই দিয়েছেন তার কবিতায়-
‘আমিই তোমার একমাত্র টিপসই ঊর্ধ্বকমার ভেতর সরলতার মোম জ্বেলে রাখি। কোটি কোটি বছরের হ্রেষাধ্বনি ধরে আছি বুকের মাজারে। দাগ নম্বর চিহ্নিত হলে ধরে নিও, পথের পাশে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত কাঁচলই আমার ব্যক্তিগত মৌজা।’
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তার ভক্তদের বরাবরই বলতেন ‘কামিনী কাঞ্চন’ চামচিকার বিষ্ঠার মতো। একবার গায়ে লাগলে সাত ঘটি জল দিয়ে ধুলেও গন্ধ যেতে চায় না! কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি হলো ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতা ব্যক্তিকে ‘অনন্তের উপলব্ধিতে’ নিয়ে যায় না। যে উপলব্ধি অড়হৎ হয়ে উঠার উপলব্ধি!
‘দাগ নম্বর চিহ্নিত হলে ধরে নিও, পথের পাশে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত কাঁচলই আমার ব্যক্তিগত মৌজা।’- দাগ নম্বর বা সীমানা চিহ্নিত হয়ে গেলেই কবির মৃত্যু হয়। কবি, কামিনী কাঞ্চনে নিজের সীমানা টেনে দেন। ভারতীয় স্পিরিচুয়ালিজমের এই দর্শনটিকে কবি হাসনাইন হীরা এই সময়ে কি সহজাত ভাবে নিজের বাহ্য জীবনের মধ্য দিয়ে তার কবিতায় প্রকাশ করেছেন।
কবি হলেন অনন্তের যাত্রী। তিনি চলতে থাকেন ব্রহ্মান্ড বুকে নিয়ে শাশ্বতের অন্তরালে। কোটি বছরের হ্রেষাধ্বনি বুকের মাজারে ধরে থাকার উচ্চারণ মূলত কবির পরিণত ভাবনা আর বিকাশের স্পষ্টতাকেই তুলে ধরে। আমরা খেয়াল করলে দেখবো, শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা রহস্য আর মেটাফোর নিয়ে উপস্থিত হলেও সেগুলো প্রতিনিয়ত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে আমাদের কাছে। আমি সেই চেষ্টাটিই এই সময়ে রাজধানী বিমুখ, একজন কবির মধ্যে দেখতে পাই।
হয়তো উর্দু সাহিত্যের কাব্যেশ্বর মীর তকি মীরের কবিতার মতো তার কবিতার কোথাও ধ্বনিত হচ্ছে বা হবে,
যদিও কবিদের মাঝে নির্জন কোণে বাস
তবুও আমার এই কবিতা জগৎ ছুয়ে গেছে।

অজিত দাশ
কবি ও অনুবাদক।জন্ম ১৯৮৯ সালে কুমিল্লা শহরে। শৈশব ও বেড়ে ওঠা গোমতী নদীর তীরে। কলেজ জীবন থেকেই যুক্ত ছিলেন লিটল ম্যাগাজিন 'দৃক' এর সঙ্গে। কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যয়ন শেষে বর্তমানে চাকুরিজীবী। বর্তমান আবাস ঢাকার মোহাম্মদপুর। কবিতা ও ছোটগল্পের পাশাপাশি ইংরেজী ও হিন্দি থেকে অনুবাদ করেন। হিন্দি থেকে বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি তার অনূদিত বাংলা থেকে হিন্দি কবিতা ইতিমধ্যে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ এবং দেরাদুন থেকে প্রকাশিত স্বনামধন্য লিটল ম্যাগাজিন ও অনলাইন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।
এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত বই দুটি। 'ওশোর গল্প (বেহুলাবাংলা, ২০১৮), 'প্রজ্ঞাবীজ (মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৯)। এ বছর নিজের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের পাশাপাশি বাংলায় হিন্দি কবিতা অনুবাদ সংকলণ এর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।