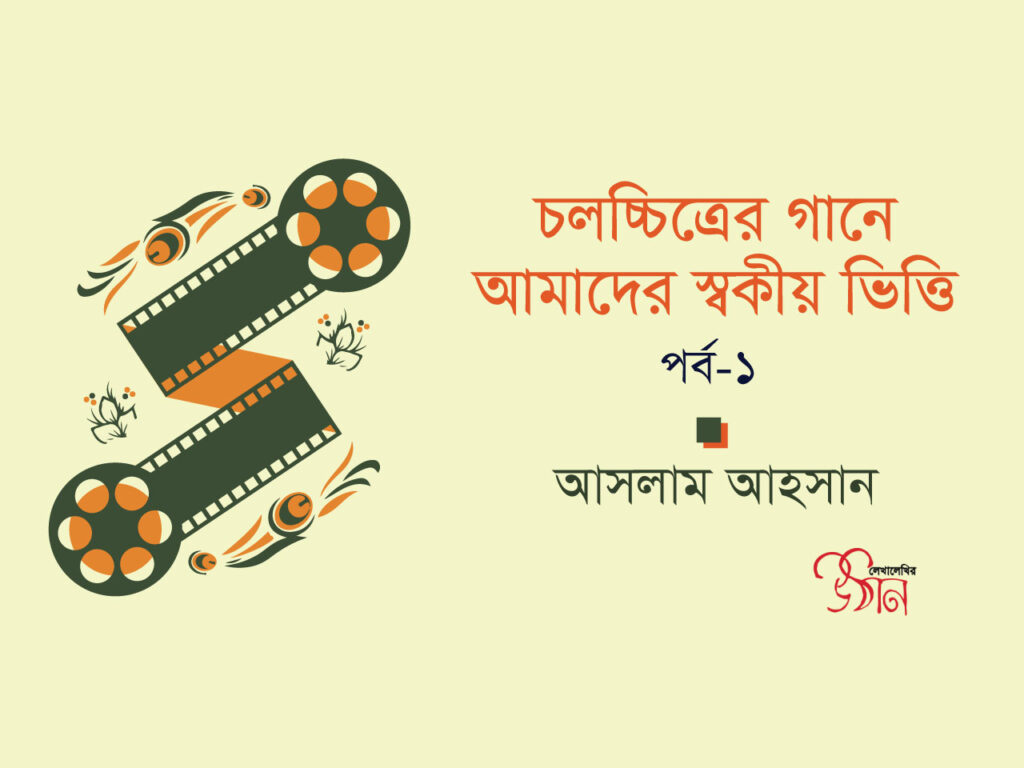মোটেও অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের গানকে একরকম ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। ভাবটা এমন: চলচ্চিত্রের গান? বাংলা চলচ্চিত্রের গান? তাও আবার ‘ঢাকাইয়া’ বাংলা চলচ্চিত্র? এই অবজ্ঞা মূলত অজ্ঞতাপ্রসূত। যৌক্তিক কারণ অবশ্য কিছু আছে। কিন্তু এত্তসব ‘আবর্জনা’ ঘাটতে কে নামবে বাংলা চলচ্চিত্রের গানের অভ্যন্তরে? স্বকীয়কতার খোঁজে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে ইতিহাসের পাতায়।
১
ষাটের দশকে শিল্প-সাহিত্য-সংগীতের যে সময়টাকে আমরা স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত করি, কারা ছিলেন সে সময়ের সারথী? সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আনোয়ার উদ্দীন খান, আসাফউদৌলা, মোস্তফা জামান আব্বাসী, সৈয়দ আব্দুল হাদী, ফেরদৌসী রহমান, সৈয়দ আহসান আলী সিডনি, আঞ্জুমান আরা বেগম, বুলবুল আহমেদ, রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, আবদুল্লাহ আল মামুন, মাসুদ করিম, কে জি মোস্তফা: এক কথায় নক্ষত্রসমাবেশ!
উক্ত ব্যক্তিবর্গের সবাই অবশ্য চলচ্চিত্র অঙ্গনে যুক্ত হননি যারা হয়েছেন, তারাও একসঙ্গে যুক্ত হননি, সময় সুযোগমতো যুক্ত হয়েছেন পর্যায়ক্রমে। অজস্র প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অনেক স্বপ্ন নিয়ে শুরুর কাজটা করে গেছেন আবদুল জব্বার খান। বহু ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে আমাদের চলচ্চিত্র যাত্রা। একটু খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাব— ১৯৩১ সালে খুব কাছাকাছি সময়ে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে উপমহাদেশের চলচ্চিত্র জগতে:
ক. ১৯৩১-এর ১৪ মার্চ মুক্তি পেল ভারতের প্রথম সবাক হিন্দি ছবি ‘আলম আরা।’
খ. ‘আলম আরা’ মুক্তির প্রায় এক মাস পর সে বছরই ১১ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায় প্রথম সবাক বাংলা ছবি ‘জামাই ষষ্ঠী।’
গ. একই বছর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (আজকের বাংলাদেশ) প্রদর্শিত হয় প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক ছবি ‘দ্যা লাস্ট কিস।’
পূর্ব পাকিস্তানে তখন ৯২টি চলচ্চিত্র হল। সর্বত্র ঢাকায় তখন উর্দু ছবির প্রচুর চাহিদা। ‘নাজ’ হলে চলত শুধু ইংরেজি ছবি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমদানীকৃত বাংলা ছবি চলত ‘রূপমহলে’। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১-এর পর পর্যন্ত ঢাকায় নির্মিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত উর্দু ছবির সংখ্যা প্রায় ৬২টি। জহির রায়হান, মুস্তাফিজ, এহতেশামের মতো পরিচালকদেরকে তখন উর্দু ছবিই নির্মাণ করতে হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হককেও তখন দেখা গেছে উর্দু ছবি (ফির মিলেঙ্গে হাম দোনো-১৯৬৬) পরিচালনা করতে। সৈয়দ হক অবশ্য ঐ একটি মাত্র উর্দু ছবিই পরিচলনা করেছিলেন। পরিবেশটা বাংলা ছবি নির্মাণের জন্য অনুকূল ছিল না মোটেই। পরবর্তী সময়ে জহির রায়হান এ বলয় থেকে বেরিয়ে আসেন।
২
কিন্তু সে তো পরের কথা। বিস্তৃত আলোচনায় যাবার আগে— ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’ (১৯৫৬) নির্মাণের নেপথ্যকথা প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার সচিবালয়ের পূর্ববঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ড. আবদুস সাদেক স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মী, চিত্রব্যবসায়ী, প্রদর্শকদের এক সভা আহবান করেন। অবাঙালি চিত্রব্যবসায়ী ফজলে দোসানী বললেন ‘এখানকার আবহাওয়া খারাপ, আর্দ্রতা বেশি। কাজেই এখানে ছবি তৈরি সম্ভব নয়।’ প্রতিবাদ করলেন আবদুল জব্বার খান: ‘কলকাতায় যদি ছবি হতে পারে তবে ঢাকায় হবে না কেন? […] মিঃ দোসানী আপনি জেনে রাখুন, যদি আগামী এক বছরের মধ্যে কেউ ছবি না করে তবে আমি জব্বার খানই তা বানিয়ে প্রমাণ করব।’ এমন বৈরী পরিবেশে আবদুল জব্বার খান চ্যালেঞ্জকে প্রথম প্রথম কেউ স্বাগত জানায়নি। কিউ. এম. জামান বললেন ‘ভুল করলে হে, চলচ্চিত্র তুমি করতে পারবে না।’ হাল ছাড়লেন না আবদুল জব্বার খান। নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

সংগীত পরিচালনার জন্য ১,৫০০ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হন সমর দাস। সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবে নেওয়া হয় ধীর আলী মিয়াকে। ‘সারথী’ ছদ্মনামে গান লেখেন আবদুল গফুর। গান গাওয়ার সম্মানী বাবদ আবদুল আলীমের সঙ্গে চুক্তি হয় একটি গানের জন্য ৭৫ টাকা, প্রতিবার যাতায়াত ভাড়া বাবদ ১ টাকা। চুক্তিপত্র অনুযায়ী মাহবুবা হাসনাৎ-এর সম্মানী নির্ধারিত হয় ৩টি গানের জন্য ৩০০ টাকা, যাতায়াত ভাড়া এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে। শেষ পর্যন্ত গান অবশ্য রেকর্ডিং করা হয় দুটি; মাহবুবা হাসনাতের কণ্ঠে একটি ‘মনের বনে দোলা লাগে’ এবং আবদুল আলীমের কণ্ঠে একটি ‘আমি ভিন গেরামের নাইয়া’। শান্তিনগরের ‘ইকবাল ফিল্মস’-এর অফিস রুমের দেয়ালে কাপড় টেনে গান দুটি রেকর্ডিং হয়েছিল রাত ১২টার পর, অনুকূল সাউন্ডলেস পরিবেশ তৈরি করার জন্য এছাড়া উপায় ছিল না।

লাহোরের শাহনূর স্টুডিওতে সম্পাদনার কাজ করা হয়। সেখানে গিয়ে নবীন পরিচালক আবদুল জব্বার খানকে অনেক বিড়ম্বনা সইতে হয়েছে, টিটকিরি শুনতে হয়েছে। সম্পাদনা দেখতে এসে ম্যাডাম নূরজাহান ‘মুখ ও মুখোশ’-এর নাম দিয়েছিলেন ‘মাখ্খন-টোস্ট!’ চরম বিশৃঙ্খলা ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে আবদুল জব্বার খান চলচ্চিত্র তৈরি করেই ছাড়লেন। চলচ্চিত্র তো তৈরি হলো। কিন্তু প্রদর্শনের জন্য হল পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ হল মালিকদের কাছে ইতোমধ্যে এরকম একটা খবর পৌঁছে গিয়েছিল যে, এটা কোন ছবিই হয়নি। ছবি দেখতে এসে অযথা দর্শকরা চেয়ার টেবিল ভাঙবে এটা তারা চাননি। অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই রাজি হলেন ‘রূপমহল’ প্রেক্ষাগৃহের মালিক কমল বাবু।
১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট মুক্তি পেল দেশের প্রথম সবাক ছায়াছবি ‘মুখ ও মুখোশ।’ অদম্য আবদুল জব্বার খান অবশেষে দেখিয়ে দিলেন কোনটা মুখ, আর কোনটা মুখোশ: সফল করে তুললেন তাঁর চ্যালেঞ্জ মূলত যা ছিল একটি জাতিসত্তার চ্যালেঞ্জ।
৩
বহুরকম কাহিনি নিয়ে নানা ধরনের চলচ্চিত্র হয়েছে এদেশে। মোটামুটিভাবে গানকে অঙ্গীভুত করেই এগিয়েছে আমাদের চলচ্চিত্র। সব ছাপিয়ে এখানে যা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বকীয়তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে— নিঃসন্দেহে তা লোককাহিনি, লোকসুর এবং লোকজ কথার গান। বাংলা লোকসুরের যে কী জাদু, বোম্বের চিত্রজগতে তা দেখিয়ে গেছেন শচীনদেব বর্মণ। শুরু থেকেই আমাদের চলচ্চিত্রর গান লোকসুরের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে। পাকিস্তানী ও ভারতীয় ছবির ভিড়ে আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র সগৌরবে টিকে ছিল এই একটি কারণেই। বাংলা ছবি তো বটেই, এহতেশাম পরিচালিত উর্দু ছবিগুলোর সুরেও ছিল বাংলা লোকজ সুরেরই স্পষ্ট প্রভাব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ‘চান্দা’ (১৯৬২) ছবির গানগুলোর কথা। গানগুলোর ভাষাই ছিল কেবল উর্দু। বিষয়বস্তু ও সুরের ঢং একান্তই বাঙালিয়ানায় ভরপুর। এক্ষেত্রে রবিন ঘোষকে পথিকৃৎ বলা চলে। রবিন ঘোষ সুরারোপিত ‘চান্দা’ (১৯৬২) ও ‘তালাশ’ (১৯৬৩) ছবির গানগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যায়, কেন পরবর্তীকালের সুরকার ও সংগীত পরিচালকগণ চলচ্চিত্রর গানে পল্লীসুরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশে যত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তার অধিকাংশই নায়ক-নায়িকাভিত্তিক এবং সে কারণেই প্রেম বা রোমান্স একটি বড় বিষয় এখানে। সে সূত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকের চলচ্চিত্রয় বহু প্রেমের গান তৈরি হয়েছে এখানে, অনেক গান বিখ্যাত হয়েছে, জনপ্রিয়তা পেয়েছে; কিছু গান উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কালের সীমারেখা।
বাংলা চলচ্চিত্রর লোকজগানে প্রেমচেতনা মৌলিক। অস্বীকার করা যাবে না যে, গ্রাম্য তরুণ-তরুণীর রোমান্স ভাবনায় স্থুলতা এসেছে কখনো কখনো। কিন্তু ‘মলুয়া’ (১৯৬৯) ছবিতে লোকমান হোসেন ফকিরের লেখা ওমর ফারুকের সুরে নায়িকা কবিতার লিপে আমরা যা শুনি, বিস্মিতই হতে হয়
‘এই জলেরই আরশিতে সই দেখি বন্ধুর মুখ
নিদয়া তুই হইস না সখি, ভাঙিস না সে সুখ
ঐ ছবি মোর মন কাইড়াছে চোখ সরানো যায় না ’

জলের আরশিতে বন্ধুর মুখের প্রতিবিম্ব দেখছে নায়িকা; সখির প্রতি তাই অনুনয়‘আর জলে ঢেউ দিও না।’ একই ছবিতে শাহেদ আলী মজনু রচিত লোকমান হোসেন ফকির ও সাবিনা ইয়াসমেনের যুগলকণ্ঠে গাওয়া একটি গানে পাই অদ্ভুত সুন্দর চরণ, জটিল মনস্তাত্তি¡ক বিশ্লেষণ। ঢেউয়ের দোলায় ডিঙ্গায় দুলছে একজোড়া মানব-মানবী, সেই সাথে তাদের মনও দুলছে। এমন মায়াবী লগ্নে একান্ত কাছে পেয়ে দুজনের মনোভাব কি তৃপ্তিতে ভরা?
‘দুই চোখেতে ঘুম আসে না
কাছে পেয়েও মন হাসে না
আকুল এ মন ব্যাকুল থাকে সদাই উচাটন
বন্ধু, কেন অকারণ ’
প্রিয়জনকে কাছে পেয়েও মন হাসছে না কেন? এ বড় জটিল মনস্তত্ত¡। প্রসঙ্গত কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি গানের মুখ উদ্ধৃত করা যায়
‘আমার দুখের বন্ধু, তোমার কাছে চাইনি ত’ এ সুখ
আমি জানিনি ত’ বুকে পেয়েও কাঁদবে এ মন বুক।’
আমাদের প্রথম দিককার চলচ্চিত্রর গানে যে রোমান্স ভাবনা ছিল, পরবর্তীকালে সেটা আরও বেশি পরিশীলিত ও বিস্তৃত হয়েছে।

নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত ‘নীল আকাশের নীচে’ (১৯৬৯) ছবিতে কবরী (নেপথ্যে ফেরদৌসী রহমান) যখন গায়, ‘সারা বেলা এত সুর নিয়ে/ নিজেরে কেমনে বলো রাখি লুকায়ে’ এবং বার বার দেয়ালে টানানো নিজের ছবির দিকে তাকায়, বুঝতে পারি জীবনে ‘বিশেষ কেউ’ এসে গেছে! তাই তো আয়নার বার বার নিজের মুখ দেখার ইচ্ছা, আগুন নিয়ে খেলার দুর্নিবার বাসনা। এই অবাধ্য ইচ্ছার কথাই বর্ণিত ‘গ্রাম্য’ কবির নিরাভরণ ভাষায়:
‘ইচ্ছা করে পরানডারে গামছা দিয়া বান্ধি
আইরং বাইরং কইলজাডারে মসল্লা দিয়া রান্ধি ’
দ্বিতীয় পর্ব পড়তে ক্লিক করুন