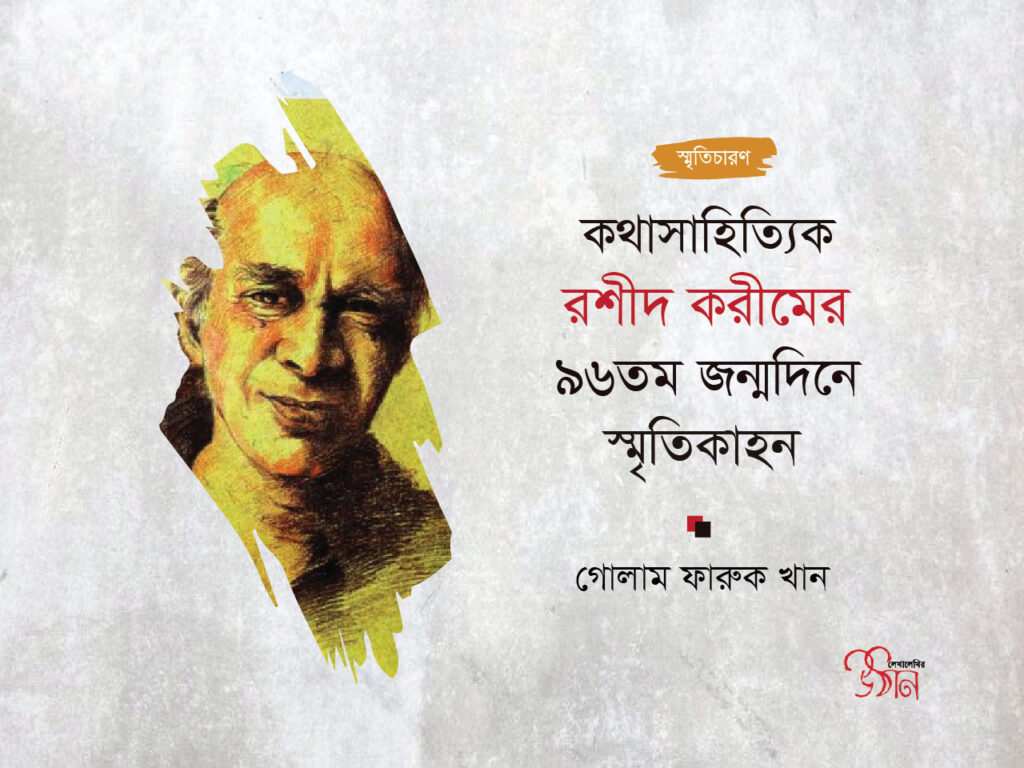‘বাংলা’ শব্দটির সাথে বাঙালি জনগোষ্ঠীর আত্মিক সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। অথচ শব্দটি মোটেও বাংলা নয়। সংস্কৃত শব্দ ‘বঙ্গ’ থেকে এর উৎপত্তি। ইতিহাসের ভাষ্য মতে আর্যরা উপমহাদেশের এই অঞ্চলটিকে ‘বঙ্গ’ নামে অভিহিত করতো। বঙ্গে বসবাসকারী মুসলমানেরা বঙ্গ শব্দটির সঙ্গে ফার্সি ‘আল’ প্রত্যয় যোগ করায় অঞ্চলটির নামকরণ হয় ‘বাঙাল’ বা বাঙালা’। জমির বিভক্তি বা নদীর ওপর বাঁধ দেয়াকে ‘আল’ বোঝানো হয়। যা নদীমাতৃক এবং ফসল উপচানো মাঠে সমৃদ্ধ অঞ্চলটির জন্য যথাযোগ্য নাম বলেই বিবেচিত হতো। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, “মুসলমান শাসনামলে বিশেষ করে ১৩৩৬ থেকে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত এবং ১৫৭৬ সালে মোঘলরা বাংলা দখল করার পরেও এই অঞ্চলটি বাঙাল বা বাঙালাহ নামেই পরিচিতি পায়।” মজার কথা হচ্ছে বাংলা, বাঙালা বা বাঙালহ এই তিনটি শব্দই ফার্সি। একটি সমৃদ্ধ ভূখণ্ড হিসেবে এই অঞ্চলের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজরাজাদের দখলদারিত্ব বহাল হয় এবং ক্ষমতাসীন রাজারা তাদের ইচ্ছে মাফিক বাংলাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। বিপুল নিয়ামতের লোভে কতবার যে এই অঞ্চলের দখলদারিত্ব কায়েমের হামলা চলেছে ইতিহাস তার সাক্ষী।
বাংলা, বাঙাল বা বাঙালা যে নামেই ডাকা হোক না কেন আদিকাল থেকে এটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে সমৃদ্ধ উপত্যকা এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় বদ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমানে সারা বিশ্বে বাংলা ভাষায় কথা বলে অন্তত ৩৭ কোটি মানুষ, যার মধ্যে ২৩ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বাঙালী জাতির ঐতিহ্য অন্তত চার হাজার বছর প্রাচীন। ভারতবর্ষে নানান জাতি গোষ্ঠির সভ্যতার যে বিবর্তন ঘটেছিল মধ্যযুগে, আর্থ ও সামাজিক অবস্থার যে রূপান্তর ঘটেছে কালে কালে তার মধ্যে বাংলা ছিল একটি অগ্রগণ্য নাম। মোগল রাজদরবারের যে কোন ফরমানে বাংলা শব্দটি লেখার আগে ‘ভারতের স্বর্গভূমি’ অভিধাটি যুক্ত করা হতো সম্মানের সাথে। যা বাংলার সমৃদ্ধ অবস্থানের অন্যতম একটি প্রমাণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা দখলের মাধ্যমেই তাদের ঔপনিবেশিক রাজত্ব শুরু করেছিল। বাংলাকে পরাজিত করার মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছিল। এমনই ছিল বাংলার প্রভাব।
বৃটিশ রাজত্বের সময় বাংলার এই প্রভাবকে কমিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে। ১৮৩৬ সালে প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বাংলার উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোকে আলাদা করে একজন লেফটেনেন্ট গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তারপর রাজনৈতিক (১৯০৫) অজুহাতের সম্মিলিত খগড়ের নীচে পড়ে বাংলা। ঘটে বঙ্গভঙ্গের ঘটনা, অঞ্চলটিকে দু’টুকরো করার ফলে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধিকেই শুধু বাটোয়ারা করা হয় না একই সাথে বহুবছরের একাত্মতায় ধরানো হয় ফাটল। রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাকে দুই অংশের বিভক্তির ক্ষত ইতিহাস শুধু নয় শত শত ভুক্তভোগী জনসাধারণ আজও বয়ে চলেছেন। রক্ত আর অশ্রুসিক্ত ইতিহাসের সে অধ্যায়টি এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয় বলে আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গে দৃষ্টি ফেরাবো।
দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে, এক সময় এই উপমহাদেশের মর্যাদার আসনে থাকা বাংলা আজকে হারিয়েছে তার অতীতের সমৃদ্ধি, ঐতিহ্য। ইতিহাসের পাতায় থেকে গেছে তার জৌলুশময় অতীতের কাহিনি। সেসব পাঠ করতে গেলে অনেক সময় হয়ত মনে হবে রূপকথার গল্প পড়ছি। আজ এই একুশ শতকে এসে বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যাটি বাদে তার আর কোনো মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নেই। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। আমাজনের কিণ্ডলে বই প্রকাশের যে ব্যবস্থা আছে সেখানে ভারতের চারটি ভাষাকে জায়গা দেয়া হলেও তার মধ্যে বাংলা নেই। আছে শুধু হিন্দি, মারাঠি, তামিল, মালায়ালম। মাত্র একশো বছর আগেও এটা কল্পনা করা যেত না। বাংলা ভাষার এই দুরাবস্থার জন্য দায়ী কারা সেটা গবেষণার বিষয়। কেবল ভাষা নয়, আরো নানান দিকে বাংলা ক্ষয়ে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। বাংলার অতীত ঐতিহ্যের অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে।
বাংলার উপর ভারতের অংশে যে আগ্রাসন চলছে সেখানে অন্যান্য প্রতিযোগী ভাষা সংস্কৃতির প্রভাব আছে, কিন্তু বাংলাদেশে যে আগ্রাসন সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের অবহেলাঘটিত। বাংলাদেশে প্রায় নিরঙ্কুশভাবে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখার সুযোগ থাকলেও সেটাকে অবহেলার সাথে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। বরণ করে নেয়া হয়েছে ভিনদেশী অনেক আচার-আচরণ। নিজেদের কৃষ্টির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাশীল যত্নবান না হওয়ার কারণে একটি সমৃদ্ধ জনপদ দিন দিন হতদরিদ্রে পরিণত হয়েছে। কত কত নির্দশন-কৃষ্টি যে বাংলা হারিয়ে ফেলেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতীতচারীতায় কেবল জানা সম্ভব হয় বাংলার একদা সুয়োরাণী থাকার ঠাটবাটের গালগল্প।
লেখার সূত্রে অগ্রগণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের একটা কথার প্রতিধ্বনি এখানে করা যেতে পারে- “আমরা বর্তমানে বাঁচি, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি, কল্পনা করি। পেছনে যেটা ফেলে আসি সেটা অতীত, তা নিয়ে যখন কথা বলি সেটা হয়ে যায় স্মৃতিচারণ। মানুষের জীবনে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ- অতীত, বর্তমান না ভবিষ্যৎ?” বর্তমান সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কেননা আমাদের জীবিত থাকাটা এ সময়ের সাথে সরাসরি জড়িত। কিন্তু বর্তমানের যে ভিত্তিটার উপর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা, তার অধিকাংশ অতীতের হাত ধরে সৃষ্ট। ঐহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি যা কিছু নিয়ে আমরা গর্ব করি তার শেকড় অতীতের মাটিতে পোঁতা। যুগের পর যুগ ধরে বাঙালি যা ধারণ ও লালন করে এসেছে। নানা ঐহিত্যবাহী পণ্য, রীতি-নীতি কিংবা আচার-আচরণে বাঙালির সংস্কৃতির ভাঁড়ার পরিপূর্ণ ছিল। ছিল বলছি এই কারণে বাঙালি তথা বাংলা থেকে তার অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে কিংবা হারানোর পথে। এই হারানোর তালিকা এত দীর্ঘ যার বর্ণনায় বিষন্নতার আলেখ্য লেখা হয়ে যাবে হয়ত।
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে অজর একটি গান উপহার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যে গান আমাদের আত্মার সাথে জুড়ে থাকে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে বর্ণিত বাণী’র হাত ধরে শুরু করা যাক বাংলার হারিয়ে যাওয়া অতীতের পথপরিক্রমা। এ গানের বাণীতে রবীন্দ্রনাথ যে বাংলার ছবি এঁকেছেন এখনকার বাংলার সাথে তার কতটুকু মিল পাই আমরা? কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক এক সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, শৈশবে তাঁরা যখন এই গানটি গাইতেন তখন চারপাশের পরিবেশের সাথে অদ্ভূতভাবে একাত্মবোধ করতেন। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে গানের বাণী’র সাথে একাত্ম হওয়ায় কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। কোথায় সেই নিবিড় শ্যামল শোভা, মায়ের ভাইয়ের স্নেহ! কোথায় মায়ের মলিন বদনের দিকে তাকিয়ে বুকে হাহাকার বেজে ওঠার প্রগাঢ় অনুভূতি! এই সময়ে দাঁড়িয়ে এর অনেকটাই অলীক মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় ভর করে এ গানের বাণী লিখেননি। তিনি যে সময়ে বসে গানটি রচনা করেছিলেন সেসময় বাংলার জল, বাংলার মাটি, মানুষের নিবিড়স্নেহ আর আন্তরিকতায় ঘেরা একটা পরিবেশ ছিল। কালের বিবর্তনে আজ যা আমাদের কাছে কল্পগল্প মনে হয়। শুধু যে পরিবেশের ভরন্ত জৌলুশটুকুই হারিয়েছে তা তো নয়; একই সাথে সেসময়কার মানুষের আন্তরিকতা, দেশকে সততার সাথে ভালোবাসবার নিষ্ঠা, বাংলার নানা আচার-আচরণ আজ বহুদূর ভেসে গেছে। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কাছে আজ দেশ কিংবা দেশের মানুষ ততটা গুরুত্ব রাখেনা, যতটা নিজের আখের গোছানোর ভাবনা তাকে তাড়িত করে। শোভাময় একটা ভূখণ্ডের সবুজ শ্যামলিমা আমাদের নিষ্ঠুর লোভের থাবায় বিরাণভূমি আজ। গানে বর্ণিত সেই শোভা কিংবা মানবিক আন্তরিকতায় ঘাটতি দেখা গেলেও আমাদের প্রাণের গান হয়ে যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতীয় সঙ্গীতের সম্মানের আসনে এটি থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
তৃষ্ণার্ত মানুষকে খালি মুখে ফিরিয়ে না দেয়ার যে অপূর্ব রীতি ছিল একদা বাংলার ঘরে ঘরে আজ সেখানে সন্দেহ আর অবজ্ঞার জটিল কুটিল হিসাব-নিকাশ মনে সর্বাগ্রে থাবা বসায়। পথক্লান্ত মানুষকে ডেকে নিজের দাওয়ায় বসিয়ে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি বিবিধখাদ্যে তাকে আপ্যায়নের সত্যি কাহিনিগুলো আজ আমাদের কাছে অলীক কিছু। অথচ একুশ কি পঁচিশ বছর আগে এমন ঘটনা আকছারই ঘটতো এই জনপদে। একুশ শতকের কথাসাহিত্যিক কুলদা রায়ের জীবনস্মৃতি এমন আন্তরিক বাস্তব কাহিনিতে ভরপুর। হ্যাঁ এর সাথে আর্থিক অসঙ্গতি, কর্মহীনতা তথা দারিদ্রতার প্রশ্ন জড়িত একথা ঠিক, কিন্তু আর্থিক অসঙ্গতির সাথে সাথে মানুষের মনটাও কি আজ তস্য গরীব হয়ে যায়নি?
এই জনপদের হারিয়ে যাওয়ার তালিকায় ঐশ্বর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মানুষের মানবিকতা খোয়ানোর বাস্তবতাকে তাই সবার আগে স্হান দিতে হয়। অবশ্য এই দৃশ্য আজ কম-বেশি পৃথিবীর তাবত ভূখণ্ড জুড়ে দৃশ্যমান।
আজকের আধুনিক সময়ে অত্যাধুনিক সংস্কৃতি ও পণ্যের কাছে, অত্যাধুনিক কলাকৌশলের কাছে কোণঠাসা হতে হতে বাঙালির অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক অনেক কিছুই আজ বিলুপ্তির পথে। হারিয়ে যাওয়া বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভেসে যাওয়া কিছু আচার এবং প্রতীকের কথা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করে আলোচনার সুতো গোটাবো।
শীত ও খেজুরের রসের মধ্যে গভীর একটি সম্পর্ক রয়েছে। তবে বর্তমান গ্রাম-বাংলায় এ সম্পর্ক ক্রমেই কমে যাচ্ছে। একটা সময় ছিলো গ্রামাঞ্চলের নারীরা খেজুরের রস দিয়ে নানা ধরনের পিঠাপুলি তৈরি করতেন। সে ধারাটি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে কালের বিবর্তনে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। গাছ থেকে রস নামানোর পর থেকে গ্রামে গ্রামে চলতো সেসব খাওয়ার ধুম। অতিথি আপ্যায়নেও এর বেশ কদর ছিল। আগের মতো খেজুর গাছের কদর আর নেই, নেই গাছে উঠে রস নামানোর পর্যাপ্ত লোক। জীবন-জীবিকার টানে গাছীদের অনেকেই আজ অন্য পেশায় নিযুক্ত। যে কারণে প্রয়োজনের তুলনায় খেজুরের রস না পাওয়ায় গুড় দিয়ে পিঠা-পুলি তৈরি করতে হয়। অবশ্য এসব পিঠা-পুলি সুস্বাদু হওয়ায় পরিবারের যেসব সদস্যরা অতীতে কখনও খেজুরের রস আস্বাদনের সৌভাগ্য অর্জন করেননি তাদের কাছে সমাদরই পায়।
বাঙালি হাত পাখার বাতাস খেয়ে প্রাণ জুড়িয়েছে এই কয়েক দশক আগেও। হাতপাখার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল নকশি পাখা। নকশি পাখার মূল উপকরণ সুতা, বাঁশ, বেত, খেজুরপাতা, শোলা, তালপাতা ইত্যাদি। আগে এখানে ময়ূরের পালক ও চন্দন কাঠের পাখাও তৈরি হতো। নকশা অনুযায়ী এসব পাখার নামও রয়েছে। যেমন- শঙ্খলতা, গুয়াপাতা, পালংপোষ, কাঞ্চনমালা, ছিটাফুল, তারাফুল, মনবিলাসী, মনবাহার, বাঘবন্দি, ষোলকুড়ির ঘর, মনসুন্দরী, সাগরদীঘি ইত্যাদি। এখন এইসব হাতপাখা প্রায় ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। একটা সময় হয়ত “তোমার হাত পাখার বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে আসে…” কেবলি গানের কলি হয়ে গ্রাম বাংলার মানুষের প্রাণে অতীত স্মৃতির অনুরণন তুলবে।
এক সময় বাংলার অনেক ঘরেই শীতল পাটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। গরমকালে শীতল পাটিতে আরামের ঘুম ঘুমাতে কিংবা বাড়ির ছাদে সন্ধ্যাকালীন আড্ডাগুলোতে এই পাটির জুড়ি ছিল না। গ্রামে বিশেষ অতিথি এলে শীতল পাটির বিছানা দেওয়া হতো। বেত গাছের ছাল থেকে তৈরি হয় শীতলপাটি। নকশা করা শীতলপাটিকে নকশিপাটিও বলে। সিলেট এই পাটির জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও বরিশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা ও লক্ষ্মীপুরও শীতলপাটি তৈরিতে বিখ্যাত। সেই শীতলপাটি আজকাল কোনো হাটবাজারেও সহসা খুঁজে পাওয়া মুশকিল।
এই যুগের অনেক শিশু-কিশোর সরাসরি বসে পুতুল নাচ দেখার ব্যাপারটি হয়ত জানেই না। অথচ একসময় বাংলার মানুষের অন্যতম বিনোদনের আকর্ষণ ছিলো পুতুল নাচ। সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে পুতুল নাচ হতো। এখন বিশেষ কোনো পালা পার্বণে গ্রামীণ কোনো মেলায় বা টিভি পর্দায় পুতুল নাচের আয়োজন হঠাৎ কখনও কখনও চোখে পড়ে। বাঙালি সংস্কৃতির এই অংশটি এখন প্রায় হারিয়ে যাওয়ার পথে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।
রেডিও টেলিভিশন আসার আগে মানুষের অবসর বিনোদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল মুখে মুখে বলা ধাঁধা লোকজ ছড়া ইত্যাদি। এ ছাড়া যে কোনো কাজে উৎসাহ বাড়াতে ও চিত্তবিনোদনের জন্য অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে মুখে মুখে ছড়া তৈরি হতো। এক সময় বায়োস্কোপ নামের এক চমকপ্রদ আনন্দ মাধ্যম ব্যাপকমাত্রায় প্রচলিত ছিল যা এখন খুববেশি দেখা যায় না। এই বায়োস্কোপ দেখানোর সময় ছড়া কেটে ছবির বর্ণনা দেয়ার রীতি। পুতুল নাচের মতো বায়োস্কোপেও গ্রাম বাংলার জনপ্রিয় লোককাহিনি, আর কাল্পনিক ছবিছাবা দেখানো হতো। বায়োস্কোপ নামের মাধ্যমটি ছিল মুড়ির টিনের মতো একটি টিন বা কাঠের বাক্স, যার কাচের জানালায় চোখ রাখলেই ছবি আর বায়োস্কোপওয়ালার কন্ঠের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠতো এক অজানা ভুবন। বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি বাক্সের কাঁচের জানালায় চোখ রেখে বায়োস্কোপ দেখার এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে পিপ শো নামে অভিহিত করা হয়। যার মানে হচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখা। বায়োস্কোপ দেখানোর প্রক্রিয়া থেকে চলচ্চিত্র উদ্বাভবনের সূত্রপাত বলে অনেকের ধারণা। আজও কোথাও কোথাও বায়োস্কোপওয়ালার উপস্হিতি ঘটলে ছেলে বুড়ো তুমুল উৎসাহে চৌখুপিতে চোখ রেখে তুলে নিতে চান আঁজলা ভরা আনন্দ। ছড়া, বায়োস্কোপ ইত্যাদির পাশাপাশি এদেশের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ-প্রবচন লোক-পরম্পরাগত বিশেষ উক্তি বা কথন। মুখে মুখে উচ্চারিত সেইসব লোকজ ছড়া ও ধাঁধার আসর এখন বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “পালকি চলে! পালকি চলে! গগন-তলে আগুন জ্বলে! স্তব্ধ গাঁয়ে আদুল গায়ে যাচ্ছে কারা রৌদ্রে সারা!” তুখোড় ছন্দের ছড়াটি আমাদের অনেকেরই পরিচিত। এটিতে সুর দিয়ে অনবদ্য একটি গানও গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। না, ছড়াকার কিংবা গায়ককে নিয়ে এখানে কিছু বলবো না। বলবো ছড়ায় ব্যবহৃত ‘পালকি’ নিয়ে। বাঙালির ঐহিত্যবাহী প্রাচীন এক বাহন ছিল এই পালকি। যান্ত্রিক কলাকৌশলে এগিয়ে থাকা এই সময়ে মানুষ বাহিত এই বাহনের চল সঙ্গত কারণেই আজ আর নেই। বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা উপমহাদেশে ভ্রমণকালে পালকি চড়ে বিভিন্নস্হানে ভ্রমণ করেন বলে তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায়। বিজ্ঞানের কল্যাণে আধুনিক যানবাহন আবিষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণিরা পালকি চড়ে একস্হান থেকে অন্য স্হানে যাতায়াত করতেন। গরীবগুর্বাদের পদযুগল ছিল ভরসা। অবশ্য গরীব ঘরের মেয়েটির রূপ কিংবা কপাল গুণে(!) বড় ঘরে বিয়ে হলে পালকিতে চড়ার একটা সুযোগ জুটে যেত। পালকি চড়ে নববধূ তার শ্বশুরবাড়ির আঙিনায় এসে উপস্হিত হতো। পাড়া-পড়শি আর আত্মীয়-স্বজনদের উপস্হিতিতে পরিবারের প্রচলিত রীতি রেওয়াজ শেষে পরম আদরে ঘটতো তার গৃহপ্রবেশ। ‘উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে স্টীমার ও রেলপরিবহন চালু হওয়ায় পালকির ব্যবহার কমতে থাকে। ক্রমশ সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি এবং পশু-চালিত যান চালু হলে যাতায়াতের বাহন হিসেবে পালকির ব্যবহার কমে যায়। ১৯৩০-এর দশকে শহরাঞ্চলে রিকশার প্রচলন হওয়ার পর থেকে পালকির ব্যবহার উঠেই গেছে বলা যায়’। ইদানিং অবস্হাপন্নদের বিয়েতে পালকিতে করে বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনের উপস্হিতি দেখা যায়। যেটা সংখ্যায় খুবই নগন্য।
চিরায়ত গ্রাম বাংলায় এক সময় ঢেঁকির ব্যাপক প্রচলন ছিল। যার ব্যবহার আজকাল খুবই কম। একসময় গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ঢেঁকি থাকতো। ঘরের বৌ-ঝিদের ঢেঁকিতে পাড় দেবার ছন্দবদ্ধ আওয়াজে গ্রামের বুকে বেজে উঠতো এক অপার্থিব মূর্চ্ছনা। ঢেঁকিতে ধান ভানার ফাঁকে গ্রামীণ নারীরা নিজেদের সুখ-দুঃখের আলাপে মশগুল হতেন। হাস্যরসে ডুবে যেতেন। গান প্রিয় নারীরা গানের সুর তুলতেন ঢেঁকির ছন্দে ছন্দে। অনেকেই ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাংলার অনেক কালজয়ী গল্প উপন্যাসে ঢেঁকির ব্যবহার চোখে পড়ে। সেরকম একটি উপন্যাস হলো শহীদ জহির রায়হানের হাজার বছর ধরে। ঢেঁকি নিয়ে বহুল প্রচলিত একটি গান আজও বাঙালি গাইতে ভালোবাসে – “ও বউ ধান ভানো রে…ঢেঁকিতে পাড় দিয়া, ঢেঁকি নাচে বউ নাচে হেলিয়া দুলিয়া”। মেশিনে ধান গম ইত্যাদি ভাঙা শুরু হওয়ার পর বাংলার গ্রামীণ জীবন থেকে ঢেঁকির ব্যবহার বহুল মাত্রায় কমে গেছে। আগের মতো ঢেঁকি পাড়ের শব্দের সাথে বৌ-ঝিদের গানের সুর গ্রামীণ পরিবেশে আর মৌতাত না তুললেও উপন্যাস আর গানের বাণী প্রাচীন সংস্কৃতির স্মৃতি ধরে রাখবে সন্দেহ নাই।
বাংলার বুক থেকে হারিয়ে যাওয়ার মিছিলে প্রচুর নাম আছে, সবটা তো আর এই ছোট্ট পরিসরে বলা সম্ভব না। তবে কিছু কিছু জিনিস হারিয়ে গিয়ে নতুন চেহারায় ফিরে আসছে। যেমন হুঁকো বা হুক্কা। আগের দিনের হুঁকো বা হুক্কা ছিল নলচে-লাগানো নারকেল খোলে তৈরি দেশি প্রথার ধূমপানের একটা বিশেষ যন্ত্র। কাজের অবসরে কিংবা কাজে যাওয়ার আগে গ্রামের বাড়ির উঠানে বসে কৃষক, জেলে কিংবা শ্রমিক মানুষটি হুঁকোতে গুরুর গুরুর শব্দ তুলে কয়েকটা সুখ টান দিয়ে তৃপ্তি নিয়ে যার যার কর্মক্ষেত্রে রওনা দিতেন। অনেক অভিজাত পরিবারের পুরুষ শুধু নন নারীও হুঁকোতে আসক্ত ছিলেন। অভিজাত শ্রেণীর ব্যবহৃত হুঁকো হতো বেশ বাহারি ধরনের। হুঁকোর জায়গা কেড়ে নেয় বিড়ি-সিগারেট। ধুমপানের মতো ক্ষতিকারক একটি প্রথার চল উঠে গিয়ে ক্ষতি হয়নি বরং ভালোই হয়েছে বলে তৃপ্তির সুযোগ নেই, কারণ আদ্দিকালের সেই হুঁকো অভিজাত চেহারা নিয়ে আবারও ফিরে এসেছে। বিভিন্ন রেস্তোরাঁর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে এটির চল দেখা যায়।
একই ভাবে প্রায় ৩০০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ঢাকাই মসলিনকে ফিরিয়ে আনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এক সময় ঢাকায় তৈরি মসলিনের ছিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সূক্ষ্ণ সুতার মাধ্যমে হাতে বোনা মসলিন নামের এই মূল্যবান বস্ত্র ইউরোপীয় বণিকদের কাছে খুবই আদরের বস্তু ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী কোনো কোনো এলাকায় ‘ফুটি’ নামে এক প্রকার তুলা জন্মাত। এর সুতা থেকে তৈরি হতো সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র। সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিনের নাম ছিল মলমল। বিদেশি পর্যটকরা এই মসলিনকে কখনও কখনও মলমল শাহী বা মলমল খাস নামে উল্লেখ করেছেন। এগুলো বেশ দামি এবং এরকম এক প্রস্থ বস্ত্র তৈরি করতে তাঁতীদের দীর্ঘদিন, এমনকি ছয় মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত। মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি বেড়ে যায় এবং তা দূর-দূরান্তের বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। মুগল সম্রাট ও অভিজাতগণ ঢাকার মসলিন শিল্পের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্রাট, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পদস্থ কর্মকর্তা ও অভিজাতদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্মতম মসলিন বস্ত্র সংগ্রহ করা হত। একসময় মুঘল শাসনের জৌলুস কমে আসে, মুঘলদের তাঁতখানার সবেচেয়ে অভিজ্ঞ তাঁতিরা দারিদ্র্যে আর অনাহারে পেশা পরিবর্তন করে। ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় রাজা এবং মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলা তাঁতখানা স্হবির হতে থাকে। অভিজ্ঞ আর দক্ষ তাঁতিদের জ্ঞান পরের প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরের সুযোগ কমে আসে, আর বাংলায় বিশেষ করে ঢাকার আশেপাশে মসলিনের তাঁতখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, কারিগরদের পলায়ন, সর্বোপরি বৃটেনে সংঘটিত শিল্পবিপ্লব ইত্যাদি কারণে মসলিনের প্রধান কাঁচামাল ফুটি কার্পাসের চাহিদা কমে আসে, ওইসব জমিতে বিকল্প চাষাবাদ শুরু হয়। বিশ্বজোড়া খ্যাতি বয়ে আনা মসলিন একসময় হারিয়ে যায়।
সময় পরিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের খাদ্যাভ্যাসেও এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। চিরকালীন নবান্ন উৎসব এখন যান্ত্রিক জীবনের চাকার নীচে চাপা পড়েছে প্রায়। বাঙালীর হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলতে যা ছিল তার অনেক কিছুই অবশিষ্ট নেই। কবিগান, জারিসারি, যাত্রা পালা এসব এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের সামনে যা তুলে ধরে আমরা তাই হজম করি। গ্রামেগঞ্জে নৌকা বাইচ, মাছ ধরার প্রতিযোগিতা, শীতকালের চড়ুইভাতি এসবের সেই হইহই আয়োজন আর তেমন চোখে পড়ে না।
খেলাধূলা বলতে আজকাল গ্রামের ছেলেরাও ক্রিকেট ফুটবল বোঝে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কোন খেলাধূলা দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, হা ডু ডু, বলিখেলা ইত্যাদির সেই সুদিন আজ আর নেই। শহরের মতো গ্রামীন সমাজের লোকজ আচারও বদলে গেছে। একসময় বিয়ে শাদি ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যে ঘরোয়া সৌন্দর্য ছিল, এখন সেটা ক্লাব পর্যায়ের আন্তরিকতাবিহীন দায়সারা আয়োজনে রূপান্তরিত।
ধানের গোলা, খড়ম, খাগের কলম, গরুর গাড়ি, কাঠের পিঁড়ি, পাটজাত নানা শৌখিন জিনিস, ডুলি, মাথাল, সোনালী আঁশ নামে খ্যাত পাট ইত্যাদি ব্যবহারের দিনগুলো আজ ভেসে গেছে বহুদূরে।
পুরাতনকে সরিয়ে নতুন জায়গা করে নেয় একথা যেমন সত্যি, একই সাথে এটাও সত্যি সব শূন্যতার পূরণ সম্ভব হয়না। চিরায়ত বাংলার বুক থেকে যা হারিয়েছে তার অনেক কিছুই আর মাথা কুটলেও ফিরে পাওয়া সম্ভব না। বর্তমানের ঝাঁ চকচকে যান্ত্রিক আড়ম্বরের ভিড়ে ভেসে যাওয়া দিনের স্মৃতি সন্তর্পণে ছায়া ফেলে যাবে সন্দেহ নাই। আমরা চিরায়ত বাংলার হারানো ইতিহাস ঐহিত্যের সেসব বিবরণ পড়ে স্মৃতি কাতর হবো, এবং বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সুন্দর আগামির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধাবিত হবো।
তথ্যসূত্র:
১.বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) – নীহাররঞ্জন রায়
২. দৈনিক প্রথম আলো
৩. বিডিনিউজ২৪ডটকম
৪. হাসান আজিজুল হকের সাক্ষাৎকার
৫.একুশে টেলিভিশন: ঢাকাই মসলিন।
৬. উইকি এবং বাংলাপিডিয়া

নাহার তৃণা
নাহার তৃণা জন্ম ২ আগস্ট, ঢাকায় বর্তমানে উত্তর আমেরিকায় বসবাস করছেন। ২০০৮ সালে লেখালেখির জগতে প্রবেশ। কমিউনিটি ব্লগ এবং লেখক ফোরামের পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে লিখতে শুরু করেছেন দুই বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যপত্রিকা এবং ওয়েবজিনে। নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন প্রবন্ধ, গল্প, অনুবাদ, সাহিত্য সমালােচনা। সম্প্রতি ফেসবুককেন্দ্রিক বইপ্রিয় গ্রুপ বইয়ের হাট থেকে ইবক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর শিশুতােষ অনুবাদ গ্রন্থ ‘এক ডজন ভিনদেশি গপ্পো'। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০-এ ‘পেন্সিল পাবলিকেশনস প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযােগিতায় তার ‘স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট সেরা গল্পগ্রন্থ নির্বাচিত হয়।