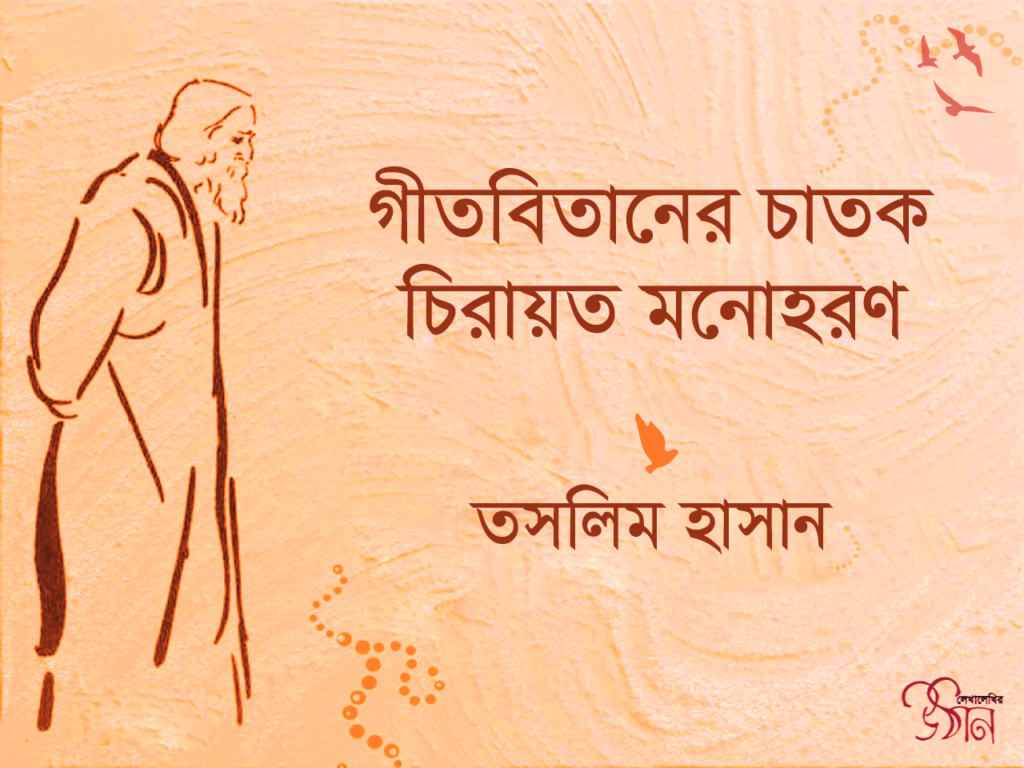ভাটির যে চলাচল সেটাকে অনুকূলের সহায়তায় বয়ে যাওয়া বা ভেসে যাওয়া বলা সঙ্গত। উজান দেশের নাইয়া যারা তাদের অভীষ্ট নিয়ে চিন্তার কোনো শেষ থাকে না ভাবনার কারিগরদের। মূল্যায়ন একদিকদর্শী হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায় বলে কোনো কোনো কারণে একজন চিন্তককে এমন সব আচরণের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হতে হয় তার কিছু ফিরিস্তি যোগ করে দেয়া অন্যায় হবে না বলে মনে করি। আমাদের সখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজানের পথে চলার ক্ষেত্রে, অনির্দিষ্ট পাথার ভাঙার ক্ষেত্রে, গন্তব্যের দিকে গুণ টানার ক্ষেত্রে এক চিরায়ত চাতক এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসরণকারী। ‘পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে’ – এই গানে এবং আরো কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ‘পান্থজন’, ‘পথিকজন’, ‘পথিকপরাণ’ বা শুধু ‘পথিক’ বলেছেন। খুব নতুন কথা নয় এটা। সাধু সন্তরা, আউল-বাউলেরা, সুফী-দরবেশরা, মরমিয়া কবিরা নিজেদেরকে চরম প্রেমের করুণ-রঙিন অথচ প্রাণান্ত-কঠিন পথের পথিক বলে জেনেছেন বহুকাল যাবৎ।’১
পরম ও জীবের মিলনে এমন কী অস্তিত্বের প্রশ্ন দেখা দেবে বাহ্যত যার কোনো প্রমাণ নেই। চাতক যেখানে অনায়াসে যে কোনো পানি পান করতে পারে নাকি তার সত্তা মেঘের বারি ছাড়া পান করার মত অন্যান্য জলকে জলই ভাবে না অথবা এখানেই কাব্যের মারেফত আত্মগোপন করে থাকে। ঈশ্বরবাদীদের নিয়তি যদি আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে তাহলে প্রতীক্ষা ছাড়া হাতে খুব পুঁজি আছে বলে মনে হয় না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় মাপের কবি এই প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো সুন্দর করে তুলেছেন, মনোহরণকে নিয়ে গড়েছেন অপূর্ব সব কাব্য ও গান। তাঁর ঈশ্বর নির্ভরতার বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীর ২য় খণ্ডে বলেছেন যে, প্রবন্ধ ‘রবীন্দ্রসাহিত্য রবীন্দ্রদর্শন রবীন্দ্রজীবনের মূলকথা এই অহেতুকী ঈশ্বরনির্ভরতা।’২ প্রভাতকুমার যথার্থই বলেছেন যার কারণ হিসেবে বলবো, কাব্য নির্মাণে হিসেবী চলন রস আহরণে আহত করে; যেখানে কারণের মাত্রাতিরিক্ত জাগতিক দার্শনিক বিচার কাব্য চয়নকে ব্যাহত করবে। আবার অন্যদিকে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন: ‘সত্য শ্রেয় ও সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মানুষের জীবনকে নিছক জৈবিকতার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তার সাময়িক কিন্তু সম্পূর্ণ বিলয় – সেই অনির্বচনীয় ভয়ঙ্কর সম্ভাব্যতার মুখোমুখি দাঁড়ানোটাকেই বলে – ‘encounter with nothingness’। নাস্তিকতার চেয়েও নিদারুণতর যে চূড়ান্ত নাস্তি, তার সঙ্গে ভীম পরিচয় ভক্ত ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের, শুভ্র ও সুন্দরের বেদিতে আত্মনিবেদিত রবীন্দ্রনাথের, যে কখনোই ঘটেনি তা নয়।’৩ জনাব আইয়ুব রবীন্দ্রনাথকে এমন এক অন্ধকারের যাত্রী হিসেবে দেখতে পান যেখানে সূক্ষতর শূন্যবাদ না থাকলেও তাদের শক্তি তিনি ধারণ করেছিলেন নইলে প্রেমাষ্পদের জন্য হতাশার বিরুদ্ধে লড়বেন কী করে। তিনি তাঁর ঈশ্বরীকে অর্ধেক সত্য আর অর্ধেক কল্পনার মিশ্রণে গড়ে তুলেছিলেন । অর্থাৎ তার ঈশ্বরী যেন সত্যেরও অধিক। যা প্রকাশিত তা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মন গহনে। জগৎ প্রকাশিত হচ্ছে আপন অঙ্গে।
আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে॥ (পূজাপর্ব : ৬৬)
২.
প্রেমাষ্পদের জন্য আছে প্রতীক্ষা, আছে মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এই বাসনা অভুক্ত তৃষ্ণার্ত চাতককে বাঁচিয়ে রাখে সুদীর্ঘকাল। প্রতীক্ষার এই পথ ক্লান্তিকর ও বেদনা জাগানিয়া। মহাকবি হাফিজ বলেন: ‘পথিকদের পথক্লান্তি নাই/ প্রেম পথও বটে, গন্তব্যও বটে’। রবীন্দ্রনাথে পাই ‘আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ’ অথবা ‘পথে চলা, সেই তো তোমায় পাওয়া’। ‘রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে এই সুন্দর ভুবনকে ভালোবেসেছিলেন, তবে বিশ্বের সৌন্দর্য যে একটি শতদল পদ্মের মতো নিখুঁত নিটোল নিষ্কলুষ সৌন্দর্য নয় – এ উপলব্ধি তাঁর ক্রমশ গভীর হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর ভালোবাসাও প্রাজ্ঞ এবং কঠিন হয়েছে। তবু তা কখনো শিথিল হ’য়ে যায়নি, তাতে এমন কোনো ফাটল ধরেনি যা বিশ্বকবিকে এক মূহুর্তের জন্যেও বিশ্ববিমূখ ক’রে দিতে পারতো।’ ৪ কিন্তু প্রিয়ের গৃহে যাবার পথে তাঁর জন্য যে পদ্ম-অর্ঘ্য সাজিয়ে নেয়া তা শুকিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ জীবের অর্ঘ্য পরম পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। কাজেই পরমের দরবারে ক্ষমা চাওয়ার ভেতর দিয়ে মূলত ‘প্রচেষ্টাকে হোক তা ব্যর্থ তবুও মন তো আশা ছাড়েনি’ তাকেই প্রকাশে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁর কণ্ঠে বলা যায়-
ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু॥
শেষ দুই পঙক্তিতে বলছেন:
দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো ক্ষমা করো প্রভু॥ (পূজাপর্ব : ১৫৭)
ভক্ত, প্রেমিক কথার মালা রচনা করে প্রিয়ের গলায় পরিয়ে দেবে বলে। অথচ না আছে তার সাক্ষাত, না আছে তার কথোপকথন। চোখের শান্তি আর কথা বলার সুখ কোনোটাই ভাগ্যে জুটছে না। কাজেই কমপক্ষে প্রতীক্ষার দেবতা এসে আসন পেতেছে। না দেখার দেখা এসে পরশ একে দিয়েছে; না বলার বলা আজ চোখে ফুটেছে; না শোনার শোনা হৃদয়ের গহীনে বেজে মন হরণ করেছে। যেন অধরাকে ধরার নাগালে বোঝার উপক্রমণ। এই তো সুন্দরতম প্রচেষ্টা, চাতকের স্বভাব। এটাকে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান রচনায় মূল সুর বললে একেবারে ভুল হবে না। একটি পূজা পর্বের কাব্য তুলে দেই-
আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে॥
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে
আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীড়ে-
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে॥ (পূজাপর্ব: ৫৬)
‘কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না, তবু আকুল প্রাণে কোথা থেকে যেন সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে, বাঁচিয়ে রাখে – বেঁচে থাকার – মানুষ হ’য়ে থাকার – ইচ্ছাটাকে একে বলা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থায়ীভাব।’৫ যে বাঁশি আজ অবধি কেউ শোনেনি; যার শব্দ হয়তো এখনো জগতের লোকে আন্দাজও করতে হিমসিম খাবে তা যদি কবির অন্তরের গভীরে বেজে ওঠে, তবে কি অপার্থিব কোনো আহবান তাঁকে দশাপ্রাপ্তির দিকে টেনে নিচ্ছে। এ থেকে যে সুখের মত ব্যথা তিনি পেলেন তাকে ধরে ফেললেন লুকিয়ে রাখলেন সমূহ অশ্রুপাত হবার আগেই।
৩.
আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উছাসে॥ (পূজাপর্ব: ৬৬)
পরম যদি জীবের সাথে আত্মা হয়ে মিশে থাকে তবে কেন এই মিনতি এই পথ চাওয়া। প্রেমিক বুঝে গেছে যে প্রিয় তার সর্বস্ব চেয়ে বসেছে তবে আহবান এসেছে দেহের গহীন থেকে। সব জেনে শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়ের অসীম সাগরে ডুবে যেতে রাজি। যতই ছলনার আশ্রয় খুঁজুক সে তো নাগালে আসছে না। রসিক বলে, যাকে পেলে আসবে পূর্ণতা, হবে জীবনের মোক্ষ লাভ। কাজেই সোনার হরিণের মোহ ছেড়ে দেয়া মানে উজান ছেড়ে ভাটিতে ভেসে যাওয়া, তাতে বিরহের আনন্দটুকু থেকে হতে হবে বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথের এতে সন্তুষ্টি আসবে কী করে? দেহের গহীন থেকে আসা এলহাম অগ্রাহ্য করার শক্তি কার থাকতে পারে আর অবহেলা করার দরকারটাই বা কেন? এমন এক অন্তরঙ্গের আহবানের শিকার তিনি যে, অনায়াসেই তাঁকে মজে যেতে হয় আত্মবিসর্জন দিতে। এখন কার আহবানে কে সাড়া দেবে বুঝতে না বুঝতেই এক সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন রবি বাবু-
আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি যে জন পথে ভাসায়॥
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে- ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়॥ (প্রেমপর্ব: ৮৯)
মহাভারতে দেখা যাবে, যুধিষ্ঠিরকে অবশেষে ইন্দ্রের সভায় ঢুকতে জাগতিক দেহ ত্যাগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ জাগতিকতা পরমের দরবারের গলিতে গলিতে ঘুরে ফেরে, দরজা অবধি যায়। ঘরে প্রবেশে তার ইহলৌকিক বসন-ভূষণ, অলংকার, ভাষিক উৎকর্ষ – সব সাজানো অর্ঘ্য মলিন হয়ে যায়। কাজেই জীবের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। রসিক কবি তাই প্রিয়ের প্রতি সকল আয়োজন করে আপন দেহ-মনকে দেবতার আসন বানিয়ে ভজনায় বসে যায়। প্রিয়ের স্বভাব কিন্তু কটাক্ষ চালে এগোয়; তাঁর সকল গতি রসিকের আয়োজনের একদম বিপরীত। ‘তবু আশ্চর্য নয়। প্রেমের পরিমিত অভিজ্ঞতায় প্রেমিক খুঁজেছে অপরিমিত কিছু, অপার্থিব কিছু। যার মাধুরী জীবনের পাত্রে ধরা যাবে না, যাকে ধ্যানের ধন বললেও একটু বাড়িয়ে বলা হয়, কারণ তা সম্পূর্ণ ধ্যেয় নয়, তাকেই সে খুঁজছে একটি সীমিত, সামান্য, রক্তমাংসের ক্ষুদ্র মানবিক বেষ্টনিতে। পুকুরের চৌহদ্দিতে অকুল সমুদ্র খোঁজা কেন?’৬ চাতকের স্বভাব, অধরার প্রতি তার যত আদিখ্যেতা যেন বেদনার চোখ রাঙানি।
তপস্যা ছাড়া কে পেয়েছে শ্বাশতের খোঁজ? উপনিষদে আছে স্বয়ং ব্রহ্মাও তপস্যার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তপস্যা নিঃসৃত বেদনার শেষ কোথায়? ঋষি তাপস চাতক রবীন্দ্রনাথের এই ধৈর্যের মর্ম সাধক যেমন বুঝবেন, রসিক হবেন তার যোগ্য সারথী। চাতকের কাজ মেঘের বারি ঝরলে পান করা। খুঁজতে গেলে পাবে না সে কোনো কালে তাও জানে। কারণ তার পথ চেয়ে চাতক তো আর একা বসে নেই, মেঘের আশেকান অজস্র অগণিত। ইকবাল শিক্ওয়াহ গ্রন্থে বলছেন:
‘কভী হম্সে গৈরোসেঁ শনাসায়ী হৈ,
বাত কহনে কী নহীঁ – তূ ভী তো হর্জাই হৈ।’ ৭
(কখনও আমাদের সঙ্গে কখনো অন্যদের সঙ্গে তোমার ভাব,
কথাটা মুখে আনতে নেই – তুমিও তো হর্জাই)।
কিন্তু তারপরও প্রেমাষ্পদের প্রতি তার চেয়ে থাকা থামে কই? এ এক অন্তরঙ্গের আহবান বৈকি। যদি না দেবতা আপন গুণে মেঘের বারি কাউকে দান করে তবে চাতকের কী দশা হবে ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। আবার চাতক নাছোড়বান্দা, সে জেনে শুনে বিষমভাবে আক্রান্ত হয়েছে অন্যদিকে মেঘ তার আপন গতিতে অন্য দেশে চলে যায় আর যাওয়াটা যেহেতু তার স্বরূপ, কাজেই চাতকেরও একটা ‘পকড়’ ৮ থাকা চাই। চাতক যাকে আকাঙ্ক্ষা করে, হোক না সে অন্য পথের পথিক, থাক না তার অসীমতার চলন; তাতে চাতকের প্রতীক্ষার প্রদীপ ধপ করে জ্বলে উঠে তিলে তিলে জ্বলতে জ্বলতে তাকেও জাগিয়ে রাখবে। তার প্রেমাষ্পদের পিয়াসকে অনুরাগের সলতে দিয়ে পোড়াবে। অসম্ভবের পায়ে কুড়োল মেরে তাই রবীন্দ্রনাথ গেয়ে ওঠেন-
ফিরিবে না তা জানি, তা জানি –
আহা, তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি॥
গাঁথবে না মালা জানি মনে,
আহা, তবু ধরুক মুকুল আমার বকুলবনে
প্রাণে ওই পরশের পিয়াস আনি॥
কোথায় তুমি পথ ভোলা,
তবু থাক্-না আমার দুয়ার খোলা।
রাত্রি আমার গতিহীনা,
আহা, তবু বাঁধুক সুরে বাঁধুক তোমার বীণা
তারে ঘিরে ফিরুক কাঙাল বাণী॥ (প্রেমপর্ব: ২৫৯)
প্রিয় তার আহবানে সাড়া দিক আর না দিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূর্যস্তুতি ও আশেকী আয়োজন চালিয়ে যাবেন সেটা নিশ্চিত হওয়াই যায়। একটি কূপের জল যদি আশা করে সে সমুদ্রে যাবে, প্রিয় হিসেবে ঠিক করেছে সাগরকে, তার সাথে মিলনে কূপ জলের নির্বাণ। কিন্তু সজল বরষা না হলে কূপকে সারাজীবন অপেক্ষার প্রহর গুণে প্রিয়ার জন্যে ধ্যানস্থ মন নিয়ে কাটিয়ে দিতে হবে। আবার প্রেমাষ্পদ বলে কথা! বাসনার প্রদীপ কাজেই অনায়াসে জ্বলে যায়। আবার সেই বরষা অন্য কোথাও হলে কিন্তু চলবে না। লালন সাঁই বলেন:
রাখলেন সাঁই কূপ জল করে
আন্ধেলা পুকুরে।
নদীর জল কূপজল হয়
বিল বাওড়ে পড়ে রয়
সাধ্য কী জল গঙ্গাতে যায়
গঙ্গা না এলে পরে
তেমনি জীবের ভজন বৃথা
তোমার কৃপা নাই যারে॥
রবীন্দ্রনাথ তাই আপন মনে গেয়ে ওঠেন-
ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি।
অন্যভাবে যদি দেখতে চাই তবে গালিবের একটি শের মনে পড়ছে যেটা আবু সয়ীদ আইয়ুব গালিব নিয়ে তাঁর আলোচনায় এনেছিলেন। সেখানে দেখা যাবে একটি ধূলিকণার সূর্য পর্যন্ত পৌঁছানোর ছলনায় দার্শনিক অবস্থান, যা রবীন্দ্রনাথের নাছোড়বান্দা স্বভাবের সাথে চমৎকার ভাবে মিলে যায়। শেরটা পার্সি :
“জিজ্ঞাসা করলাম- ‘একটি ধূলিকণার পক্ষে সূর্যে পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব?’ সে বললো- অসম্ভব প্রায়।’
জিজ্ঞাসা করলাম- তবু কি আমি চেষ্টা করে যাবো? সে বললো- তাই সঙ্গত।”
৪.
নৈকট্যের ফাঁকি যে কত বড় সুক্ষ্ণ প্যাঁচ তা গীতবিতানের চাতক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভালো বুঝেছিলেন। ‘তাঁর রসিকতার শেষ কোথায়’- এই সত্য জেনে তিনি সুন্দরতার রচনায় বসেছেন আকুল অনুরাগে। আর নৈকট্যের ফাঁকি চাতককে দিশাহারা করে দিতে পারে যা ধরতে গেলে রবি ঠাকুরের চেয়ে উত্তম শিকারী কেই বা আছে?
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে রয়েছ হৃদয়ে গোপনে॥ (পূজাপর্ব: ৪৮৭)
নৈকট্যের ফাঁকে ফাঁকে কে তৈরি হয় বেদনা। প্রিয়ের বিচ্ছেদ এমন যে, ভক্তের ব্যথাকে আবার আসন না বানালে সইবে কী করে। ভগবানের এমন উপস্থিতি যে কাউকে বিভ্রমে ফেলে দিতে পারে। তার অধীন্যস্ত হবার এমন কৌশল পরাস্ত করতে পারে মিলনের বাসনাকে। কাজেই চাতক পাখির দশা এই যে, বিরহ হয়ে ওঠে তার পুঁজি, আর অনুরাগ চলার সাথী; দেখা পাওয়া যেখানে ছলনার সমকক্ষ। এখানে পর্ব পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।গীতবিতানে আমরা পূর্ব পরিচয়ের সুর অনেকটাই আত্মসাৎ করেছি। তারপরও কাকে চিনলে কাকে চেনা হয়? অন্তরঙ্গ থেকে তাই গেয়ে ওঠা –
কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও॥
মনের মত কারে খুঁজে মরো,
সেকি আছে ভুবনে-
সে যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মত সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও॥
তোমার আপনার যে জন দেখলে না তারে
তুমি যাবে কার দ্বারে।
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও॥ (প্রেমপর্ব: ৩৬০)
অবশেষে যখন বারির মরশুম আসে চাতক তখন সেই প্রকৃতিকে ‘ছল করে দেখা অনুক্ষণ’ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে নারাজ। আবার বৃষ্টিতে ভিজে টইটম্বুর হয়েও অনুরাগের দহনে উষ্ণ রাখে মেজাজকে। আমাদের চাতক ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের দশাপ্রাপ্তির ইতিকথা গীতবিতানের পরতে পরতে এমনিভাবে কটাক্ষ করে যাচ্ছে। প্রিয়ের দুরত্ব-নৈকট্যের ব্যঞ্জনাময়, সরস, সুন্দরতম মূল্যায়নে যেন তিনি অহর্নিশি চাতক প্রায়, মেঘের কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে ব্যগ্র-মহাশয়।
তথ্যসূত্র ও টীকা
১. আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা, দে’জ পাবলিশিং, সূচনা।
২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ১৮।
৩. আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৪. আবু সয়ীদ আইয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ২২।
৫. আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থজনের সখা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
৭. ‘হর্জাই’ শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে ‘সর্বব্যাপী’ ও ‘সর্বত্রগামী’, কিন্তু প্রচলিত ভাষায় কথাটা ‘বহু পুরুষের শয্যাগামিনী’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।
৮. রাগের রূপ প্রকাশ করার প্রয়োজনে যে অল্প সংখ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বর ব্যবহার করা হয় তাকে ‘পকড়’ বলে।
মননরেখা ।। জুন ২০১৮ এ প্রকাশিত

তসলিম হাসান
জন্ম ৩০ জানুয়ারি ১৯৯১ , পাবনা জেলায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।সাহিত্য, সঙ্গীত ও দর্শনের প্রতি অনুরাগ । পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক। প্রকাশিত কবিতার বই দরবেশ ও দিশেহারা পাখি