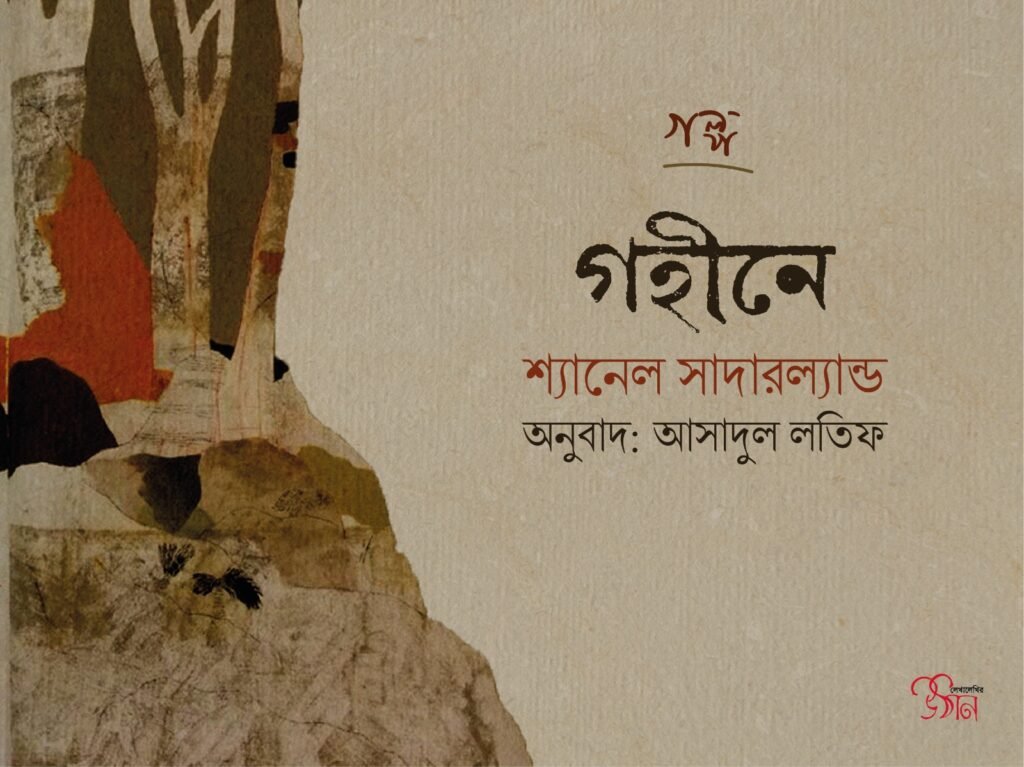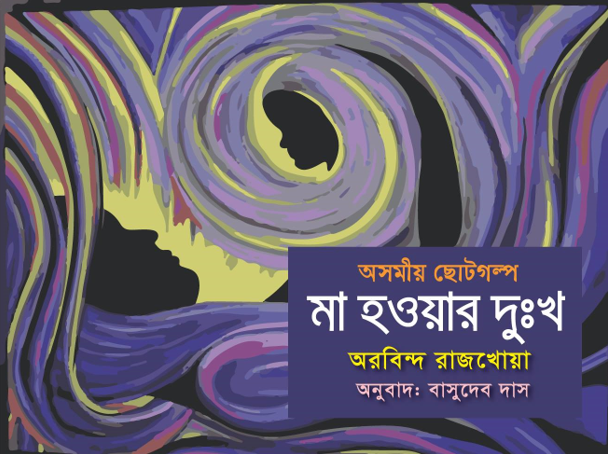[কমনওয়েলথ শর্টস্টোরি প্রাইজ ২০২৫ বিজয়ী এবং কানাডা ও ইউরোপ অঞ্চল থেকে রিজিওনাল উইনার শ্যানেল সাদারল্যান্ড-এর জন্ম সেইন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনসে। এখন বাস করেন মন্ট্রিয়লে। তাঁর প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ লেঅ্যাওয়ে চাইল্ড ২০২৬ সালে প্রকাশিত হবে হাউজ অব আনান্সি থেকে। শ্যানেল ২০২১ সালে সিবিসি নোটিফিকেশন প্রাইজ এবং ২০২২ সালে সিবিসি শর্ট স্টোরি প্রাইজ জেতেন । মূল গল্প: ডিসেন্ড]
গহীনে, জাহাজের পেটের গভীরে, গোঙানি শুনতে পেলাম আমরা: তার ভারী শরীরের নিচে কাঠের টানাহেঁচড়া, দেওয়ালের গায়ে জং-ধরা শেকলের ধাক্কা। এমনকি যারা লুট করতে এসেছে আমাদের ওপর তলায় তাদেরও পা টালমাটাল। বুঝতে পারছি দরজায় কড়া নাড়ছে মৃত্যু।
আর কোন উপায় না পেয়ে চারপাশের অন্ধকারে হাতড়াতে থাকি, যেন ওই স্যাঁতসেঁতে তক্তা থেকেই মৃত্যু ছুটে আসবে। জানিনা আমাদের কাকে কোথায় থেকে আনা হয়েছে, মৃত্যুর কত যে রূপ আছে; অন্ধকারে পিছু নিয়েছে চিতাবাঘ, আসলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। তবে নিচ থেকে আমরা শুধু চারটে শরীরের আবছা অবয়ব দেখতে পেলাম, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পিঠে পিঠ মিলিয়ে শক্ত করে মোড়ানো।
শেকলের যন্ত্রণা ঘুমাতে দেয় না আমাদের, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এভাবে ঘষা খেয়ে খেয়ে কব্জি আর গোড়ালিতে পঁচন ধরেছে। গভীর অবসাদে কখনও চোখ লেগে আসলে সেটা আরো বেশি যন্ত্রণার, তাড়া করে ফেরে বাড়ির দুঃস্বপ্ন – কাছের মানুষদেরও যেন নির্মম করে তুলে। যখন এই সমস্ত যন্ত্রণা থেকে একে অপরকে বাঁচানোর সব রকমের চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই ছোঁয়াচে অসুখটা ছড়িয়ে পড়ল। চামড়াগুলো যখন ফুলে ফেঁপে ফেটে যেতে থাকে, নখের আঁচড় কাটা ছাড়া তখন আর কীই করার থাকে। যদিও তাতে এতোটুকু আরাম হয় না, হাড় অব্দি পঁচন ঠেকানোর জন্য জ্বলুনি কমাতে শরীরের মাংস খাবলে তুলে ফেলি আমরা।
উপর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া নোনাজল ঘায়ে কামড় বসায়, মাথার চুলগুলো শক্ত হয়ে জটা বেঁধে যেতে থাকে।
যন্ত্রণার কাছে হার না মানার চেষ্টা করে যেতে থাকি। আমাদের হাহাকার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। শুরুর দিকে এক মহিলা তীব্র চিৎকার করেছিল, সাথে সাথে অস্ত্র হাতে একজন সাদা মানুষ নেমে আসে। আসমানের দিকে উঠে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে চলে যায় লোকটা। এরপর সেই মহিলাকে আর দেখিনি। অবশ্য রাতে ওর কান্নার শব্দ শুনতাম। এই শব্দের স্মৃতি আমাদের সবাইকে নিঃশব্দ করে দেয়, যেন হায়েনার হাসিতে লুকিয়ে থাকা মৃত্যুর শঙ্কা।
অনেকে তো প্রার্থনা করাও ছেড়ে দিয়েছিল। তারপরও কারো কারো আশা ছিল – হয়তো অজানা নিয়তির কাছে পৌঁছানোর আগে সফেদ সাগরের জল দয়া করে এই জাহাজটাকে গ্রাস করে নিবে গভীর করুণায়।
এখানে মেঝেতে ছড়ানো পূঁজ আর প্রস্রাবের পূঁতিগন্ধে ভারী হয়ে আসা বাতাস আমাদের গায়ের চামড়ায় আর নিঃশ্বাসে আটকে থাকতে থাকতে একসময় শরীরের অংশ হয়ে যাবে – যখন আর বুঝতে পারব না কোথায় দুর্গন্ধের শেষ আর কোথায় আমাদের শুরু, হয়তো তার আগে কোন মুক্তি নাই। এভাবেই আমরা একে অন্যে বিলীন হয়ে যেতে থাকি, যন্ত্রণায়, মলে, রক্তে।
সময়টাকে শুধু পার করার জন্য কিংবা বলা যায় সবকিছু ভুলে থাকার জন্য বেঁচে থাকা টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো আঁকড়ে ধরে থাকি। এই গহীনে ভাবনা খুব দামী জিনিস। আমাদের পুরো জীবন বয়ে নিয়ে যায় সেটা। একজনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুরনো দৃশ্য, বউটা ঘুমুচ্ছে তাদের ছোট্ট কুড়েঘরে, ছোট্ট বাচ্চাটা মুখ গুঁজে আছে বুকের কাছে – কী কোমল আর নিষ্পাপ চেহারা। হয়তো স্বপ্নেই দেখা হয় তাদের, যেখানে সে তখুনি পৌঁছতে চায়। কিন্তু হাত নাড়তেই এক মুহূর্তে সবকিছু হারিয়ে ফেলে, যে সমস্ত কিছু একসময় তার ছিল।
এই হারানো দৃশ্যপট তাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে যায়, অন্ধকারে বসে কাঁদে আর অজানা অচেনা এক ভাষায় বিড়বিড় করতে থাকে। আমাদের মাঝখানের ছোট্ট জায়গাটা ভরে ওঠে তার সেই তীব্র আর ভয়ানক বিষাদে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নিচু গলায় কাঁদতে অভ্যাস হয়ে গেছে, কদাচিৎ কেউ বিলাপ করে। আর এবার এই বিষাদের সাথেও মানিয়ে নিতে হয়।
‘পুরনো কথা মনে পড়েছে?, কাঁদতে থাকা লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে একজন।
ফোঁপানো থামায় সে, নিচু হলেও নিস্তব্ধতাকে গিলে খাওয়ার মতো দৃঢ় তার গলার স্বর। ‘সবকিছু’ বলে সে, ‘আমার সারা দুনিয়া। যে মাটিতে জন্মেছি, যে রোদে পুড়েছি, আমার পূর্ব পুরুষের আওয়াজ’।
এসব কথা অনেকের কাছেই তখন কতগুলি এলোমেলো শব্দ ছাড়া আর কিছুই না, ওর কথায় একটা চেনা টান ঠাহর করতে পেরে অন্ধকারের ভেতর থেকে কথা বলে ওঠে আরেকজন।
‘বাড়ি কোথায় তোমার?’
‘আনোমাবো। আর তুমি?’
‘আসিন মানসো, ওই যে বড় জঙ্গলের পাশেই’
তাদের গলার স্বরে হঠাৎই অদ্ভুত এক মরিয়া আনন্দ, যেন অন্ধকারে দুটো আত্মা এক হয়ে যাচ্ছে। আর সেই মিলনে আন্দোলিত হয়েই যেন আমাদের পায়ের নিচে জাহাজটা দুলে ওঠল। উপরতলার চলাফেরা ক্রমেই উন্মত্ত হয়ে ওঠে, সাদা মানুষগুলোর নিচু গলার কথাবার্তা চিৎকারে পরিণত হতে থাকে। কুয়াশার মতো করে ভয়ের ভারী পর্দা নেমে আসে।
‘কাঁদছিলে কেন বলো? পুরনো দিনের কথা বলো শুনি’, অন্য কেউ একজন বলে ওঠে আবার।
কেঁপে ওঠা শ্বাস টেনে নিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে লোকটা। ‘ওর কথা ভুলতে পারি না’, শব্দের নিচে চাপা পড়া গলায় বলে সে। তার সেই নিরবতা দীর্ঘ হয়ে আমাদের সবাইকে ঘিরে ফেলে। পরেরবার যখন মুখ খোলে, বড়জোর ফিসফিসের মতো শোনা যায়। ‘দুনিয়ার সব শক্তি এক হলেও তাকে কখনও ভুলতে পারব না’।
আমরা সবাই দম আটকে তার কথা শুনতে থাকি। শব্দগুলো যেন আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে, আরো কাছে টেনে আনে, ক্রমেই জড়িয়ে ফেলে তার বিষাদে। ধীরে ধীরে সেসবের সাথে চেনাশোনা হয়ে যায়, তার ভেতরে ডুবে যেতে থাকি, যেন ওরাই আমাদের অন্য কোথাও থেকে এই স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকারে টেনে নিয়ে এসেছে।
আর এভাবেই গল্প বলার শুরু, একটা থেকে আরেকটা গল্পের জন্ম। যা আমাদের উষ্ণ রাখে, শরীরে একটু জোর জোগায়, ব্যথার উপশম করে, বিদ্যুতের মতো বয়ে যায় শিরা উপশিরা বেয়ে। জাহাজের পাটাতন ভেঙে তারা এক টুকরো আকাশ আর ফেলে আসা দুনিয়ার ছবি দেখায়।
অতএব আমরা গল্প চালিয়ে যেতে থাকি আর জাহাজের অন্ধকারে সেই গল্প বলা মানুষটা যেন ছড়িয়ে দেয় নরম আলোর প্রভা।
জমির কিনারা
রোজ সকালে জমির এক কিনারে আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকত সে, পিঠে একটা ঝুড়ি আর ঠোঁটের কোণে ভ‚বন ভোলানো হাসি নিয়ে। গাঁয়ের এক বুড়ো কবিরাজের মেয়ে, চোখে ছিল মায়ের মতো বুদ্ধির দীপ্তি।
ওর স্বপ্নের কথা জানতাম – যে স্বপ্ন ছড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের চাষের জমিন থেকে আরো বহু দূরে, যেমন জীবন আমরা গড়ে নিতে চাই তার থেকে আরো বেশি কিছু। স্বামী, সংসার, ছেলেপুলে নিয়েই সবাই খুশি থাকতে চাইতো, সে না। তার চাওয়া ছিল অন্য কিছু। জমিনের রোগ সারাতে চাইতো, বৃষ্টি নামানোর কিংবা ফসলের জমিকে আবারও উর্বর করার উপায় খুঁজত। গ্রামটা মরুভূমি হয়ে উঠলে ফেটে যাওয়া মাটি আর শুকিয়ে যাওয়া ফসল খুব বিচলিত করতো তাকে।
দিনের সব কাজকর্ম শেষে দুদন্ড শান্তি নেমে আসলে অসীম নীল আকাশের নিচে বসে এসব কথা বলত মেয়েটা। মাটি ভেদ করে চলে যাওয়া শেঁকড় আর মুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় থাকা জমিনের ভেতরের শক্তির কথা বলত। বিশ্বাস করত, মায়ের শেখানো শেঁকড়-বাকল আর খোদার কাছে মিনতির বাইরেও একটা কিছু আছে। সে যা দেখতে পেত, অন্যরা পেত না, কিংবা আদৌ দেখত না।
ওর ভাবনা সবসময় আলাদা ছিল। ছেলেপুলে মানুষ করা, রান্নাবান্না, স্বামীর দেখভালের মতো এতো কাজ থাকতে কেন মেয়েটা শুধু জমির কথাই ভাবে সেটা গাঁয়ের বৌঝিদের মাথায় ঢুকত না। সবসময় মাথা একদিকে কাত করে কিছু একটা শোনার চেষ্টা করত যেটা আদতে কেউ শুনতেই পাচ্ছে না, এসব দেখে অনেকেই ওকে পাগল ঠাওরাতো। কেউ বোকা বলত, কেউ একগুঁয়ে। তবে আমার কাছে সে ছিল একটা দিব্যদৃষ্টি, নিরব মাধুরীতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি, ওকে ভালোবাসতাম।
ওর এই স্বপ্ন, নিজের মতো করে দুনিয়া দেখার ব্যাপারটা তার বাবা মায়েরও অস্বাভাবিক মনে হয়, এসব তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলতে পারে। সবাই বুড়ো কবিরা কে মান্য করলেও নিজের মেয়েকে সে বাঁচাতে পারেনি কানকথা থেকে। বাঁচাতে পারেনি বিয়েশাদি কিংবা বাচ্চা পয়দা না করে গাছ আর বৃষ্টির কথা ভাবতে থাকা আজব মেয়েটাকে তাদের বাঁকা চোখগুলো থেকে।
সেই দিনটার কথা আজো মনে আছে যেদিন আমাকে ডাকা হয়েছিল ওদের বাড়িতে। ওর বাবা মুখোমুখি বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। রুক্ষ হাত আর কড়া চোখের শান্ত মানুষটা কথা শুরুর আগে ইতস্ততঃ করলে তার চোখে দ্বিধা দেখতে পেয়েছিলাম। ‘তুমি তো জানোই সে আর দশটা মেয়ের মতো না’, সাবধান বানীর মতো করে বলে, ‘ও কিন্তু কখনও বদলাবে না। ওকে বিয়ে করলে সারাজীবন এইসব আজগুবি ভাবনা নিয়েই থাকতে হবে’।
‘জানি’, নির্দ্বিধায় বললাম তাকে, ‘এইজন্যই তো ওকে আমার চাই’।
বাবা-মা চোখ চাওয়াচাওয়ি করে, মা’র ভ্রু কুঁচকে ওঠে, ঠোঁট শক্ত হয়ে যায়। তারা যে ওকে ভালোবাসে সেটা জানি, সেই সাথে এমন পয়মন্ত আর রহস্যময় একটা মেয়েকে নিয়ে কী করবে ভেবে পায় না। অবশেষে রাজি হয় তারা, আমি তাকে খুব সুখে রাখতে পারব সেজন্য না, বরং হয়তো আর কাউকে পাওয়া যাবে না সেই কারণে। তারা ভাবে হয়তো আমিই ওর সবচেয়ে উপযুক্ত।
হয়তো সেটাই ঠিক। অন্যরা তাকে নিয়ে কী ভাবত সেসব কথায় কখনও পাত্তা দিইনি, আদৌ সে গতানুগতিক বউয়ের ছাঁচে পড়বে কীনা সেসব নিয়েও মাথা ঘামাইনি। আমার কাছে সে ছিল সেই সমস্ত কিছু যার প্রয়োজন আগে কখনও বুঝিনি। গভীর অন্ধকার কোন জগতে এক মুহূর্তের বুনো স্ফুলিঙ্গ।
আমার পিতা কিংবা পিতামহের মতো করেই জীবন গড়ি আমরাও। গাঁয়ের ছায়া দেওয়া শিমুল গাছগুলোর মতো লম্বা হয়ে ওঠে আমাদের ছেলেরা। সহজে নেতিয়ে পড়ে না এমন গভীর শেঁকড়ের গাছ লাগানো শুরু করে সে, যেদিকে সচরাচর কেউ নজর দেয় না, সেই সাথে কাসাভা আর ভুট্টার সারির মাঝে নানা রকম ঔষধি আর ফুলের গাছ। সে বলে এগুলো নাকি জমিনের ওষুধ। ‘জমিরও তো শ্বাস নেওয়ার দরকার আছে’ বলতে বলতে গাঢ় বিশ্বাসে চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ‘শরীরের মতোই তাদেরও যত্ন নিতে হবে’।
ওকে দেখে গর্ব আর ভয়ের মিশেলে আমার বুক ভরে উঠত। কথাগুলো বিশ্বাস করতে চাইতাম, আবার গাঁয়ে এসব নিয়ে কানাকানির কথাও জানতাম। উবু হয়ে ফিসফিস করে চারাগাছদের সাথে কথা বলতে দেখে হতাশায় মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কীবা করার ছিল তাদের?
‘এইসব গাছ কী কাজে আসবে?’ বলত ওরা, ‘খেতে তো পারবে না এগুলো’।
এসব কোন কিছুই পাত্তা দিত না। ঠিক সন্তানের মতো করে গাছগুলোর যত্ন নিতো। যখন সবাই বলত পানি দেওয়া বৃথা তখনও গাছগুলোকে জল দিত, সন্ধ্যায় তাদের জন্য গান গাইত। গানের গলা ছিল খুব নিচু আর কোমল। তারপর ধীরে ধীরে প্রায় অদৃশ্য এক বদলে যাওয়া দৃশ্যপটের ভেতর দিয়ে মাটি সাড়া দিতে শুরু করে। যেটা একসময় শুকনো বাদামী মাটি ছিল সেই জায়গাটাই ধীরে ধীরে কোমল হতে থাকে, একটু একটু করে সবুজের আভাস দেখা যেতে থাকে।
না এটা কোন জাদু, না গায়েবী ব্যাপারস্যাপার। আসলে এটা একটা – প্রতিশ্রুতি, একটা শুরু। যদিও আশেপাশের কেউ বুঝতে পারেনি, তবে জানতাম একটা কিছু করতে যাচ্ছে সে। শেষ বিকেলে ওকে ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম, বাতাসে দুলত ওর চুলের বেনীগুলো, তাকে দেখে মনে হতো ওই মাটিরই একজন, যেভাবে সে মাটির অংশ হয়ে উঠেছিল সেটা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব ছিল না।
ওর আর সব ব্যাপারের মতো এটাও ঘটে গেল একেবারে নিঃশব্দে। একদিন সকালে বলল তার জঠরে আমাদের সন্তান। নিজের পেটের ওপর হাত রেখে এমন শান্ত আর নিশ্চিত ভঙ্গিতে কথাটা বলল যে এক মুহূর্তের জন্য দম আটকে গেল আমার। যখন বলল পুত্র সন্তান তখনও বিশ্বাস করলাম, কারণ এসব জেনে ফেলার উপায় তার কাছে ছিল।
ছেলের জন্ম হলো এক পূর্ণিমার রাতে, মাঠের কোলে নেমে এসে রূপালি আলোয় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া এমন বিশাল পূর্ণচন্দ্র আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ওর নামে রাখল আমানি, যার অর্থ শান্তি।
শেষবারের মতো ওদের দুজনকে ঘুমুতে দেখার কথা মনে পড়ছিল। সেদিন সকালে বেরিয়ে আসার সময় হাতটা ধরে রেখেছিল বেশ কিছু সময়। আমার চোখে কিছু একটা খুঁজছিল, যেন সবকিছু জানত। ওকে বললাম পরের মাসেই চলে আসব। কথা দিয়েছিলাম। সব সময়ের মতো ফসলের মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকবে এই আশা নিয়ে আমিও বেরিয়ে আসলাম।
জানিনা এখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে কীনা।
–
তার কথাগুলো যেন বাতাসের ভেতরে আটকে থাকল। অনেকটা সময় ধরে শুধু একে অপরের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনলাম – ঠুনকো আর ভাঙা ভাঙা ছন্দে। এই গল্প সবার মনের বিষাদ টেনে বের করে নিয়ে অন্ধকারে ধোঁয়ার মতো কুন্ডলি পাকিয়ে দিয়ে গেল। যদিও সেটা খুব বেশি সময় থাকল না।
জাহাজটা গর্জন করে দুলে ওঠল। আমরাও সেই সাথে কেঁপে উঠলাম, পাটাতনগুলো নড়তে লাগল, শেকলগুলো তাতে ঘষা খেতে থাকল। সব মোহ মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। সামনে কী হতে চলেছে সেটা ভেবে নড়েচরে বসলাম। এমন সময় অন্ধকারের এক কোণ থেকে আরেকটা গলার স্বর শোনা গেল, কাঁপাকাঁপা কিন্তু দৃঢ় সেই নারী কন্ঠ।
‘আমরাও জমি নিয়ে লড়াই করেছি’, বলে সে। ‘তবে তোমার বউয়ের মতো যত্ন নিইনি, খোদার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম’।
প্রাচীন আর জীর্ণ সেই গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় উলুখাগড়ার বনের ভেতর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের ফিসফিসানি।
প্রার্থনার প্লাবন
বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলাম আমরা। মাসের পর মাস আমাদের পায়ের নিচের তৃষ্ণার্ত মাটি ফেটে যাচ্ছিল পুরনো শুকনো কাদার মতো। নদীটা শুকিয়ে নালায় পরিণত হয়েছিল, ছাগলগুলো এমন শুকিয়ে গিয়েছিল যে চামড়ার নিচে থেকে ওদের পাঁজরের হাড়গুলো গোনা যেত। রোজ সকালে গাঁয়ের মাঝখানে এক হয়ে আকাশের দিকে করজোড়ে ভিখ মাঙতাম আমরা।
প্রার্থনা শুরু করতো বয়স্করা, আসমানের দিকে তোলা হাতের সাথে সাথে তাদের গলার স্বরও চড়তে থাকত। চাইতে চাইতে ভেঙে যাওয়া গলায় তাদের সাথে তাল মেলাতাম। খুব অল্প পরিমাণে হলেও খাবার এনে গাঁয়ের মাঝখানটাতে রেখে দিতাম এই আশায় যে খোদা হয়তো আমাদের আহাজারি দেখে কিছু জবাব দেবে। এভাবে দিন পার হয়ে যেত। তবু আকাশ আগের মতোই পরিষ্কার আর নির্মম।
আর তারপর একদিন বৃষ্টি আসল।
প্রথমে ছোট ছোট কতগুলি ফোঁটা এসে পড়ল জমিনে, যেন খোদা তার উপহারের পরীক্ষা নিচ্ছে। আনন্দে মেতে উঠলাম আমরা। মুখ উঁচু করে সেই বৃষ্টির শীতলতা অনুভব করতে করতে দু হাত বাড়িতে নেচে ওঠল মেয়েরা। বৃষ্টির ছন্দের সাথে সাথে হর্ষধ্বনি মিলে মিশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে। কাদায় মাখামাখি হয়ে খালি পায়ে গ্রাম জুড়ে ছুটোছুটি করল ছেলেপুলেরা। আমি শুধু দূরে দাঁড়য়ে মাটিকে তার তৃষ্ণা মেটাতে দেখছিলাম। এক রকমের পাপ মোচন বলে মনে হলো আমাদের।
কিন্তু পরের দিন যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আর কোন রিমঝিম বৃষ্টি না, এবার একনাগাড়ে ঝরতে থাকে, যেন মাসের পর মাস শুঁষে নেওয়া পানি একবারে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভাবতেও পারিনি এতো তাড়াতাড়ি নদীটা এভাবে ফুলে উঠবে। শুকনো ফসলের মাঠগুলো ডুবে যাচ্ছে, যে ফসল বাঁচানোর জন্য এতো যুদ্ধ সেগুলো ভেসে যাচ্ছে।
প্রথমে এসব নিয়ে কেউ কথা বলেনি। ভেবেছিলাম হয়তো বৃষ্টি ধরে আসবে, তাই প্রার্থনা শোনার জন্য খোদার কাছে শোকর জানায় সবাই, মনের জোর হারায়নি কেউ। তবে আশেপাশে কেউ না থাকলে আমরা ফিসফিসিয়ে বলতাম, হয়তো বেশি বেশি প্রার্থনা করা হয়ে গেছে।
একদিন সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তখনও বৃষ্টি পড়ছে। ক’দিন আগের শুকনো ধারাটা ততদিনে ধেয়ে আসা বুনো নদীতে পরিণত হয়েছে। দুই পার ভেঙে ক্রমাগত মাটি খেয়ে চলেছে। চোখের সামনে একটা পবিত্র গাছ মুহূর্তেই নদীর বুকে বিলীন হয়ে গেল, যেন ওখানে কিছু ছিলই না।
এটা আসলেই ঈশ্বরের উপহার, নাকি তার ক্রোধ ভেবে পাই না।
বাড়ির ভেতরে গাদাগাদি করে সবাই শুধু দেওয়ালে বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে থাকি। মুখে কেউ কিছুনা বললেও সবাই মনে মনে বুঝতে পারে, দয়া ভিক্ষে করলেও বিনিময়ে যা পেয়েছি তা বেশি হয়ে যাচ্ছে।
–
‘পানি ওখানে!’
পুরনো স্মৃতির খাতা খোলার মতো করে বুড়ির নরম গলার আওয়াজে কিছুই খেয়াল করিনি। যতক্ষণ না সেটা আমাদের গোড়ালি অব্দি উঠে আসে।
‘ভেতরে চলে আসছে’, আরেকজনের চিৎকার শোনা যায়, ‘দেওয়ালের দিকে দেখো!’।
ফাঁক ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সাপের মতো কাঠের শরীর বেয়ে নামছে পানি। নড়েচরে বসি – তাতে শেকল ঝনঝন করে, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ে, জলের ওপরে ঢেউয়ের মতো করে ভয় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
অন্ধকারের কোনখান থেকে একটা মেয়ে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, ‘সামনে দেখো! একেবারে ফুলের মতো’ বলে সে। তার গলায় খুশি, তবে জ¦রের স্পর্শের মতো দ্বিধাগ্রস্ত।
ভয় কাটানোর জন্য ওর সাথে তাল মেলায় আরেকজন, ‘হ্যাঁ, ছোট ছোট। একদম ফুলের মতো’।
‘ফুলগুলো আমি চিনি’, ফিসফিস করে বলে মেয়েটা, এক অস্থির আনন্দে বিড়বিড় করার মতো শোনায়, ‘সদর দুয়ারে ওপাশ থেকে ওগুলো তুলেছিলাম’।
‘সেসব দুয়ারের বাইরে’, মন ভোলানোর জন্য বলে আরেকজন, ‘সেগুলো নিয়ে অনেক স্মৃতি, তাই না?’
‘হ্যাঁ’, আনমনে বলে মেয়েটা, ‘হয়তো পানি চলে গেলে দেখব ফুলগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে’।
উপর থেকে চিৎকার ভেসে আসে – সাদা মানুষগুলোর মুখে যেন তীর ছুটছে – তবে সেসব শোনার আর সময় নেই। আমাদের ভেতরে জমাট বাঁধা ভয় ধীরে ধীরে গলে যেতে থাকে, সরে যাওয়া জোয়ারের মতো মিলিয়ে যেতে থাকে গভীর অন্ধকারে।
‘বলো’, অন্ধকার থেকে আকুতি করে সেই কন্ঠস্বর, ‘দরজার বাইরের ফুলের কথা বলো আমাদের’।
আর এভাবেই আরেকটা গল্প শুরু, আমাদের মাঝখানের অন্ধকারে সেটা নরম কুঁড়ির মতো ফুটে থাকে, যার শব্দগুলো কিছু সময়ের জন্য হলেও যেন সমুদ্রকে আটকে রাখে।
দুয়ারের ওপাশে ফুল
সেদিন ভেবেছিলাম সদর দুয়ার থেকে খুব বেশি দূরে যাব না। সূর্য ততক্ষণে দীর্ঘ আর সরু ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার দিকে নজর রাখছে। অবশ্য ছায়া এতো দীর্ঘ হওয়ার মতো অতোটা বেলা হয়নি তখনও। ঝুড়িটা একপাশে শক্ত করে চেপে ধরে নিজেকে বুঝালাম, তাড়াতাড়ি করতে হবে, যে কোন সময় কেমি’র সন্তান হতে পারে। ব্যথা কমানোর জন্য এই বুনো শেঁকড় আর পাতাগুলো জোগাড় করতে এসেছি। এসব কাজে ওরা সবসময় আমার ওপরেই ভরসা করত।
কোন গাছের শেঁকড় সেদ্ধ করতে হয়, কোন গাছের পাতা বেটে নিতে হয় খুব ভালো করে জানা ছিল। এসব আমাদের রক্তে মিশে আছে। নানীর কাছ থেকে পেয়েছিল মা আর মায়ের কাছ থেকে আমার কাছে এসেছে। সঠিক শেঁকড়টা খুঁজে পেলে আর কোন বিপদ নাই।
পাহারাদাররা সদর দুয়ারের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, ওদের হাতের বর্শাগুলো সাদা দাঁতের মতো ঝকঝক করছে। দিগন্ত জুড়ে মেলা তাদের চোখ। এরা চোখের সামনে আছে মানে আর কোন ভয় নেই। উবু হয়ে বসে আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে শেঁকড় তুলতে থাকি। এই পরজীবী শেঁকড়গুলো এমন শক্ত আর পাকানো যে সহজে উঠে আসতে চায় না। আরো জোরে টান দিলাম, কেমির জন্য দরকার এগুলো। কিনকেলিবার পাতা দিয়ে বানানো তেতো চা প্রসব বেদনা কমাতে ভালো কাজে দেয়। অথচ এই উপকারি গাছগুলো ঘরের আশেপাশে জন্মায় না, উল্টো এরা জমির ফসল নষ্ট করে।
ঠিক তখনই গাছটা চোখে পড়ল – চিনিকা। সবুজ পাতার ভেতরে গোলাপী, লাল আর সাদা উজ্জ্বল পাঁপড়িগুলো তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। এগুলো তো এখন এখানে থাকার কথা না, মানে এই মৌসুমে এমন শুকনো বাতাসে। যখন মাটিয়ে শুকিয়ে চৌচির তখন হওয়ার কথা না। তারপরও দেখছি বেশ বহাল তবিয়তেই রয়েছে। জখম সারাতে কিংবা জ্বর কমানোর জন্য এর শেঁকড় বেশ কাজের। তবে এটাও জানতাম যে সৈন্যরা তাদের বর্শার ফলায় এটা মাখিয়ে নিতো। শুধু একটুখানি খোঁচা দিতেই রক্তের বন্যা বয়ে যেত।
আবারও পাহারাদারগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে বোঝালাম, খুব বেশি দেরী হবে না। ফুলগুলো খুব বেশি দূরে না, এই তো কয়েকটা গাছের পরেই, একটু দূরে যেখানে পৃথিবী বুনো শ্বাস নেয়। একটু তাড়াতাড়ি করলে কেউ খেয়াল করবে না।
উঠে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। রেশমের মতো নরম কোমল পাপঁড়িগুলো আমার আঙুলে ছুঁয়ে গেল। তাদের অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ যেন বুকের ভেতর অচেনা কোন সুর গেঁথে দিল। অল্প কয়েকটা তুলে ঝুড়িতে ভরে নিলাম। এটুকুতে হবে না, আরো লাগবে।
যতোই তুলতে থাকি, মনে হয় আমার আরো লাগবে। শেঁকড়গুলো ঘুমন্ত সাপের মতো পেঁচিয়ে ছিল, যেমন মোলায়েম তেমনি মারাত্মক। তাদের ক্ষমতা অবাক হওয়ার মতো – এমন সুন্দর একটা জিনিস যেমন জীবন বাঁচাতে পারে তেমনি পারে কেড়ে নিতে, নির্ভর করছে সেটা কার হাতে পড়েছে।
মাথা তুলে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম কতটা দূরে চলে এসেছি। আশেপাশে না আছে কোন পাহারাদার, না কোন গ্রাম। হঠাৎ করে বাতাসটাকেও কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো – খুব বেশি স্থির আর শূন্য। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ঝুড়িটাকে শক্ত করে আকঁড়ে ধরে দৌড়তে থাকি, শেঁকড়গুলোতে পা হড়কে গেলেও সামলে নিয়ে আবার দৌড়াতে থাকি সদর দুয়ারের দিকে।
ফিরে যেতেই মহিলারা এগিয়ে আসল, ঝুড়িতে থাকা ফুল আর শেঁকড়গুলো নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালো তারা। চিনিকা’র কথা বললাম ওদেরকে, কেমন ভীষণ জ্বলজ্বল করছিল। এই মৌসুমের জন্য সেটা একটু বেশিই, তবে ওগুলো সদর দুয়ারের বাইরে ছিল। সবটা বুঝতে পেরে ওদের চোখ চকচক করে ওঠল।
‘আজ রাতেই যাওয়া উচিত’, একজন ফিসফিস করে বলল জরুরি ভঙ্গিতে। ‘ফুলগুলো তরতাজা থাকতে থাকতেই’।
কিন্তু পথ আগলে দাঁড়ায় পাহারাদার। ‘রাতে যাওয়া যাবে না’, নিচু গলায় শাঁসায় তারা। ‘বিপদ হতে পারে। সাদা শয়তানরা নজর রাখে, গ্রাম থেকে বেশি দূরে গেলে ধরে নিয়ে যায়’।
ওদের কথা শুনে হাসি। ‘কী আজব কথা? সাহসী সৈন্যরা এসব আষাঢ়ে গল্প শুনে বড় হয়েছে তাহলে?’। তবে ওদের চেহারা গম্ভীর, হাত বর্শায় স্থির। অতএব অপেক্ষা করতে থাকি, ঠিক করি খুব ভোরে রাতের শীতলতা হারিয়ে যাওয়ার আগেই যাব ওখানটাতে।
সূর্যের প্রথম আলো মাটিতে পড়তেই খুব ভোরে ওঠে তাড়াহুড়ো করে জঙ্গলের দিকে ছুটলাম আমরা। কিন্তু ওখানে পৌঁছে দেখি জ্বলজ্বলে ফুলগুলো আর নেই। না কোন পাঁপড়ি, না তার কোন চিহ্ন। শুকনো আর ফেটে চৌচির শূন্য মাটি দেখে মনে হয় না এখানে কখনও কিছু জন্মেছিল।
সদর দুয়ারের কাছে ফিরে আসার পথে কেউ কোন কথা বলল না। শুধু আমাদের পায়ের নিচে শুকনো পাতার খচমচে শব্দ শোনা যাচ্ছিল, প্রতিটা ধাপে ধাপে কিছু একটা হারানোর বেদনা হাড় অব্দি গিয়ে পৌঁছায়। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে শুধু কতগুলো ফুল ছিল, তবে সেটা নিজের কাছেই সত্যি বলে মনে হয় না। আরো অন্য কিছু চলে গেছে হাতের নাগাল থেকে, নাম না জানা একটা কিছু।
–
এক মুহূর্তের জন্য মেয়েটার গলায় অদ্ভুত হাসি ঝুলে থাকে, অনেকটা স্যাঁতসেঁতে কাফনের মতো। ওর গল্পে শুনতে পাই শুধুই এক শূন্যতা, দূরের সুর, কোন ভাঙা বাদ্য থেকে ভেসে আসা গুঞ্জনের শেষ কাঁপুনিটুকু। একটা কিছু হাতের নাগাল ছেড়ে যাওয়ার শব্দ।
ওর আগের জীবন নিয়ে কিছুই জানার কোন উপায় ছিল না আমাদের।
তবে এটুকু বুঝতে পারি এই গল্প নিছকই কোন ঘটনা না – সম্ভবত এটাই ছিল ওর শেষ স্মৃতি। কিংবা মাথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এটাই একমাত্র স্মৃতি। এটাও জানি, জীবনের শেষ সম্বলের মতোই এই স্মৃতিটুকু আঁকড়ে ধরে আছে – পায়ের নিচে ভেঙে চূরমার হয়ে যাওয়া পৃথিবীর একটা সত্যিকারের কিছু।
‘ফুলগুলো আমি চিনি’, আবারও ফিসফিস করে বলে মেয়েটা, ‘সদর দুয়ারের ওপাশ থেকে ওগুলো তুলেছিলাম’।
আমাদের চারপাশের সমুদ্র কাঠের ওপর আরো জোরে জেঁকে বসতে থাকে, যেন বুনো জানোয়ারের দল এখুনি পাটাতনগুলো ভেঙে ঢুকে পড়বে। নোনাজল পায়ের কাছে এসে ঘূর্ণি তুলে, বাড়তে থাকে ঠান্ডা, তবু কেউ একটুও নড়েচড়ে বসে না। কোন অভিযোগও করে না। কেবল চুপচাপ বসে অপেক্ষা করে থাকি পরের কন্ঠস্বরের জন্য। আরেকটা গল্প শোনার জন্য, হারানো দুনিয়ার সাথে আরো খানিকটা সময় জুড়ে থাকার জন্য।
তারপর প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করে অন্ধকার থেকে একটা গলার স্বর ভেসে আসে। ‘একটা ছেলে ছিল’, শুরু করে সে।
জাহাজটা যেন একটা নিচু ফাঁপা আওয়াজ করে বলার চেষ্টা করে ‘আমিও শুনছি’।
শিকারির হাত
শুরুতে গলার স্বরটা এতো নিস্তেজ ছিল যে জলের আওয়াজ আর কাঠের ক্যাঁচক্যাঁচের ভেতর দিয়ে শোনাই যাচ্ছিল না। পরে সেটা ধীরে ধীরে তেজী হয়।
‘একটা ছেলে ছিল’, আবারও শুরু করে। ‘মাত্র ছয় বছর তার বয়স। ছোটখাট আর শুকনো পাতলা শরীর, তবে ওর ভেতরে একটা আগুন ছিল, ওই ছোট্ট শরীরটাতে আঁটে না এমন এক প্রচন্ডতা। ভাইদের মতো যোদ্ধা হতে চাইতো সে। তীক্ষè বর্শা হাতে উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে দৌড়াতে চাইত, শক্তিশালী আর সাহসী হতে। অথচ তাল পাতার সেপাই বলে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করত তারা। তবু সে তাদের সাথে লেগে থাকত, মাঝেমাঝে পিছিয়ে পড়লেও অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত একরোখা জেদ নিয়ে’।
একটু থামতেই গলাটা এমনভাবে কেঁপে ওঠে যেন খুব ভারী কিছু বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।
‘একদিন সন্ধ্যায় সূর্য পটে নেমে এলে জমিনে দীর্ঘ ছায়া পড়ল, ভাইয়েরা শিকার থেকে ফিরে আসল। ছোট ছেলেটা নেই তাদের সাথে। নাম ধরে ডাকাডাকি করল সবাই, তবু কোন জবাব নেই। গায়ের জোর দেখানোর জন্য এবারও নিশ্চয় চুপিচুপি সটকে পড়েছে। ওদের মা … ভীষণ রেগে গেল, ওর নাম ধরে চিৎকার করতে লাগল, নিজের চুল ধরে টানতে থাকল। সে জানে বাইরে কত শ্বাপদ জানোয়ার আছে, ফলার মতো ধারাল তাদের দাঁত, অন্ধকারে জ¦লজ¦ল করে চোখ’।
গল্পে সাড়া দিতে জাহাজটাও যেন আওয়াজ করে ওঠল। পানিও আরো উঁচুতে উঠতে লাগল।
‘শুধু পশুর থাবায় তাদের ভয় ছিল না। সেখানে আরো অন্য কিছু ছিল – যাদেরকে বলতাম সাদা দানব। ছায়ার মতো হেঁটে চলা মানুষগুলো চোখের পলকে শিশুদের ছিনিয়ে নিতো, তাদের আর পাওয়া যেত না। এমনভাবে হারিয়ে যেত, যেন কোন অস্তিত্বই ছিল না। সারারাত ধরে ওকে খোঁজে সবাই, ঝোপঝাড়ে, পাহাড়ে, নদীতে কিন্তু কোথাও নেই। একটা পায়ের ছাপ পর্যন্ত না। যেন জমিন গিলে খেয়েছে ওকে’।
বাতাসের মতো দুলতে দুলতে ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসে গলার স্বর, তারপর আবারও দৃঢ় হয়ে ওঠে নতুন এক যন্ত্রণায় – যার নাম আশা।
‘খোঁজ থামেনি’, চলতে থাকে গল্পের স্বর। ‘পরের দিন অনেকক্ষণ ধরে জঙ্গলের ভেতরে চিরুনি অভিযান চালায় ওরা, নাম ধরে ডাকে, কোন একটা চিহ্ন কিংবা কোন ফিসফাস আওয়াজের সন্ধান করতে থাকে। আর তারপর সূর্য ডুবুডুবু ঠিক এমন সময়ে ওকে খুঁজে পাওয়া গেল। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল, কোলের ওপর একটা সজারু – ওটার গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট বর্শার মতো কাঁটা। ওর হাতগুলো কেটে রক্তে মাখামাখি, তবু এতটুকু ভয় নেই, একটুও সরে আসছে না। সজারুটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য খুব সাবধানে আঙুল নাড়িয়ে একে একে কাঁটাগুলো তুলে নিচ্ছিল।
‘কী করছ এখানে?’, খুঁজে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করে ভাই। শুকনো দেহের ছোট্ট ছেলেটা মুখ তুলে তাকায়, ওর চোখে শান্ত আগুন। ‘শিকারী তার লোকদের খাওয়ায়’, বলে সে, ‘আমিও তোমাদের মতো কিছু নিয়ে ফিরতে চেয়েছিলাম। পারব, কিছু একটা করতে পারব’।
রক্তে মাখামাখি হাত আর আঙুলের ফাঁকে ঘুমিয়ে থাকা সজারুটাকে দেখে ওরা বুঝতে পারে সে আসলে হারায়নি। সেও খুঁজছিল – তবে সেটা বাড়ি ফেরার পথ না, নিজেকে প্রমাণ করার উপায়। আর ঠিক ওই মুহূর্তে ওরা কোন শিশু না একটা যোদ্ধাকে দেখতে পায় ওরা – ছোট হলেও যার বুক ভরা সাহস, রক্তাক্ত হলেও যার হাত কখনও থামবে না।
বগলের নিচে সজারুটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসলে গোটা গ্রামের মানুষ ভীড় করে ওকে দেখার জন্য। আর কেউ ওকে তাল পাতার সেপাই বলে না। ওর হাত দেখে সবাই বুঝতে পারে সাহস কাকে বলে। সেদিনের পর থেকে আর কখনও পেছনে পড়ে থাকেনি সে। শুধু বড় শিকার নিয়ে আসা নয়, আসল শিকারি কখনও হার মানে না, না যন্ত্রণায়, না রক্তাক্ত হাতে’।
ফিসফিসানির মতো নরম শোনায় তার গলার আওয়াজ। ‘আমরা সবসময় পথ ভুলে হারাই না, পথ খুঁজতে গিয়েও হারাই। আর কখনও যেটা খুঁিজ সেটা না পেলেও যা পাই তা ঢের বেশি। সেটাই যথেষ্ট’।
পানি উঠতে উঠতে আমাদের বুক থেকে গলা অব্দি পৌঁছে যেতে থাকে, তবু মানুষটার কথায় হেরফের হয়না এতোটুকু। ধীরে ধীরে একটু নড়ে বসতেই ওর হাতে ধাতব একটা কিছু চকচক করে ওঠে, ছোট আর ধারাল, শুকিয়ে যাওয়া গাঢ় রক্তের দাগ ওটার গায়ে। ‘শুধু কি ওই ছেলেটাই শিখেছিল কীভাবে এগিয়ে যেতে হয়’, বলে সে, ‘পায়ের তলায় জখমের ভেতর করে এটা বয়ে বেড়িয়েছি দিনের পর পর, নিজেকে মুক্ত করার একটা মুহূর্তের অপেক্ষায়। আজকের রাতে সেটা পেয়েছি’।
ধারাল জিনিসটা ওর আঙুলের ফাঁক গলে কাঠের মেঝেতে টোকা মেরে চাপা ধাতব শব্দ তুলল। শেকলের বাঁধনগুলো আলগা হতেই ওটার কাজ শেষ। ‘শিকারি তার লোকদের জন্য খাবার জোগায়’ বিড়বিড় করে বলে সে, তার চোখ শান্ত আর স্থির। ‘আর যোদ্ধা উপায় খুঁজে নেয়, সেটা যতো ছোটই হোক’।
সবার ভেতর ভেতর একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে – একটুখানি আশার ঝিলিক, ম্লান হলেও সত্যিকারের। জাহাজের গভীরে, গহীন অন্ধকারে বসে আবারও আশায় বুক বাঁধি।
আমাদের পৃথিবী শেষ হয়ে যায়নি, দেখো। ভেঙেছে, দুমড়ে-মুচড়ে গেছে, তবু শেষ হয়নি। সমুদ্র হয়তো আমাদের শরীরগুলোকে চাইতে পারে, কিন্তু যে গল্পগুলো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল, যে আশায় আমাদের নিঃশ্বাস ছিল সেগুলো ছিনিয়ে নিতে পারেনি।
আমরা এখনও এখানে, শ্বাস নিচ্ছি, বেঁচে আছি আমাদের গল্পে। সেটা ওরা কেড়ে নিতে পারেনি।

আসাদুল লতিফ
লেখক ও অনুবাদক।
প্রকাশিত অনূদিত উপন্যাস: হান ক্যাং-এর “দ্য হোয়াইট বুক” (২০২৫); আব্দুলরাজাক গুরনাহ’র “মেমোরি অব ডিপারচার” (২০২৪); সাতোশি ইয়াগিসাওয়া’র “মোর ডেইজ অ্যাট দ্য মরিসাকি বুকশপ” (২০২৪)। ছোটগল্প: হারুকি মুরাকামি’র “শেহেরজানের অসমাপ্ত গল্প” (২০২৩); বিভিন্ন লেখকের “কিছু বিষাদ উপাখ্যান” (২০২১)। কবিতা: “আরাধ্য সময়” (২০২০)। জন্ম ১৯৭৯ রাজশাহীতে। ঢাকায় কাজ করছেন বেসরকারি ব্যাংকে।