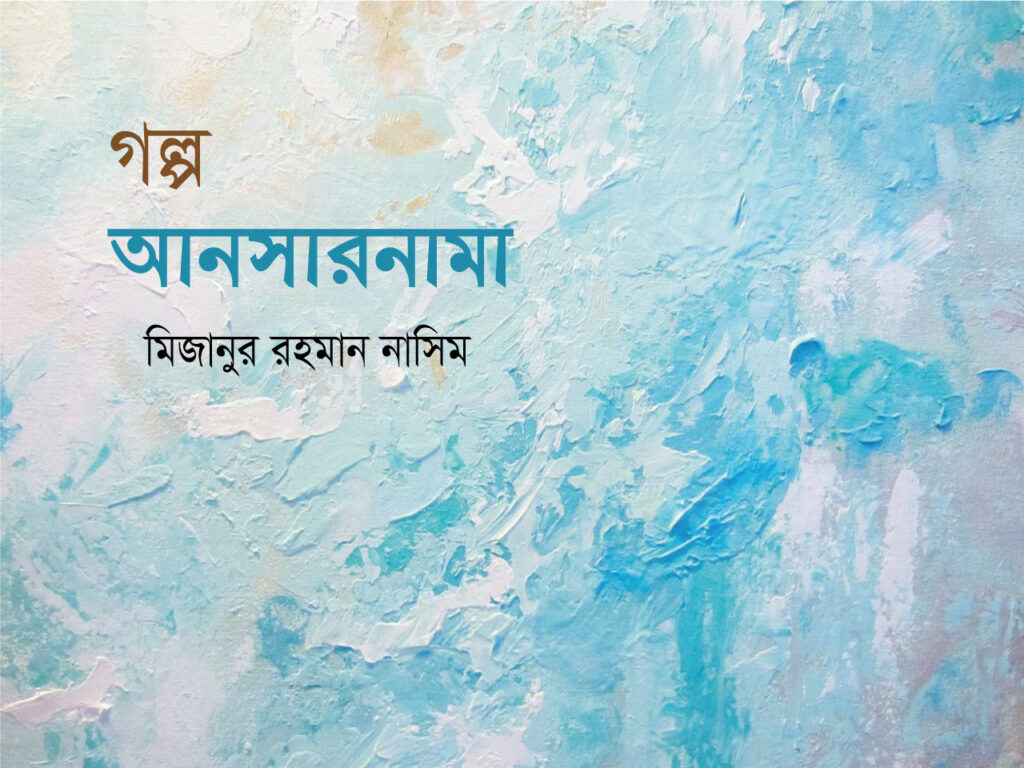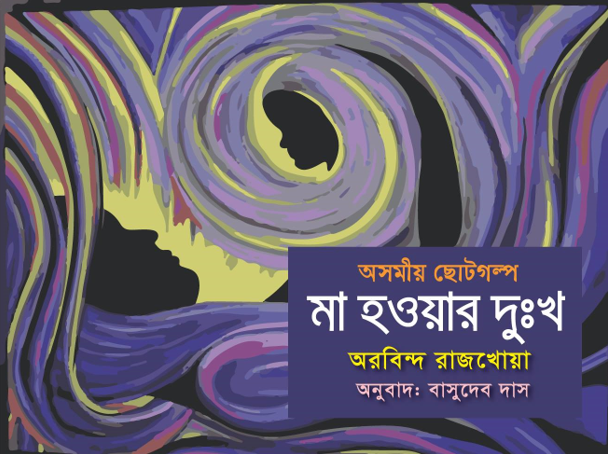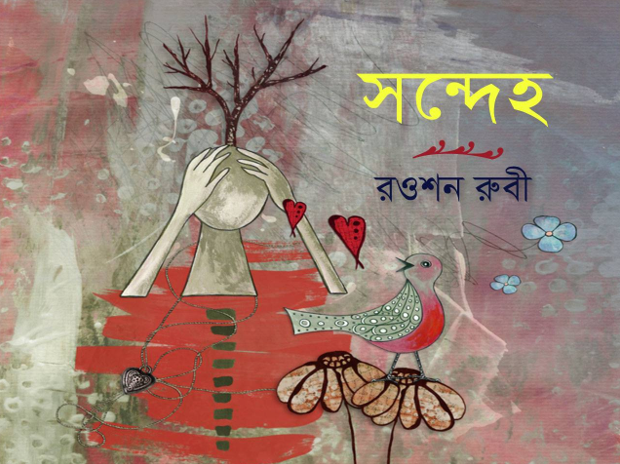তানাক্কা পাড়া রোড ধরে এগুতে থাকবেন, দুই কিলো যাওয়ার পর দেখবেন রাস্তার ওপরে হেডম্যানের একটা মুরাল, মুরালের সামনে দিয়ে বামে যে রাস্তা চলে গেছে সেটা ধরে আরো দুই কিলো অগ্রসর হবেন, এরপর থেকে হাতের ডান দিকে কেবল খেয়াল করবেন, রাস্তাটা অনেক ওপরে ওঠে যাওয়ার পর ডান দিকে দেখবেন অনেক বড় একটা শিমুল গাছ; পুরো গাছ লাল হয়ে আছে। গাছটা বড় বললে ঠিক বলা হবে না, অনেক বড়, আমার বিশ্বাস এতোবড় শিমুল গাছ কখনো দেখেননি। যাওয়ার পথে ডান দিকে আরো দুইটা শিমুল গাছ পাবেন, সেগুলো প্রকাণ্ড নয়, তবে বড়।
বড় গাছের নিছে থামবেন, তারপর একশ মিটার পিছনে এলে ডান দিকে একটা খাড়া রাস্তা নেমে গেছে। বাম দিকে আম গাছের ছায়ায় গাড়ি রেখে খাড়া রাস্তা দিয়ে নামতেই একটি মাটির ঘর দেখবেন, সেটা আসলে গির্জা, তারপর আম বাগানের শুরু, বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটা পথে এগুতে থাকলে একসময় পেয়ে যাবেন বাঁশের একটা গেট, গেটটা ঠেলে ঢুকতেই দেখবেন হাতের ডানে কয়েকটা মালটা গাছ জড়াজড়ি করে আছে, এই পথে সামান্য অগ্রসর হলে এই অধমের কুঠির দেখতে পাবেন।
গতরাত থেকে জাহিদের পাঠানো ম্যসেজটা তিনবার পড়ি। জাহিদের সঙ্গে আমার কোন বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ হয়নি, কোনদিন একসঙ্গে সময়ও কাটাইনি, এমনকি কোথাও দেখা হয়েছে সে কথও মনে পড়ে না, তবু জাহিদের প্রতি কেমন যেন একটা আকর্ষণ বোধ করি।
শিমুল গাছের নিচে গাড়ি থেকে নামতে নামতে এখন আরো একবার পড়ি, আমি শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকি, ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন, এতোবড় শিমুলগাছ জীবনে দেখিনি, ঝটপট কয়েকটা ছবি তুলি।
‘দেখ দেখ কতোবড় শিমুল গাছ।’
আমার উচ্ছ্বাস দেখে নিজাম মোবাইলের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে বিরক্তি নিয়ে শিমুল গাছটার দিকে তাকায়, কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে টেনে টেনে বলে, ‘শরীরজুড়ে কাঁটায় ভরা গাছটার মধ্যে সৌন্দর্যের কি দেখলি সেটাই বুঝতে পারছি না। তোদের বাঙলার মাস্টারদের এই এক সমস্যা, সবকিছুতে সৌন্দয্য বের করা চাই।’
আমি তার কথায় পাত্তা দিই না, আসলে কোন কোন প্রশ্ন আছে সেগুলোর উত্তর দেয়ার চাইতে না দেয়া ভালো। আমি বরং দূরে পাহাড়ের গায়ে কর্মরত নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকি।
আমার বাল্যবন্ধু নিজাম সম্পর্কে কিছু বলি, আমি কলেজে মাস্টারি করার পর থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কয়েক বছর আগে ফেসবুকের কল্যাণে আবার যোগাযোগ।
জাহিদ অনেক আগেই আমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছেন, যাবো যাবো করে যাওয়া হয়নি। নিজামকে বলায় সে বলে আমার সঙ্গে একদিন চল, আমার প্রায় যাওয়া হয়। পরে জানতে পারি সেখানে সে বেশ কয়েকটা পাহাড় কিনেছে, আরো দুটো কেনার ধান্ধায় আছে। আরো জানতে পারি, আসলে পাহাড় কেনাটা তার একটা নেশা। এই তথ্য জানার পর মনটা দমে যায়, পাহাড় কেনা একটা মানুষের নেশা হতে পারে কী করে। তার সঙ্গে যোগাযোগটা প্রায় ছেড়ে দিই, হঠাৎ সে কল করে বলে, তুই তৈরি থাকিস কাল সকালে পাহাড়ে যাবো। তার মুখের উপর না করতে পারিনি।
ঢাকা ছেড়ে আসার পর সে জানায়, জরুরি কাজে রাতেই ঢাকায় ফিরতে হবে এবং জমির দালালকে আজ পাওয়া যাবে না। আমি না থাকলে সে তখনই গাড়ি ঘুরিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা দিত।
মুহুর্তে দমে যাই, জাহিদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে রাত কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছাটা পূরণ হচ্ছে না। পাহাড়ের প্রকৃতি দেখে এই দুঃখ ভুলার চেষ্টা করি। পথে ফনিমনসার গাছ দেখিয়ে বলি, দেখ কতোবড় ফনিমনসার গাছ, এতোবড় ফনিমনসা কখনো দেখিনি।
নিজাম গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে আবার মোবাইলের স্ক্রিনে মনোযোগ দেয়।
সাজনা গাছের ফুল দেখিয়ে তাকে বলতে ইচ্ছা করে, দেখ তো এটা কি ফুল, পরে মনে হলো তাকে এসব কথা বলা নিরর্থক। অনেকের কাছে ফুলের গন্ধের চাইতে টাকার গন্ধ অনেক বেশি প্রিয়, নিজাম সেই গোত্রেরই।
শিমুল গাছের কথা চিন্তা করতে গিয়ে দাদীর কথা মনে পড়ে, দাদী প্রতিবছর বৈশাখে শিমুল তুলা দিয়ে বালিশ বানাতেন, আমরা সেই বালিশে মাথা রেখে শিমুল তুলা ওড়ে যাওয়ার গল্প শুনতাম। দাদী বলতেন চৈত্রমাসে ঢাকের বাড়ি পড়লে তুলো বীজ ফেটে পড়ে, বুকের মধ্য ছোট ছোট বীজ নিয়ে ছেড়া ছেড়া তুলো দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে মাটি জলের সংস্পর্শের আশায়।
আম বাগান পেরিয়ে আমরা বাঁশের বেড়া ঠেলে অগ্রসর হতে দেখি সরু রাস্তা, ডানদিকে ঢালু দিয়ে ফলের বাগান, বাম দিকে বিভিন্ন ধরনের পাহাড়ি ফুল। হঠাৎ কাঠের ঘরটা চোখে পড়ল, ঘরটা সম্পর্কে যা ভেবেছি তার চাইতে সুন্দর। কায়েকটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠে এলাম কাঠের বারান্দায়, ঘরটার দুই দিকে বড় বারান্দা, বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে ছিলেন জাহিদ, উঠে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। চোখ বুলিয়ে দেখলাম কাঠের দেয়ালের সঙ্গে একটা মাথাল ঝুলানো। আমার বন্ধু নিজামকে জাহিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর তিনজনে মুখোমুখি বসি।
বারান্দার কোণে রাখা বাঁশের ঝুঁড়িতে লতাপাতার মধ্যে রাখা একটা পেঁপে অতি যত্নে তুলে এনে আমাদের সামনে রাখেন। এটা আমাদের বাগানের, খেয়ে দেখেন কেমন লাগে।
সরাসরি খাড়া ঢালুতে কাঠের খুটির ওপর ঘরটা বানানো, ডান দিকের বারান্দা থেকে নিচের দিকে তাকালে মনে হয় ঘরটা শূন্যে ঝুলে আছে।
‘আপনার ঘরটা তো আদিবাসীদের ঘরের মতো। আচ্ছা এই ঘরটা সামনের সমতল জায়গায়ও করা যেত?’
জাহিদ একটু হেসে বলেন, ‘যেটুকু সমতল জায়গা আছে এর মধ্যে ঘর করলে হাঁটাচলা করবো কি করে?’
‘কেটে আরো কিছুটা সমতল করে নেয়া যেত।’
‘আদিবাসীরা পাহাড়ের ঢালে ঘর করে, এটাই পাহাড়ের প্রযুক্তি। কিছু মনে করবেন না, সমতলের মানুষের এক সমস্যা, তারা সমতল ছাড়া কিছু চিন্তা করতে পারে না। প্রথমেই তাদের মাথায় আসে পাহাড়ের মাথা ছেটে দিয়ে তাকে সমান করতে হবে।’
‘আপনি বলতে চাইছেন, পাহাড়িরা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে, উন্নয়নের দরকার নাই।’
‘আমি কী সে কথা বলেছি, আমি উন্নয়নের বিরোধিতা করছি না, কিন্তু উন্নয়ন নিয়ে আমাদের শহরের মানুষের শেখানো পড়ানো একটা ধারনা আছে, তা দিয়ে তারা পাহাড়কে বুঝতে চায়। পাহাড়ের মানুষ কিন্তু তাদের মতো দেখে না।’
ধরেন, আপনারা একটা রাস্তা করলেন, আপনারা মনে করলেন উন্নয়ন হচ্ছে, কিন্তু ওই রাস্তা করতে গিয়ে দুটো নদী মেরে দিলেন, নদীর ইকোনমি হিসাবে নিলেন না। নদীর ইকোনমি হিসেবে নিলে এটা উন্নয়ন, নাকি অনুন্নয়ন? নদী বহমান রেখে রাস্তা করার প্রযুক্তির আপনারা উদ্ভাবন করতে পারলেন না, করলেও সেটা নিয়ে ভাবলেন না। পাহাড়ের মানুষ এই হিসেবটা করে, অথচ আপনাদের দৃষ্টিতে তারা পশ্চাদপৎ।’
কথাগুলো বলার সময় জাহিদের গলার স্বরটা কেমন যেন অন্য রকম লাগে। তার প্রশস্ত কপাল, বড় বড় শান্ত চোখ, কথা বলেন আস্তে আস্তে, ছোট ছোট বাক্যে, নিচু স্বরে। তার মধ্যে অস্থিরতা, উদ্বেগ যে নেই তা নয়, মানুষ হিসেবে থাকারই কথা, কিন্তু চশমার মোটা কাচের নিচে চোখ দুইটা দেখলে মনে হয়, দূর থেকে দেখা বড় দিঘির শান্ত জল, ভিতরের প্রবাহটা চোখেই পড়ে না। আগের তুলনায় অনেক স্থুল হয়ে গেছেন, বলেন হাঁটুর ব্যথা বেড়ে গেছে, মনেও সবকিছু ঠিকঠাক মতো থাকে না। ভাবি এই শান্ত স্বভাবের মানুষটার গলা এমন বদলে যায় কিসের জোরে?
নিজাম কথাগুলো বিরোধিতা না করলেও মেনে নিতে পারেননি, তার চোখমুখ দেখে বোঝা যায়। পরিবেশ হালকা করার জন্য বলি, ‘আপনার পেঁপেটা খুব মিষ্টি, বড় করে পেঁপের বাগান করতে পারেন।’
‘করি তো, এটা বাগানেরই পেঁপে, তবে আমরা গাছ কেটে বাগান করি না।’
নিজাম সোজা হয়ে বসে বলে,‘গাছ কেটে বড় করে বাগান করলে অসুবিধা কোথায়? কমার্শিয়ালি ভায়াবল করতে হলে বড় বাগান লাগবে।’
জাহিদ আবার হাসে। বলে, ‘আমাদের অনেকের কাছে উন্নয়নের কনসেপ্টটা অদ্ভূত, বন থাকার দরকার কি, বাগান থাকলে প্রডাকশন বাড়বে, প্রডাকশন বাড়া মানে উন্নয়ন।’
নিজাম বলে, ‘বাগান হলে সমস্যা কী, খাদ্যের উৎপাদন বাড়বে, খাদ্যের উৎপাদন বাড়ুক আপনি চান না? এ ব্যাপারেও আপনার আপত্তি?’- কথাটা বলে নিজাম সিগারেট ধরায়।
‘উৎপাদন বাড়ানো নিয়ে আপত্তি থাকবে কেন? এতো উপাদন হচ্ছে, কই অভাব কি যাচ্ছে? সবাই কি খাদ্য পাচ্ছে?’
বনের সঙ্গে কতো প্রাণির অস্তিত্ব জড়িত, বাগান হলে তারা কই যাবে? বন থাকা মানে পশু পাখি জীব জন্তু অনেকের একসঙ্গে বাঁচা, আর বাগান মানে আপনি একা বাঁচবেন। একা একা বাঁচাকে আপনারা বলছেন সভ্যতা, উন্নয়ন, আধুনিকতা। মানুষের অস্তিত্বের জন্য এদের বেঁচে থাকার কি দরকার নেই? প্রডাকশন বৃদ্ধি কি কম হচ্ছে? তাতে দুনিয়াব্যাপী কামড়াকামড়ি কি কমেছে?’
কোথা থেকে চিরিক চিকির শব্দ আসছে। আমি বলি এই শব্দটা কিসের? জাহিদ হাসতে হাসতে বলে, ‘পিছনের দিকে থাকান।’
আমি আর নিজাম ঘাঢ় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, দুইটা কাঠবিড়ালি পেঁপে গাছে দৌড়াদৌড়ি করছে। নিজাম অনেক সময় নিয়ে কাঠবিড়ালি দুইটার ছবি তুলে মোবাইলের স্ক্রিনে আমাদের দেখিয়ে বলে, ‘দেখ লেজ কতো বড়।’
‘এরা পেঁপে খেয়ে ফেলে না?’
‘খায় তো, এরা খায়, বানর খায়, পাখি খায়- সবাই খায়, সবটা খায় না, কিছু অংশ খায়,বাকীটা আমরা খাই।’
আমি বলি অনেক গুরুগম্ভির কথা হলো, এবার আপনার স্কুলটা দেখি।’
জাহেদ হাঁক দিলেন, ‘মায়া, তোমার স্কুলটা দেখাও।’
ভিতর থেকে মুহুর্তে ছিপছিপে গড়নের একটা মেয়ে এমনভাবে বেরিয়ে এলো, মনে হলো সে ডাকের অপেক্ষায় ছিল; তার সাদা পায়জামার সঙ্গে নীল জামা, কপালে সবুজ টিপ, গাঢ় করে চোখে কাজল, সাদা ওড়নাটা পরিপাটি।
‘এই হচ্ছে মায়া, স্কুলের নতুন শিক্ষক, আরো দুইজন আছেন একজন উনি মং মারমা, অন্যজন শান্তি ত্রিপুরা। তারা বাড়ি থেকে এসে ক্লাস শেষে চলে যান।’
আমরা মায়া সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকি, লম্বালম্বি একটা ঘর, তার সামনে সামান্য খালি জায়গা, তার পরে ফুলের বাগান।
‘এটা হলো সেই স্কুল- বিন্দু।’
স্কুলের সামনে বাঁশ কাঠ দিয়ে বানানো একটা শহীদ মিনার। শহীদ মিনারটা দেখিয়ে মায়া বলে, ‘কয়েক দিন আগে এখানে বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলের একটা অনুষ্ঠান হয়েছে।
‘বাচ্চারা ‘আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো’ গানটা গাইতে পারে?’
‘পারবে না কেন? মায়ের ভাষা হারানোর ভয় কি আমাদের আছে? আছে এদের, আমাদের কাছে কেবল একটা আনুষ্ঠিকতা, আর এদের কাছে হৃদয়ের আকুতি।’
‘আপনি দেখছি আপনার স্যারের মতো কথায় পাক্কা, আপনাদের সঙ্গে কথায় পারবো না।’
আমরা মায়ার কথা শুনতে শুনতে স্কুলের ভিতরে ঢুকি। ছোট ছোট পাটি বিছানো, বাঁশের বেড়ার গায়ে বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা আর শিশুদের ছবি।
নিজাম বলে, ‘এখানে কোন কোন উপজাতির ছেলে-মেয়েরা পড়ে?’
মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে এমনভাবে নিজামের দিকে তাকাল, নিজাম কিছুটা ঘাবড়ে যায় মনে হয়।
‘এই কথাটা আমার স্যার শুনলে খুব রাগ করতেন, আমরা এদের উপজাতি বলি না, এরা নিজেরা জাতি, কারো উপ নয়। এদের সম্পর্কে আমরা আরো অনেকগুলো শব্দ বলি, ‘ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী’, ‘ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী’, ‘পাহাড়ী’; এগুলো এক একটা শব্দ হলেও এক একটা কনসেপ্ট, আমিও প্রথম প্রথম শব্দগুলো বলতাম, স্যার যখন বুঝিয়ে দিলেন তখন থেকে আর বলি না।’
একটু দম নিয়ে মায়া আবার বলে, ‘স্যার কি বলেন জানেন, বাঙলিরা উগ্র জাতীয়তাবাদে অন্ধ হওয়ায় জাতিগুলোকে উপেক্ষা করে থাকে, প্রত্যেক জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র লুকিয়ে থাকে।’
মায়ার কথাগুলো নিজামের পছন্দ হয়নি, তার চোখমুখ দেখে বুঝা যায়, তবে আমার ভালো লাগে। আমি তাড়াতাড়ি বলি, আপনারা শিশুগুলোকে কি পড়ান, কিভাবে পড়ান সেটা একটু বলেন।
‘আমাদের দুইজন শিক্ষক আছেন তারা এদের নিজের ভাষায় বিভিন্ন বিষয় বুঝিয়ে দেন যাতে শিশুরা ক্লাসের পড়া ধরতে পারে, মাতৃভাষায় শিক্ষাটা যাতে শুরু করতে পারে, বাংলার সঙ্গে একটা ব্রিজ করা আর কি।’
‘ওদের তো অনেকেরই বর্ণমালা নেই, মাতৃভাষায় শিখবে কিভাবে?’
‘অনেকের বর্ণমালা নেই, এটা ঠিক, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বর্ণমালা কি খুব দরকার? বর্ণমালা না থাকলেও এদের মুখের ভাষা আছে, সেই ভাষায়ই তারা শিখবে।’
স্কুল থেকে বের হয়ে আমরা চারজন চলি রাবার বাগানের দিকে। রাস্তাটা খাড়াখাড়ি নেমে একটা চত্বরের মতো, মাঝখানে একটা বাদাম গাছ, গাছের নিচে গোল করে বাঁধানো বাঁশের মাচায় কয়েকজন বসে তামাক খাচ্ছে। চত্বরের তিন দিকে তিনটা দোকান, তার পরে রাস্তাটা চলে গেছে রাবার বাগানের দিকে। জাহিদকে দেখে ছোট ছোট বাচ্চারা ছুটে আসে, পাখির মতো কিচিরমিচির করতে করতে অনেকগুলো বাচ্চা তাকে জড়িয়ে ধরে, দৃশ্যটা দেখে হ্যামিলনের বংশিবাদকের কথা মনে হয়।
আমরা রাস্তার ডান দিকের দোকানে ঢুকি চা খেতে। কয়েকজন চাকমা নারী পুরুষ আড্ডা দিচ্ছে। কম বয়সী ত্রিপুরা নারী চা বানাচ্ছেন। সবার মনোযোগ জাহিদের দিকে, জাহিদ তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কি সব বলল কিছু বুঝলাম না।
জাহিদ আমাদের বলেন, কয়েক দিন আগে এখানে স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে যে প্রোগ্রাম হয়েছে সেটা তারা ভুলতে পারছেন না, ওই রকম প্রোগ্রাম তারা আগে কখনো দেখেননি। আমি বাইরে উঁকি দিয়ে দেখি, বিভিন্ন গাছের সঙ্গে এখনো রঙ্গিন কাগজ ঝুলছে।
চা খেয়ে আমরা রাবার বাগানের দিকে হাঁটতে থাকি, নিজাম বলে তার হাঁটতে ভালো লাগছে না। সে গাড়িতে ল্যাপটপে কি যেন কাজ করছে।
কয়েক কদম এগুতেই এক মারমা যুবতী শিশু কোলে নিয়ে এগিয়ে আসছে, জাহিদ তার সঙ্গে কি সব বলল, এক সময় দেখি শিশুটি মায়ের কোল থেকে ঝাপিয়ে পড়ে জাহিদের কোলে। জাহিদ অনেক দিন পাহাড়ের মানুষের মধ্যে থাকেন, ভালোবেসে বিয়ে করেছেন পাহাড়ের নারীকে, এখানকার সবগুলো জাতির ভাষায় কথা বলতে পারেন, তার চেহারাটা বাঙালির হলেও আগাগোড়া পাহাড়ের মানুষ এই ধারনা আমার রয়েছে, তবে কতোটা সে তাদের আপন মানুষ হতে পেরেছেন এই সংশয়টা ছিল। কিন্তু মায়ের কোল থেকে দুগ্ধপোষ্য শিশু তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে আর কোন সংশয় নেয় জাহিদ পুরো দস্তুর তাদের মানুষ।
একটা মারমা কিশোরী কাঁখে সিলভারের কলসি নিয়ে এগিয়ে আসে, পাতাবিহীন রাবার গাছের ফাঁক দিয়ে আসা সকালের রোদ সিলভারের কলসি আর কিশোরীর মুখের ওপর পড়ে চিকচিক করছে। আমি মনে করেছি খাওয়ার পানি নিয়ে আসছে, কাছাকাছি আসতে দেখি কলসির মুখে সাদা তরল পদার্থ, দুধ হতে পারে।
‘মেয়েটা দুধ নিয়ে ..’
‘দুধ না, রাবারের কষ।’
আমাদের অতিক্রম করে না যাওয়া পর্যন্ত মেয়েটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারিনি। কিছুটা এগিয়ে আবার পিছনের দিকে তাকাই, সকালের দীর্ঘ ছায়া ধরে ধরে মেয়েটা এগিয়ে চলে।
জাহিদকে দেখে মেয়েটার চোখেমুখে হাসির ঝিলিক, জাহিদ তাকে কি যেন বলে।
আমি বলি এই কথার মানে কি?
মানে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।
আমরা কিছু দূর গিয়ে হেরিংবনের রাস্তা ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকি, ঝরাপাতার কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে চলি সারিবদ্ধ গাছের মাঝ দিয়ে, সামনে জাহিদ, মায়া, সবার শেষে আমি।
‘এই সময়টা রাবার বাগানের জন্য রিস্ক, আগুন লাগলে পুরো বাগান শেষ..’
আমি বলি, ‘আগুন লাগবে কেন, কেউ লাগিয়ে না দিলে?’
‘মানুষই তো লাগাবে, মানুষ ছাড়া প্রকৃতির বড় শত্রু আর কে আছে? ’
কপালের ঘাম মুছে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি গাছের মাথায় চিকন চিকন ডাল থেকে কচি পাতা উঁকি দিচ্ছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে যেসব গাছ, হাত বাড়ালেই যেন সেগুলোর মাথা ছোঁয়া যাবে, হাতটা যদি লম্বা করা যেত তা হলে কচি কচি পাতাগুলোতে হাত বুলিয়ে দিতাম।
শুকনো পাতার ওপর আমাদের বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপগুলো এলোমেলো শব্দ তৈরি করলেও এর মধ্যে একটা ছন্দ পাই, যেন শুকনো পাতার অর্কেস্ট্রা বাজে আমাদের পায়ে পায়ে।
মায়া বলে, ‘পুরানো পাতা ঝরে গিয়ে নতুন পাতাদের সুযোগ করে দেয়, রুক্ষ আবহাওয়ায় পাহাড়ে পানির জন্য যখন হাহাকার সে সময় এই ঝরা পাতা আপন গাছের গোড়ার মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখে, এর পর বৃষ্টি হলে নিজেকে পচিয়ে মাটির পুষ্টিগুণ বাড়ায় – ক্ষয়ের মধ্যে সৃষ্টির এই এক অনন্ত প্রক্রিয়া; আমরা কেবল নতুনের আগমন দেখি ঝরাপাতাদের অবদান দেখি না।’
আমি বললাম, ‘জোরে বাতাস এলে পাতাগুলো নিশ্চয় ওড়তে থাকে , তখন দারুণ একটা সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়।’
‘হয় তো, পাতার ঝড়, আপনি নাম দিতে পারেন : শুকনো পাতার গান, বা ঝরা পাতার সংগীত।’
ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাবার গাছগুলোর দিকে তাকালে খারাপ লাগে, মনে হয় এদের অনেক কষ্ট, এই দুঃখে তাদের শরীর বেয়ে কষ নেমে আসে।
পাহাড়ের লোঙ্গার দিক থেকে একটা শব্দ কানে এসে বাজছে, কাঠের সঙ্গে শুকনো কাঠের ঠোকাঠুকির শব্দ। আমি বলি, ‘আস্তে আস্তে.. একটু থামেন…কিসের যেন একটা শব্দ। সবাই থেমে গেলে শব্দটা আরো স্পষ্ট হয়।’
মায়া হেসে বলে, ‘চেষ্টা করে দেখেন না কিসের শব্দ। আমি আরো কান পেতে বুঝার চেষ্টা করি, শব্দটা যে পাহাড়ের নিচের দিকে থেকে আসছে এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু ..’
জাহিদ আমাকে আর পরীক্ষায় না ফেলে একটু হেসে বলেল, ‘গরুর গলায় ঝুলানো কাঠের ঘন্টির শব্দ, পাহাড়ের নিচে রাস্তা দিয়ে গরুর পাল যাচ্ছে। এই শব্দ অনুসরণ করে বাকিরা যেতে থাকবে।’
‘আপনি বলে দিলেন কেন? ’
আবার আমরা হেরিংবনের রাস্তায় ফিরে এলাম, তখন রাবার বাগানের শেষ প্রান্তে চলে এলাম, এরপর রাস্তার দুপাশে মেহগনি, শিরিষ, গর্জন, সেগুনের সারি।
উঁচু উঁচু গাছের ছায়ায় আমরা এগুতে থাকি, আমি বলি, ‘রাবার বাগান তো শেষ..’
‘এতো দূর যখন এসেছি, দুধ চা না খেয়ে ফেরা কি ঠিক হবে?’
‘এই গহীন বনে কে চা নিয়ে বসে আছে?’
মায়া বলে,‘আছে একজন, সে হলো আমাদের স্যারের প্রিয় কর্ম।’
রাস্তাটা হঠাৎ করে যেখানে খাড়াভাবে নেমে গেছে তা আগে ডান দিকে একটু সমতল জায়গার মাঝখানে বড়সড় তেঁতুল গাছ, এর নিচে কাঠের টেবিল চেয়ার, এর পরে কর্মের টিস্টল।
এপ্রিলের শুরু হলেও ঘেমে আমাদের সবার অবস্থা খারাপ। ওড়না চেপে চেপে যত্ন করে কপালের ঘাম মুছে মায়া, যাতে টিপটা স্থানচ্যুত না হয়।
আমরা কর্মের দোকানে যখন পৌছায় তখন বেলা বারোটা গড়িয়ে যায়, দোকানের সামনের তেঁতুল গাছের নিচে আমরা তিনজন গোল হয়ে বসি। পিছনে একটা বড় বাতাবি লেবুর গাছ অনেক জায়গা নিয়ে আছে, অনতি দূরে কতবেল গাছ, এটাও কম জায়গা নিয়ে নেই। গাছগুলোকে কতোটুকু জায়গা নিয়ে থাকতে পারে মনে হয় তার একটা গোপন প্রতিযোগিতা আছে।
বাতাবিলেবুর গাছের নিচে দুইটা কুকুর পাশাপাশি অলসভাবে শুয়ে আছে।
দোকানের ভিতরে বাঙলা ছবি চলছে। ফাইটিংএর শব্দ ভেসে আসে।
আমার মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে, শালা এখানেও ফাইটিং..
পুরো পথে মায়ার সঙ্গে আমার সরাসরি কোন কথা হয়নি, জাহিদ আমার সম্পর্কে এর মধ্যে দুইবার ধারনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।
আমি কর্মের দোকান থেকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে মায়ার দিকে তাকাতে সে বলে, আপনার বন্ধু এলো না যে, পাহাড় তাকে টানে না বুঝি।
‘আমার বন্ধুর কথা বলছেন, সে ব্যবসায়ী মানুষ, তার কথাবার্তা নিশ্চয় শুনেছেন।’ মনে মনে বলি, টানে নিশ্চয়, তবে সেটা অন্য কারণে।
তেঁতুল গাছ থেকে কয়েকটা ঘুঘু অবিরাম ড়েকে চলে। ঘাড় তুলে ঘুঘু দেখার চেষ্টা করি, দেখি লকলকে তেুঁতুল ঝুলছে।
‘আপনি ঘুঘু খুঁজছেন, এখানে ঘুঘুর অভাব নেই। আমার ঘুঘুর ডাক শুনে শুনে দুপুরটা কেটে যায়। মাঝে মাঝে কেমন অস্থির লাগে ডাক শুনে। আচ্ছা বলতে পারেন ঘুঘুগুলো দুপুরে ডাকে কেন?’
‘ঘুঘু কেবল দুপুরে ডাকে আপনাকে কে বলেছে? যে ঘুঘুগুলো ডাকছে সেগুলো পুরুষ ঘুঘু। যখন ইচ্ছা তখন ডাকে, দুপুরে কোলাহল কম বলে বেশি শোনা যায়, আপনার মতো নারীরা উদাস থাকেন বলেই ..’
ঘুঘু বিষয়ক আলোচনার মাঝেই কর্ম ত্রিপুরা চা নিয়ে হাজির।
কর্ম জাহিদকে বলল,‘ যেভাবে পাহাড়ের বন উজাড় হচ্ছে ঘুঘুর ডাক আর পাবেন কোথায়?’
আমি বলি, আসার পথে ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় একটা বাগানের মতো দেখলাম..?’
জাহিদ বলে,‘এখানে বন কেটে বাগান করার একটা হিড়িক পড়েছে, বড় বড় বৃক্ষ কেটে হচ্ছে সাজানো পরিপাটি শখের বাগান, কর্ম ঠিকই বলেছে ঘুঘু কেন কোন পাখির অস্থিত্বই পাওয়া যাবে না।’
কর্মের চা খেয়ে আমরা ফিরতে শুরু করি। জাহিদ অনেক দূর এগিয়ে যায়, অনভ্যাসের কারণে আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার ওপর বড় বড় গাছের ছায়া, রাস্তার একদিকে উচু পাহাড়, অন্যপাশে খাড়া ঢাল, মায়া আমার জন্য অপেক্ষা করে।
‘আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে?’
‘হচ্ছে কিছুটা।’ বলে আমি লম্বা করে নিঃশ্বাস নিই। বন্য ফুল-গাছ-পালার অদ্ভূত গন্ধ পাই, গন্ধটার মধ্যে কেমন যেন মাদকতা আছে।
আমি বলি, ‘আমি শুনেছি আপনি শহরের মানুষ, বহু বছর ভালো চাকরি করেছেন, নাটক করেছেন, গানও জানেন। এখানে, এই পাহাড়ে একাকি পড়ে থাকতে ভালো লাগবে?’
আমরা পাশাপাশি হাঁটছি, কিছুক্ষণ পর মায়া বলে, ‘একাকি কি বলছেন, বাচ্চারা আছে না। তাদের নিয়ে সময় কেটে যায়, বাকী সময় পাহাড় দেখি, গাছ দেখি, পাখির ডাক শুনি, গান গাই। আমি শহরের কোলাহলে বড় হওয়া মানুষ, আমি পালিয়েই এখানে এসেছি, আর পালাবো কোথায়? বাচ্চাগুলোর সঙ্গে যখন থাকি তখন মনে হয় আমার আর কোন সুখের দরকার নেই।’
এই চাকরিতে পোষাবে?
‘চাকরি অনেক করেছি, অনেক টাকা কামিয়েছি, আর ভালো লাগে না টাকার পিছনে দৌড়াতে।’
‘কিছু মিনিমাম চাহিদা..’
‘একটু থাকা আর খাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে জীবনে আর কী চাই, এই দুটোর ব্যবস্থাই এখানে আছে।’
‘এখানকার একঘেঁয়ে জীবন ভালো লাগবে আপনার?’
‘একঘেঁয়ে পরিবেশ কাকে বলছেন, সৌন্দর্যের মূল রহস্য রয়েছে বৈচিত্র্যে, পাহাড়, পাহাড়ের বৃক্ষ হচ্ছে বৈচিত্র্যের পূজারি। আমি সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে আছি, একঘেয়ে যদি লাগেও বুঝতে হবে আমার ভেতরের সৌন্দর্য্যবোধ শুকিয়ে গেছে।’
আমি আর কথা বাড়াই না, এই সহজ কথা ভাবতে পারিনি বলে অস্বস্থি হয়। ভাবি, সমাজে নিজামরাই কেবল নয়, মায়ারাও আছেন।
‘আপনি গান জানেন, একটা গান গাওয়া যাবে।’
এমন খাড়া খাড়া রাস্তায় হাটা গান হাওয়ার জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়, তবু কেন বলি জানি না, মায়া সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়, ‘
ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়েও গান থামায়নি মায়া।
রাবার বাগান বেড়ানো শেষে জাহিদের হাতের রান্না খেয়ে আমরা জাহিদ আর মায়াকে বিদায় জানিয়ে পড়ন্ত বিকেলে গাড়িতে উঠে বসি। গাড়িতে বসে মায়ার গাওয়া গানের সুর মনে করার চেষ্টা করি, অদ্ভূত ব্যাপার হচ্ছে কিছুতেই গানের সুর মনে করতে পারছি না, এর কি কারণ হতে পারে? ভাবতে ভাবতে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাই, পাহাড়-বনবীথি-পাখির ডাক- প্রকৃতির বিস্তৃত একটা সঙ্গীতের মধ্যে আমাদের স্নায়ুগুলো আচ্ছন্ন হয়েছিল মনের অজান্তে, সে জন্য অন্য সুর আর জায়গা করে নিতে পারেনি।
পাহাড়ি রাস্তা, গাছ-পালা দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি জানি না।
দূর থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে, আমাদের ছোটবেলা চৈত্রের শেষের দিকে পালপাড়ার দিকে থেকে যেরকম ঢাকের শব্দ ভেসে আসতো সেরকম। সেই প্রকাণ্ড তুলা গাছ যার শাখাপ্রশাখায় থোকা থোকা ফুল ফুটে আছে সেই গাছে বাদামি রঙের তুলার ফল ধরে আছে; ঢাকের শব্দে তুলার বীজগুলো ফেটে তুলা ছড়িয়ে পড়ছে পড়ন্ত বিকেলের স্বচ্ছ আকাশে, ছেঁড়া ছেঁড়া তুলা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে কোথায় গিয়ে থিতু হবে কে জানে। তুলার মধ্যে ভেসে বেড়ানো একটা মুখচ্ছবি দেখতে পাই, এই ছবিটাকে চিনতে পারি– এটা নিজামের ছবি, এই ছবিকে ঘিরে অনেকগুলো শিশুর মুখ, কি সব ভাষায় তারা কথা বলছে, হাসছে, চোখের ভাষায়, ঠোঁটের মৃদু কাঁপুনিতেও তারা ভাব বিনিময় করছে। তাদের চোখে-মুখে অন্যরকম আনন্দ, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ..জাতির বুঝতে অসুবিধা হয় না; নিমিষে দুটো জাহিদ হয়ে যায়, একটা শিশুকালের জাহিদ, আর একটা নাকের নিচে তুলোর মতো সাদা গোঁফের বুড়ো জাহিদ। সবুজ রঙের শাড়ি পরা মায়াকে দেখি শিশুগুলোকে ডাকছে, পাঠশালার সময় হয়ে গেছে, এই তোমরা কোথায় যাও, এক্ষুণি পাঠশালা শুরু হবে। ফিরে এসো বাচ্চারা…
শিশুগুলো মায়ার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, সঙ্গে শিশু জাহিদও, আর বীজ বুকে নিয়ে ভেসে বেড়ানোর মতো বুড়ো জাহিদকে নিয়ে সাদা তুলাগুলো দেখতে দেখতে সাদা মেঘের মধ্যে হারিয়ে যায়।
বিকট হর্নে তন্দ্রা কেটে গেলে, নিজাম বলে, পাহাড়ী রাস্তা শেষ, চল চা খাবো।

খোকন দাস
খোকন দাসের জন্ম ফেনী জেলার দাগনভূঞা উপজেলার চাঁদপুর গ্রামে; ১৯৭০ সালের ৩১ ডিসেম্বরে। গল্পকার এবং প্রাবন্ধিক। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন সংগ্রামই তার লেখার বিষয়বস্তু। প্রকাশিত গল্পের বই : কাক ও অন্যান্য গল্প, খড়ের মানুষ। তিনি কর্মসূত্রে খাগড়াছড়িতে থাকেন।