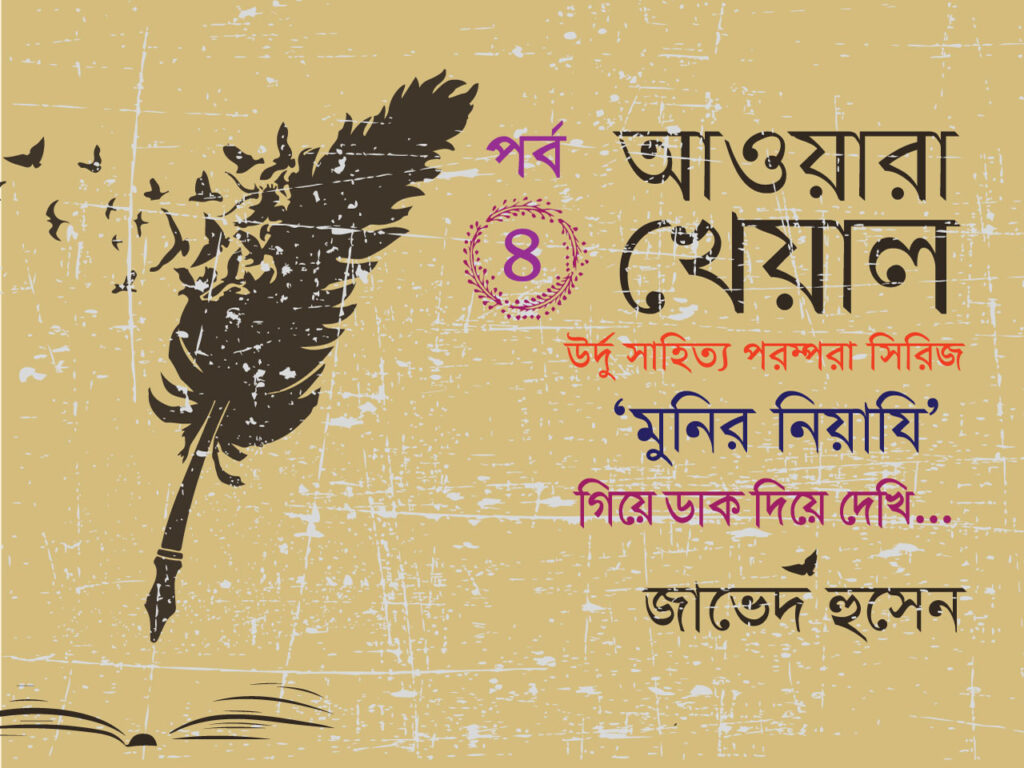একটা কবিতা পড়ার আসর। লাহোরে। বেশ নাম করা সব কবি, সাহিত্যিকদের জমায়েত। একজন কবি নিজের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। সাদা চুলের সুদর্শন কবি। তাঁর চেহারা, ধীর চলনে, থেমে থেমে ক্লান্ত লয়ে কবিতা পড়ায় এক অদ্ভুত স্থিতধী ভাব এসেছে। চেহারায় ছাপ ফেলেছে বয়স। কবিতা পড়লেন যা তা উর্দুর প্রিয় ফর্ম গজল নয়। একটা নজম। মানে মুক্ত দৈর্ঘের কবিতা। এখানে প্রতি দুই লাইনে গজলের মতো বিষয় পালটে যায় না। একটা বিষয়ই পুরো কবিতা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। এটাই নজমের বৈশিষ্ট। এক মিনিটও নয় তাঁর কবিতার সময়। ক্লান্ত স্বরে, আর কোন তাড়া নেই, নেই আর কিছু পাওয়ার জন্য ছুটে চলার তাগিদ, পাওয়া আর না পাওয়ার অর্থ বুঝে গেছেন কবি – এই সব অনুভূতি তাঁকে দেখলেই এসে ধাক্কা দেয়। যখন এমনি করে কবিতার মাঝামাঝি এসেছেন কবি, সামনে বসা অধিকাংশ মানুষের চোখে জল। একবারে সামনে বিখ্যাত গজল শিল্পী ফরিদা খানম। নিজে কত জনের চোখে জল এনেছেন সুরে গজল গেয়ে। এখন তিনি সেই কবির কবিতা শুনে স্বভাবসিদ্ধ ‘ক্যামেরা লুক’ ভুলে চোখের জল মুছতেও ভুলে গেছেন। কবিতাটির বাংলা এরকম :
সব সময় দেরি হয়ে যায় আমার
কোন জরুরী কথা বলতে গিয়ে
কোন প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে
তাকে ডাকবো কি ডাকবো না ভাবতে গিয়ে
তাকে – ফিরে এসো বলতে গিয়ে
সব সময় দেরি হয়ে যায় আমার
তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে গিয়ে
কোন বন্ধুকে – ভয় নেই বলতে গিয়ে
অনেক পুরোনো কোন পথে
কি জানি কার সাথে দেখা করতে গিয়ে
সব সময় দেরি হয়ে যায় আমার
বদলে যাওয়া মৌসুমে
ঘুরে বেড়াতে গিয়ে
কাউকে মনে রাখতে গিয়ে
কাউকে ভুলে যেতে গিয়ে
সব সময় দেরি হয়ে যায় আমার
মৃত্যুর আগে কাউকে
কোন দুঃখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে
সত্যটা অন্য কিছু ছিল
তাকে বলতে গিয়ে
সব সময় দেরি হয়ে যায় আমার
এই কবি মুনির নিয়াযি। ১৯২৮ সালে জন্মেছেন অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবে এক পাঠান গ্রামে। লিখেছেন উর্দু আর পাঞ্জাবি ভাষায় কবিতা, সিনেমায় জনপ্রিয় গান, ছোট গল্প, রেডিওর নাটক, পত্রিকায় মতামত। ১৯৩৯ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করে বোম্বে আসেন। উদ্দেশ্য নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়া। আগে কবিতার ভুত মাথায় ছিলো না কখনো। শুকনো দেশের পাঠান ছেলে তিনি। সমুদ্র দেখে অন্যরকম হয়ে গেলেন। সঙ্গে আরেক বন্ধু জুটে গেল। সে আবার কবিতা লেখে। উৎসব চললো দুজনে বসে রাত দিন গজল পড়ার । নৌবাহিনী প্রশিক্ষণ মাথায় উঠলো। বাহিনীর কড়াকড়ি ভালো লাগে না। মাথায় শুধু কবিতা ঘোরে। তিনি পালালেন। ধরে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হলো। শাস্তি জুটলো। আবার পালালেন। এরকম চার বারের পর নৌবাহিনী আর পরিবার দুইই হাল ছেড়ে দিলো। মুনির এবার সাহিত্য নিয়ে লাহোরের দয়াল সিং কলেজে, পরে শ্রীনগরের অমর সিং কলেজে। সঙ্গে জুটলো সব কবি বন্ধুদের ভিড়।

১৯৪৭এ দেশ ভাগ হলো। পরিবার এসে আশ্রয় নিলো আজকের পাকিস্তানের সাহিওয়ালে। পরে তিনি লাহোরে এসে পাকাপাকি বসত করলেন। কিন্তু এই জনারণ্য আর বন্ধুদের হারানোর বেদনা কখনো ভোলেননি। একা একা লাহোরের পথে ঘুরে বেড়ানো বেশি পছন্দ করতেন। নিজে একটা বই ছাপানোর ব্যবসা শুরু করলেন। কবিতা নিয়ে আলোচনা তর্ক এড়িয়ে চলতেন। অন্য সবার কাছে এটা পরিচিত হয়ে গেল মুনির নিয়াযির ঔদ্ধত্ব হিসেবে:
তুমি তো নিজের অভ্যাস বানিয়ে ফেললে মুনির
যে শহরেই থাকো শুধু বিরক্তি নিয়ে বাঁচো
(আদত হি বানা লি হ্যায় তুম নে তো মুনির আপনি
জিস শ্যাহের মেঁ ভি র্যায়হনা উকতায়ে হুয়ে র্যােহনা)
মুনির প্রয়োজনে নিজেও ফুঁসে উঠতে দ্বিধা করেন না। ১৯৬০এর দশকে আহমেদ নাদিম কাসমির সঙ্গে মুনিরের কবিতা নিয়ে তর্ক সাধারণের বেশ নজর কেড়েছিল। তবে মুনির নিয়াযি নিজের ভাবনাকে, কবিতাকে কারো কাছে জবাবদিহির বিষয় বলে মনে করতেন না:
কাউকে আমার কাজের হিসেব কি দেবো আমি
সব প্রশ্ন ছিল ভুল, উত্তর কী দেবো আমি
(কিসি কো আপনে আমল কা হিসাব কেয়া দেতে
সওয়াল সারে গলত থে জওয়াব কেয়া দেতে)
এই ঔদ্ধত্ব আসলে জগতের অসংখ্য রঙ আর রূপের মাঝে দিশেহারা এক মানুষের উদ্ভ্রান্তি, যে নিজেকে বড় অসহায় বলে চিনতে পেরেছে বলে নিজের চাওয়াকে কাঙ্ক্ষিতের জন্য অযোগ্য বন্ধন বলে মনে করে:
আমার প্রেমিকাদের হৃদয় হাওয়ার পথের পথিক ছিলো
তাদের এক ঘরে বন্দী করে রাখার সাজা কী করে দিই?
(হাওয়া কি তরহা মুসাফির থে দিলবরোঁ কে দিল
উনহেঁ বস ইক হি ঘর কা যাব কেয়া দেতে)
মুনির, মরুর হাতে শুরু থেকেই মরিচিকার আশ্রয় ছিল
সেই আয়নাকে আমার বাসনার জলে ঝপ্সা কেন করবো আমি
(একে মুনির দশত শুরু সে সারাব আসা থা
উস আয়িনে কো তামান্না কি আব কেয়া দেতে)
যে দৃশ্য আর রঙের জগত তাঁকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে, সেই জগতের প্রতি তিনি একার্থে কৃতজ্ঞও বটে। এই অনুভূতি কবিতা হয়ে তাঁকে এমন স্থান দিয়েছে যা অর্জনের জন্য অনেক কিছু তিনি ছেড়ে আসতে রাজি আছেন। এই দৃষ্টির জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে তা তিনি জানেন, তবে যা পাওয়া গেছে সেই ঋণও বা তিনি শোধ করবেন কী দিয়ে:
লক্ষ্য চেহারার ভীড়ে একা থাকাই আমার কাজ
বেশ বদলে দেখতে থাকি ঝড়ো হাওয়ার খেলা
একদিকে শব্দের সুর্য অন্যদিকে বোবা সন্ধ্যার অন্ধকার
শরীরের সুগন্ধ একদিকে অন্যদিকে তার ক্ষয়
আমার দৃষ্টির ফাঁদ তো আমার ঘাতক হলো দেখছি
সবচেয়ে বড় খোদা আর এর পরই আমার নাম
মুনিরের কবিতা উর্দুতে একটা অচেনা স্বাদ দিয়েছে। তিনি কবিতার মধ্যে ছোট ছোট গল্প বলতে পছন্দ করেন। সেখানে বাড়তি কোন শব্দ থাকে না, গল্পের বিষয় মানুষের অনুভূতি। ভালো গল্প কে না পছন্দ করে! উর্দু কবিতায় তিনি চোখে দেখা এই আশেপাশের পৃথিবীকে এক অদ্ভুত অজানা জগতে বদলে ফেলেন। নিচের কবিতাটির নাম, ‘ভয় পাওয়া মাটি’:
অনেক ফসল, অনেক সম্পদ
দাফন হয়ে আছে এই মাটির তলে
বাঁজা হয়ে।
ভয় পাওয়া মানুষের মতো
নিজের ইচ্ছে লুকিয়ে রেখেছে
এই মাটি
লুকিয়ে রেখেছে নিজের ফসল সকল সম্পদ
শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উর্দু কবিতা খুবই হিসেবি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উর্দু কবিরা মনে করতেন শব্দের ব্যবহারের বৈচিত্রই কবিতায় অভিনবত্ব নিয়ে আসে। এই হিসেবের বাইরে গিয়ে মির্জা গালিব শব্দের প্রচলিত জীর্ণ অর্থে নতুন অর্থ দেওয়াকে কবিতার উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করলেন। মুনির নিয়াযি আবার শব্দের ব্যবহারে দক্ষতাকে গুরুত্বযোগ্য বলে প্রচার করলেন। নিচের কয়েকটি শেরে তিনি যে দক্ষতায় শব্দকে কাজে লাগিয়েছেন, তাতে মনে হয় অভিধান যেন সকল সম্পদ নিয়ে নিয়ে মুনির নিয়াযির বশম্বদ হয়ে আছে:
যার ভাবনা ভেবেছি তাকে ভাবনাতেই পেয়েছি
প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছি যা সেও প্রশ্নেই
(খায়াল জিস কা থা মুঝে খায়াল মেঁ মিলা মুঝে
সওয়াল কা জওয়াব ভি সওয়াল মেঁ মিলা মুঝে)
জানতাম আমরা কেউ রক্ষা করতে পারবো না একে
তুমি ওয়াদা করলে বলে আমিও ওয়াদা করলাম
(জানতে থে দোনো হাম ইস কো নিভা সাকতে নেহিঁ
উসনে ওয়াদা কর লিয়া ম্যায় নে ভি ওয়াদা কর লিয়া)
পরের কাছ থেকে পাওয়া সব ঘৃণা নিজের জন্যই খরচ করলাম
তাকিয়ে দেখি, যতটা ছিলাম নিজেই নিজে তার অর্ধেক করে ফেলেছি
(গ্যায়র সে নফরত জো পা লি খর্চ খুদ পর হো গ্যায়ি
জিতনে হাম থে হাম নে খুদ কো উস সে আধা কর লিয়া)
আরেকটা জায়গায় মুনির সমকালীনদের ছাপিয়ে গেছেন। সেটা হলো কল্পনার অতিরঞ্জন। তাঁর বিশ্ব রঙিন। পাঠক শ্রোতাকে থমকে দেয়। আর তিনি নিজেও সেই জগতের বৈচিত্রে শিশুর মতো বিস্ময় নিয়ে কবিতা উচ্চারণ করেন।
ঠোঁটের রক্তিমতা ছলকে ছলকে ছড়িয়ে পথ চলো
নিজের সঙ্গে এক পুষ্পকুঞ্জের সৌরভ নিয়ে চলতে ভুলো না
(ছলকায়ে হুয়ে চলনা খুশবু লবে লালি কি
ইক বাগ সা সাথ আপনে ম্যাহকায়ে হুয়ে র্যাহনা)
কাজলের অপার্থিব মায়ায় সন্ধ্যের আবেশ ডেকে এনো
আর চোখের তারায় চাঁদের আলো ছড়িয়ে দিতে ভুলো না
(ইক শাম সি কর রাখনা কাজল কি কারিশমে সে
ইক চাঁদ সা আখোঁ মেঁ চমকায়ে হুয়ে র্যাহনা)
তবে সহজ আর বিস্ময়ের সীমা পার হলেই বোঝা যায় এই সহজ তাকে পাওয়ার সামনে বড় বাঁধা। এই কথা মির্জা গালিব বুঝেছিলেন:
তোমার দেখা পাওয়া কঠিন হলে তো সহজই হতো
কিন্তু কঠিন ব্যাপার হলো এই তোমার দেখা পাওয়া তো কঠিন নয়
(মিলনা তেরা গর আসাঁ নেহিঁ তো স্যাহেল হ্যায়
দুশওয়ার তো য়ে হ্যায় কে দুশওয়ার ভি নেহিঁ )
সেই পথ বেয়ে মুনির সহজ পথ বেছে নেন। যাই গিয়ে ডাক দিয়ে দেখি:
ডাক দিয়ে দেখো হয়তো পেয়ে যাবে তাকে
নইলে এই জীবন ধরে চলা ব্যর্থই তো হবে
(আওয়ায দে কে দেখ লো শায়েদ ও মিল হি জায়ে
বরনা য়ে উম্র ভর কি সফর রায়েগা তো হ্যায়)
তবে ডাক দিয়ে দিতে দিতে কখন তার দেখা পেয়েও ডাকের নেশায় তাকে চিনতে না পেরে ভুল হয়ে যায় কে জানে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার নেশা তাকে তা পেয়েও হারাতে বাধ্য করেছে। মুনির নিজেও সেই আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না:
এ কেমন নেশা, এ কেমন খোয়ারি আমার
তুমি এসে চলেও গেলে আমি অপেক্ষাতেই আছি
(য়ে ক্যায়সা নাশা হ্যায় ম্যায়ঁ কিস আজব খুমার মেঁ হু
তু আ কে জা ভি চুকা হ্যায় ম্যায়ঁ ইন্তেযার মেঁ হু)
তবে এই হারিয়ে ফেলা তো যে চায় একা তার দোষ নয়:
আমি বলতাম না যে সময় বড় নির্দয়
দেখো! তুমিও কেমন স্বপ্ন হয়ে গেলে
(হাম না ক্যাহতে থে ওয়াক্ত যালিম হ্যায়
দেখ লো! খোয়াব হো গ্যায়ে তুম ভি )
এই সকল কিছুর মাঝে মুনির নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই জেনে নিতে আগ্রহী। অজস্র কবিতায়, কাব্যতত্ত্বের পন্ডিতি আলোচনার প্রবল চোখ অন্ধ করে দেওয়া ধুলো ঝড়ের মাঝে শেষ পর্যন্ত চমকে ওঠে তাঁর পংতি। সেখানে আপাতঃ দৃষ্টিতে যাকে উচ্চাঙ্গের ভাবনা বলে মনে হয় তার কোন সম্ভাবনা নেই, সেই কবিতা বড় সরল, কিন্তু সেখানে সকল দ্বিধা আর সংশয়ের উত্তর পাওয়ার সুযোগ আছে:
একদিন যাবো আমি মুনির তাকে দেখতে
তার দরজায় গিয়ে এক দিন ডাক দেবো আমি
(ম্যায় মুনির জাউঙ্গা ইক দিন উসে মিলনে
উস কে দরপে জা কে ম্যায় ইক দিন সদা দুঙ্গা)
মুনির নিয়াযির শের শুনতে ক্লিক করুন
জাভেদ হুসেন
জাভেদ হুসেনের জন্ম ১লা আগস্ট ১৯৭৬, কুমিল্লায়। সোভিয়েত পরবর্তীত সক্রিয় মার্কসীয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি। মার্ক্সের লেখা এবং মার্ক্সীয় দর্শন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়াও তিনি একজন গালিব গবেষক। উর্দু-ফার্সি সাহিত্য বিষয়ে রয়েছে তাঁর বিস্তৃত জানাশোনা। মূল উর্দু ও ফার্সি থেকে অনূদিত বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে।