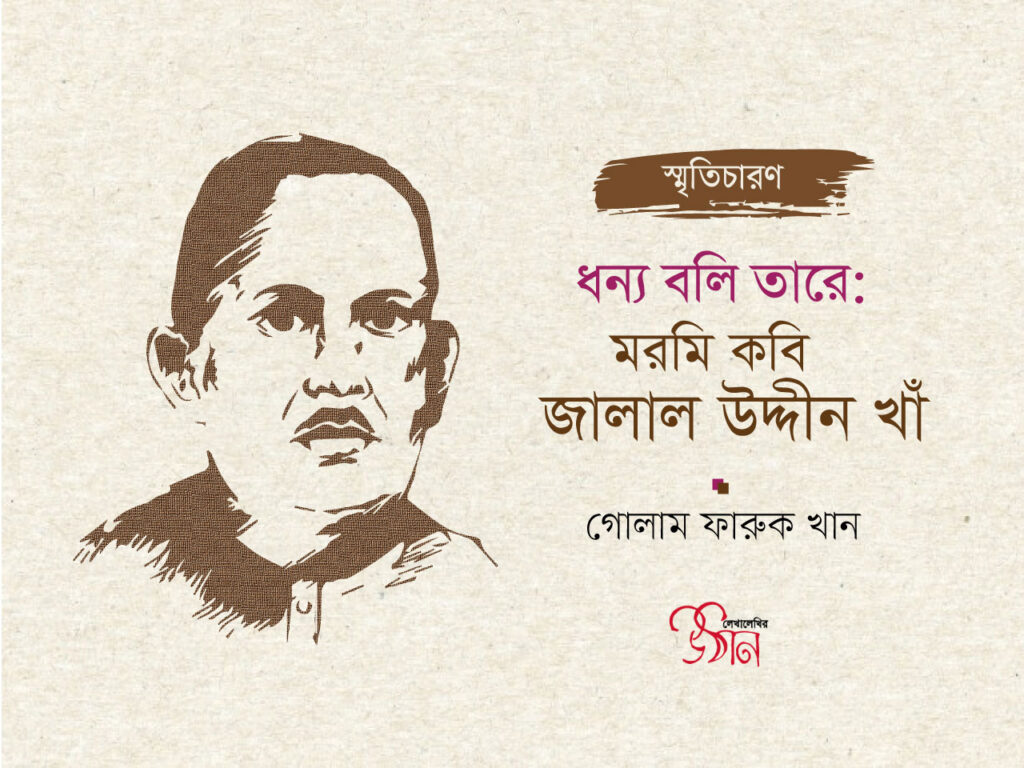“আমি ধন্য বলি তারে —
আপন দেশে যে-জন বসে চিনতে পারে আপনারে।”
আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে এই দিনে — সেই স্তব্ধ, বিষণ্ণ শ্রাবণসন্ধ্যায় — তিনি এই মরপৃথিবীর বাস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। রাধাঝুমকোলতায় ছাওয়া যে দক্ষিণমুখি ঘরটিতে তিনি থাকতেন তা ছিল অজস্র জালালি কবুতরের অভয়াশ্রম। দিনের বেশিরভাগ সময় বুকের নিচে বালিশ রেখে তিনি মগ্ন থাকতেন গান লেখায়। ছাদ থেকে নেমে অনেক কবুতর তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করত, খেলত, ডানা ঝাপটাত। তাদের সঙ্গে খেলতাম আমরা — তাঁর অবুঝ শিশুপৌত্রেরা। ভাবতাম, যেহেতু তাঁর নাম জালাল উদ্দীন খাঁ, সেই নামেই পরিচিতি পেয়েছে প্রিয় কবুতরগুলি। একটু বড় হয়ে জানলাম, এইসব কবুতরের নাম এসেছে হজরত শাহজালালের নাম থেকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার পিতামহ কীর্তিমান লোককবি ও দার্শনিক জালাল উদ্দীন খাঁর প্রয়াণের পর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায় তাঁর ঘরের আনাচে-কানাচে বাসা বেঁধে-থাকা জালালি কবুতরগুলি। শুকিয়ে যায় ঝুমকোলতার বিস্তৃত পুষ্পপল্লব। এইসব ফুল-পাখির সঙ্গে কোনো প্রাণের যোগ ছিল কি তাঁর? অথবা তাঁর স্নেহ-পরিচর্যায় নিশ্চিন্ত-নিরাপদ বোধ করত তারা? এ কথা এখনো মাঝেমাঝে ভাবি।

শৈশবে দেখতাম, কী জানি ভাবতে ভাবতে সারাদিন তিনি লিখছেন। কখনো দেখতাম, শিয়রের কাছে ঝোলানো একটি একতারা কিংবা দোতারা টেনে নিয়ে নিজের লেখা কথাগুলি সুর করে গাইছেন। মাঝেমাঝে গিয়ে বসতেন একটি টিনের গোলঘরে। প্রতিদিন বিচিত্র ধরনের সব মানুষ আসতেন তাঁর কাছে। কেউ শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মৌলানা, কেউ জটাজুটধারী ফকির, কেউ ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী, কেউ-বা আবার কপালে তিলককাটা বৈষ্ণব। আসতেন অনেক বাউল গায়ক যাঁরা তাঁকে গান শোনাতেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি কীসব কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করতেন যার কিছুই আমরা বুঝতাম না। শুধু মনে হতো খুব বড় কোনো কাজে লিপ্ত রয়েছেন তিনি। বয়স বাড়ার পর একটু একটু করে বুঝেছি জগৎ ও জীবন বিষয়ে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক বিষয়ে কী গভীর মরমিয়া অথচ জিজ্ঞাসামুখর বাণী নিয়ে এসেছিলেন তাঁর গানে। এখনো তাঁর অনেক কথা বোঝার বাকি রয়ে গেছে, যদিও তা সুরে সুরে খুব সহজেই প্রবেশ করে মর্মে।

যাঁরা তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁদের একজন বাংলাদেশের মনস্বী লেখক যতীন সরকার। তিনি তাঁর বহুল-আদৃত বই “পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শনে”র অনেক অধ্যায়ে সে দেখার অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়: “…অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছি আমি পূর্ব ময়মনসিংহের প্রখ্যাত কবি জালাল উদ্দীন খাঁকে। জালাল খাঁর বাড়ি আমাদের পাশের পল্লী সিংহেরগাঁও-এ। উনিশ শো পঞ্চাশ সাল থেকেই আমি তাঁর স্নেহ-সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি। তাঁর কাছ থেকে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক ও প্রথাবিরোধী সংস্কৃতির যে-রকম অন্তরঙ্গ পরিচয় পেয়েছি, সে-রকমটি কোনো সংস্কৃতি-তাত্ত্বিকের বই পড়ে পাইনি। পঞ্চাশ সালে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে একাডেমিক শিক্ষা থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু জালাল খাঁর কাছে পাওয়া লোকায়ত সংস্কৃতির জীবন্ত শিক্ষা আমার মনের দারিদ্র্য দূর করে দিয়েছে।”

অন্যত্র তিনি লিখেছেন: “বাড়ি থেকে আড়াই মাইল হেঁটে স্কুলে গিয়েছি। যেতে হতো সিংহেরগাঁওয়ের জালাল উদ্দীন খাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। তাতে এই বাউল কবি জালাল খাঁ আর তাঁর পুত্র আধুনিক কবি খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিমের (হেকিম ভাই) স্নেহসান্নিধ্য পাওয়া আমার জন্য খুব সহজ হয়েছে। স্কুল থেকে ফেরার পথে একেক দিন বিকেলে তাঁদের ‘গোলঘর’-এর আড্ডায় বসে গেছি। গোলাকৃতির এই ঘরটিই ছিল সংস্কৃতি ও রাজনীতিরও কর্মকেন্দ্র। এটিই ছিল হেকিম ভাই-প্রতিষ্ঠিত ‘আবেহায়াৎ সাহিত্য মজলিস’-এর অফিস। এখানেই জালাল খাঁ ও তাঁর শাগরেদদের আসর বসতো।…এ-আড্ডায় আলোচনা হতো না এমন কোনো বিষয় বোধ হয় জগৎ-সংসারে নেই। শরিয়ত-মারফতের ভেদ নিয়ে শুরু হয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক পর্যন্ত গড়াতো।”
প্রখ্যাত কবি ও লোকসংস্কৃতি-গবেষক রওশন ইজদানীও জালাল উদ্দীন খাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। ২২ কার্তিক ১৩৬০ তারিখে “দৈনিক আজাদ” পত্রিকায় “বাউল কবি জালাল উদ্দীন খাঁ” শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি বলেন: “মোমেনশাহীর সমস্ত বাউল গীতিকারের মধ্যে জালালের আসন সকলের ঊর্ধ্বে। বাউল গীতিগানে তিনি একাধিক নতুন ধারার প্রচলন এবং বহু নতুন পল্লী রাগ-রাগিণীর উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর বহু শিষ্য আজও তাঁরই নবোদ্ভাবিত সুরে সেসব গান গেয়ে থাকেন।” খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ ১৯৪৯ সালে এক চিঠিতে তাঁর বন্ধু জালাল উদ্দীন খাঁকে লিখেছিলেন: “কোন অজ্ঞাতনামা গ্রামে ফুটিয়া আপন সৌরভে আপনি মাতোয়ারা হইয়া রহিয়াছেন। আপনাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে টানিয়া রেডিওর বুকে ছড়াইয়া দিতে চাই।” বরেণ্য গণসঙ্গীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর “উজান গাঙ বাইয়া” গ্রন্থে ময়মনসিংহ ও সিলেট এলাকার গানের সুরে একটি বিশিষ্ট “জালালী ঢং”য়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

এতসব প্রসঙ্গ টানলাম শুধু এইটুকু বোঝাতে যে, সমকাল গভীর আন্তরিকতায় গ্রহণ করেছিল জালাল উদ্দীন খাঁকে। উত্তরকালে তাঁর পরিচিতি হয়ত সেভাবে ব্যাপ্ত হয়নি, অথচ তাঁর অনেক গান মানুষের মুখে মুখে ফেরে। আব্বাস উদ্দীন আহমদ, আবদুল আলীম এবং আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পী গেয়েছিলেন এইসব লোকপ্রিয় গান: “ও আমার দরদী আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নায় আর চড়তাম না,” “আরে ও ভাটিয়াল গাঙ্গের নাইয়া, ঠাকু ভাইরে কইও আমায় নাইয়র নিতো আইয়া,” “সেই পাড়ে তোর বসতবাড়ি, এই পাড়ে তোর বাসা,” “দয়াল মুর্শিদের বাজারে — কেউ করিছে বেচাকেনা, কেহ কাঁদে রাস্তায় পড়ে।” এগুলো তাঁর সুপরিচিত গান, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ৭০২টি গানের অধিকাংশই গভীর তত্ত্বাশ্রয়ী।

জালাল উদ্দীন খাঁ জন্মেছিলেন ১৮৯৪ সালের ২৫ এপ্রিল আর গত হন ১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই। তাঁর পিতা সদর উদ্দীন খাঁ নিজেও একজন কবি ছিলেন। পিতার কাছ থেকেই জালাল কবিতা ও গানের প্রতি আকর্ষণ অনেকটা পেয়েছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় তাঁর কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তখনই তিনি মুখে মুখে গান বেঁধে তা গাইতেন। তবে গান ও তত্ত্বের চর্চায় তিনি পুরোপুরি নিজেকে নিবেদন করেন ১৯২২ সালে পত্নী ইয়াকুতুন্নেসার আকস্মিক মৃত্যুর পর। শোকার্ত ও উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় তিনি ময়মনসিংহ ও সিলেট এলাকার পির-ফকির-বাউলদের সঙ্গে সময় কাটাতে থাকেন। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সুফি সাধক সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। চিশতিয়া তরিকার এই সাধক বিশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ব ময়মনসিংহ এলাকায় একটি বিশাল ভক্তগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। এই সাধক-পুরুষের কাছ থেকেই জালাল ইসলাম ধর্মের সুফি পন্থা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন এবং “ওয়াহিদাতুল ওয়াজুদ”পন্থী সুফি ভাবধারায় উদবুদ্ধ হন।
প্রথম জীবনে তিনি সমসাময়িক বাউলদের সঙ্গে অনেক বড় বড় আসরে তত্ত্ববিচারমূলক গান করেছেন। কিন্তু ১৯৫০-এর দশক থেকে আসরে উঠে গান গাওয়া ছেড়ে দেন এবং পুরোপুরি গান লেখা ও তত্ত্বচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তেরোটি তত্ত্বে তিনি নিজের গানকে বিন্যস্ত করেছিলেন। এখানে আত্মতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, নিগূঢ় তত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি পারমার্থিক বিষয় যেমন রয়েছে, তেমনি আছে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা ও মানবিক আবেদনে জারিত লোকতত্ত্ব, দেশতত্ত্ব, ভাটিয়ালি ও বিরহতত্ত্ব। গানের সংকলন “জালালগীতিকা”র চারটি খণ্ড তিনি নিজেই বের করে গিয়েছিলেন। “বিশ্বরহস্য” নামে একটি প্রবন্ধের বইও বের করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর “জালালগীতিকা পঞ্চম খণ্ড” প্রকাশিত হয়। এসব বই একত্র করে ২০০৫ সালে “জালালগীতিকা সমগ্র” বের করা হয়। অধ্যাপক যতীন সরকার বইটি সম্পাদনা করেছেন।
বাংলাদেশের লোকসমাজ জীবন-জগৎ-ধর্ম-দর্শন নিয়ে যা ভেবেছে তার মোটামুটি ১৩-১৪ শ বছরের ইতিহাস আমরা পাই এবং এইসব চিন্তার মণিরত্ন পেয়ে যাই যাঁরা সাধারণ মানুষের দার্শনিক তাঁদের উচ্চারণে। জালাল উদ্দীন খাঁর মতো কবি-সাধক-ভাবুকরাই এই সাধারণ মানুষের দার্শনিক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলার লোকসমাজ যে তত্ত্বদর্শন গড়ে তুলেছে তার সারাৎসার জালাল খাঁর গানে আছে। এখানে যেমন প্রচলিত ব্যবস্থা, বিধিবিধান ও নানা ধরনের ভেদবিচার সম্পর্কে অনেক তীব্র-তীক্ষ্ণ প্রশ্ন আছে, তেমনি আছে অন্তরের চোখ দিয়ে, প্রেমের চোখ দিয়ে সবকিছুকে দেখার প্রয়াস। আর আছে নিজের দেহের মধ্য দিয়ে গভীরভাবে নিজেকে জানার প্রয়াস এবং নিজের মধ্য দিয়ে পরম সত্তাকে জানার আকুতি। আছে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে অভেদ-কল্পনা।
এই উপলব্ধি থেকেই জালাল উদ্দীন খাঁ বলেছেন: “কী ছুরত বানাইলে খোদা রূপ মিশায়ে আপনার,/এই ছুরত দোজখে যাবে যে বলে সে গোনাগার।” বলেছেন: “ন্যায়ে থাক সত্য রাখ, ধর্মরক্ষা তারেই কয়/বিশ্ববোধের ধর্মে দেওয়া মানবত্বের পরিচয়।/মিথ্যাটাকে দেও বিসর্জন, সত্য সেবায় রাখ জীবন/হিংসা হতে আপনি আপন থাকবে সরে সব সময়।” সব মরমি সাধকের মতোই তিনি ধর্মের খোলসটাকে নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে তার ভেতরের শাঁসটিকে পেতে চেয়েছেন। আর ভেতরের শাঁসটি কী? সত্য, ন্যায়, দয়া, অহিংসা, বিশ্ববোধ — এগুলোই। এই শাঁসটিকে যদি মানতে পারি তাহলে মানুষের জাত কী, ধর্মীয় পরিচয় কী তা নিয়ে এত ভ্রাতৃঘাতী দ্বৈরথের প্রয়োজন হয় না। অকুণ্ঠচিত্তে জালাল বলে গেছেন: “বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে হিন্দু কে মুসলমান।/রক্ত মাংস একই বটে সবার ঘটে একই প্রাণ।।”এবং “একই যদি সবার গোড়া, আছে যখন স্বীকার করা/ভিন্ন করে ভবে কারা দিয়ে গেল বিভেদের জ্ঞান?” তারপর বলেছেন: “একের বিচার কোথায় গেল, পরম কিসে চিনা হল/জালাল উদ্দীন ঠেকে রইল গাইল শুধু ভাবের গান।” যিনি পরম তিনি তো এক। সেই একই সবকিছু, সবই সেই একের প্রকাশ। আমরা যদি বিভেদকে বড় করে তুলি তাহলে পরমকে আমাদের কতটুকু চেনা হলো? একই ধরনের ভাব জালালের অনেক পূর্বসূরির উচ্চারণে ধ্বনিত হয়েছে। কারণ এগুলিই বাংলার প্রাণের কথা, বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যের গভীরতম বাণী। এসব বাণী আমাদের বুঝতে শেখায়, আমাদের মাটির ভেতর থেকে যুক্তি ও ভাবের যে নিরন্তর প্রবাহ উৎসারিত হয়েছে তা পশ্চিম থেকে আসা ধ্যানধারণার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
আজকের দিনে দেশে দেশে স্বার্থ আর ক্ষুদ্রবুদ্ধির প্রতাপে যখন অহরহ মানুষের এক পরিচয়ের সঙ্গে অন্য পরিচয়ের নিষ্ঠুর লড়াই বাঁধিয়ে তোলা হচ্ছে এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সংঘাত রক্ত ঝরাচ্ছে অবিরাম, তখন জালাল উদ্দীন খাঁর মতো লোকবাংলার সাধক-কবির এই কথাগুলি তো আরো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তাঁর এই সরল ও মহৎ অভিজ্ঞান দিয়েই আজ তাঁকে স্মরণ করি।