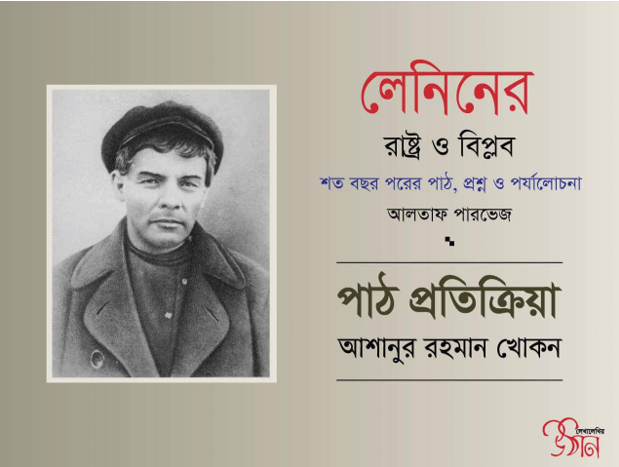মননরেখা’র কবি আহমেদ ইলিয়াস সংখ্যা
বর্ষ ৪, সংখ্যা ৭ ॥ পৌষ ১৪২৭, ডিসেম্বর ২০২০
সম্পাদক: মিজানুর রহমান নাসিম প্রচ্ছদ: আরাফাত করিম, অলঙ্করণ: অজিত দাশ। উৎসর্গ : প্রয়াত কৃতী অনুবাদক জাফর আলম (১৯৪৩-২০২০)
বাংলাদেশের প্রবীণ উর্দুভাষী কবি আহমেদ ইলিয়াসকে নিয়ে প্রকাশিত মননরেখার এই সংকলনটি মননরেখার উর্দুভাষা ও সাহিত্যকেন্দ্রীক দ্বিতীয় সংকলন। এর আগে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের আর এক কিংবদন্তীতুল্য উর্দুকবি নওশাদ নূরীকে নিয়ে মননরেখার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই এ বিষয়ে কর্মপরিকল্পনার মানসভূমি তৈরি হয়। বর্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয়তে এ বিষয়ে একটি বক্তব্য রয়েছে।
কবি আহমেদ ইলিয়াসের অবস্থান বাংলাদেশের বাংলাভাষাকেন্দ্রীক মূলধারার সাহিত্য বলয়ের বাইরে। ফলে গত ৬ দশক ধরে কবিতা লিখলেও ভিন্নভাষী বলে তিনি মোটাদাগে অপঠিত, অচর্চিত ও বলা যায় অস্বীকৃত। কবি হিসেবে তাঁর পরিচিতি তাঁর সগোত্রীয় শিক্ষিতজনদের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। মননরেখার চেষ্টা সেই ক্ষুদ্রায়তন থেকে মুক্ত করে কবি আহমেদ ইলিয়াসকে বাংলাদেশী সাহিত্যের বিস্তৃত জমিনের ক্যানভাসে উপস্থাপন করা। শুরুটা করতে হয়েছে তাই সম্পাদকীয় থেকেই, সেইসাথে সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি দিয়ে যাতে চোখ বুলিয়ে একটা আন্দাজ তৈরি হবে এবং ইলিয়াসপাঠপর্বে প্রবেশে পাঠক খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। এরপর ইতিহাস-ঐতিহ্যের নিরিখে বাংলাদেশে উর্দু সাহিত্য চর্চার একটি বয়ান আছে জাভেদ হুসেনের ‘উর্দুভাষী বাংলাদেশী কবিদের আখ্যান’ প্রবন্ধে। ইলিয়াস কাব্যের মূল আলাপে প্রবেশের আগে এটি দ্বিতীয় দরোজা। উপমহাদেশে ‘ভাষার রাজনীতি’র স্বরূপ অন্বেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন ভাষা কিভাবে শাসকের হাতিয়ার হয়ে জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করাতে পারে, ইংরেজরাই প্রথমে যা সূচারুরূপে করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা যায়, উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্তে ভাষা কীভাবে জাতি-হিংসার শিকার হতে পারে। এই বাস্তবতার পটভূমিতেই ভাষা আন্দোলনোত্তর বাংলাদেশে উর্দুভাষীদের সাহিত্যচর্চা হচ্ছে।
কবি আহমেদ ইলিয়াসের জন্ম ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩৪, কলকাতায়। তাঁর পূর্বপুরুষের ভিটা ভারতের বিহার রাজ্যের মুঙ্গের জেলায়। লেখাপড়া করেছেন কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়ায় ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। এরপর পাবিবারিক সংকট, আর্থিক সমস্যায় যখন টালমাটাল জীবন, আর এক অবাঙালি বন্ধুর আহবানে ১৯৫০ সালে আগপাছ না ভেবেই ঢাকা চলে আসেন, যদি পড়ালেখাটা চালিয়ে যাওয়া যায় এই আশায়। কিন্তু টিকতে পারলেন না, ফিরে গেলেন কলকাতায়। এবার ওখানকার বন্ধুদের সহায়তায় আবার শুরু করলেন। ইসলামিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হলেও অসুস্থতার কারণে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে ফের ১৯৫৩ সালে স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে এলেন। ১৯৫৮ সালে প্রাইভেটে ম্যট্রিক পাশ করলেন, পরের বছর কর্মজীবনের পাশাপাশি নাইট শিফটে ভর্তি হলেন কায়েদে আযম কলেজ (সোহরাওয়ার্দী কলেজ)। ১৯৫৯ সালে হোসনে আরার সাথে দাম্পত্যজীবন শুরু করেন। পাকিস্তান জিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগে সার্ভেয়ার হিসেবে কয়েক বছর কাজ করে ১৯৬২ সাল ঢাকা প্রেসক্লাবে ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন। এরপর সাংবাদিকতা পেশার শুরু ‘পাসবান’ পত্রিকায় উপ-সম্পাদক হিসেবে। ১৯৬৮-১৯৭১ পর্যন্ত ‘রুদাদ’, ‘জারিদা’, ‘ওয়াতান’, করাচিভিত্তিক ‘ডেইলি আজাদ’-সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে কর্মজীবন অতিবাহিত। ১৯৭০ সালে ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের পত্রিকা ‘ল্যায়ল ও নাহার’ এর ঢাকা প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান; সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৮৩ সালে আল-ফালাহ বাংলাদেশ-এ কার্যনির্বাহী পরিচালক পদে যোগদান করেন। ভূমিকা রেখেছেন বাংলা উর্দু সাহিত্য ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠায়। কবি আহমেদ ইলিয়াসের প্রকাশিত উর্দু কাব্যগ্রন্থসমূহ: আইনা রেযে (১৯৮৯), হরফে দারীদা (২০১০), আযাবে আগহী (২০১৩), যখম শাখে হিজর কা (২০১৪), মাহাযে শব্ (২০১৫) এবং শিকস্ত ও রুখত। উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : Biharis: The Indian Emigres in Bangladesh : An Objective Analysis, The World I Saw: Memoir of A Commoner; A Long Walk. গদ্য-পদ্য মিলিয়ে মোট ১৫টি প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রকাশের অপেক্ষায় ৪টি। পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন: শামসুল হক ফাউন্ডেশন, সৈয়দপুর কর্তৃক একুশে পদক (২০০৮), তমদ্দুন মজলিস, ঢাকা কর্তৃক ‘২১ ফেব্রুয়ারি পুরস্কার’ (২০০৯), কর্ণাটক উর্দুু একাডেমি কর্তৃক সংবর্ধনা (২০১০) এবং জ্ঞাতিজন সংবর্ধনা, ঢাকা (২০১৪)।
কবি আহমদ ইলিয়াসের আত্মজীবনী গ্রন্থ The World I Saw: Memoir of A Commoner তাঁর জীবন ও কাব্য সম্পর্কীত এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। ব্যক্তিগত জীবনের ছোট ছোট ঘটনা বর্ণনার সাথে তিনি ত্রিকাল (বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ) দর্শনের জান্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। উপমহাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের ক্যানভাসে তাঁর সমগ্র জীবনাভিজ্ঞতা ও অর্জনের এ এক অনন্য দলিল। এই আত্মজীবনীর একটি নির্বাচিত অংশ পড়ে বিশিষ্ট অনুবাদক ও প্রবন্ধিক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস তাঁকে বড় মাপের কথাসাহিত্যিক বলে উল্লেখ করেছেন। আশানুর রহমানের প্রাঞ্জল অনুবাদে মননরেখার এই সংখ্যায় আহমেদ ইলিয়াসের আত্মজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ আমরা পাবো। খালিকুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছেন, ‘এই আত্মজীবনীতে আমাদের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন এবং অন্যান্য ছোটবড় অনেক সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর যে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা, ষাটের দশকে এখানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় শান্তিকামী বাঙালি নেতাদের সঙ্গে মিলে তাঁর এবং তাঁর মত আরো কিছু প্রগতিশীল অবাঙালি নেতাদের যে ভূমিকা তা পড়ে যে কেউ মনে করতে পারে যে এ ধরনের মানুষ যদি উর্দুভাষী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাল ধরতেন তাহলে হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি আর সংখ্যালঘু অবাঙালি সম্প্রদায়ের নানা তিক্ততা, রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং পরস্পরকে না-চেনা, না-বোঝার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যেত। এই আত্মজীবনীতে তিনি কেবল নিজের কবি হয়ে ওঠা সম্পর্কেই নয়, এদেশের সব সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণারই পরিচয় দিয়েছেন। স্বাধীনতাপরবর্তী সম্প্রদায়গত অবিচার, অত্যাচারের কথা যেমন নির্ভীক কণ্ঠে বলেছেন, তেমনি শাসনতন্ত্রে ক্ষুদ্র ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা অধিকার সংরক্ষণ করা হয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন।’
নিজের কবি হয়ে ওঠার গল্পে ইলিয়াস তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, ‘কলকাতার ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমি আমার নিজের উর্দু কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ পাই। ওটাই প্রথম অনুষ্ঠান যখন আমাকে কবি হিসাবে মুশায়রায় আমন্ত্রণ করা হয়। আমি খুব ঘাবড়ে যাই এবং সভায় আমার গজলটি পড়ার আগে সেটা দেখার জন্য কলকাতার প্রবীণ উর্দু কবি আবদুল হাফিজ রাজ্জাকীকে অনুরোধ করি। তিনি অত্যন্ত সদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমার ভুলগুলি সংশোধন করে দেন এবং আমাকে মুশায়রায় অংশ নিতে উৎসাহিত করেন। সেই সময় আল্লামা জামিল মাজহারী বিহার এবং বাংলার অন্যতম প্রবীণ প্রগতিশীল উর্দু কবি হিসাবে গণ্য হতেন। তিনি ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক মুশায়রাতে সভাপতিত্ব করেন। যাহোক সেই অনুষ্ঠানে, আমার পালা এলে আমি নিজের গজল আবৃত্তি করলাম।’ এরপর তাঁর বর্ণনায় বুঝা যায় যে, তাঁকে আর পেছনে ফেরত তাকাতে হয়নি।
কবি আসাদ চৌধুরী আক্ষেপ করে বলছেন, ‘বাংলাদেশে যারা অবহেলিত – যাদের একটা পত্রিকা নাই, যাদের একটা প্রেস নাই, যাদের একটা কথা বলার মত প্লাটফর্ম নাই, পাবলিকেশনস নাই, সেইখানে ইলিয়াস একাই প্রতিষ্ঠানের মত কাজ করে যাচ্ছেন।’ আসাদ চৌধুরী এও বলছেন, ‘আর এখন যিনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি করছেন তিনি আহমেদ ইলিয়াস। আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।’ আক্ষেপ দেখি আলতাফ পারভেজের লেখাতেও, ‘৮৬ বছর বয়সী কবিকণ্ঠের এই আর্তিকে একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রক্ষার আবেদন আকারে দেখা যায়। বাংলাদেশের জন্য এটা গৌরবের হবে যদি উর্দুভাষীদের পুনর্বাসনে যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তাতে মাতৃভাষার লিখন-পঠনে মদদ দানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এভাবে আমরা আরও জোরের সঙ্গে বলতে পারব, কোনো ভাষার বিরুদ্ধে নয়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের বিরুদ্ধে। উর্দুভাষী মানুষগুলোকে সমাজের মূলধারায় নিয়ে এসে বাংলাদেশ একাত্তরের বিজয়কে নৈতিকভাবে আরও বড় উচ্চতায় নিতে পারে। আহমেদ ইলিয়াসের মত লিখিয়েদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে বাংলা একাডেমির মত প্রতিষ্ঠানগুলো আক্ষরিক অর্থেই বহুভাষী বাংলাদেশের মননশীলতার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের সামনে তাই স্ব-আরোপিত একটা ভাষাগত গণ্ডি পেরোনোর চ্যালেঞ্জ এসেছে আজ।’
মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তাঁর প্রবন্ধে আহমদ ইলিয়াস সম্পর্কে বলছেন, ‘পার্টিশন লিটারেচারের কোন্ কাতারে ফেলা যাবে আহমেদ ইলিয়াসকে এমন প্রশ্ন আমাকে বিব্রত করে। সব ছাপিয়ে মনে করিয়ে দেয় ফিওদর দস্তয়েভস্কির কথা, যাঁর সম্পর্কে বলা হয় মানুষের বেদনা এমন নিবিড়ভাবে আর কেউ অনুভব করেনি। প্রকাশ বিচারে নয়, পার্টিশনের বেদনা অনুভবের বিচারে ইলিয়াসকে মনে হবে দস্তয়েভস্কিয়ান। আর সে-কারণেই ইলিয়াসের কবিতা কেবল ইতিহাস ও ভূগোলে প্রোথিত নয়, এই কবিতা বিতাড়িত মানবভাগ্য থেকে উৎসারিত, যে মানব-মানবী উৎসন্ন বিচ্ছিন্ন বিতাড়িত, ঘরের সন্ধানে পথ চলছে, এমন এক বিড়ম্বিত সময়ে যখন ঘর নেই, পথও নেই, আছে শুধু চলা। তাই সময় থেকে উৎসারিত হয়ে সময়হীনতার দিকে হাত বাড়ায় তাঁর কবিতা, হয়ে ওঠে বিচূর্ণ আত্মার আর্তি, মানবভাগ্যের কবিতা।’ আর এই আত্ম-উপলব্ধির চূডান্ত নির্যাস আহমদ ইলিয়াসের এককটি নযম, শের আর গজল। তিনি জীবনযুদ্ধের এমন এক সৈনিক যিনি হাল ছাড়েন না কখনও, তাঁর লড়াই অব্যাহত থাকে একের পর এক। মূলত ইলিয়াসের জীবন-অভিধানে পরাজয় শব্দটি একেবারেই অনুপস্থিত।
শেকলপরা এই উপমহাদেশের মানুষকে নিজের ইতিহাস জানতে দেয়া হয়েছে কমই। নানান পরিচয়ের রাজনীতিতে তাদের ভাগ করে আসল একক ইতিহাস বাদ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম সব উপ-ইতিহাস। আর জনসমাজ নানান উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বন্দনা করে চলে সেসব উপ-ইতিহাসের। আহমেদ ইলিয়াসের কবিতা সেসব উপ-ইতিহাসের ট্রাজেডি এবং প্রহসনকে তুলে ধরে যেন। একই সঙ্গে এক জীবনে তিন দেশের নাগরিক কবি আহমেদ ইলিয়াসের অলংকারহীন কবিতাবলী দক্ষিণ এশিয়ার মূল ইতিহাসের দিকে আমাদের দিকনির্দেশ করে। এই অর্থে তাঁর কবিতা এক ধরনের আশা ও ভবিষ্যতেরও প্রতীক বটে। পার্টিশন লিটারেচারের অবশ্য পাঠ হয়ে উঠেছেন কবি আহমেদ ইলিয়াস। ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেন, “দেশভাগ। ইতিহাসের বৃহত্তম এক্সোডাস। দেশভাগের স্মৃতিজাত সকল বয়ানই ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং জানায়: ‘কী ছিল আমার’, ‘কী হারিয়েছি আমি’ ‘কে ছিলাম আমি’। এসব বয়ান স্মৃতিধর কর্তাপক্ষের ‘অতীত’ যেমন জানায়, তেমনি বুঝতে সাহায্য করে তাঁর/তাঁদের পরিচয়ের পূর্বাপর। ভবিষ্যতের কাছে তাদের দাবির আভাসও এ থেকে মিলতে পারে। দেশভাগের শিকারদের পরিচয়ের বিপরীতে থাকে এই ট্রমাটিক ঘটনার জন্য দায়ী ‘অশুভ’র পরিচয়ও। এভাবে এসব স্মৃতিকথা আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে শত্রুর পরিচয়ও নির্মাণ করে। অথচ আহমেদ ইলিয়াসের সত্তার বিপরীতে, তাঁর কবিতার জগেতে কোনো শত্রু নাই, অশুভ নাই। কেবল রোদন আছে।” একই সুর শুনতে পাই মননকুমার মণ্ডলের লেখায়, “আহমেদ ইলিয়াস একজন সাংবাদিক, একজন পরিচয়হীন উর্দু কবি। এমন এক কবি যিনি শুধু নিজের পরিচয়ের খোঁজেই লিখে চলেন। বাংলাদেশে ‘মোজাহের’ হয়ে আসা বিহারি মুসলমান এবং পরবর্তীতে প্রত্যাখ্যাত ‘উদ্বাস্তু’ পরিচয়ে রূপান্তরিত মানুষগুলির একটা মুখ তিনি। এইসব মানুষগুলির রিলিফ, রেপার্টিয়েশনের আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়ে থাকা একজন সংগঠক; যিনি উর্দুভাষার পরিচয় নিয়ে পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লিখে চলেছেন। এনসিআরসি-র মাধ্যমে জেনেভা ক্যাম্পের সংগঠক হিসেবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে উর্দুভাষী মানুষদের যে ন্যূনতম অধিকারটুকুও আজ স্বীকৃত হয়েছে তা আইনি পথেই হয়েছে। পার্টিশনের যে ক্ষত বহন করে বিগত সত্তর বছর এই উপমহাদেশে পরিচিত সত্তার রাজনীতি সচল থেকেছে, সেখানে এমন ‘দেশ’ হারানো মানুষগুলির সংকটকে আমরা যদি গুরুত্ব দিতাম তাহলে উপকৃত হতাম আমরাই। আগ্রাসনের ভাষাকে কোনো সমাজ-ব্যবস্থাই মেনে নিতে পারে না। ”
রুখসানা কাজল খুঁজে পান এক অসহায় কবিকে, ‘অখণ্ড ভারতবর্ষের নাড়িছেঁড়া শেষ প্রজন্মের সন্তান তিনি। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং শেষের এ বার্ধক্যকালের সাক্ষী হচ্ছে, তিন তিনটি দেশ এবং জাতির শাসনকাল। বৃটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। সময় তাঁকে অভিজ্ঞতার এক মহাপথিকে পরিণত করে তুলেছে। আর ভাগ্য তাঁকে দান করেছে সতত বিড়ম্বনা, নিরাপত্তা-সঙ্কুল দিনরাতের সাথে সৌভাগ্যের সুবাসহীন এক হতাভাগা জীবন। তিনি বাংলাদেশের উর্দুু কবি আহমেদ ইলিয়াস।’
ফ্রস্টের কবিতার উদাহরণ টেনে মোঃ মেহেদী হাসান তুলে ধরেছেন আহমেদ ইলিয়াসকে। তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে, আহমেদ ইলিয়াস বলছেন, ‘শহরের এই যে রাস্তা দ্বারে দ্বারে নাড়ছে কড়া/ এই এক সঙ্গী আজও ছেড়ে যায়নি আমায়। এতো কোলাহল, হৈচৈয়ের মাঝে একমাত্র রাস্তা তাঁকে ছেড়ে যায় নি; এটা অনন্য একটা ঘটনা। কারণ বহমানতার জন্যে কবির দরকার একটা রাস্তার। মার্কিন কবি ফ্রস্টের (১৮৭৪-১৯৬৩) রাস্তার কথা আমাদের মনে পড়ে। ফ্রস্টের রাস্তা বাছাই করার সুযোগ ছিল। তিনি দুটো রাস্তার মধ্যে একটি বাছাই করেছেন চলার জন্যে। তারপর আক্ষেপ করেছেন অন্যটিতে তার চলা হয় নি বলে, কিংবা কোনোদিন হবে না বলে। কারণ জীবনতো একমুখী এক অগ্রসরমানতা মাত্র। পেছনে ফিরে আসা যায় না। আহমেদ ইলিয়াসের ক্ষেত্রে সমস্যাটা তেমন নয়। আহমেদ ইলিয়াস যে রাস্তা ধরে চলেন সে রাস্তা আসলে তাঁর নিজের পছন্দ করা রাস্তা নয় ফ্রস্টের মত। অনেকটা বাধ্য হয়ে এ রাস্তায় তাঁকে নামতে হয়। কারণ না চলে তাঁর উপায়ও নেই, ‘পথ চলায় তো পেয়েছি দেয়াল দরজা প্রতিটি মোড়ে/ নিজের ঘরের পর ইলিয়াস কোথায়ও পেলাম না ঘর’। একটা ঘর না পেলেও রাস্তা ধরে তিনি চলেন ঠিকই। তাঁর অভিজ্ঞতাও কম হয় না, ‘আমার পথ চলার এই অভিজ্ঞতা হে ইলিয়াস/ গন্তব্য মেলে না পদচিহ্নের আগে’। এভাবে না-ছোড় রাস্তা ধরে তিনি আসলে কোথায় পৌঁছান? মোটাদাগে আরেকটি রুবাইতে বরং হতাশাই ধ্বনিত: ‘বহুদিন ধরে চলছি তবু জানি না/ এই পথই চলছে না কি আমি চলছি পথে/ কেউ আমার পথ হারানোর ইতিহাস লিখতো যদি/ আমি অক্ষরে অক্ষরে ছিন্ন হয়ে আছি পথে’।
মিজানুর রহমান নাসিম তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘বিহারিদের প্রগতিশীল অংশ সেদিন পাকিস্তানি বাহিনীর চাপিয়ে দেয়া আগ্রাসী যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ করেছে। নিজ কমিউনিটির লোকজনকে স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণের জন্যে পরামর্শ উদ্বুদ্ধ করেছে। তারা অনেক বাঙালির জীবনরক্ষায়ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছে। এ সকল প্রগতিশীল উর্দুভাষী মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের চক্ষুশূল ছিলেন। তাঁরা পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নিগৃহীতও হয়েছেন। তাঁদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী। অথচ পরিহাসের বিষয়, যে বাঙালিদেরকে তাঁরা জীবন বিপন্ন করে সমর্থন করলেন তাঁদের চোখেই আবার স্বাধীনতার পর তাঁরা শত্রু বনে গেলেন। তবে প্রগতিশীল কিছু বাঙালি রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের সদস্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় কিছু বিহারি পরিবারকে রক্ষা করেন।’
এ টি এম মোস্তফা কামাল কবির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, ‘আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি, আমাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ন্যায্যতার প্রতি সমর্থন ছিলো ইলিয়াসের। পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের ন্যায়ের লড়াই যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই সে বিশ্বাস ফুটে উঠেছে বিখ্যাত নযমটিতে-
আমি দেখছি ঘরের সব তরুণ মুখ আমাদের/কালো ঝড়ের সাথে লড়তে লড়তে/চুপচাপ শুয়ে পড়েছে ভোরের আগে/ পলকে পলকে অশ্রু হয়ে/হারিয়ে গেছে কালো ঝড়ে/ আমি জানি/যে ঘরেই নিভেছে প্রদীপ/ সেখানেই সূর্য উঠবে (কালবৈশাখি/অনু.-জাভেদ হুসেন)
একাত্তরের সেই ভয়াল কালো রাত ভয়ঙ্কর কালবৈশাখি রূপে আমাদের সবকিছু তছনছ করে দিয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকদের কালো হাতের কলঙ্কময় কাজের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি অনন্য দক্ষতায়। কবিতার সমাপ্তিও আত্মবিশ্বাস আর আশাবাদে দ্যুতিময়।’
বিশিষ্ট উর্দু কবি শামীম জামানভি মনে করেন, ‘আহমেদ ইলিয়াস প্রকৃত অর্থে যদি ফলো করেছেন তবে বলতে হয় ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে ফলো করেছেন। ফারাজকেও না, সরাসরি ফয়েজকে। ইলিয়াস ভাইয়ের সব কবিতা হয়ত বিখ্যাত হয় নি, কিন্তু উনার কবিতায় একটা পথনির্দেশ আছে।’
উর্দু কবি আলিমুল্লাহ হালি মনে করেন, ‘আহমেদ ইলিয়াসের দক্ষতা সম্পন্ন সৃজনী-যাত্রা উর্দু সাহিত্যের গতানুগতিক ধারা দিয়ে শুরু হয়। তবে এই গতানুগতিক ধারা তাঁর জন্য একটি প্লাটফর্ম ছিল মাত্র। কারণ, পরে তিনি এখান থেকে বেরিয়ে এমন এক স্থানে চলে আসেন যেখানে গতানুগতিক ধারা অনেক পিছনে থেকে যায়। আশ্চর্য আরো যে, নতুনত্বেরও কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না। কবির সৃষ্টিকর্মে কাউকে অনুসরণ করার কোন আলামত নেই বরং সেখানে নতুন এক ধারা তৈরি হয় যেখানে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা একাকার হয়ে আছে।’
জহির হাসান কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ আর মনে করেন আহমেদ ইলিয়াস পরিহাসপ্রিয় কবি , ‘আহমেদ ইলিয়াসের নযম-গজল-শের তথা কবিতা পাঠের মুগ্ধতা নানা মাত্রায় দেখা যায়। তাঁর কবিতাগুলি রংধনু আর প্রজাপতির রং ছিটানো। নানা দিক-তলে বিভাজিত তাঁর কবিতা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কবিতার এতো মুগ্ধ পাঠক হই পড়বোনে প্রথমে ভাবি নাই। আমার পুরা ইলিয়াসপাঠই জাভেদের অনুবাদ নির্ভর। জাভেদের অনুবাদ না হইলে বাংলাদেশের এত বড় একজন কবিরে আমরা হারাই ফেলতাম! জানতামই না ঘরের কাছেই আরশি নগর! পরিহাসপ্রিয় কবি আহমেদ ইলিয়াস। তাঁর কাব্যের এই রসগুণ আমারে মুগ্ধ করে। ঠাট্টা, তামাশা হাজির রয় তাঁর কবিতায়। এইসব পরিহাস এমনভাবে হাজির হয় যে, জীবনের কেন্দ্র থাকি খুব দূরে ন সেই পরিহাস। কেন্দ্রীয় কোনো ধারণা কিংবা কোনো নিয়তিরে যেন অবলীলায় তামাশা ঠাট্টার মাধ্যমে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। কিংবা নিজেই নিজের আত্মারে কাঁটাবিদ্ধ করি তামাশায় মাতেন।’
বিশিষ্ট উর্দুভাষী কবি ও প্রাবন্ধিক আতাউর রহমান জামিলও একইভাবে বলছেন, ‘…কিন্তু পরে তাঁর কবিতার দরজা একের অধিক খুলে যায়। ফয়েজের মত তাঁর কণ্ঠস্বরও কোমল। আহমেদ ইলিয়াসের নযম কিছু দূর পর্যন্ত অন্তমিলের রীতিনীতি মেনে চলে। কিন্তু এর পরিমাণ খুব কম। পরের সব নযম মুক্ত কবিতা। মুক্ত কবিতার এক ধারণা হল এই যে, অন্তমিলের জবরদস্তি প্রয়োগের কারণে ভাব আর শব্দের মাঝে যে দ্বন্দ্ব হয় তা থেকে কবিতাকে রক্ষা করা। দেখে দুঃখ হয় যে, কম উর্দু নযমই এই মানদণ্ডে পার হতে পারে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, কয়েকটা পংক্তি বা লাইন যদি কবিতা থেকে বাদ দেয়া হয় পুরো কবিতারই বিষয়ের অর্থে কোনো ঘাটতি হয় না। কখনও বরং কবিতাটা যেন আরও ভাল হয়ে যায়। দেখে ভালো লাগে যে, আহমেদ ইলিয়াস এই মুক্ত কবিতার শক্তি খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছেন।’
প্রাবন্ধিক সামিউল ইসলাম মনে করেন, ‘আহমেদ ইলিয়াস বলতে গেলে এক জীবন্ত কিংবদন্তী। পালাবদলের স্মারক, খণ্ডিত মানচিত্রের জাজ্বল্যকালের স্বাক্ষী। ক্ষুৎ-পিপাসা, প্রণয়-বিচ্ছেদ, মৃত্যুর হাতছানির আঁচড় গভীর চিহ্নরেখা এঁকে দিয়েছে তাঁর স্মৃতিপটে। তাই তো স্মৃতির বেদনাগুলো বার বার শব্দমালার আদলে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার ভেতরদেশে। হতাশা-বেদনার ভাস্কর্যরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে কবিতার মধ্যে।’
জাহিদুর রহিম শহীদ কাদরীর উদাহরণ টেনে আক্ষেপ করে বলছেন, ‘কবির বাসকালীন জনপদে যদি স্বভাষা চর্চা না থাকে, মারাত্মক সমস্যা হয়। আমাদের হাতের কাছের উদাহরণ শহীদ কাদরী বা এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কারণ ভাষা একটা গতিশীল বিষয়, জীবন্ত। আহমেদ ইলিয়াসের কবিতা দূর থেকে পড়লে মনে হবে উনি জানালা দিয়ে জীবন দেখছেন, দরজা খোলেননি। এই জানালা স্মৃতির জানালা। তাঁর সেই দরজা হয়ত ওনার স্বভাষী জনপদের অপেক্ষায় বন্ধ ছিল। সেটা খুলে গেলে কি হত আমরা জানি না, অন্তত অন্যরকম হত এতে সন্দেহ নাই। আহমেদ ইলিয়াস যদি দিল্লী বা লখ্নৌ বা লাহোরে বসে লিখতেন তাহলে অবশ্যই তাঁর কবিতার ভাষা আলাদা হত। অনুভূতি আর অনুভূতির প্রকাশ আলাদা হত। কিন্তু স্মৃতির জানালা দিয়ে তাঁর এই দেখা আর লেখা থেকে বুঝা যায় কবিতা থেকে তিনি বেঁচে থাকার রসদ কুড়িয়েছেন। যে কবিতা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও আপন ভাষায় কবি লিখে ফেলেনÑ তার মধ্যে যে প্রয়োজন (প্রোপেন্সিটি) থাকে – সেটাই কবিতার স্বার্থকথা। ’
আর উর্দু কবি ও গল্পকার জয়নুল আবেদিনের মতে, ‘আহমেদ ইলিয়াসের কবিতাকে আমরা ট্রিলজি বলতে পারি। তাঁর কবিতার এই তিন পর্বে মানুষের অভিবাসনের ট্রাজেডি পাওয়া যায়। সেই ট্রাজেডি সাম্রাজ্যের নিপীড়নের ফল। এই পরম্পরা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এর প্রভাব আজও বহাল আছে। আজও যেদিকে তাকাই, মাটির বুকে মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে পিঁপড়ের মত এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। লক্ষ্য একটাই, টিকে থাকা। সব দিকে টুকরো টুকরো যুদ্ধ আজও চলছে। শান্তি আর সমৃদ্ধি কেবল এক কল্পনা হয়ে রয়ে গেছে। আহমেদ ইলিয়াসের কবিতায় সেই বদলে যাওয়া সময়ের সাথে বিষয়েরও বদল ধরতে পারা যায়।’
তসলিম হাসান সঠিকভাবেই উর্দু সাহিত্যে আহমেদ ইলিয়াসের অবস্থান নির্ধারণ করছেন এভাবে, ‘আমাদের দৃষ্টিতে কেবল বাংলাদেশের নয়, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ পরবর্তী উর্দু সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আহমেদ ইলিয়াস। অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরে তিনি বাংলার হাওয়া-জল-মাটির স্পর্শে লালিত-পালিত হয়েছেন। আপন মাতৃভাষায় স্বপ্ন দেখেছেন। বাংলাদেশের উত্থানের সাথে তিনিও নিবিড়ভাবে প্রত্যাশা করেছেন একটি স্বাধীন মানবীয় জীবনের। কেবল ভাষাগত কারণে তাঁর সাথে বাংলাদেশী-বাঙালিদের দূরত্ব গড়ে উঠুক, হৃদয়বান পাঠক হিসেবে আমরা তা মোটেও আশা করি না। আমরা চাই গজলে আর্তনাদ-আহাজারির প্রকাশ ঘটুক। তবে তা উর্দুভাষার প্রতি এ দেশের বাংলা ভাষাভাষী মানুষ দ্বারা কৃত পীড়নের ফলাফল হিসেবে যেন প্রকাশিত না হয়ে যায়।’
বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আসিফ আসলাম ফাররুখি আধুনিক উর্দু সাহিত্যের তত্ত্ব তালাশ করে বলেন, ‘‘উর্দু কবিতায় প্রতিনিধিত্বশীল নামগুলো হল আহসান আহমদ আশক, আতাউর রহমান জামিল এবং নওশাদ নূরী। অন্যদিকে, আহমদ ইলিয়াসের ‘আইনা-রেযে’ কবিতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ। ‘ভাঙ্গা আয়না’র এই ছবিগুলো তীক্ষ্ণ এবং পরিষ্কার। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে উৎসর্গিত নযম ও গজলের এই সংগ্রহ শৈলিতে অনবদ্য। প্রেক্ষিত নির্বাচনে হৃদয়স্পর্শী।”
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের বর্ষীয়ান অধ্যাপক আব্দুল লতিফ মনে করেন কবির পরিচিতি মোটেও আড়াল করবার মত না। তিনি মনে করেন, ‘‘সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর পরিচিতি আড়াল করার মত মোটেই নয়। দুইটি দিওয়ান কথা আমার জানা। আর গদ্য-তে তো বেশ কয়েকটি বই আছে তাঁর। ইংরেজি এবং উর্দু দুই ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশেষত বিহারী জনগোষ্ঠী এবং তাদের সমস্যগুলো। সাংবাদিকতা শুরু করেন কলকাতা থেকেই। ঢাকায় ‘পাসবান’ পত্রিকার সাথে জড়িত হন। পরে কিছুদিনের জন্য গমন করেন পশ্চিম পাকিস্তান। সেখানে বিখ্যাত ‘দৈনিক ডন’-এর সাথে কাজ করেন। সেখানে তিনি স্বনামধন্য কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ’এর সাথে অনেকদিন কর্মব্যস্ত থাকেন।”
করাচি থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র ‘রোশনাই’ এর সম্পাদক আহমদ যায়নুদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে বলেন, “কবিতার মাধ্যমেই তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত ব্যথা-বেদনা ও জাগতিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর কাব্যচিন্তার মূল দর্শন প্রগতি ও মানবতাবোধ। তাঁর গজলগুলো বর্ণনায় চমৎকার। তিনি আধুনিক কালের কবিতার চাহিদা, প্রয়োজন সম্পর্কে সমধিক অবগত ছিলেন। তাঁর কাব্য মূলতঃ দেশান্তরীত, হতভাগ্য ও অসহায় জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি অতিবাহিত সময়ের প্রতিটি ক্ষণকে, জীবনের নাড়ি-নক্ষত্রকে খুব ভালভাবে উপলব্ধি করেছেন। আর ওগুলোকেই তিনি নিজ চিন্তা-চেতনার অংশ বানিয়ে নিয়েছেন। তাঁর দুঃখ-কষ্ট একক হলেও সামগ্রিক অন্তর্দৃষ্টির দর্পণ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আহমেদ ইলিয়াসের প্রথম কবিতা সংকলনের নাম ‘আয়না রেযে’ (ভাঙ্গা আয়না) এবং তাঁর দ্বিতীয় কাব্য সংকলন ‘হরফ দরিদা’ (ছিন্নপত্র)-ও জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল, বাংলাদেশে সাহিত্যিকগণ ও জ্ঞানী-গুণীরা বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে নিকটবর্তী করার বিষয়ে ‘বাংলা-উর্দু সাহিত্য ফাউন্ডেশন’ প্রতিষ্ঠিত করে সীমাহীন কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখেছেন। ”
সবকিছু মিলিয়ে মননরেখার কবি আহমেদ ইলিয়াস সংখ্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল। পত্রিকার সম্পাদক মিজানুর রহমান নাসিমকে ধন্যবাদ জানাই এত পরিশ্রমসাধ্য একটি সম্পাদনার জন্য।
মননরেখা আহমেদ ইলিয়াস সংখ্যার সূচি:
সম্পাদকীয়
আহমেদ ইলিয়াসের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি
প্রবন্ধ
উর্দুভাষী বাংলাদেশী কবিদের আখ্যান : জাভেদ হুসেন
আমার বন্ধু আহমেদ ইলিয়াস : আসাদ চৌধুরী
আহমেদ ইলিয়াস ও পার্টিশন সাহিত্য : মফিদুল হক
আহমেদ ইলিয়াস: একজন সৎ বুদ্ধিজীবীর প্রতিকৃতি : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস
সেইসব ঝরাপাতা ও ইলিয়াসের ‘দেশ’ : মননকুমার মণ্ডল
আহমেদ ইলিয়াস: উর্দু কবিতার বাংলাদেশী সংশপ্তক : এ.টি.এম. মোস্তফা কামাল
আহমেদ ইলিয়াসদের প্রতি বাংলাদেশের দায় : আলতাফ পারভেজ
অনুবাদকের হাত ঘুরে আহমেদ ইলিয়াস : মো. মেহেদী হাসান
আহমেদ ইলিয়াস: সংস্কৃতির এক মানব সেতু : রুখসানা কাজল
কবি আহমেদ ইলিয়াসের কাগজের যত ঘর-বাড়ি : জহির হাসান
আহমেদ ইলিয়াসের তীর্থযাত্রা: ঘর, শহর ও আঙিনা : ফারুক ওয়াসিফ
উর্দু কবিতার নীড়হারা বুলবুল – আহমেদ ইলিয়াস : সামিউল ইসলাম
স্মৃতির কারাগারে বন্দী কবি : জাহিদুর রহিম
আহমেদ ইলিয়াস: নিঃসঙ্গ ডানাভাঙা পাখির আর্তনাদ : তসলিম হাসান
অনূদিত প্রবন্ধ
ভাঙা আয়নার ছবি: বাংলাদেশে উর্দুর দৃশ্যপট, মূল ইংরেজি: আসিফ আসলাম ফাররুখি, অনুবাদ: গৌরাঙ্গ হালদার
আহমেদ ইলিয়াস এক কাব্য-কানন, মূল উর্দু : আব্দুল লতিফ, অনুবাদ : সালাম হামিদী
অনূদিত প্রবন্ধ ‘রোশনাই’ (উর্দু) থেকে
শিল্পের আয়নায় : আতাউর রহমান জামিল, অনুবাদ: জাভেদ হুসেন
আহমেদ ইলিয়াসের কাব্য: জয়নুল আবেদিন, অনুবাদ: জাভেদ হুসেন
আহমেদ ইলিয়াসের সৃজনী যাত্রা: আলিমুল্লাহ হালি, অনুবাদ : সালাম হামিদী
আয়না রেজে’র আহমেদ ইলিয়াস: মুশরক সিদ্দিকী, অনুবাদ: সালাম হামিদী
আহমেদ ইলিয়াস সম্পর্কে কিছু কথা: আহমদ যায়নুদ্দীন, অনুবাদ: মাজদার হোসাইন
বই আলোচনা
‘বিহারিজ : দ্য ইন্ডিয়ান ইমিগ্রান্ট ইন বাংলাদেশ: এন অবজেকটিভ এনালাইসিস’ প্রসঙ্গে : মিজানুর রহমান নাসিম
বধ্যভূমির ঘ্রাণ, ফুল্লগন্ধভরা কুঞ্জকোণ : পিয়াস মজিদ
আহমেদ ইলিয়াসের প্রবন্ধ
ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, উর্দু থেকে অনুবাদ: নীলিমা সুইটি
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সাক্ষাৎকার
‘কখনও হাল ছাড়িনিÑ লড়াই করেছি একের পর এক….’ -আহমেদ ইলিয়াস
‘…উনি কবিতায় একটা গাইড দিতে পারেন, যা অন্যরা পারেন না।’ – শামীম জামানভি
আত্মজীবনী
The World I saw: Memoir of a Commoner এর সংক্ষেপিত অনুবাদ : মূল ইংরেজি: আহমেদ ইলিয়াস, অনুবাদ: আশানুর রহমান
কবিতা
আহমেদ ইলিয়াসের নির্বাচিত কবিতা
নযম – গজল – শের
চয়ন ও ভাষান্তর : জাভেদ হুসেন

রুখসানা কাজল
রুখসানা কাজল পেশায় অধ্যাপক। পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। দেশ ও দেশের বাইরের পত্র পত্রিকায় গল্প ও নিবন্ধ লেখেন। এ পর্যন্ত দুইটি উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ এবং অনুগল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে।