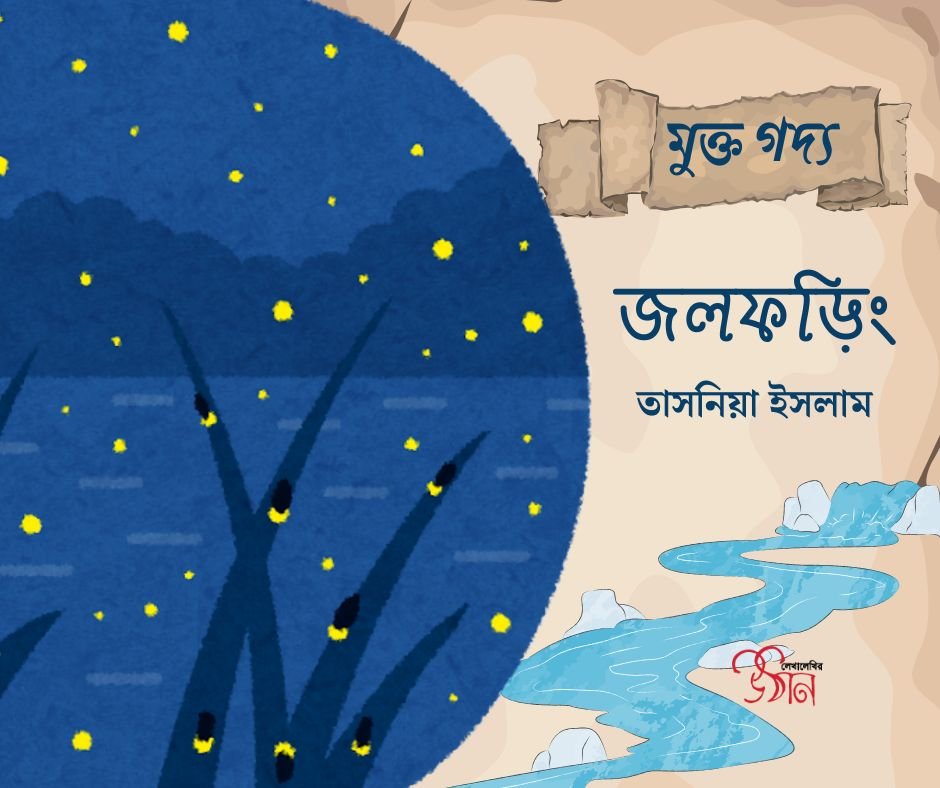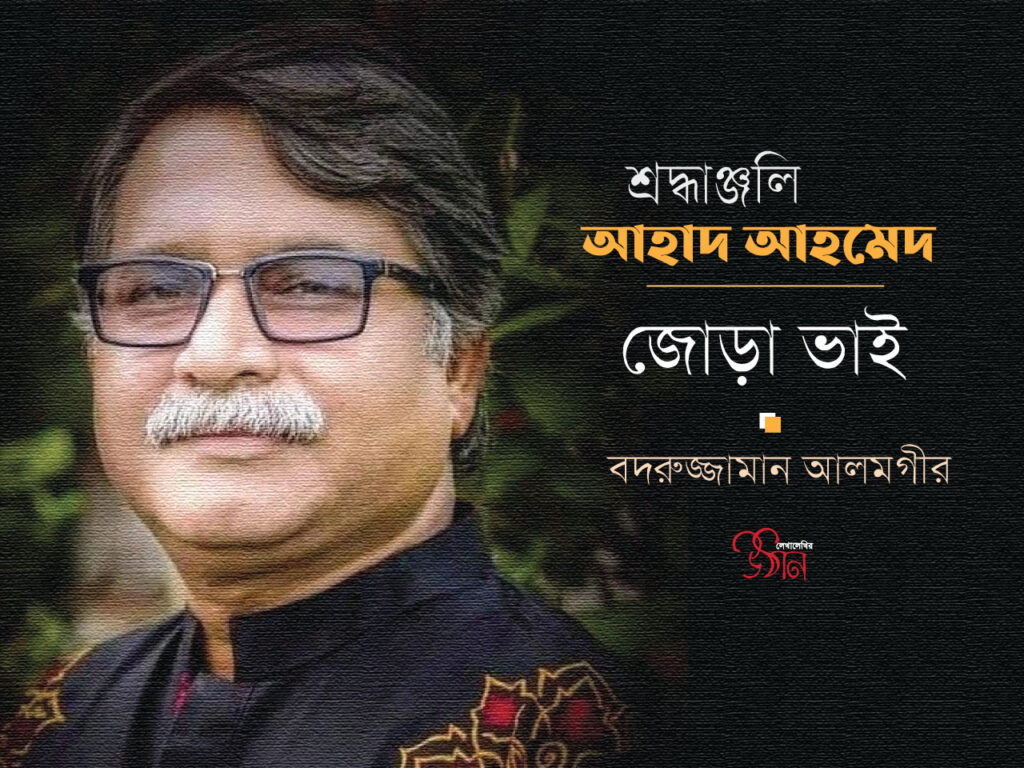অনেকটা সময় ধরে সংশয়ে থাকবার পর শেষে মনস্থির করলাম যে একটা পত্রই লিখব। বাংলা অভিধানে পত্র শব্দটার বেশ কয়েকটা মানে আছে। আর এই সব কয়টা মানেই কোনো না কোনোভাবে একরকম উড়ালের সাথে সম্পর্কিত। তবে পত্র লেখার মূল কারণ হয়ত এটাই যে কেবল পত্রেই নিজের কথা খুব সহজ করে মন খুলে বলে ফেলা যায়, মুক্ত করে দেওয়া যায় বহুদিনের বন্দি হয়ে থাকা বোল। আমি সত্যি ভেবেছিলাম যে আমার কথাগুলো হয়তো কোন দিনই বলা হয়ে উঠবে না। আমার বেড়ে ওঠার গল্পগুলো নৈশব্দেই রয়ে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন যেদিন এই নশ্বর শরীরকে নিশ্ছিদ্র নিরবতা ঘিরে ধরবে সেদিন আমার গল্পগুলোও আমার সাথে মহাকালে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু আজ যখন হঠাৎ করেই ভীষণ কৌতুহলী একটা জলফড়িংয়ের দৃষ্টি আর পেতে থাকা কান পাওয়া গেল তখন যেন সেই গল্পগুলো মুখর হয়ে উঠতে চাইল। পাতলা স্বচ্ছ কাঁচের নিরবতার দেওয়ালে তাদের নখের আঁচড়ে যে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজটা হচ্ছিল তাতে আমার মধ্যে একরকমের সৃষ্টিছাড়া অস্বস্তি মাথাচারা দিতে শুরু করেছিল। তাই ভাবলাম , অনেক হয়েছে, এবার মৈত্রী স্থাপন করা যাক। আর এই সুন্দরের সাথেই গল্পগুলোকে ভাগ করে নেওয়া যাক। তবে মুখে সবটা বলে ওঠা আমার জন্য বেশ কঠিন। তাই পত্রযোগেই গল্পযোগের সিদ্ধান্ত। কিন্তু সে পত্রের ভাষা ঠিক কেমন হবে, কোথা থেকে শুরু করবো, কোথায় গিয়ে শেষ করবো বা আদৌ ঠিক করে শেষটা টানতে পারবো কিনা ইত্যাদি ভেবে বেশ বিপাকেই পড়ে গেছিলাম শুরুতে। তবুও খুব সাহস করে লিখতে আরম্ভ করলাম । আসলে কখনো তো লিখিনি এমন করে নিজের কথা, তাই কেমন একটা জড়তা কাজ করছিল যেন। এটা অনেকটা প্রথম প্রথম কুমোরের চাকায় কাদা মাটির পাত্র গড়তে যাবার মত। শিহরণটা খুব হবে, মনে হতে থাকবে, এই তো! কলসটা হয়েই আসছে বুঝি। কিন্তু আদতে দেখা যাবে যে সেটাকে কিছুতেই যেন সঠিক আকার আর পাওনা মসৃণতাটুকু দেওয়া যাচ্ছে না। পরে ভাবলাম, হোক না এবার একটু এবড়ো থেবড়ো, পরেরবার শুধরে নেব না হয়!
শুরু থেকে শুরু করা যাক তাহলে। আসলে গল্পে ডুবে থাকা আমার বরাবরের নেশা, আর এই ব্যাপারটা আমার বেশ ছোটবেলা থেকেই। দাদার শৌখিনতার বেশকিছু নমুনার মধ্যে একটা ছিল তার নিজের হাতে গড়া লাইব্রেরিটা। সেগুন কাঠের তৈরি নকশা কাটা শেলফে থরে থরে সাজানো ছিল বই। যদিও লিখতে শিখেছিলাম আমি দেরিতেই, অনেকটা বড় হবার পর, কিন্তু জেঠুর কল্যাণে পড়তে পারাটা অন্য সবার এমনকি নিজেরও অজান্তে আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম খুব ছোটতেই। প্রতিবার সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি আসলেই বিকেলবেলাগুলোতে জেঠু আমাদেরকে, মানে আমাদের দু তিন গন্ডা চাচাতো ফুফাতো ভাই বোন যাদের বয়স ঘরে চার থেকে আট বছর, তাদেরকে খুব গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়ে নিজের চারপাশে বসিয়ে বইয়ের পাতায় আঙ্গুল ঠেকিয়ে গড় গড় করে গল্প পড়তেন।
প্রথম প্রথম বইয়ের পাতাগুলোকে আমার হিজিবিজি নিরর্থক আঁকিবুকি বলেই মনে হতো বৈকি। তবে গল্প পড়তে থাকার সময় গুলোতে জেঠুর মুখের চওড়া হাসিটা আর তার আতস কাঁচের মতো চশমার ভেতর দিয়েও দিব্যি দেখতে পাওয়া যায় এমনই উচ্ছ্বসিত জ্যোতির্ময় চোখ দুটো দেখে আমার মনে হয়েছিল যে পড়তে পারার ব্যাপারটা হয়তো মন্দ না। তাই ভীষণ একটা আগ্রহ নিয়েই জেঠুকে, তার দাঁতের এক কোণা দিয়ে কামড়ে ধরে থাকা নিম ডালের উঠানামা, আর তার আধবুড়ো মুখের চামড়া আর মাংসপেশিগুলোতে বইয়ের পাতার লাইনগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকা বিভিন্ন অনুভূতির তরঙ্গ, তাদের হঠাৎ হঠাৎ পাঁক খেয়ে ওঠা, আবার হঠাৎ খুব শান্তিময় নিস্তরঙ্গতায় প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়া দেখতে থাকতাম আমি। সেই সাথে খুব মন দিয়ে জেঠুর ঠোঁট থেকে বের হয়ে আসতে থাকা ধ্বনি এবং বইয়ের পাতার আঁকিবুকিগুলোকে মিলিয়ে নিতে নিতে পড়তে পারাটা বেশ একটা প্রকৃতিজাত উপায়েই শিখে গিয়েছিলাম যেন। গল্প আর গল্পের বইয়ের প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করাটাও সেখান থেকেই শুরু।
সারাদিন নানান কিসিমের দস্যিপনা তো চলতোই আমার, তবে ডাঙ্গার থেকে জলের সাথে সখ্য বেশি ছিল বলে সে দুরন্তপনা আর যারই হোক মানুষের চোখে তেমন একটা পড়তো না। খুব ভোরে উঠে গরম গরম ভাত শাকপাতা আর ঘি দিয়ে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম আমি। আশপাশের ছোট ছোট কয়েকটা গ্রাম, এই যেমন, চন্ডিপুর, গাড়ানাটা, মহিপুর, পার্বতিপুর, ঠুটিয়াপাকুড়, আর তাদের আদাড় বাদার দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। তবে কেন জানি না একা ঘোরাই বেশি পছন্দ ছিল আমার সবসময়ই। এরপর সূর্য মাথার উপরে ঠিক করে তাপ ছড়াতে শুরু করলেই আমি নেমে পড়তাম আমাদের বাড়ির পিছনের মস্ত বিলটায়। সেখানে খেলবার জিনিসের কোন অভাব ছিল না, কচুরিপানা, শাপলা-শালুক, মাছ, ব্যাঙ, জলসাপ, মাছরাঙ্গা, বিচিত্র কত কীট পতঙ্গ আর উল্লসিত জল। এদের সবারই সাথে ছিল আমার বন্ধুত্ব। নাহ, ঠিক শুধু বন্ধুত্ব না, আত্মীয়তা—আত্মার সম্পর্ক। বিলের ধারে একটা জায়গা একটু ফাঁকা মতন করে নিয়ে সেখানে আমি আমার কল্পনার একটা গ্রামও বানিয়ে নিয়েছিলাম। শাপলার ডাঁটা রোদে শুকিয়ে সেগুলো দিয়ে বানানো একগুচ্ছ কুঁড়েঘর আর আঠালো দোআঁশ মাটি দিয়ে গড়া এক সমাজ মানুষও ছিল সেখানে, আর তাদের সবার ছিল হাসিমুখ। ওদের সাথেই কখনো ভাব কখনো আড়ি করতে করতেই সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যেত, তখন বাড়ির পথে রওনা দিতে হত আমার।
দাদুর তৈরি কড়া কানুন ছিল, ঠিক সময়মত দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে হবে; আর এরপর, অন্তত এক ঘণ্টার কর্মবিরতি ও ভাতঘুম। কেউই এর আওতার বাইরে ছিল না। তাই দুপুরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে পুরো শিউলিকুঞ্জটা (বাড়ির এ নামটাও দাদুরই দেওয়া) একটা ঘুমন্তপুরীতে পরিণত হতো। বাড়ির ভিতরের ঘরগুলোতে ঘুমাবার জন্য আড়াল ছিল কিন্তু বারান্দা আর বৈঠকখানার জলচৌকিগুলোতে ঘুমিয়ে থাকা মানুষগুলোকে দেখতে বেশ বিতিকিচ্ছিরি লাগত আমার। আসলে ঘুম ব্যাপারটা আমার কাছে সবসময়ই খুব গোপন একটা কাজ হলে মনে হয়। থাক সে কথা, আমি যে সেই সময়টায় ঘুমাতাম না সেটা বলাই বাহুল্য। তবে ওই সময়টায় তো বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিল, তাই লাইব্রেরিটায় ঢুকে বইগুলোকে উল্টেপাল্টে দেখবার থেকে বেশি মজার অন্য কিছু করবার ছিল না।
শুরু শুরুতে ছবিওয়ালা বইগুলোতেই ঘোরাঘুরিটা সীমাবদ্ধ ছিল আমার। পরে আস্তে আস্তে মনে হতে শুরু হলো যে ছবি না থাকলেই বা কি! গল্প পড়েই তো ছবি ভেবে নেওয়া যায়। তাতেই বরং সুবিধা বেশি। চিত্রকরের দেওয়া আকার আর রঙই কেন মেনে নিতে হবে? ছবি আমার মনের মতো করে সাজবে, আমার পছন্দের রংএ। তারপর থেকেই শুরু হলো মজার খেলাটা। গল্প পড়ে সেগুলোতে রঙ চড়ানো আর তার আত্মিকরণ। নিজেকে একটা মস্ত ব্লটিং পেপারও মনে হতে শুরু করলো, যেন শুষে নিচ্ছি গল্পের অপার সৌন্দর্য। সব গল্প অবশ্য আমার পছন্দ হতো না। একদম শুরুতে অন্য দশটা বাচ্চার মতোই রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানো, রাজপুত্র-রাজকন্যা আর পঙ্খিরাজের গল্পই তীব্রভাবে টানতো আমায়। তবে একটু বড় হচ্ছিলাম যখন, কিছু বিশেষ গল্প জোঁকের মতো ওদের মুখের গোল গোল চাকতিগুলো দিয়ে আমার সমস্ত মনোযোগ প্রতি নাভিশ্বাসে টেনে নিতে শুরু করেছিল। এই গল্পগুলোও রূপকথার গল্পগুলুোর মতই জাদুর, তবে একটু অন্যরকম। এই যেমন, কালিদাস কি করে তার তল্লাটের সব থেকে বোকা মানুষটা হয়ে জিভে দেবীর ত্রিশূলের একটিমাত্র খোঁচা খেয়েই অনর্গল কাব্যের ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। কিংবা, যখন পুরো মহাজগত শূন্য ছিল, ছিল নিঃশব্দ তখন ধ্যানমগ্ন শিব অর্থাৎ রুদ্রের চারপাশে শক্তি নেচে বেড়াতে আরম্ভ করতেই মহাদেব কেমন করে মহাশূন্যকে প্রকম্পিত করে তিব্র ও একটানা ধ্বনি তুলতে লাগলেন। আর তার হাঁ করা মুখ থেকে একে একে বিচ্ছুরিত হল নক্ষত্ররাজি, গ্রহ, উপগ্রহ, উপত্যাকা, জলাশয় আর প্রাণীকুল।
আবার যেমন সিদ্ধার্থ গৌতমের গল্প। রাজঘরেই জন্ম, কিন্তু আরাম আর স্বস্তির জীবনটা তার খুব বেশিদিন ভাল লাগল না। তিনি দিব্যি বুঝতে পারলেন যে এই জীবন ও তার সকল অনুষঙ্গই কালের চক্রে আবদ্ধ। তাই একদিন কাউকে কিছু না বলে তিনি বের হয়ে পড়লেন মুক্তির অন্বেষণে। বড় কঠিন সাধনার সে পথ। শেষমেশ একটা খুব সরু শাখা নদী পার হতে গিয়ে তিনি যখন প্রায় মারাই যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ কি মনে হতে সমস্ত সন্ধান ভুলে খুব শান্ত হয়ে নদীটির পাশের ডুমুর গাছটার তলায় এসে বসলেন। আর পূর্ণিমা চাঁদটাও ঠিক তখনই দেখা দিলো মাঝ আকাশে। শান্ত হলো মন, এক পলকে কেটে গেল বেশ কয়েকমাস। গৌতম জেনে গেলেন যে সমস্ত সন্ধানের শুরু আর শেষ দুইই নিজের মধ্যে। তিনি হয়ে উঠলেন বুদ্ধ। আলেকজান্ডারও নাকি এসেছিলেন এই ভারতেই। এসেছিলেন চিরযৌবন আর অমরত্ব প্রাপ্তির আশায়। অনেক সাধককে জিজ্ঞেস করে করে তিনি নাকি পেয়েও গেছিলেন সে অমৃতের সন্ধান, যার কয়েক ফোঁটাই দিতে পারে অমরত্ব, মহাকাল ধরে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা। কোন এক ঘন জঙ্গলের ভিতরে দুর্গম পাহাড়ের গোপন এক গুহায় ছিল সে পানীয়। তবে সে অমৃত তিনি পান করেননি। নিশ্চয়ই করেননি। নইলে তো বেবিলনে বিষপানে তার মারা যাবার কথা নয়। যাহোক! গল্পে ছিল যে একটা কাক নাকি তাকে বলেছিল যে মৃত্যুর ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে সে বড় কষ্টের। জীবন টাকে খুব বেশি ভারী মনে হতে শুরু করলেও তার থেকে নিস্তার মিলবে না কখনো। বিশ্রাম আর কখনোই জুটবে না কপালে। আমার আজও প্রায়ই মনে হয়, ভাগ্যিস! ভাগ্যিস কাকটা কথা বলে উঠেছিল! নইলে আরো কত অগণিত শিরশ্ছেদ হত অনন্ত কাল ধরে কে জানে? আরো মনে হয় ওই প্রথম হয়ত আলেকজান্ডার একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছিলেন। আর এই জন্যই বোধ হয় “আলেকজান্ডার দি গ্রেট” পর্যন্তই লোকে বলে “ফুল” শব্দটা উহ্যই রয়ে যায়। তবে এগুলো সবই তো বইয়ের পাতায় লেখা থাকা গল্প। এমন আরও অনেক গল্পই ছিল, তবুও তাদের পরিমাণও তো নির্দিষ্ট। তাই বেশ কয়েকবার করেই পড়া হয়ে গেল সবকয়টা। কিন্তু তারপর? আরো তো রসদ চাই আমার!
এরপরের গল্পগুলো আর বইয়ের পাতায় আটকে থাকা গল্প না। সেগুলো আমি জোগাড় করতাম নানান জায়গা থেকে। কখনো পড়ন্ত বিকেলে সারি বেঁধে বসে চুপচুপে করে তেলমাখা চুলে বিনুনি করতে থাকা বিভিন্ন বয়সী নারীদের থেকে। কখনো বা সন্ধ্যারাতে হাট করে ফিরতে থাকা চাচাজান অথবা দাদুভাই গোছের মানুষদের কাছ থেকে। সেগুলো গল্পের বেশিরভাগই অবশ্য ছিল আধিভৌতিক, আর তাদের প্রায় সবগুলোই কোন না কোনভাবে আমাদের বাড়ির সীমানার শুরুতেই যে কয়েকশ’ বছরের পুরনো ছোট্ট কালীমন্দিরটা আছে আর সেটাকে চতুর্দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে আলিঙ্গন করে রাখা প্রায় একই বয়সে মস্ত গগনচুম্বী বটগাছটা আছে তাকে ঘিরে। কিন্তু ভূত আর অতৃপ্ত আত্মার গল্প আজ থাক, অন্য সময় বলবো। এই মুহূর্তে আমার বরং মনে পড়ছে যে মায়ের কাছে একদিন ভীষণ বকুনি খেয়েছিলাম নানান গল্পের আধার ও অচেনা রহস্যে ঢাকা ওই জায়গাটা ঘেঁটে দেখতে গিয়ে। মা অবশ্য বকেছিলেন বিজ্ঞানসম্মত কারণেই। আধভাঙ্গা মন্দির আর প্রাচীন বটগাছের ঘুটঘুটে অন্ধকার কোটরগুলো আসলে বাস্তুসাপদের খুব পছন্দের জায়গা। তাদের কোন একটার এক ছোবলেই আমার প্রাণটা যেতে পারত। এখানে বলে রাখা ভাল যে আমার মা ওই তল্লাটের বেশ কয়েকটা গ্রাম মিলে যে একটিমাত্র প্রাইমারি স্কুল ছিল তার সহকারী শিক্ষক। তাই কোনটি বিশেষ জ্ঞান আর কোনটি কুসংস্কার সে বোধ তার মধ্যে পাকাপোক্তভাবেই ছিল। যদিও বড় হতে হতে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে সংস্কার শুধু সংস্কার; তার কোন “কু” বা “সু” হয় না, ওগুলো আরোপিত ধারণা। বরঞ্চ কুসংস্কার নামক ওই একটি শব্দ ব্যবহার করে হাজার হাজার মানুষের শত বছরের লালিত বিশ্বাসের জগৎটাকে বানচাল করে দেওয়া মানে জীবন থেকে জাদু আর তার সম্ভাবনাগুলোকে হটিয়ে দেওয়া। আর জাদু না থাকলে গল্পের মজাই বা থাকল কোথায়? ওই দিনের পর থেকে অবশ্য মাকে দেওয়া কথাটা আধাআধি রেখে বটেশ্বর আর তার প্রেমিকা কালী ঠাকুরের ঘরটাকে একটু দূর থেকেই দেখতাম আমি। তবে সত্যি বলছি, ওই জায়গাটা অন্য যেকোনো জায়গার থেকে বেশ আলাদা ছিল। ও জায়গার বাতাসে অদ্ভুত সব ঘূর্ণি থাকতো প্রায় সবসময়ই। পড়ন্ত বটের পাতাগুলোকে খেয়াল করতে থাকলে সেটা খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যেত। আমার মূল কাজ অবশ্য ছিল গল্প শুনবার আশায় সেখানকার বাতাসে কান পেতে থাকা। আর শুনতেও পেতাম। হিন্দু পুরাণের বইগুলো থেকে পড়া দেব-দেবীর গল্পগুলো যেন ফিশফিশিয়ে গুঞ্জন তুলত সেই বাতাসে, সেগুলো আমার শিরায় শিরায় বইতে থাকা রক্তপ্রবাহে ধ্বনি তুলত ।
তবে এগুলো সবই দিনের বেলার কথা। আমার কিন্তু বরাবরই বেশি ভালো লাগত রাত। দাদি বলতেন আমার জন্ম শুক্লপক্ষের রাতের তৃতীয় প্রহরে। সেইরাতে নাকি নতুন রূপার থালার মতো ঝকঝকে চাঁদ উঠেছিল মাঝ আকাশে। আর বাবা নাকি আমাকে প্রথম কোলে নিয়ে উপস্থিত সবাইকে রীতিমত হকচকিয়ে দিয়ে কুরআন আর গীতা দুটো থেকেই আমার কানে পাঠ করেছিলেন। বাবা একটু অমনি। “ট্রানসগ্রেশন” শব্দটা বাবা শিখিয়েছিলেন কিনা ঠিক মনে নেই, তবে অনেক ইংরেজি শব্দই বাবার কাছ থেকে শেখা আমার। বাবা বিবিসি শুনতে খুব ভালোবাসেন। সেসময়ও ছুটিতে বাড়ি আসলেই সন্ধ্যা ঠিক সাতটা পঁচিশে আমায় নিয়ে হাঁটতে বের হতেন বাবা। তার এক হাতে থাকত লেদারে মোড়ান মাঝারি সাইজের একটা রেডিও যার পেটে পোড়া ছিল হকের দুটো বড় সাইজের লাল-সাদা ব্যাটারি, আর অন্য হাতে থাকতো চারটা পেন্সিল ব্যাটারি চালিত একটা সরু ও লম্বামতন টর্চলাইট। বলাই বাহুল্য যে আমাদের গ্রামে ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না তখন। এখন যদিও পল্লিবিদ্যুত আছে কিন্তু তা মাঝে মাঝে আসে। তবে বাড়ির সামনের রাস্তাটা শত তদবির সত্বেও পাকা হয়নি এখনো। এখন যেমন আছে তখনও অনেকটা এমনই ছিল, একটু এবড়ো থেবড়ো। তো বাড়ির ভিতরে রেডিও সিগন্যাল ঠিক করে পাওয়া যেতনা বলে বাবা যখন আধো অন্ধকারে বাড়ির বাইরেরে মাটির রাস্তাটি ধরে রেডিওতে বিবিসি বাজিয়ে হাঁটছেন আর ব্রিটিশদের ইংরেজি শুনে আহা উঁহু করছেন, তখন আমি ভাবছি অন্য কথা। রেডিওটির দেড় থেকে দুই মিটার এর রেঞ্জটুকুর বাইরে পুরো গ্রামটাই কিন্তু তখন মৃদু মৃদু কাঁপছে অন্য একটা শব্দ তরঙ্গে। সেটার ভাষাটাও আমার অজানা, আর অস্বীকার করবো না খটমটে ইংরেজির থেকে সেটা অনেক বেশি সুরের, লয়ের আর ছন্দের। মোজার্ট বা বিটোভেন এর কম্পোজিশন তখনও শোনা হয়নি আমার। তাই তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কিন্তু সুর আর ধ্বনি সম্পর্কে যেটুকুই বুঝতাম সে সময়ে তাতে হলফ করে এইটুকু বলতে পারি ওই সময় গুলোতে গ্রামের রাতগুলো জাদুকরী উঠবার খুব বড় একটা কারণ ছিল ঝিঁঝিঁ, জোনাকি ও আরও অজস্র নাম না জানা পোকাদের তৈরি করা অসাধারণ এক অর্কেস্ট্রাতে। সঙ্গীত মানে যদি হয় শব্দ আর নৈঃশব্দের সমন্বয়, তবে এতটুকু বলা যায় যে এই দুইয়ের সংমিশ্রন এদের থেকে ভালো আর কেউ জানে না। যেহেতু বেশিরভাগ সময়ই ভোর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতাম, তাই আমি জানতাম যে ঠিক দুইটা পনেরোতে এই শিল্পীদের মধ্যে একটা পালাবদল ঘটে। সুর, ধ্বনি, গীত ও ছন্দ চারটাই বদলে যায় হঠাৎ করে। আর তখন অন্যরকম একটা মূর্ছনা শুরু হয়। এসব পোকাদের সময়জ্ঞানও অসামান্য। মনুষ্য প্রজাতিকে খুব ছোটবেলা থেকেই সময়ানুবর্তিতার রচনা চিবিয়ে, গিলিয়ে আর পরীক্ষার খাতায় অসংখ্যবার বমন করিয়েও সময় সম্পর্কে এতটা সচেতনতা তাদের মধ্যে তৈরি হতে খুব একটা দেখা যায় না।
তবে এইসব দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে যখন বড় হচ্ছি তখন বুঝছি যে গ্রামীণ জীবনের এত সব সৌন্দর্যের মাঝে অনেক অসুন্দরও আছেু, সুরের মাঝে অনেক অসুরও আছে। তবে আমার কৈশরের দিনগুলোতে সবথেকে ভয়ঙ্কর যে দানব টাকে খুব কাছ থেকে দেখছিলাম সেটা ছিল ক্ষুধা, সত্যিকারের ক্ষুধা। দেড় বা দুই দিনের বেশি সময় ধরে আঙিনার একটিমাত্র মাটির উনুনের শীতল পড়ে থাকবার ক্ষুধা। দেখছিলাম অভুক্ত মায়ের আধভেজা ঘোলা চোখে বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি পানিতে একমুঠো আটা গুলিয়ে পেটপুরে খাইয়ে দেওয়ার ক্ষুধা। যে বাড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে তার রসুইঘরের সামনে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থেকে ভাতের মাড়টুকু চেয়ে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে দেওয়ার ক্ষুধা। আবার, কিছু খাবার পাওয়া যেতে পারে এই আশায় কোন এক অভুক্ত তরুণের, স্বচ্ছল গৃহস্থ ঘরের বখে যাওয়া যুবক ছেলেটির কিছু খামখেয়ালী শখ পূরণের জন্য জীবন বাজি রেখে খাপছাড়া সব খেলা দেখাতে রাজি হয়ে যাবার ক্ষুধা। এই যেমন একজন সজোরে একটা দা ছুঁড়ে দেবে ঠিক তার বুক বরাবর আর সে খপ করে তা ধরে ফেলবে সেটা বুকে গেঁথে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে।
ক্ষুধা নামক এই রাক্ষসটির তাণ্ডব আরো কতোই তো দেখেছি, তার অনেক খুঁটিনাটি হয়তো ভুলেও গেছি এখন। এখানে এটা বলে নেওয়া জরুরি যে আমি যে সময়টার কথা বলছি সে সময় পর্যন্ত আমাদের গ্রামের ওইদিকটাতে ফিলিপাইনের ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে আসা উন্নত জাতের ধানের বীজ মানে ইরি ঠিক করে পৌঁছায়নি। দেশি ধানের জাতগুলো, যেমন আমন যা হেমন্তে আর আউশ যা গ্রীষ্মে ফলত, সেগুলো খুব ভালো ফলনেও বিঘা প্রতি পাঁচ থেকে ছয় মণের বেশি ঘরে উঠত না। তার উপরে আউশ এর ফলন প্রায় প্রতি মৌসুমেই অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হতো। পার্থক্যটা বুঝবার জন্য এটুকু বলছি যে ইরি বিঘাপ্রতি কমপক্ষে ত্রিশ মণ ফলে, আর ইরি পুরোপুরি সেচ নির্ভর। তাই বৃষ্টি না হলেও কোনো কৃষকের আত্মহত্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আমি এমন বেশ কয়েকটা ঘটনাই দেখেছিলাম আমার ছোটবেলায়। দারিদ্র্য, অভাব আর ক্ষুধার কাছে হার মানতে অনেক মানুষকেই দেখেছি আমি। আবার এর উল্টোটাও দেখেছি, কারো কারো খুব অদ্ভুত ভাবে জিতে যাওয়াও। একটা বুড়ির গল্প আমার মনে খুব করে গেঁথে আছে। বুড়িটা দেখতে অবিকল ঠাকুমার ঝুলির ডাইনি বুড়ির মতোই ছিল; কুঁজো পিঠ, হেলে পড়া কোমর, এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে কাপড়ের তৈরি মস্ত ঝুলি। তার মাথার সব চুল ছিল পাকা, তোবড়ানো গাল আর দাঁত বিহীন বোয়াল-মুখে আঁশটে গন্ধ। থাকতও সে একা, গ্রামের এক কোনায় ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরে। গল্পের ডাইনির মত ছোট ছেলে মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে চিবিয়ে খেতে পারলে তার আর তেমন কোন সমস্যা থাকত না, গ্রামে তো আর বাচ্চার অভাব ছিল না। কিন্তু তার যা দরকার ছিল তা হলো খাবার, আর ভিক্ষে করে সেটা জোটানো বেশ কঠিনই ছিল তার জন্য। অনেক দূরের পথ সে হাঁটতে পারত না। কাছাকাছি যে কয়েক ঘর মানুষ ছিল তারাও যে খুব স্বচ্ছল ছিল তেমনটা নয়। তাই তারাও প্রতিদিন ভিক্ষে দিতে চাইতো না। আর দেবেই বা কতজনকে?এমন ডাইনি তো আর গ্রামে একজনই না। গরীব এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে দীর্ঘায়ু পেয়ে গেছে এমন সব নারীই কর্মক্ষম জীবনটা পার করবার পর ডাইনি হয়ে যায়। যা হোক, আমার এই বিশেষ ডাইনি বুড়িটি অনেক যুদ্ধের শেষে হঠাৎ একদিন সিদ্ধান্ত নিল যে আজ সে এই মহাদানব রাক্ষসটাকে বধ করেই তবে ক্ষান্ত হবে। জাদুবলে দৈত্য তার থেকে এগিয়ে থাকবে সেটা সে আর কিছুতেই মানতে পারছিল না। তাই সেদিন বিকেল বেলা সে চেয়েচিন্তে আনা পুঁটি মাছের শুঁটকিটুকু সে হালকা আঁচে টেলে নিল। সেটাকে ধুতুরা আর লেবুপাতার সাথে ভালো করে পাটায় বেটে তাতে একটু বেশি করে শুকনো মরিচ, এক কোয়া রসুন ও পেঁয়াজ কুচি দিল। ভর্তাটা তৈরি হয়ে যেতেই সে সারাদিনের ভিক্ষে থেকে জোগাড় করা চাল টুকু দিয়ে জাউ ভাত বানালো আর ভর্তাটা দিয়ে খুব করে মেখে তৃপ্তি করে খেয়ে পরম আনন্দে চোখ বুজলো। বুড়ি মারা যাবার পর তার ছেলে মেয়েরা কেঁদেছিল নাকি খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে বুড়ো মায়ের দায়িত্ব নেয়নি বলে গ্রামের লোকজন তাদের আর গঞ্জনা দেবে না সে কথা এখন আর আমার মনে নেই। তবে এইটুকু জানি যে এদেরও অনেকেই ওই একই নিয়তির দিকে ধাবিত হয়েছিল ক্রমে।
তবে এত সব মন খারাপ করা গল্পের মধ্যে থেকেও যখন দেখতাম যে গ্রামের এই ভালোমন্দে মিশেল মানুষগুলোর মনের গভীরে দাম্ভিক বট গাছের মতোই শেকড় পুঁতে থাকে আশা, বিশ্বাস আর প্রতীক্ষা, সেটা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপারই বৈকি। কঠোর বাস্তবতার শ্বাসরোধ করা গণ্ডিটা যে জাদুর ডানায় ভর না করলে পার হওয়া যায় না সেটা এই মানুষগুলোর কাছেই শেখা আমার। একজন সাধুর গল্প দিয়েই এই পত্রটা শেষ করি আজ। বেশ অনেক বছর আগে আমাদের গ্রামে অথবা তার আশপাশের কোন এক গ্রামে একজন সাধু বাস করতেন। সে নাচলেই বৃষ্টি হতো। কৃষিপ্রধান সমাজ, বৃষ্টি মানে প্রাণ, তাই লোকে তাকে ভক্তিও করতো অনেক। একবার হলো কি, শহর থেকে কয়েকজন শিক্ষিত ও প্রগতিশিল তরুণ এসে উপস্থিত হলো সেই গ্রামে। স্বভাবতই, বিশেষ কোন ক্ষমতা, জাদু বা অলৌকিকতায় তাদের কোন আস্থা ছিল না। এসেই তারা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলো সাধুকে। তাদের যুক্তিটা ছিল এই যে নাচের সাথে বৃষ্টির কোন যোগ নেই, আর যদি থাকেই তাহলে যে কেউ নাচলেই বৃষ্টি হবে। তারা দাবি করে বসলো যে তারাও পারবে নেচে আকাশে মেঘ জড়ো করতে আর বৃষ্টি নামাতে। তারা সংখ্যায় ছিল চারজন। তো নাচ শুরু হলো। প্রথমজন কিছু সময় নেচেই ক্ষান্ত দিল। দ্বিতীয়জন একটু জেদী প্রকৃতির, সে ঘণ্টা দুয়েক নৃত্যকর্মটি চালিয়ে নিতে পারলো ঠিকই কিন্তু তাতে তেমন কোন লাভ হলো না। সূয্যিমামা মধ্যগগনে দিব্যি হাসছেন তখনও। অগত্যা নৃত্যে ছেদ ঘটিয়ে বসে পড়ল সেও। একে একে তৃতীয় আর চতুর্থ জন্ও চেষ্টা করে দেখলো। পালাক্রমে চারজনই তিন দিন ধরে চেষ্টা করে চলল কিন্তু বৃষ্টির নাম গন্ধও নেই ত্রিসীমানায়। শেষমেশ নিজেদের ব্যর্থতা মেনে নিল তারা। এবার তবে সাধুর পালা। তাকে তো প্রমাণ করতে হবে যে এই জাদুটা সেই শুধু জানে। পরদিন সকালে তাই সাধু নাচতে শুরু করলেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এলো, সাধু তবু নেচেই চলেছেন। নাচতে নাচতে রাতটাও পেরিয়ে গেল। ভোরের আলো ফুটলো, সকাল হলো, তখন আকাশের কোনায় হালকা মেঘ জমেছে। সাধু নেচেই চলেছেন। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আর উপস্থিত সবাইকে বিস্ময়ে পাথরের মূর্তিতে পরিণত করে দিয়ে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। প্রাথমিক ধাক্কাটা কোনমতে সামলে নিয়ে সেই তরুণদের একজন যখন সাধুকে জিজ্ঞেস করল যে সে কি করে ঘটালো এমন, ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি ফুটিয়ে সাধু বললেন, “আমি বিশ্বাস করি যে আমি নাচলেই বৃষ্টি হয়, আর আমি ততক্ষণ পর্যন্তই নাচি যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি শুরু না হয়”।
Mazhar Ziban
সম্পাদক, লেখালেখির উঠান । কলেজ জীবন থেকে রূপান্তরবাদী রাজনীতির সাথে জড়িত। সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। একটি বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলেন। অনূদিত কবিতার বই আমিরি বারাকা'র কেউ আমেরিকা উড়িয়ে দিয়েছে। হাওয়ার্ড জিনের নাটক এমা, সম্পাদক: মাঠের পারের দূরের দেশ: দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছোটগল্প সংকলন, সহলেখক: • বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়: বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা বরেন্দ্রী আদিবাসীদের চালচিত্র Colonialism Casteism and Development: South South Cooperation as a 'New' Development paradigm