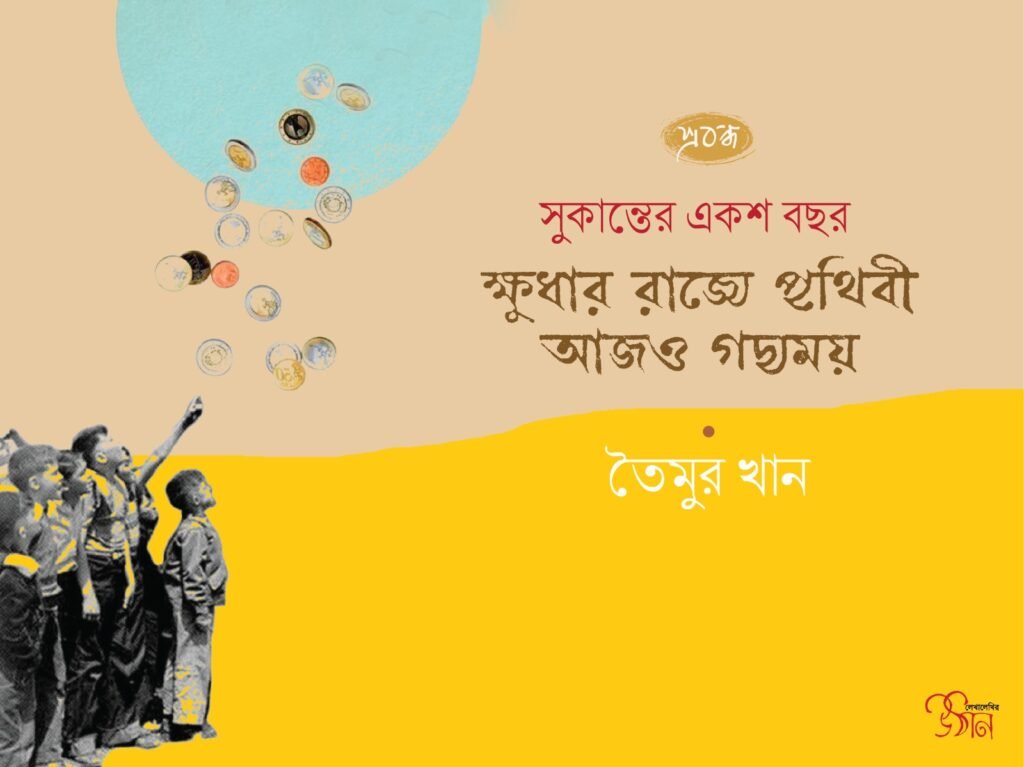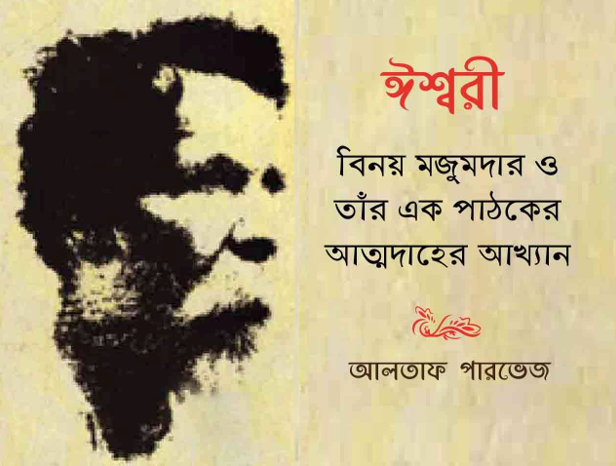“আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ” সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৫ আগস্ট ১৯২৬–১৩মে ১৯৪৭) একশো বছর বয়সের হলেও তিনি আজও ‘অঙ্কুরিত বীজ’ হয়েই বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর বাগিচায় রয়ে গেছেন। বট-বৃক্ষের সমাজে কখনোই তিনি তুচ্ছ নন, ক্ষুদ্র শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি উপলব্ধি করেই স্বপ্ন লালন করে চলেছেন। বিশাল অরণ্যের চেতনা আর বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে ভাবী বনস্পতি হয়ে উঠবেন। সেদিন কঠিন কুঠার হানলেও তিনি বারবার হাতছানি দেবেন। তিনি আমাদেরই আপনজন একই মাটিতে পুষ্ট সে কথা বোঝাবেন। তাই ফুল-ফল-পাখির কূজন দিতেই থাকবেন।
যে আবেগ নিয়ে একটি বাঙালি শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং যে স্বপ্ন তার চোখে ধরা পড়ে সেই আবেগ ও স্বপ্নের মুকুলিত ভাষাকেই সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন। সত্য, ন্যায় ও ভালোবাসার পথেই নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং সাম্য-স্বাধীন ও মানবতাবাদী সমাজ গঠনের এবং শোষক-অত্যাচারী ধনী-বণিকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবার মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমেই তিনি প্রত্যেকের মনেই ‘অঙ্কুরিত বীজ’ হয়ে উঠেছেন। একটি কিশোর মনে তাঁর সেই কবিতার মন্ত্র যতটা আলোড়িত করতে পারে, যতটা আপন করে নিতে পারে তা অন্য কারো লেখায় সেই সম্ভাবনা নাও থাকতে পারে। কারণ সুকান্ত ভট্টাচার্য চিরজীবন্ত প্রাণ, একটি সময়ের, একটি জাতির, একটি মানবীয় মুহূর্তের উপলব্ধিময় তাঁর চেতনার স্রোত একসময় সকলকেই প্লাবিত করেছিল। পরাধীন দেশ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশ, মন্বন্তরের সীমাহীন ছোবল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সব মিলিয়েই যে সংকট সৃষ্টি করেছিল— সেখানে খালি পেট, বাঁচার অনিশ্চয়তা, বিপন্ন অস্তিত্ব এবং অস্থিরতাই স্বাভাবিক। সময়কে বাদ দিয়ে, জীবনকে বাদ দিয়ে, এই পরাধীনতার গ্লানিকে বাদ দিয়ে সুকান্ত কী-ই বা লিখতে পারতেন? সেই সময় আকাশে চাঁদও ছিল, নক্ষত্রও ছিল, গাছে গাছে পাখিও, ফুলও ছিল, কিশোরীর লাবণ্যও ছিল— কিন্তু কিশোর সুকান্তের কাছে সেইসব রোমান্টিকতার ভাবনা কখনোই তাঁকে আক্রান্ত করেনি। পীড়িত নির্যাতিত শোষিত মানবাত্মার ক্রন্দন তিনি শুনেছিলেন। ব্যক্তিজীবনের ক্ষুধার্ত রূপেও সমষ্টিজীবনের পরিচয় দিয়েছিলেন। নাগরিক জীবনের বিষণ্ণতা, একাকিত্ব, ব্যর্থতা, ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি সজীব প্রাণের মতোই নিজেকে সজীব উদ্দাম রাখতে চেয়েছিলেন। দেশের ও জাতির সংকটকে এবং সমূহ মানবাত্মার ক্রন্দনকে আত্মস্থ করেই সাহিত্যের সচেতন প্রয়াসী কাব্যরচনার প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিলেন। তাই যা লিখেছিলেন সচেতন মনেই সরাসরি স্পষ্ট ভাষায়। তা কখনো প্রতিবাদ হয়েছিল, কখনো বিদ্রোহ, কখনো সত্য ও সতর্ক বার্তার মতো— তাতে কোনো ছলনা ছিল না।
শতবর্ষ পূর্ণ করেও তিনি কতখানি প্রাসঙ্গিক আমাদের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে, সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিশ্লেষণ করা জরুরি বলে মনে করি। প্রত্যেক জাতিরই একটি কিশোর অবস্থা থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তিরও এই অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। যখন স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালি যুবকেরা আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে চলেছেন, তখন তাঁদের মনন চিন্তন কার্যকারণের প্রকীর্ণ প্রেক্ষাপটেই সুকান্তের কাব্য ভাবনার উচ্ছল তরঙ্গ বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। একটি দিশেহারা জাতিকে পথ দেখাবার প্রয়াস পেয়েছিল। স্বাধীনতার সহাবস্থানের এবং নিজেদের ঐতিহ্য ইতিহাসকে জাগ্রত করবার ও মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠার জন্যই সুকান্তের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রত্যেকটি কিশোর যখন দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ পায়, যখন তাঁর ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে শেখে, সাহিত্যও তাঁর কাছে অনুসন্ধিৎসু বিষয় হয়ে ওঠে—তখনই বাঙালিত্বের গৌরব তাঁকে আত্মজাগরণের পথ দেখায় এবং জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বহু ছাত্র-ছাত্রী আজও সুকান্তকে স্মরণ করেই তাদের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনগুলিতে কবিতা লেখেন। বেশিরভাগ সেইসব কবিতার বয়ান প্রায় একই :
“বাংলার কবি সুকান্ত
তুমি হওনিকো খান্ত।
নবীন-যুবার প্রাণের মাঝে
তুমি আজও আছো বেঁচে।”
হ্যাঁ, বেঁচে আছেন। আজও সেইসব নবীন-যুবারা পূর্ণিমা চাঁদকে ‘ঝলসানো রুটি’ বলেই মনে করে। আজও তারা জানতে পারে ‘বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায়’। আজও তারা অনুভব করতে পারে ‘সবচেয়ে খেতে ভালো গরীবের রক্ত’। তাই তার দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায় মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত হয়। যতক্ষণ না এ পৃথিবী এ শিশুর বাসযোগ্য হয় ততক্ষণ তার এই সংগ্রাম থেমে যায় না। সেই সংগ্রামেরই জন্ম দিয়ে গেছেন আমাদের বিবেক ও চেতনায়, আমাদের বেঁচে থাকা ও বাঁচার ইতিহাসে, আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নের আয়োজনে।
মাত্র একুশটি বসন্তও তাঁর জীবনে পূর্ণ হয়নি। ক্ষণজন্মা কবি বালক সূর্যের মতোই তাঁর উদয় ও অস্ত যাবার মাঝখানে বেশি সময় ছিল না। বিশ্বের ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর কবিদের সারিতেই তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই জন কিটসকে মাত্র ২৫ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মারা যেতে। টমাস চ্যাটারটনকে মাত্র ১৭ বছর বয়সে আর্সেনিক রোগে নিহত হতে। রেমন্ড রেডিগুয়েটকে ২০ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে চলে যেতে।
আলাইন-ফোর্নিয়ারকে ২৭ বছর বয়সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হতে। সিলভিয়া প্লাথকে ৩০ বছর বয়সে আত্মহত্যা করতে। এমিলি ব্রন্টেও ৩০ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে বিদায় নেন । পার্সি বিশি শেলিও ২৯ বছর বয়সে নৌকাডুবিতে চলে যান। আর্থার রিমবাউ ৩৭ বছর বয়সে ক্যান্সারে মারা গেছেন। স্টিফেন ক্রেন ২৮-২৯ বছর বয়সে যক্ষ্মায় মারা গেছেন। ব্রিটিশ ফরাসি আমেরিকান প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিক-কবিরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যও তাঁর সৃষ্টিতেই পরমায়ু রচনা করেছেন, বেঁচে থাকার আয়ুতে নয়। সুতরাং ১০০ বছর তাঁকে জরাগ্রস্ত করেনি। বাঙালি, বাংলা ভাষা, বাঙালির ইতিহাস, দেশপ্রেম, আত্মচেতনা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজ ও মানবিকতা পৃথিবীতে যতদিন থাকবে—সুকান্তও ততদিন উচ্চারিত হবেন; ততদিন তিনি বাঙালির কাছে সমাদৃত এবং নন্দিত হতে থাকবেন। বাঙালি তাঁকে স্মরণ করেই নতুন বিশ্বের দিকে ধাবিত হবে এবং সেটাই তার ‘ছাড়পত্র’:
“যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম:
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে।”
মানবশিশুর আবহমান জন্ম এবং আবহমান অধিকার ব্যক্ত করার প্রবল প্রবাহ পৃথিবীতে আন্দোলিত হবেই এবং শেষপর্যন্ত মানবিক পৃথিবী সংঘটিত হলে নতুন ইতিহাস রচিত হবে। রক্তপাত নয়, যুদ্ধ নয়, হিংসা নয়, ধ্বংস নয়, নতুন শিশুর চায় বাঁচার অধিকার। আনন্দের, স্বপ্নের জাগরণ তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এই বার্তা থেকেই সুকান্তের কাব্য পরিক্রমা আজও উচ্ছ্বসিত হয়ে চলেছে।
স্বল্প সময়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীল ও মার্কসবাদী চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর কবিতাগুলোতে মূলত সমাজের দরিদ্র ও শোষিত নির্যাতিত মানুষের জীবন এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর মৃত্যুর পরেই কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়। কাব্যগুলি হল: ছাড়পত্র (১৯৪৮), পূর্বাভাস (১৯৫০), মিঠেকাড়া(১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩), ঘুম নেই (১৯৫৪), হরতাল (১৯৬২) এবং গীতিগুচ্ছ (১৯৬৫)
সুকান্ত ভট্টাচার্য কলকাতার কালীঘাটের ৪৩, মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে পৈতৃক বাড়ি ছিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার ঊনশিয়া গ্রামে। পিতা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও মাতা সুনীতি দেবী। ছাত্রজীবন থেকেই সুকান্তের রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা ছিল গভীর। বলেই ছাত্রজীবন থেকেই বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন।
সুকান্ত নিজেই বলেছেন “আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি”, তিল তিল করে মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখেছেন। একদিকে খিদের যন্ত্রণা, অন্যদিকে সামাজিক পীড়ন শোষকও শোষিত মানুষের সংঘাত। বিনিদ্ররাতে যুদ্ধের সতর্ক সাইরেন বেজে চলেছে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের “শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস” এ কথাকে তিনিও সমর্থন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে উপলব্ধি করেই তিনি যে শক্তি সঞ্চয় করেছেন তা শুধু কাব্যশক্তি নয়, জীবনীশক্তিও। দানবের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি। নিজেকে সৈনিক বলে মনে হয়েছে। হ্যাঁ, তিনি অক্ষর-সৈনিক। সৈনিক হয়েই দৈনিক ইতিহাস লিখে চলেন। ইতিহাস হয়তো তাঁদের মনে রাখবে না। ‘ছাড়পত্র’ কাব্যের ‘প্রস্তুত’ কবিতায় লিখেছেন :
“অস্ত্র ধরেছি এখন সম্মুখে শত্রু চাই,
মহামারণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সম্ভাষণ
তাদের প্রভাবে রাখিনি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করায়।”
প্রাণের বৃথা ক্রন্দন সহ্য করেও বিপ্লবী মনের উদ্বোধন করেছেন। নিরন্ন মনেই রক্তিম পথ অনুধাবন করে আনতে চেয়েছেন আগামীর ভোর। হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত প্রতীক্ষায় থেকেছেন। সূর্যের কাছেই উত্তাপ প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু কলম কি সব লিখতে পেরেছে? অনেক ইতিহাস অলিখিত থেকে গেছে। কলম হয়েছে ক্রীতদাস। প্রত্যেকটা লেখাই বেরিয়ে এসেছে তার দীর্ঘশ্বাস। কখনো কবিকে মনে হয়েছে আগ্নেয় পাহাড়। শান্তির ছায়াসুনিবিড় গুহায় নিদ্রিত সিংহের মতো।
দুর্ভিক্ষের স্রোত দেখেও সমুদ্র পর্বতে অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন। হতাশা নৈরাশ্য অবসাদকে কখনো জায়গা ছেড়ে দেননি। কবিতাকে করতে চেয়েছেন আগুনের ভাষা, আত্মপ্রত্যয়ের ভাষা, মৃত্যুঞ্জয়ী গান। দরিদ্র শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষদেরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সকলেই সভ্যতার সৈনিক। সকলের ঐক্যবদ্ধতাতেই বিপুল শক্তি জাগরিত হবে। নতুন শস্যই আবার দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি ঘটাতে পারবে। তাই ‘কৃষকের গানে’ও কবি লিখেছেন:
“আমার প্রতিজ্ঞা গ’ড়ে তোলে
ক্ষুধিত সহস্র হাতছানি।
দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ।”
বিপ্লবের ডাক দিতে দিতে কবি ইতিহাসের দিকেও মুখ ফিরিয়েছেন দেখেছেন জুলাই বিপ্লবের চেতনা মানুষের মনে কিভাবে উত্তাল সামর্থ্য এনে দিয়েছিল। তাই জুলাই বিপ্লবকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ মহামারী শোষণ অত্যাচার যতই বৃদ্ধি পেয়েছে কবি দেখেছেন :
“রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত।”
এই বিদ্রোহের খবর চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়েছে যে, বিদ্যুৎ বাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ‘ঘুম নেই’ কাব্যের ‘বিদ্রোহের গান’ কবিতায় লিখেছেন :
“বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক।
উঠুক তুফান মাটিতে পাহাড়ে
জ্বলুক আগুন গরিবের হাড়ে
কোটি করাঘাত পৌঁছাক দ্বারে
ভীরুরা থাক।”
সব বাধা অতিক্রম করে এই যুদ্ধ ঘোষণা। কেউ তার গতি রোধ করতে পারবে না। যশ-খ্যাতির জন্য লড়াই নয়, অধিকার আদায়ের লড়াই। গোলামি থেকে মুক্তির লড়াই। নিজের স্বর্গ দখলের লড়াই। সুকান্ত আত্মশক্তির যে জাগরণ টের পেয়েছিলেন তাতে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তাই লক্ষ করেছিলেন:
“আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহের পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়,
জানি না কেউ।”
এই ছিল ‘কবিতার খসড়া’। প্রহরীর যেমন ঘুম থাকে না, তেমনি কবিরও ‘ঘুম নেই’। ‘প্রিয়তমাসু’-তে লিখলেন :
“সীমান্তে আজ আমি প্রহরী।
অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক’রে
আজ এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি—
স্বদেশের সীমানায়।”
তখন পুরোপুরিভাবেই কবি সৈনিক। তিনি বহু পরাধীন দেশের নাগরিকও অর্থাৎ বিশ্বনাগরিক। তাই তিউনিসিয়া থেকে ইতালি, তারপর বিপ্লবী ফ্রান্স এবং প্রতিবেশী বার্মাতেও তিনি ছিলেন। স্বদেশকে ভালোবাসতে পারা মানে অন্যদেশও কবির কাছে শত্রু নয়, সেটাও স্বদেশ যখন তিনি সেই দেশের সৈনিক। তাই সমস্ত দেশপ্রেমিক সৈনিক হয়েই তিনি সৈনিকের বেশ ধারণ করেছেন:
“আজ দেহে আমার সৈনিকের কড়া পোশাক,
হাতে এখনো দুর্জয় রাইফেল,
রক্তে রক্তে তরঙ্গিত জয়ের আর শক্তির দুর্বহ দম্ভ,
আজ এখন সীমান্তের প্রহরী আমি।”
নিজেকে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত করে তোলা, দেশকে এবং মানুষকে ভালোবাসা, স্বাধীনতাকে রক্ষা করা একজন প্রকৃত সৈনিকেরই কাজ। এই সৈনিক হয়েই তিনি নীলআকাশের নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। স্বদেশের হাওয়ায় অনুরোধ এসেছে। চোখের সামনে খুলে ধরেছে শস্য-শ্যামলা সবুজ চিঠি। কিছুতেই তিনি এড়াতে পারেন না। জীবনের এই প্রত্যয়, এই অবিনাশী ভালোবাসা কবিকে চূড়ান্তভাবেই মহাকালের মহাসৈনিকের সামর্থ্য যুগিয়েছে—বলেই তিনি এই কবিতায় আরো উচ্চারণ করেছিলেন :
“পরের জন্য যুদ্ধ করেছি অনেক,
এবার যুদ্ধ তোমার আর আমার জন্যে।
প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ করে পেলাম কী? উত্তর তার—
তিউনিসিয়ায় পেয়েছি জয়
ইতালিতে জনগণের বন্ধুত্ব,
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র ;
আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম ঘরে ফেরার তাগাদা।”
দেশ-রক্ষা, জাতি-রক্ষা, মানবিকতা-রক্ষা এবং দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও পরাধীনতা থেকে রক্ষা কবির কাছে জরুরি হয়ে পড়েছিল। মহামারী বন্যা দারিদ্র বারবার বিপন্ন করেছে দেশকে। অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চেয়েছে। তাই একের পর এক যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটতে হয়েছে সৈনিক হয়েই। সেইসবই নিজের ঘরের দুঃসহ অন্ধকার। তাই আলো জ্বালাতে হবে সেই ‘বাতিওয়ালা’ হয়ে তিনি তাঁর আকুলতা ব্যক্ত করেছেন। শপথ নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় যুদ্ধের কবি সিডনি কিজ(২৭মে ১৯২২-২৯এপ্রিল ১৯৪৩)-এর কথা। তিনি কবি সুকান্তর সমবয়সী এবং কিশোর কবি বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই তিনি একজন সৈনিক ছিলেন এবং কবিও ছিলেন। তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাবনাও সমবিন্দুতে মিলে যায়।
১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ২০ বছর বয়সেই ‘দ্য আয়রন লরেল’ প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সৈনিক হিসেবে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে তিউনিসিয়ান অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়ে লড়াই করার জন্য তাঁর রেজিমেন্টের ১ম ব্যাটালিয়নে, যা ৪র্থ ডিভিশনের অংশ, দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি কবিতা লিখেছেন। ‘War Poet’ নামে একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :
“I am the man who looked for peace and found
My own eyes barbed.
I am the man who groped for words and found
An arrow in my hand.
I am the builder whose firm walls surround
A slipping land.
When I grow sick or mad
Mock me not nor chain me;
When I reach for the wind
Cast me not down
Though my face is a burnt book
And a wasted town.”
অর্থাৎ
আমিই সেই মানুষ যে শান্তি খুঁজেছি এবং পেয়েছি
আমার নিজের চোখ কাঁটায় ভরা।
আমিই সেই মানুষ যে শব্দ খুঁজেছি এবং আমার হাতে একটি তির পেয়েছি।
আমিই সেই নির্মাতা যার দৃঢ় দেয়াল
একটি পিছলে যাওয়া জমিকে ঘিরে রেখেছে। যখন আমি অসুস্থ বা পাগল হয়ে যাই
তখন আমাকে উপহাস করো না
বা আমাকে শিকল দিও না;
যখন আমি বাতাসের জন্য হাত বাড়াই
তখন আমাকে ছুঁড়ে ফেলো না
যদিও আমার মুখ একটি পোড়া বই
এবং একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর।
একদিকে সৈনিকের দায়িত্ব, অন্যদিকে দেশপ্রেম, সর্বব্যাপী মানবতাবাদী চেতনা, প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে নিবিড় করে রাখা সবই তাঁর যুদ্ধের আয়োজনের মধ্যেই পড়ে। কিশোর কবির এই ভাবনার মধ্যেই ফুটে ওঠে আকুতি ও বিনয়। শান্তি ও সহাবস্থানের খোঁজ। কিন্তু যুদ্ধ তো এড়ানো যায় না, এড়ানো যায় না তার ধ্বংসের ভয়াবহতাকেও। শতশত দুঃখ কান্না চেপে রেখেও তবু যুদ্ধ করে যেতে হয়। সেই কবি-সৈনিকের কাছে শব্দ যেমন সুতীক্ষ্ণ বোধের অনুবর্তী, তেমনি তা মেধাবী অস্ত্রও। তাই হাতে উঠে এসেছে তির। এই তিরই কলম। নিজের মুখকেই পোড়া বই বলে মনে হয়েছে। আর নিজের দেশকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর। কবি যখন সৈনিক অন্তরের তাগিদেই হয়ে ওঠেন, তখন সব উপলব্ধি এরকমই হয়। ‘পূর্বাভাস’ কাব্যের ‘হদিস’ কবিতায় তাই সুকান্ত লিখলেন:
“আমি সৈনিক, হাঁটি যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রভাতী আলোয় অনেক ক্লান্ত দিনের পরে,
অজ্ঞাত এক প্রাণের ঝড়ে।
বহু শতাব্দী ধরে লাঞ্ছিত পাইনি ছাড়া
বহু বিদ্রোহ দিয়েছে মনের প্রান্ত নাড়া
তবু হতবাক্ দিইনি সাড়া।”
সৈনিকেরা চিরদিনই প্রহরী হয়ে জীবন কাটান। হৃদয়ের ক্ষত বহন করে নিয়ে রক্তক্ষরণ চেপে রেখে তাঁদেরকে পথ চলতে হয়। কত সমস্যার সামনাসামনি দাঁড়াতে হয়। হেরে গেলে চলে না। সুকান্ত সেই জয়লাভেরই কবিতা লিখেছেন। সেই মানসিক উৎকর্ষ আনার এবং দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। ‘বিদ্রোহ’, ‘রক্ত’, ‘শপথ’, ‘ক্ষত’, ‘মুঠি’, ‘মিছিল’, ‘বাহিনী’ প্রভৃতি শব্দগুলি বারবার তাই ফিরে এসেছে। ‘আগুন’ ও ‘আন্দোলনে’র লেলিহান শিখা উত্তাল হয়েছে। ‘খিদে’, ‘বুভুক্ষা’, ‘উপবাস’,’মিছিল’ শব্দগুলির পরিপূরক হয়ে উঠেছে ‘খাদ্য’ বা ‘খাবার’, ‘শস্য’ বা ‘ফসল’। ‘চাষি’, ‘লাঙল’, ‘কাস্তে’ পরিপূর্ণ সভ্যতার সদর্থক হয়ে ফিরে এসেছে। একটা সময়ের ভয়ংকরতা কতখানি ছিল, অমানবিকতা কত গভীর ছিল, শোষণ ও পীড়ন কত তীব্র ছিল সেই দর্পণেই সুকান্ত নিজস্ব মুখ দেখেছেন। সমগ্র জাতিকেই প্রতিফলিত করেছেন সেই আয়নায়। সুতরাং ইতিহাস, জাতীয় চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধেরই পরিচয় থাকবে তাঁর কাব্যে এটাই যথার্থ। তাই তাঁর রচনা “শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।”
মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করলেও আগামীর স্বপ্নে স্পন্দিত হতে কবি ভোলেননি। তাই একদিকে আঠারো বছরের তরুণ যৌবনকে আহ্বান করেছেন, যে যৌবন কখনো কাপুরুষ এবং ভীরু নয়। সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারে সহজেই। প্রিয় শহর কলকাতা যখন ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে, কবি সেখানেও হানাহানি আর রক্তের ভেতর হৃৎস্পন্দন শুনতে পেয়েছেন। শান্তিহীন কলকাতায় রক্তের কলঙ্ক আতঙ্কিত করেছে। সার সার বাড়িগুলি কবরের মতো। চারিদিকে মৃত্যুর স্তূপ। মিলিটারি আর লরির গর্জন। রাত্রির ঘোষণায় তবু কবি ‘জনরব’ উঠে এসেছে:
“পাখিদের মাতামাতি: বুঝি মুক্তি নয় অসম্ভব,
যদিও ওঠেনি সূর্য, তবু আজ শুনি কলরব।”
এই কলরব তো প্রাণের। ‘ঘুম নেই’ কাব্যে তাই ‘সূর্যের গান’ও জেগে উঠেছে। ‘পূর্বাভাস’ কাব্যে নিজের গোপন সূর্য অস্তাগামী হলেও গোধূলি আকাশ কবিকে জানিয়ে দিয়েছে :
“তোমার বিশাল পৃথিবীতে
এখনো বসন্ত বেঁচে আছে।”
কবির মৃত্যুর পর হয়তো গুঞ্জন থেমে যাবে। বুকের স্পন্দনটুকু ঝিল্লির ঝংকারে পরিণত হবে। উজ্জ্বল আলোর চোখে আঁকা হবে আঁধার-অঞ্জন। তবু লাঞ্ছনায় বেদনায় প্রত্যেকের অন্তর পৃষ্ট হবে বলেই কবি বিশ্বাস করেন। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুকে অনুভব করতে করতেই জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করেছেন। কিন্তু জীবন তো অপরিমেয় তা অন্য সব জীবনের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং তা আগামীর সূর্য হয়ে তীব্র আলোর বেগ নিয়ে প্রতিফলিত হবে। নতুন ভোরের ঠিকানা আছে সেইখানেই। আশাবাদ বারবার উজ্জীবিত করেছে। শুধু সশরীরে বেঁচে থাকাই একমাত্র বেঁচে থাকা নয়। স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে থাকাকেই কবি জীবনের পরমায়ু বলে মেনেছেন। আর এখানেই সুকান্ত চিরন্তন উত্তরণের সোপান রচনা করে গেছেন।
সারা বিশ্বময় উত্তাল এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেমন সুকান্তের কবিতায় স্থান করে নিয়েছিল, তেমনি স্বদেশ চেতনার সর্বব্যাপী রূপও মানবিক প্রজ্ঞাকে ধারণ করেছিল। শুধু সাহিত্যের জন্য সাহিত্য নয়, শুধু শিল্পের জন্য শিল্প নয়, জীবনের জন্য সাহিত্য, বেঁচে থাকার জন্য সাহিত্য, স্বপ্ন দেখার জন্য সাহিত্য এবং সংগ্রামের জন্যও সাহিত্য। সুকান্ত একথা বুঝতে পেরেছিলেন। ক্ষুদ্র আয়ুর জীবনে তিনি তাই সীমাবদ্ধ হতে চাননি, নিজ দায়িত্বভার তুলে দিতে চেয়েছিলেন আগামী প্রজন্মের হাতে। নিজ যৌবনের উদ্দাম স্বপ্নভারও সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। আজও প্রতিটি কবির মনেই এই প্রশ্ন: আমরা মানবিক পৃথিবী কখন পাব? আমরা সমূহ সৃষ্টি যেন সেখানেই উৎসর্গ করে চলেছি। কবি কি শুধু নিজের জন্য লড়াই করেন? শুধু কি নিজের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসাব করেন? না, তা হতে পারে না। কবির যুদ্ধ একটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতির জন্য, একটি দেশের জন্য, একটি মানবিক সভ্যতার জন্য। শুধু রোমান্টিক জীবনের হাতছানি নয়, কঠোর কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হওয়াও। সুকান্ত তাই ‘হে মহাজীবন’ কবিতায় লিখেছেন:
“হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।”
শিল্প তো এই মানুষকে নিয়েই গড়ে ওঠে, সময়েরই পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপ আহরিত হয়। তাই এমন একটি সময়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে আর মাধুর্যময় কাল্পনিক রূপলাবণ্যে কবি ভেসে যেতে পারেননি। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় হয়ে উঠেছিল। পূর্ণিমা চাঁদ সেখানে ঝলসানো রুটি। লঙ্গরখানায় সেখানে সকাল থেকে লাইনে অপেক্ষা করা। শহরের রাজপথে সেখানে হাজার হাজারে মানুষ আশ্রয়হীন। প্রতিমুহূর্তে সেখানে অনিশ্চয়তা জীবনের। গোপন হিংসা কপটরাত্রির ছায়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথও দেখেছিলেন অসহায়কে আঘাত করে চলেছে। সেখানে সুকান্তও আর স্থির হতে পারেননি।
একশো বছর কেবল অংকের হিসেব মাত্র। প্রতিমুহূর্তেই কবির জন্মান্তর ঘটে। মানুষের বোধের মৃত্যু ঘটে না, বোধের বয়সও বাড়ে না। কবি তো সেইখানেই অবস্থান করেন। তাঁকে আমরা শরীরে খুঁজি না, তাঁকে আমরা মনে খুঁজি, চেতনায় খুঁজি। তিনি তো আমাদের জীবনে তাঁর জীবনের সংযোগ করে গেছেন। আমরা তাঁরই রূপান্তরিত উত্তর সাধক মাত্র। আমাদের ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী আজও গদ্যময়। গাজা-ফিলিস্তিন-ইজরাইল আজও আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করছে। আজও আমরা কাশ্মীর সীমান্তের নারকীয় হত্যা ভুলতে পারি না।

তৈমুর খান
জন্ম ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৭, বীরভূম জেলার রামপুরহাট সংলগ্ন পানিসাইল গ্রামে ।শিক্ষা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা নিয়ে পিএইচডি । পেশা : উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক । প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ :বৃত্তের ভেতরে জল, জ্যোৎস্নায় সারারাত খেলে হিরণ্য মাছেরা, নির্বাচিত কবিতা, উন্মাদ বিকেলের জংশন, স্তব্ধতার ভেতর এক নিরুত্তর হাসি, নির্ঘুমের হ্রস্ব ধ্বনি, কাহার অদৃশ্য হাতে, ইচ্ছারা সব সহমরণে যায়, আকাঙ্ক্ষার ঘরের জানালা ইত্যাদি ।পুরস্কার :কবিরুল ইসলাম স্মৃতি পুরস্কার, দৌড় সাহিত্য সম্মান এবং নতুন গতি সাহিত্য পুরস্কার ইত্যাদি।