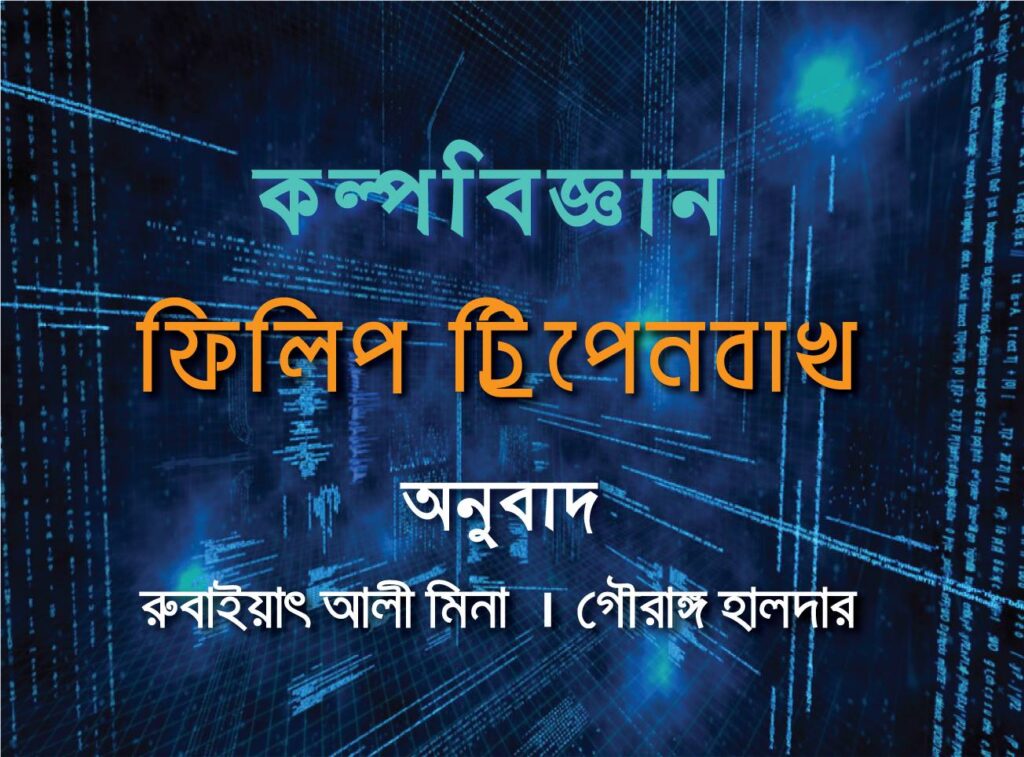[দক্ষিণ ভারত হিন্দী প্রচার সভা, মাদ্রাজ-এর চতুর্থ সনদ বিতরণোৎসব উপলক্ষে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ তারিখে প্রদত্ত শিক্ষা সমাপনী বক্তব্য]
প্রিয় বন্ধুগণ
আপনারা আমাকে এই যে সম্মান দিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদেরকে শতমুখে ধন্যবাদ জানাতে চাই; কেননা আপনারা আমাকে সে জিনিস দিয়েছেন যার জন্য আমি একেবারেই অযোগ্য। না আমি হিন্দী সাহিত্য পাঠ করেছি, না এর ইতিহাস পাঠ করেছি, না এর বিকাশধারা সম্পর্কে আমি কিছু জানি। এমন মানুষ এতটা সম্মান পেয়ে সে যদি গর্বিত না হয় তবে সে মানুষই নয়। আমন্ত্রণ পেয়ে আমি তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেছি। মানুষের মধ্যে মন চাইলেও ‘না’ বলার যে অভ্যাস থাকে সেই ঝুঁকি আমি নিতে চাইনি। এ আমার ধৃষ্টতা যে আমি সেই কাজ করতে দাঁড়িয়ে গিয়েছি যার যোগ্যতা আমার নেই; কিন্তু এধরনের চাতুর্যের জন্য আমি একা অপরাধী নই। আমার ভাই পাওয়া যাবে ঘরে ঘরে, গলিতে গলিতে। আপনাদের তো নিজেদের আমন্ত্রণের সম্ভ্রম রক্ষা করতে হবে। আমি যা কিছু আবোল-তাবোল বকব, তার খুব প্রশংসা করবেন, তার মধ্যে যে অর্থ নেই তা সৃষ্টি করবেন, তাতে অধ্যাত্ম এবং সাহিত্যের তত্ত্ব খুঁজে বের করবেন – যে পরিশ্রম করে সে কিছুনা কিছু লাভ করে।
আপনাদের সভা পনেরো-ষোলো বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে যে কাজ করে দেখিয়েছে তার জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই, বিশেষভাবে এইজন্য যে আপনারা নিজেদের চেষ্টায় এই সাফল্য লাভ করেছেন। সরকারী সহায়তার মুখ চেয়ে থাকেন নি। আপনাদের এই কাজ উচ্চ সাহসিকতার উদাহরণ। যদি আমি বলি, আপনারা ভারতের মস্তিষ্ক তবে সেটা অত্যুক্তি হবে না। অন্য কোনো প্রদেশে এমন ভাল সংগঠন হতে পারে কিনা, এমন ভাল কর্মকর্তা হতে পারে কিনা তাতে আমার সন্দেহ রয়েছে। যে সকল মস্তিষ্ক ইংরেজের রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যারা ইংরেজী ভাষার প্রভাব বিস্তৃত করেছে, যারা ইংরেজী আচার-বিচারে ভারতে অগ্রগণ্য ছিল এবং রয়েছে তারা রাষ্ট্রভাষার উত্থানের জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। তাহলে কিছু করতে পারবে না? আর এটা কত বড় সৌভাগ্যের কথা যে যে সমস্ত মস্তিষ্ক একদিন বিদেশী ভাষায় নিপুণ হওয়াকে নিজের ধ্যান মনে করেছে, তাদেরকে আজ রাষ্ট্রভাষা উদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হচ্ছে আর যেখান থেকে মানসিক পরাধীনতার ঢেউ উঠেছিল, সেখান থেকেই জাতীয়তার তরঙ্গ উঠছে। যে সমস্ত মানুষ ইংরেজি বলা এবং লেখায় ইংরেজদের মাত করে দিয়েছেন, এমনকি আজ যেখানেই দেখুন না কেন ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক পাবেন এই প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের, তারা যদি চান তবে হিন্দী বলায় এবং লেখায় হিন্দীভাষীদেরও মাত করতে পারেন। আর গত বছরের যাত্রীদলের নেতাদের ভাষণ শুনে আমাকে একথা স্বীকার করতে হয় যে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ‘হিন্দী-প্রচারক’- এ প্রকাশিত অধিকাংশ রচনা আপনাদেরই; তার পরিপক্ক ভাষা এবং পরিছন্নতা ও গতিশীলতা দেখে আমাদের মধ্যে অনেকের ঈর্ষা হয়। আর এটা তখন যখন রাষ্ট্রভাষাপ্রীতি পৌঁছেছে কেবল হৃদয়ের উপরিভাগে আর আজও এই প্রদেশ ইংরেজী ভাষার প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হতে চায়না। যখন এই প্রীতি হৃদয়ে হৃদয়ে ব্যাপ্ত হবে, সেই সময় তার গতি কতটা দ্রুত হবে, তার অনুমান কে করতে পারে? আমাদের পরাধীনতার সবচেয়ে অপমানজনক, সবচেয়ে ব্যাপক, সবচেয়ে কঠোর অংশ ইংরেজী ভাষার প্রভুত্ব। আর কোথাও একে এত নগ্ন রূপে দেখা যায় না। সভ্য জীবনের প্রতিটি ভাগে ইংরেজী ভাষাই যেন আমাদের বুককে পিষ্ট করছে। আজ যদি আমরা এই প্রভুত্বকে ভাঙতে পারি, তবে পরাধীনতার অর্ধেক বোঝা আমাদের ঘাড় থেকে নেমে যাবে। কয়েদি বেড়িতে যত কষ্ট পায়, ততটা আর কিছুতে পায়না। জেলখানা হয়ত তার বাড়ী থেকে বেশী হাওয়াদার, পরিষ্কার হবে। খাবারও হয়ত সেখানে বাড়ীর খাবারের চেয়ে ভাল এবং সুস্বাদু। কখনো কখনো সে সন্তানদের নিকট থেকে স্বেচ্ছায়ই বছর বছর দূরে থাকে। তার শাস্তি মনে করিয়ে দেয়ার মতো বস্তু এই বেড়ি যা উঠতে-বসতে, জাগতে-ঘুমাতে, হাসতে-বলতে কখনো তার পেছন ছাড়ে না, কখনো তাকে মিথ্যা কল্পনাও করতে দেয় না যে সে মুক্ত। এর প্রভাব সব থেকে বেশী পড়ে কয়েদির হৃদয়ে, যাকে কখনো উপড়ে ফেলতে পারে না, যা তাকে কল্পনার আনন্দও উপভোগ করতে দেয় না। ইংরেজী ভাষা আমাদের পরাধীনতার সেই বেড়ি যা আমাদের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যে আর তাদের মধ্যে কোনো ইচ্ছাও নেই। আমাদের শিক্ষিত সমাজ সেই বেড়িকে গলার হার মনে করতে বাধ্য। এটা তাদের রুটি-রুজির প্রশ্ন। আর যদি রুটির সাথে কিছুটা সম্মান, কিছুটা গৌরব, কিছুটা অধিকারও পাওয়া যায় তবে আর বলার কী আছে! প্রাণীমাত্রের মাঝেই তো প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইংরেজী ভাষা তার দরোজা খুলে দিয়েছে আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাখীর ঝাঁকের মতো সেই দরোজা দিয়ে প্রবেশ করে মাটিতে ছড়ানো শস্যদানা খেতে শুরু করেছে। এখন যতই পাখা ঝাপটাক ফুল বাগানের হাওয়া তার কপালে নেই। মজার বিষয় হলো এই যে এই পাখীর ঝাঁকের পাখা ঝাপটানো বাইরে বেরুবার জন্য নয়, কেবল একটু মনোরঞ্জনের জন্য। তার পাখা নির্জীব হয়ে গেছে, এর মাঝে উড়বার শক্তি নেই, এই ভরসা নেই যে এই শস্যদানা বাইরে পাবে। এখন তো ওই খাঁচা, ওই বদ্ধ ঘর, ওই শিকারী।
কিন্তু বন্ধুগণ, বিদেশি ভাষা শিখে নিজের দেশের গরীব মানুষের ওপর প্রতিপত্তি দেখানোর দিন দ্রুত বিদায় নিচ্ছে। প্রতিভা এবং বুদ্ধিশক্তির যে অপব্যবহার আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী করে এসেছি, যার শক্তিতে আমরা এক ধনিকতন্ত্র স্থাপন করেছি আর নিজেকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করে ফেলেছি, সেই অবস্থা এখন বদলে যাচ্ছে। বুদ্ধিবল ঈশ্বরের দান আর তার ধর্ম প্রজাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা নয়, তাদের রক্ত শোষণ করা নয়, তাদের সেবা করা। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর থেকে জনতার বিশ্বাস উঠে গেছে। জনতা শিক্ষিতদেরকে বিদেশীদের চেয়েও অধিক বিদেশী মনে করে। একি কোনো আশ্চর্যের কথা যে শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ দুদিক থেকেই ঠোক্কর খাচ্ছে? প্রভুদের কাছ থেকে এজন্য যে তারা মনে করে, আমার চৌকাঠ ছাড়া এদের জন্য আর কোনো আশ্রয় নেই। আর জনতার কাছ থেকে এই জন্য যে তাদের সাথে জনতার কোনো আত্মীয়-সম্পর্ক নেই। তাদের আচার-আচরণ, তাদের চলন-বলন, তাদের বেশভূষা, তাদের বিচার-বিবেচনা সবকিছু জনতা থেকে স্বতন্ত্র আর তা কেবল এইজন্য যে আমরা ইংরেজী ভাষার গোলাম হয়ে গিয়েছি। পরিস্থিতি যেন এমন হয়ে গেছে যে ইংরেজী ভাষার উপাসনা ছাড়া কাজ চলে না। কিন্তু আজ তো এতদিনের অভিজ্ঞতার পর বুঝতে পারা উচিত যে এই নৌকায় বসে আমরা পার হতে পারব না। তবে কেন আমরা তার সাথে লেপ্টে আছি? এইতো গত বছর এক ইউনিভার্সিটি কমিশন বসেছিল শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবার জন্য। তাতে এও প্রস্তাব ছিল যে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষা কেন করা হবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে। কেন? এইজন্য যে ইংরেজী মাধ্যম না থাকলে আমাদের বাচ্চারা ইংরেজীতে কাঁচা থেকে যাবে এবং ভাল ইংরেজী লিখতে-বলতে সক্ষম হবে না। কিন্তু এই দেড়শ’ বছরের ঘোর তপস্যার পর ভারত আজ পর্যন্ত একটিও এমন গ্রন্থ রচনা করতে পারেনি যাকে ইংল্যান্ডে ততটা সমাদর করা হয় যতটা করা হয় তৃতীয় শ্রেণীর কোনো ইংরেজ লেখকের গ্রন্থকে। মনে নেই, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেছিলেন কিংবা স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু যে পঞ্চাশ বছর ইংরেজীর গায়ে মাথা ঠুকে আজও তাদের ইংরেজীতে কথা বলবার সময় সংশয় হয়, কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে নাতো! আমরা কোমরভাঙ্গা কঠিন অধ্যবসায় করে রক্ত জল করে ইংরেজী ভাষার অভ্যাস করি, তাদের প্রবাদ-প্রবচন মুখস্ত করি; কিন্তু বড় থেকে বড় ভারতীয় সাধকের রচনা শিক্ষার্থীদের স্কুল এক্সারসাইজের বেশী গুরুত্ব পায়নি। এইতো দু-তিন দিন আগে পাঞ্জাবের গ্রাজুয়েটদের ইংরেজীর যোগ্যতার সমালোচনা করেন সেখানকার পরীক্ষকগণ, ছাত্রদের মাঝে নিজের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা নেই, অনেকে তো বানানও ভুল করে। আর এই পরিণতি অন্তত বারো বছর কঠোর তপস্যা পর। তবুও আমাদের জন্য শিক্ষার ইংরেজী মাধ্যম জরুরী, এই হল বিদ্বানগণের রায়। জাপান, চীন এবং ইরানে তো শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী নয়। তবুও তারা সভ্যতার সকল ব্যাপারে আমাদের চেয়ে ক্রোশ ক্রোশ এগিয়ে। কিন্তু ইংরেজী মাধ্যম ছাড়া আমাদের নৌকা ডুবে যাবে। আমাদের মাড়োয়ারী ভাইয়েরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কারণ অন্তত বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁদের যতটুকুন সম্পর্ক, তাঁরা জাতীয়তার রক্ষা করেছেন।
বন্ধুগণ, আমি হয়ত আমার বিষয় থেকে একটু দূরে সরে গিয়ছি; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কেবল এই যে আমরা জেনে নিই, আমাদের সামনে কত বড় মহৎ কাজ। একথা জেনে নিন যে যেদিন ইংরেজী ভাষার প্রভুত্ব ভেঙে ফেলবেন এবং নিজেদের একটি জাতীয় ভাষা গড়ে তুলতে পারবেন সেদিনই আপনি স্বরাজের দর্শন পাবেন। আমি মনে করতে পারছিনা কোনো রাষ্ট্র বিদেশী ভাষার শক্তিতে স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে কিনা। রাষ্ট্রের বুনিয়াদ রাষ্ট্রের ভাষা। নদী, পাহাড়, সমুদ্র রাষ্ট্র তৈরী করে না। ভাষাই সেই বন্ধন যা চিরকাল রাষ্ট্রকে এক সূত্রে বেঁধে রাখে এবং তার বন্ধনকে কখনো আলগা হতে দেয় না। যে সময় ইংরেজ এসেছে ভারতের জাতীয় ভাবনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বলতে পারেন, তার মাঝে রাজনৈতিক চেতনার গন্ধ পর্যন্ত ছিল না। ইংরেজের রাজত্ব এসে আপনাদেরকে এক রাষ্ট্র বানিয়ে দিয়েছে। আজ যদি ইংরেজের রাজত্ব বিদায় হয়ে যায় – আর একদিন না একদিন তো হবেই – তাহলে আপনাদের এই রাষ্ট্র কোথায় যাবে? এর কি প্রবল সম্ভাবনা নেই যে একেক প্রদেশ একেক রাজ্য হয়ে যাবে আর তারপর সেই বিচ্ছেদ শুরু হয়ে যাবে? বর্তমান দশায় তো আমাদের জাতীয় চেতনাকে সজাগ এবং সজীব রাখবার জন্য ইংরেজ রাজত্বের অমর থাকা প্রয়োজন। যদি আমরা এক রাস্ট্র হয়ে নিজেদের স্বরাজের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে চাই তবে আমাদেরকে রাষ্ট্রভাষার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং সেই রাষ্ট্রভাষার ঢাল দিয়েই আমরা রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারব। আপনারা সেই রাষ্ট্রভাষার ভিক্ষু আর সেই সম্পর্কে আপনারা রাষ্ট্রকে নির্মাণ করছেন। ভাবুন, আপনারা কতটা মহান কাজ করছেন! আপনারা আইনের সূক্ষ্মতা বিচারের জন্য উকিল হয়ে থাকেন নি, আপনারা শাসন-কারখানার মজদুর হয়ে থাকেন নি, আপনারা এক ছড়ানো-ছিটানো জাতিকে একত্র করছেন, আপনারা আমাদের বন্ধুত্বের সীমাকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, ভুলে যাওয়া ভাইদের আলিঙ্গন করাচ্ছেন। এই কাজের পবিত্রতা এবং গৌরব বিবেচনা করে এমন কোনো কষ্ট নেই যা আপনারা বরণ করে নিতে পারেননি। এ ধনের মার্গ নয়, সম্ভবত এ কীর্তির মার্গও নয়; কিন্তু আপনাদের আত্মিক সন্তোষের জন্য এর চেয়ে শ্রেয় কাজ হতে পারেনা। এটিই আপনাদের বলিদান এর মূল্য। আমি আশা করি, সর্বদা আপনাদের সামনে এই আদর্শই থাকবে। আদর্শের গুরুত্ব আপনারা খুব ভাল করেই বোঝেন। এই আদর্শ আমাদের থেমে যেতে থাকা পা-কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের হৃদয় থেকে সংশয় এবং সন্দেহের ছায়াকে মুছিয়ে দেয় এবং কঠিন অবস্থায় আমাদের সাহস যোগায়।
রাষ্ট্রভাষার তাৎপর্য আমাদের কাছে কী, এই বিষয়েও আমি আপনাদেরকে দু’একটি কথা বলব। একে হিন্দী, বলুন হিন্দুস্তানী বলুন কিংবা উর্দু বলুন, জিনিস একই। নাম নিয়ে আমাদের কোনো তর্ক নেই। ঈশ্বর তিনিই যিনি খোদা আর রাষ্ট্রভাষায় দুয়ের জন্য সমান সম্মানের স্থান থাকা উচিত। যদি আমাদের দেশে এমন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যারা ঈশ্বরকে ‘গড’ বলেন তবে রাষ্ট্রভাষা তাদেরকেও স্বাগত জানাবে। জীবিত ভাষা তো জীবিত দেহের মতো লাগাতার গড়ে ওঠে।’শুদ্ধ হিন্দী’ নিরর্থক শব্দ। যখন ভারত শুদ্ধ হিন্দু হবে তখন তার ভাষা শুদ্ধ হিন্দী হবে। যতদিন পর্যন্ত এখানে মুসলমান, খ্রীষ্টান, পারসী, আফগানী সকল জাতি উপস্থিত থাকবে, আমাদের ভাষাও থাকবে ব্যাপক। যদি হিন্দী ভাষা প্রাদেশিক ভাষা থাকতে চায় এবং কেবল হিন্দুদের ভাষা থাকতে চায় তাহলে তাকে শুদ্ধ বানানো যেতে পারে। এর প্রতিটি অঙ্গ ধরে এর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। প্রৌঢ় থেকে সে আবার শিশু হবে। এ অসম্ভব, হাস্যকর। আমাদের চোখের সামনে শত শত বিদেশী শব্দ ভাষার মধ্যে ঢুকে গেছে; আমরা তাকে রুখতে পারি না। তাদের আক্রমণ রুখবার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা। সেই চেষ্টা ভাষার বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। গাছকে সোজা এবং সুডৌল করবার জন্য চারা গাছকে কোনো খুঁটির সহায়তা দেয়া হয়। আপনারা বিদ্বজ্জনেরা এটুকু নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন যাতে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, শ্রুতিকটু শব্দ ব্যবহৃত না হয়; কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ কেবল পুস্তকেই হতে পারে। কথাবার্তায় কোনো প্রকার নিয়ন্ত্রণ রাখা মুশকিল হবে। কিন্তু বিদ্বানদেরও আশ্চর্য মস্তিষ্ক। প্রয়াগে (এলাহাবাদ) বিদ্বান এবং পণ্ডিতদের সংস্থা ‘হিন্দুস্তানী একাডেমী’তে ‘তিমাহী’, ‘সেহমাহী’ এবং ‘ত্রৈমাসিক'(তিনটি শব্দের অর্থই ‘ত্রৈমাসিক’) শব্দ নিয়ে বছরের পর বছর তর্ক চলছে এবং এখন পর্যন্ত মীমাংসা হয়নি। উর্দুর সমর্থন ‘সেহমাহী’-এর দিকে আর হিন্দীর সমর্থন ‘ত্রৈমাসিক’-এর প্রতি, আর বেচারা ‘তিমাহী’যে সবচেয়ে সরল, সহজে বলা এবং বুঝতে পারার মতো শব্দ, দু’পক্ষই তাকে বহিষ্কার করেছে। ভাষা-সুন্দরীকে নির্জন কক্ষে বন্ধ করে রেখে আপনি তার সতীত্বকে তো বাঁচাতে পারেন, কিন্তু সেটা তার জীবন-মূল্য দিয়ে। তার খোদ আত্মাকে এতটা শক্তিশালী করে তুলুন যাতে সে নিজের সতীত্ব এবং স্বাস্থ্য দুটোই রক্ষা করতে পারে। অবশ্যই আমাদের এমন গ্রামীণ শব্দকে দূরে রাখা উচিত যা কেবল বিশেষ এলাকায় বলা হয়ে থাকে। আমাদের আদর্শ তো এই হওয়া উচিত যে আমাদের ভাষা যেন অধিক থেকে অধিক মানুষ বুঝতে পারে। যদি আমরা এই আদর্শকে আমাদের সামনে রাখি তাহলে লেখার সময়ও আমরা শব্দচাতুর্যের মোহে পড়ব না। একথা ভুল যে ফারসী শব্দে ভাষা কঠিন হয়ে যায়। শুদ্ধ হিন্দীর এমন পদের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যার অর্থ বের করা পণ্ডিতগণেরর জন্যও অত্যন্ত কঠিন হবে। সেই শব্দই সরল যা ব্যবহারে আসছে। এতে কোনো বিতর্ক নেই, সেটা তুর্কী, বা আরবী, বা পর্তুগিজ। উর্দু এবং হিন্দীর মধ্যে কেন এমন তিক্ত সম্পর্ক, তা আমি বুঝতে পারিনা। যদি কোনো এক সম্প্রদায়ের মানুষের ‘উর্দু’ নাম প্রিয় হয় তবে তাদেরকে এই শব্দ ব্যবহার করতে দিন। যাদের ‘হিন্দী’ নামের প্রতি প্রীতি রয়েছে তারা তাই বলুক। এতে লড়াই কিসের? এক বস্তুকে দুই নাম দিয়ে অনর্থক নিজেদের মধ্যে লড়াই করা এবং তাকে এত বেশী গুরুত্ব দেয়া যে তা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এই মনোবৃত্তি অসুস্থ এবং দুর্বল মনের। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার স্ট্যান্ডার্ড-এ নিয়ে আসতে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা হিন্দুদের চেয়ে কম ইচ্ছুক নয়। আমি বলছি সেই হিন্দু-মুসলমানের কথা যারা জাতীয়তার জন্য পাগল। কট্টরপন্থীদের সঙ্গে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। উর্দু এবং মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র এখন আলিগড়। সেখানে উর্দু এবং ফারসীর প্রফেসর এবং অন্য বিষয়ের প্রফেসরগণের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছে তাতে আমি বুঝতে পেরেছি, মৌলভীয়ানা ভাষার প্রতি তাঁরা ততটাই বিরক্ত যতটা বিরক্ত পণ্ডিতী ভাষার প্রতি এবং তাঁরা জাতীয় ভাষা সংঘ আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে প্রস্তুত। আমি একথা মেনে নিচ্ছি যে মুসলমানদের একটি অংশ হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র থাকাকেইই নিজেদের কল্যাণ মনে করে – যদিও এই অংশের শক্তি এবং প্রভাব দিন দিন কমে আসছে – আর তারা যদি নিজের ভাষাকে আরবী দিয়ে গলা অব্দি ভরে দিতে চায়, তবে তাদের সঙ্গে কেন ঝগড়া করব? আপনারা কি মনে করেন, এমন জটিল ভাষা মুসলিম জনতার মাঝেও প্রিয় হতে পারে? মুসলমানগণের মধ্যেও সে ধরনের লেখকের সংখ্যা অধিক যাঁরা সাধারণবোধ্য ভাষায় লেখেন। মৌলভীয়ানা ভাষা লেখার জন্য এখানেও কোনো স্থান নেই। মুসলমান বন্ধুদেরকেও কিছু বলবার অধিকার আমার আছে। কারণ আমার সমস্ত জীবন কেটেছে উর্দুর সেবা করে এবং এখনো আমি যতটা উর্দুতে লিখি ততটা হিন্দীতে লিখিনা। আর কায়স্থ হওয়ার কারণে এবং বাল্যকাল থেকে ফারসীর চর্চা করবার কারণে উর্দু আমার জন্য যতটা স্বাভাবিক হিন্দী ততটা নয়। আমি জানতে চাইছি, আপনারা কি একে হিন্দীর গলার কাঁটা মনে করেন? আপনারা কি জানেন, আর না জানলে জানা উচিত, যে হিন্দীর সর্বপ্রথম কবি যিনি হিন্দীর সাহিত্যিক বীজ বপন করেছিলেন(ব্যবহারিক বীজ কয়েক শতাব্দী পূর্বেই পড়েছিল) তিনি আমির খুসরো? আপনারা কি জানেন, কমসে কম পাঁচ শত মুসলমান কবি হিন্দীকে তাঁদের কবিতা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তো অত্যন্ত উঁচু মানের কবি? আপনারা কি জানেন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত হিন্দী কবিতা উপভোগ করতেন এবং ঔরঙ্গজেবই আমের নাম রেখেছিলেন ‘রসনা-বিলাস’এবং ‘সুধা-রস’? আপনারা কি জানেন, আজও হসরত(হসরত মোহানী) এবং হাফিজ জলন্ধরীর মতো কবি কখনো কখনো হিন্দীতে কবিতা রচনা করেন? আপনারা কি জানেন, হিন্দীতে হাজার হাজার শব্দ, হাজার হাজার ক্রিয়া আরবী এবং ফারসী থেকে এসেছে আর শ্বশুরবাড়ীতে এসে ঘরের দেবী হয়ে গেছে? যদি এসব জানা সত্ত্বেও আপনি হিন্দীকে উর্দু থেকে আলাদা মনে করেন তবে আপনি দেশের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে অন্যায় করছেন। ‘উর্দু’ শব্দ কবে এবং কোথায় উৎপন্ন হয়েছে তার কোনো ঐতিহাসিক সনদ পাওয়া যায় না। আপনি কি মনে করেন, ‘ওহ বড়া খরাব আদমী হ্যায়’ এবং ‘ওহ বড়া দুর্জন মনুষ্য হ্যায়'(দুটো বাক্যের অর্থই ‘সে খুব খারাপ মানুষ’।) দুটো আলাদা ভাষা? হিন্দুদের নিকট ‘খরাব’ও ভাল লাগে আর ‘আদমী’ তো নিজের ভাই-ই। তাহলে মুসলমানদের নিকট ‘দুর্জন’কেন খারাপ লাগবে, ‘মনুষ্য’কে কেন তারা শত্রু বলে মনে করবে? আমাদের জাতীয় ভাষায় ‘দুর্জন’ ও ‘সজ্জন’, ‘উম্দা'(ভাল) ও ‘খরাব'(খারাপ) দু’য়ের জন্যই স্থান রয়েছে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত ভাষার সুবোধ্যতায় বাধা না পড়ে। এর সামনে আমরা না উর্দুর বন্ধু, না হিন্দীর। মজার বিষয় হল ‘হিন্দী’ মুসলমানদের দেয়া নাম এবং এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্ব পর্যন্ত যাকে আজ ‘উর্দু’ বলা হচ্ছে কাকে মুসলমানরাও ‘হিন্দী’ বলতেন। আর আজ হিন্দী সীমিত। আপনারা কি দেখতে পান না, ‘হিন্দী’একটি স্বাভাবিক নাম? ইংল্যান্ডবাসী ইংলিশ বলে, ফ্রান্সবাসী ফ্রেঞ্চ বলে, জার্মানীবাসী জার্মান বলে, পারস্যবাসী ফারসী বলে, তুরস্কবাসী তুর্কী বলে, আরববাসী আরবী বলে। তবে হিন্দবাসী কেন হিন্দী বলবে না? উর্দু তো না কাফিয়ায় আসে না রাদিফে (‘কাফিয়া’ ও ‘রাদিফ’ উর্দু কবিতার দুই ধরনের মিল বিন্যাস), না বহরে না ওজনে। হ্যাঁ, হিন্দুস্তানের নাম উর্দুস্তান রাখা হলে নিঃসন্দেহে এখানকার জাতীয় ভাষা উর্দু হবে। জাতীয় ভাষার উপাসকগণ নাম নিয়ে বিতর্ক করেন না, তাঁরা বিতর্ক করেন সত্যতা নিয়ে। কেন দুই ভাষার শব্দকোষ এক হয়ে যায় না? আমাদের প্রয়োজন দুই ভাষার এক সাধারণ শব্দকোষ যার মধ্যে জমা করা হবে সাধারণবোধ্য শব্দসমূহ। হিন্দীতে তো আমার বন্ধু পণ্ডিত রামনরেশ ত্রিপাঠী কিছু পরিমাণে এই অভাব পূরণ করেছেন। এ ধরনের একটি শব্দকোষ উর্দুতেও হওয়া প্রয়োজন। হয়ত এই কাজ জাতীয় ভাষা সংঘ (কৌমী ভাষা সংঘ) গড়ে ওঠা পর্যন্ত মুলতবি থাকবে। মুসলমান বন্ধুদের প্রতি আমার এই নালিশ যে হিন্দীর সাধারণবোধ্য শব্দের সঙ্গেও তাঁরা দূরত্ব রক্ষা করেন; যদিও হিন্দীতে সাধারণবোধ্য ফারসী শব্দ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা হয়।
কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, রাষ্ট্রভাষা কতদূর অব্দি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে? উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, সংবাদপত্রের রচনা, সমালোচনা যদি অনেক গূঢ় না হয়, চর্চার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষায় লেখা যেতে পারে; কিন্তু জ্ঞানচর্চায় কেবল এগুলোই তো বিষয় নয়। দর্শন এবং বিজ্ঞানের অনন্ত শাখাও তো রয়েছে যেগুলো আপনি রাষ্ট্রভাষায় নিয়ে আসতে পারেন না। সাধারণ কথাতো সাধারণ এবং সরল শব্দে লেখা যেতে পারে। বিশ্লেষণাত্মক বিষয়ে এমনকি উপন্যাসে, যখন তা মনোবৈজ্ঞানিক হয়ে যায়, আপনাকে বাধ্য হয়ে সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী শব্দের আশ্রয় নিতে হয়। যদি আমাদের রাষ্ট্রভাষা সর্বাঙ্গপূর্ণ না থাকে এবং তার মধ্যে আপনি সকল বিষয়, সকল ভাব প্রকাশ করতে না পারেন তবে তো এটা একটা বড় ত্রুটি এবং আমাদের সকলের কর্তব্য হল, আমরা রাষ্ট্রভাষাকে সেই রকম সর্বাঙ্গপূর্ণ করে তুলি, যেমন রয়েছে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পন্ন ভাষাসমূহ। এমনিতে তো এখন হিন্দী এবং উর্দু নিজের সার্থক রূপেও পূর্ণ নয়। পূর্ণ কেন, আধখানাও নয়। রাষ্ট্রভাষার লেখার যাঁদের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের স্বীকার করতে হবে, একেকটি ভাব প্রকাশের জন্য তাদের কতটা মাথা ঘষতে হয়। সরল শব্দ পাওয়াই যায়না। পাওয়া গেলেও ভাষায় মানানসই হয় না। ভাষার রূপ বিগড়ে দেয়। ক্ষীরের মাঝে লবণের দলার মতো এসে মজা নষ্ট করে দেয়। এর কারণ তো স্পষ্টই, আমাদের আমজনতার মাঝে ভাষাজ্ঞান অতি অল্প এবং সাধারণবোধ্য শব্দের সংখ্যা অনেক কম। যতক্ষণ পর্যন্ত জনতার মাঝে শিক্ষার ভাল প্রচার না হয়, তাদের ব্যবহারিক শব্দাবলী বৃদ্ধি না পায় আমরা তাদের বোঝার উপযুক্ত ভাষায় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে পারব না। আমাদের হিন্দী ভাষা এখন একশ’ বছরেরও হয়নি, রাষ্ট্রভাষা তো এখন শৈশবাবস্থায়। আপাতত আমরা যদি এতে সরল সাহিত্যই লিখতে পারি তবে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রভাষার শব্দকোষ বাড়িয়ে যাওয়া উচিত। সেইসব সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী শব্দ, যাদের দেখে আমরা এখন ভীত হয়ে পড়ি, চর্চার ভেতর চলে এলে এদের অপরিচিতি এবং কাঠিন্য দূর হতে থাকবে। ভাষা-বিস্তারের এই ক্রিয়া ধীরে ধীরেই হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার বিদ্বানদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করতে হবে, যা রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজনকে বড় করে দেখবে। সেই বোর্ডে উর্দু, হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, তামিল ইত্যাদি সকল ভাষার প্রতিনিধি রাখতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে সুব্যবস্থিত এবং গতিশীল করবার দায়িত্ব এই বোর্ডের ওপর ন্যস্ত করতে হবে। এখন পর্যন্ত আমরা নিজেদের মনোমতো কায়দায় এই আন্দোলন চালিয়েছি। অন্যদের সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করিনি। আপনাদের যাত্রী-মণ্ডলও হিন্দীর বিদ্বানগণ পর্যন্ত সীমিত রয়ে গেছে। মুসলিম কেন্দ্রে গিয়ে মুসলিম বিদ্বানগণের সহমর্মিতা পাবার চেষ্টা করেনি। আমাদের বিদ্বানগণ তো ইংরেজীতে মস্ত বড়। জনতার পয়সায় দর্শন-বিজ্ঞান এবং সমস্ত দুনিয়ার বিদ্যা শিখে এসেও তাঁরা জনতার দিক থেকে চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছেন। তাঁদের দুনিয়া স্বতন্ত্র, তাঁরা পরজীবীর মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে নিয়েছেন। যদি তাঁদের মধ্যেও জাতীয় চেতনা থাকত, যদি তাঁরাও জনতার প্রতি নিজেদের কর্তব্য অনুভব করতেন তাহলে হয়ত আমাদের কাজ সরল হয়ে যেত। যে দেশে গণশিক্ষার স্তর এত নিচে সেখানে কিছু মানুষ ইংরেজীতে নিজের বিদ্যাবত্তার তকোমা পরে নিলে কী হবে? আমরা তো তখন বুঝব যখন নিজের বিদ্যাবত্তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরকে উঁচু স্তরে তুলে নেবার ভাবনা থাকে। ভারতে কেবল ইংরেজী জানা লোক থাকে না। হাজারে ৯৯৯ জন ইংরেজী অক্ষর পর্যন্ত চেনে না। যে দেশের মস্তিষ্ক বিদেশী ভাষায় ভাবে এবং লেখে সেই দেশকে বিশ্ব রাষ্ট্র মনে না করলে কি তা অন্যায় হবে? যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার রাষ্ট্রভাষা নেই, আপনার কোনো রাস্ট্রই নেই। এই দুয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক। রাজনীতিতে পারদর্শী ইংরেজ শাসকদের আপনি রাষ্ট্রের হাঁক দিয়ে ধোঁকা দিতে পারবেন না। তারা আপনার রহস্য জানে এবং আপনার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করে।
এখন আমাদের একথা বিবেচনা করতে হবে, রাষ্ট্রভাষার প্রচার কীভাবে বাড়ানো যায়। আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের নেতাগণ এবিষয়ে অপরাধের সমপর্যায়ের গাফিলতি দেখিয়েছে। তাঁরা এখন অব্দি এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে আছেন যে এটা খুব ছোটখাটো বিষয় যা কোনো ছোটখাটো মানুষের কাজ, তাঁদের মতো বড় বড় মানুষের এই ঝামেলায় পড়বার মতো অবসর কোথায়? তাঁরা এখন পর্যন্ত এই কাজের গুরুত্ব বোঝেন নি, নইলে এ বিষয় তাদের কর্মসূচীর প্রথম সারিতে হত। আমার বিবেচনায় যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির মধ্যে এতটা সংগঠিত রূপ, এতটা ঐক্য, এতটা একাত্মতা না হবে যে তারা এক ভাষায় কথা বলতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই শক্তিও হবে না যাতে তারা স্বরাজ পেতে পারে। অসম্ভব ব্যাপার। যাঁরা জাতির অগ্রগামী নেতা, যাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হন এবং জয়লাভ করেন তাঁদের সামনে আমি আদবের সাথে নিবেদন করছি, জনাব, এ ধরনের শত নির্বাচন আসবে এবং চলে যাবে, আপনি কখনো হারবেন, কখনো জিতবেন, কিন্তু স্বরাজ আপনার নিকট থেকে ততটাই দূরে থাকবে যতটা দূরে স্বর্গ। ইংরেজীতে আপনি আপনার মাথার মগজ খুলে রেখে দিন, কিন্তু আপনার আওয়াজে জাতির শক্তি প্রকাশিত না হবার কারণে কেউ আপনার ততটুকু পরোয়াও করবে না যতটুকু শিশুর কান্নায় করে। শিশু কাঁদলে খেলনা কিংবা মিষ্টান্ন পায়। তা হয়তো আপনিও পেয়ে যাবেন, যাতে আপনার চেঁচামেচিতে পিতা-মাতার কাজে বিঘ্ন ঘটবে না। এই কাজকে তুচ্ছ মনে করবেন না। এইতো বুনিয়াদ, আপনার উচ্চমানের ইট, মসলা, সিমেন্ট এবং অতি উচ্চ নির্মাণ-যোগ্যতা যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে খরচ না হবে আপনার ইমারত তৈরী হবে না। হয়তো ঝুপড়ি তৈরি হতে পারে যা বাতাসের এক ঝাপটায় উড়ে যাবে। আসলে এখন পর্যন্ত আমরা যা করেছি, তা না করার সমান। একটি ভাল রাষ্ট্রভাষা বিদ্যালয় আমরা খুলতে পারিনি। প্রতিবছর শত শত স্কুল খুলি, যাতে দেশের কোনো প্রয়োজন নেই। ‘ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'(হায়দ্রাবাদ) কাজের জিনিস যদি তারা উর্দু এবং হিন্দীর মাঝখানকার খাদ আরো চওড়া না করে। তবুও আমি একে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাধান্য দিচ্ছি। অন্তত ইংরেজীর গোলামী থেকে তো সে নিজেকে মুক্ত করেছে। আমাদের আর যত বিদ্যালয় রয়েছে সবই গোলামীর কারখানা যা ছেলেদেরকে স্বার্থের, প্রয়োজনের, প্রদর্শনের, অকর্মণ্যতার গোলাম বানিয়ে ছেড়ে দেয়। আর মজা হল এই যে এই শিক্ষাও অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। এই শিক্ষার বাজারমূল্য শূন্যের সমান। তবুও আমরা কেন মেষের পালের মতো তার পেছনে দৌড়ে চলে যাচ্ছি? ইংরেজী শিক্ষা আমরা শিষ্টতার জন্য গ্রহণ করি না। এর উদ্দেশ্য উদর। শিষ্টতার জন্য আমাদের ইংরেজীর সামনে হাত পাতার প্রয়োজন নেই। শিষ্টতা আমাদের উত্তরাধিকার, শিষ্টতা আমাদের জন্মঔষধীর সঙ্গে মিশে আছে। আমি তো বলব, আমরা প্রয়োজনের বেশী শিষ্ট। আমাদের শিষ্টতা দুর্বলতার সীমায় পৌঁছে গেছে। পশ্চিমা শিষ্টতার মধ্যে যা কিছু আছে তা উদ্যোগ এবং পুরুষার্থ। আমরা সে জিনিস তো তা থেকে বাদ দিইনি। বাদ দিয়েছি কী? লাম্পট্য, অহঙ্কার, স্বার্থান্ধতা, নির্লজ্জতা, শরাব এবং বদঅভ্যাস। একজন অশিক্ষিত কৃষকের কাছে যান। কতটা নম্র, কতটা অতিথিপরায়ণ, কতটা ঈমানদার, কতটা বিশ্বাসী। তারই ভাই টমি, পশ্চিমা শিষ্টতার খাঁটি নমুনা, মদ্যপ, লম্পট, গুণ্ডা, অভদ্র, নির্লজ্জ। শিষ্টতা শেখার জন্য আমাদের ইংরেজের গোলামী করবার প্রয়োজন নেই। আমাদের এমন বিদ্যালয় থাকা উচিত যেখানে উচ্চতর শিক্ষা রাষ্ট্রভাষায় সহজে পাওয়া যাবে। এই সময় যদি বেশী নাও হয়, অন্তত একটি এমন বিদ্যালয় কোনো কেন্দ্রীয় স্থানে হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এখনো সেই গড্ডলিকা প্রবাহে চলেছি, সেই স্কুল, সেই শিক্ষা। এমন কোনো সজ্জন তৈরী হচ্ছে না যিনি একটি রাষ্ট্রভাষার বিদ্যালয় খুলবেন। আমার চোখের সামনে দক্ষিণের অনেক শিক্ষার্থী ভাষা পড়বার জন্য কাশী গিয়েছে; কিন্তু সেখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। একই অবস্থা অন্যান্য স্থানেও। বেচারারা এদিকে ওদিকে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে এসেছে। এখন কিছু শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু যে কাজ আমাদের করতে হবে তার তুলনায় কিছুই হয়নি বলা চলে। প্রচারের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে নাটকের অভিনয় করা ভাল ফল নিয়ে আসতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের সিনেমা প্রশংসনীয় কাজ করছে যদিও এর দ্বারা যে কুরুচি, যে নোংরামী, যে বিলাসপ্রিয়তা, যে কুবাসনা ছড়ানো হচ্ছে তা কাজের গুরুত্বকে মূল্যহীন করে দিচ্ছে। যদি আমরা ভাল ভাবপূর্ণ নাটক মঞ্চে অভিনয় করতে পারি তবে প্রচার অবশ্যই বাড়বে। আমাদের প্রয়োজন খাঁটি মিশনারীর আর আপনাদের ওপর সেই মিশনের দায়িত্ব। বড় মুশকিলের বিষয় হল এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বস্তুর উপযোগিতা প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায় না কেউ তার পেছনে নিজের সময় নষ্ট করবে কেন? যদি আমাদের নেতা এবং বিদ্বানগণ, যাঁরা রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে অসচেতন থাকতে পারেন না, রাষ্ট্রভাষার ব্যবহার করতেন তাহলে জনতার মাঝে এই ভাষার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ তৈরী হত। কিন্তু এখানে তো ইংরেজীয়ানার নেশা সওয়ার হয়ে আছে। প্রচার এর আরেকটি উপায় হতে পারে, আমরা যদি ভারতে ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষার পত্রিকাগুলোকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করতে পারি যে তাঁরা নিজেদের পত্রিকার দুয়েকটি কলাম নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রভাষার জন্য দিতে পারে। যদি আমাদের অনুরোধ তারা রক্ষা করেন, তবে এতেও অনেক লাভ হতে পারেন। আমরা তো সেই দিনের স্বপ্ন দেখছি যখন রাষ্ট্রভাষা পূর্ণরূপে ইংরেজীর স্থান দখল করবে, যখন আমাদের বিদ্বানগণ রাষ্ট্রভাষাতেই লিখবেন, যখন মাদ্রাজ এবং মহীশূর, ঢাকা এবং পুনা সকল স্থান থেকে রাষ্ট্রভাষার উত্তম গ্রন্থাদি প্রকাশিত হবে, উত্তম পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হবে এবং পৃথিবীর ভাষা-সাহিত্যের সভায় হিন্দুস্থানী সাহিত্য ও ভাষা গৌরবোজ্জ্বল স্থান পাবে, যখন আমরা ভিক্ষার সুন্দর কলেবরে নয়, নিজের ছিন্নবস্ত্রেই বিশ্বসাহিত্যে প্রবেশ করব। এই স্বপ্ন পূরণ হবে নাকি অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে, এই মীমাংসা আমাদের রাস্ট্রচিন্তার হাতে। যদি আমাদের হৃদয়ে এই বীজ পতিত হয় তাহলে সমগ্র প্রাণশক্তি নিয়ে ফুলে-ফলে ভরে উঠবে। যদি কেবল জিহ্বা পর্যন্ত থাকে তাহলে শুকিয়ে যাবে।
হিন্দী এবং উর্দু সাহিত্যের বিশ্লেষণের উপলক্ষ এটা নয়, আর করতে চাইলেও সময় নেই। আমাদের নতুন সাহিত্য অন্য প্রদেশের সাহিত্যের মতোই এখন পর্যন্ত সম্পন্ন নয়। যদি সকল প্রদেশের সাহিত্য হিন্দীতে আসতে পারে তবে হয়ত একে সম্পন্ন বলা যাবে। বাংলা সাহিত্য থেকে তো তার প্রায় সকল রত্ন আমরা নিয়ে এসেছি এবং গুজরাটী, মারাঠী সাহিত্য থেকেও অল্পবিস্তর আমরা আনতে পেরেছি। তামিল, তেলুগু ইত্যাদি সাহিত্য থেকে আমরা এখনো কিছু নিতে পারিনি। কিন্তু আশা করছি, শীঘ্রই আমরা এই ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়াব, অবশ্যই ঘরের লোক যদি আমাদের সহায়তা করে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পুরোটাই কাব্যময়। যদিও তার মধ্যে শৃঙ্গার এবং ভক্তির মাত্রা অধিক তবুও অনেক কিছু পাঠ করবার মতো রয়েছে। ভক্ত কবিদের রচনা পাঠ করতে চাইলে তুলসী (তুলসীদাস), সুর(সুরদাস), মীরা(মীরাবাঈ) প্রমুখের রচনা পাঠ করুন। জ্ঞানে কবীরের(সন্ত কবি কবীরদাস) কোনো তুলনা হয় না। আর শৃঙ্গার তো এতটাই অধিক যে তাতে এক অর্থে আমাদের পুরনো কবিতাকে কলঙ্কিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সেই কবিদের দোষ নয়, পরিস্থিতির দোষ যার ভেতর এই কবিগণের বাস করতে হয়েছে। সেই জমানায় শিল্প দরবারের আশ্রয়ে বাঁচত এবং শিল্পীকে তাঁর প্রভুর রুচি মেনে রচনা করতে হত। উর্দু কবিদের অবস্থাও একই। সেই জমানার রঙই তাই। আমাদের অভিজাতগণ বিলাসে মগ্ন ছিলেন, প্রেম, বিরহ এবং বিয়োগ-ব্যথা ছাড়া তারা কিছুই বুঝতেন না। যদি কোথাও জীবনের স্বরূপ থাকেও তবে এমন যে জীবন মাত্র কয়েকদিনের, অনিত্য আর এই দুনিয়া দুঃখের ভাণ্ডার, একে যত দ্রুত ত্যাগ করা যায় ততই ভাল। এই অসার বোধ বৈরাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। উর্দু কবিতা আজও সেই রঙ-রূপেই চলছে, যদিও বিষয়ে সামান্য গভীরতা এসেছে। হিন্দীতে নবীনেরা প্রাচীনদের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করেছে। আজকের হিন্দী কবিতা ভাবের গভীরতা, আত্মব্যঞ্জনা এবং অনুভূতির বিশ্বাসে প্রাচীন কবিতা থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। সময়ের প্রভাব তার ওপর নিজের রঙ জমিয়েছে আর তা এখন প্রায় নিরাশাবাদের ক্রন্দন। যদিও কবি এই ক্রন্দনে দুঃখী হন না, বরং বৃত্তের পরিধি এতটা ছড়িয়ে দিয়েছেন যে বড় বড় দুঃখ এবং প্রতিবন্ধকতাকে স্বাগত জানান। আর যেহেতু তিনি সেই ভাবকেই ব্যক্ত করেন যা আমাদের সকলের হৃদয়ে উপস্থিত তাঁর কবিতায় মর্ম স্পর্শ করবার শক্তি অতুল। এ কথা সকলেরই জানা যে অনুভূতি সবার থাকে না এবং যেখানে গুটিকয়েক কবি নিজের হৃদয়ের বেদনার কথা বলেন সেখানে বেশিরভাগ কেবল কল্পনাকে অবলম্বন করে চলেন।
যদি আপনি দুঃখের বিকাশ চান তাহলে মহাদেবী, ‘প্রসাদ’, পন্ত, সুভদ্রা, ‘ললী’, ‘দ্বিজ’, ‘মিলিন্দ’, ‘নবীন’, পণ্ডিত মাখনলাল চতুর্বেদী প্রমুখ কবির রচনা পড়ুন।(হিন্দী-উর্দুতে লেখকের কলমী নামকে উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতর লেখার প্রচলন রয়েছে। – অনুবাদক) আমি কেবল সেই কবিগণের নাম বললাম যাদের নাম আমার মনে পড়ছে, নইলে এমন কবি আরও রয়েছেন যাদের রচনা পাঠ করলে আপনার হৃদয় কম্পিত হবে, আপনি দুঃখের স্বর্গে পৌঁছে যাবেন। কাব্যের আনন্দ উপভোগ করতে চাইলে মৈথিলীশরণ গুপ্ত এবং ত্রিপাঠীজীর কাব্য পড়ুন। গ্রামীণ সাহিত্যের মাটির নিচের গুপ্তধনও ত্রিপাঠীজী খুঁড়ে বের করে আপনাদের সামনে রেখে দিয়েছেন। তার মধ্য থেকে যতটা রত্ন চান আনন্দের সঙ্গে বের করে নিন এবং দেখুন গ্রামীণ গানে কবিত্বের কতটা মাধুর্য, কতটা বৈচিত্র্য। নাটক পাঠের শখ যদি থাকে লক্ষীনারায়ণ মিশ্রের সামাজিক ও বৈপ্লবিক নাটক পাঠ করুন। ঐতিহাসিক এবং ভাবাত্মক নাটকে রুচি থাকলে ‘প্রসাদ’জীর সাজান ফুলবাগানে ভ্রমণ করুন। উর্দুতে সবচেয়ে ভাল নাটক যা আমার চোখে পড়েছে তা ‘তাজ’ রচিত আনারকলি। হাস্যরসের পূজারী হলে অন্নপূর্ণানন্দের রচনা পড়ুন। রাষ্ট্রভাষার সত্যিকারের নমুনা দেখতে চাইলে জি. পি. শ্রীবাস্তবের হাস্যরসের নাটকের দুনিয়া ভ্রমণ করুন। উর্দুতে হাস্যরসের বেশ কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর লেখক রয়েছেন। পণ্ডিত রতননাথ দর এই রঙে আশ্চর্য রকমের সফল। ওমর খৈয়ামের আনন্দ যদি হিন্দীতে পেতে চান তাহলে ‘বচ্চন’ কবির(হরিবংশ রাই ‘বচ্চন’) মধুশালাতে (কাব্যগ্রন্থ) গিয়ে বসুন। তার সুগন্ধে আপনার নেশা ধরে যাবে। গল্পসাহিত্যে ‘প্রসাদ’, ‘কৌশিক’, জৈনেন্দ্র, ‘ভারতীয়’, ‘অজ্ঞেয়’, বিশ্বেশ্বর প্রমুখের রচনায় আপনি সত্যিকার অর্থে জীবনের ঝলক দেখতে পাবেন। উর্দু ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে ‘শরর’, মীর্জা রুসওয়া, সাজ্জাদ হুসেন, নাজির আহমদ প্রমুখ বিখ্যাত। এবং উর্দুতে রাষ্ট্রভাষার সবচেয়ে ভাল লেখক খাজা হাসান নিজামী যার কলমে রয়েছে হৃদয়কে নুইয়ে দেবার ক্ষমতা। হিন্দীর উপন্যাসক্ষেত্রে এখনো ভাল জিনিস খুব কম এসেছে। কিন্তু লক্ষণ বলছে, নতুন অঙ্কুর এই ক্ষেত্রে নতুন উৎসাহ, নতুন দৃষ্টিকোণ নতুন সংবাদ নিয়ে আসছে। এক যুগের এই অগ্রগতি নিয়ে আমাদের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই।
বন্ধুগণ, আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি; কিন্তু ঝগড়ার কথা বাকী রয়েছে যা তুলতে আমার ভয় লাগছে। এতক্ষণ অব্দি একে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু এখন এরও সমাধান করা প্রয়োজন। সেটা রাস্ট্রলিপির বিষয়। বলবার ভাষা তো যেকোনোভাবে এক হতে পারে; কিন্তু লিপি এক হবে কেমন করে? হিন্দী এবং উর্দু লিপির মধ্যে তো আকাশ-পাতাল ফারাক। মুসলমানদের নিকট ফারসী লিপি ততটাই প্রিয় যতটা প্রিয় হিন্দুদের নিকট নাগরী লিপি। সেই মুসলমানও, যে তামিল, বাংলা গুজরাটীতে লেখাপড়া করে, উর্দুকে ধর্মীয় শ্রদ্ধার চোখে দেখে; কেননা আরবী এবং ফারসী লিপিতে সেটুকুই পার্থক্য যেটুকু নাগরী এবং বাংলা লিপিতে, বরং তার চেয়েও কম। এই ফারসী লিপিতে তাদের প্রাচীন গৌরব, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সবকিছু জড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু সৌন্দর্যও তো আছে যার শক্তিতে এই লিপি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এ এক প্রকারের শর্টহ্যান্ড। আমাদেরকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং রাষ্ট্রীয় লিপিরর প্রচার বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে করতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে নাগরী লিপির সংগঠন করা। বাংলা, গুজরাটী, তামিল প্রভৃতি যদি নাগরী লিপি স্বীকার করে নেয় তাহলে রাষ্ট্রীয় লিপির প্রশ্ন অনেকটা মীমাংসা হয়ে যাবে। আর কিছু না হোক কেবল সংখ্যাই নাগরীকে প্রাধান্য দেবে। আর হিন্দী লিপি শেখা এতটা সহজ এবং এই লিপির মাধ্যমে তাদের রচনা এবং পত্র-পত্রিকার প্রচার এতটা বেড়ে যাবে যে আমার অনুমান, তারা একে সহজেই স্বীকার করে নেবে। আমরা উর্দু লিপিকে তো মিটিয়ে দিতে চাইছি না। আমরা কেবল এইটুকু চাই যে আমাদের জাতীয় লিপি এক হয়ে যাক। যদি সমস্ত দেশ নাগরী লিপির হয়ে যায় তাহলে সম্ভবত মুসলমানগণও এই লিপি গ্রহণ করবে। জাতীয় চেতনা তাদের খুব বেশী দিন আলাদা থাকতে দেবে না। মুসলমানদের মধ্যে কি এই স্বাভাবিক ইচ্ছা হবে না যে তাদের পত্রপত্রিকা এবং তাদের গ্রন্থাদি সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ পাঠ করুক? আমরা তো কোনো লিপিকেই মিটিয়ে দিতে চাইনা। আমরা এটুকু চাই যে আন্তঃপ্রদেশীয় যোগাযোগ নাগরী লিপিতে হোক। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন আপনাআপনি মীমাংসা হয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশে এই দাবীতে আন্দোলনও হচ্ছে যে উর্দুর ছাত্রকে হিন্দী এবং হিন্দীর ছাত্রকে উর্দুর এতটা জ্ঞান দান বাধ্যতামূলক করে দেয়া হোক যাতে তারা সাধারণ পুস্তক পড়তে পারে এবং চিঠি লিখতে পারে। যদি সেই আন্দোলন সফল হয়, যার আশা করি আমি, তাহলে প্রত্যেক বালক হিন্দী এবং উর্দু দুই লিপির সঙ্গেই পরিচিত হয়ে যাবে। আর যখন ভাষা এক হয়ে যাবে তখন হিন্দী নিজের পূর্ণতার কারণে সর্বমান্য হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় এর ব্যবহার হতে শুরু করবে। আমাদের কাজ এটুকুই, জনতার মাঝে জাতীয় চেতনাকে এতটা সজীব করে তোলা যাতে তারা রাষ্ট্রীয় হিতের জন্য ছোটোখটো স্বার্থের বলিদান করতে শেখে। আপনারা এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমি জানি, আপনারা ক্ষণিক আবেগের বশবর্তী হয়ে এই সাহস করেননি। বরং এই মিশনে আপনাদের পুরো বিশ্বাস রয়েছে এবং আপনারা জানেন যে এই বিশ্বাস যে আমাদের পক্ষ সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষ, আত্মাকে কতটা শক্তিশালী করে দেয়। সমাজে সব সময় এমন মানুষের লড়াই বাঁধে যারা খাওয়া-দওয়া, ধন আহরণ এবং জীবনের অন্য ধান্দায় ব্যস্ত থাকে। তারা সমাজের দেহ। সমাজের প্রাণ সেইসব হাতেগোনা মানুষ যারা একে রক্ষা করবার জন্য সর্বদা লড়াই করে – কখনো অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, কখনো মূর্খতার বিরুদ্ধে, কখনো কুব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কখনো পরাধীনতার বিরুদ্ধে। এই লড়াকুদের সাহস এবং বুদ্ধি সমাজের অবলম্বন। আপনারা সেই সৈনিকদের অংশ। সৈনিক লড়াই করে, হার-জিতের পরোয়া সে করে না। তার জীবনের ধ্যান, সমষ্টির জন্য সে নিজেকে বলি দেবে। নিজেদের সামনে আপনারা দুরূহতার কাতার দেখতে পাবেন। এও সম্ভব, আপনাদেরকে উপেক্ষার শিকার হতে হবে। লোকে আপনাদেরকে ছিটগ্রস্থ এবং পাগলও বলতে পারে। বলতে দিন। যদি আপনাদের সঙ্কল্প সত্য হয় তাহলে আপনাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই হঠাৎ একদিন সেনানায়ক হয়ে উঠবেন। আপনাদের জীবন এমন হওয়া উচিত যাতে আপনাদের ওপর লোকের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাবোধ থাকে। আপনারা নিজেদের বিদ্যুৎ থেকে অন্যদের মাঝেও বিদ্যুৎ প্রসারিত করুন। প্রতিটি পন্থার বিজয় তার প্রচারকদের আদর্শ জীবনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে উচ্চতর উদ্দেশ্যও নিন্দনীয় হতে পারে। আমার বিশ্বাস, আপনারা নিজেদেরকে অযোগ্য হতে দেবেন না।

সফিকুন্নবী সামাদী
সফিকুন্নবী সামাদী (জন্ম: ১৯৬৩)।অধ্যয়ন: স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর (বাংলা), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। হিন্দী-উর্দু সাহিত্যে আগ্রহী। পিএইচ.ডি গবেষণায় তুলনামূলক আলোচনা করেছেন উর্দু-হিন্দী ঔপন্যাসিক মুন্সি প্রেমচাঁদ এবং বাংলা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের। তাঁর কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ বেরিয়েছে উর্দু এবং হিন্দী থেকে।