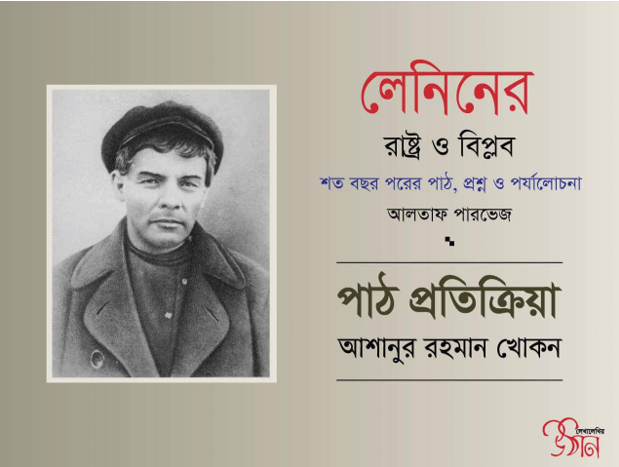এডওয়ার্ড সাঈদ ফয়েজের কবিতার ভক্ত ছিলেন। তাঁর মতে ফয়েজের কবিতা বুদ্ধিজীবীরা পড়ে যেমন আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি আনন্দ পায় সাধারণ মানুষ। তিনি মনে করতেন, ফয়েজের কবিতা এত নিখুঁত ও বিশুদ্ধ যে, সেখানে অনায়াসে শোনা যায় কিটসের ইন্দ্রিয়ময়তা ও নেরুদার তেজ। রণেশ দাশগুপ্ত এভাবে দেখেছেন, ‘ফয়েজের কবিতার বিকাশে ঐক্যের স্বত:স্ফুর্ততা রয়েছে বলেই এলিয়টের প্রথমদিককার কবিতার মতো ব্যতিক্রমের দামামা ধ্বনি নেই; কিন্তু সাবলীলতায় তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে দৃঢ় অতীতে কোন চিন্তা চক্রে যাবার সামান্যতম প্রবণতা থেকে। তাঁর দৃষ্টি সামনে, সে দৃষ্টি উদ্ধত না হয়ে পারে না। সে দৃষ্টি অনেক সময় বড় বেশি কোমল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? সেতো আত্মসমর্পন করেনি মায়া মোহের কাছে। ফয়েজের কবিতা সংগ্রামী তৎকালীন বিশ্ব কবিতার সাথে যুক্ত করে দিয়েছে যাকে সমৃদ্ধ করেছেন মায়াকোভস্কি, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, কুয়ো মোজো, পাবলো নেরুদা ও নাজিম হিকমত।’
ফয়েজের কবিতায় আধুনিকতার চাপে নিজ ইতিহাস, গজলের লিরিক প্রবণতা ত্যাগ আর ভাষার মাঝ দিয়ে বাস্তবের নতুন অর্থ উৎপাদনের প্রয়াস ছিল প্রবল রকম সফল। তাঁর কবিতায় নিজ ইতিহাসের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রবল শক্তি প্রাণ রয়েছে আত্মবিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে। মার্কস অনুসারী খাঁটি আন্তর্জাতিক ছিলেন বলে তিনি নিজ ভাষা ও মানুষের মাঝে প্রবাহমান ভাব, দর্শন, উপমা, উৎপ্রেক্ষাকে অস্বীকার করে যাননি। তিনি বুৃঝেছিলেন, নতুনের আমন্ত্রণ এই পুরেনো মাটিতেই আসর পাতার জন্য। তাঁর সমস্ত জীবন ছিল অনাগতর ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা।
ফয়েজ আহমদ ফয়েজের জন্ম ১৯১২ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত ভারতবর্ষের শিয়ালকোটে। ফয়েজ আরবি ও ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। প্রথমদিকে অমৃতসর ও লাহোরে কলেজে অধ্যাপনা এবং শেষদিকে করাচিতে একটি কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৬ সালে প্রগতিশীল লেখক সংঘে যোগদান করেন ও পাঞ্জাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া, ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত আফ্রো এশিয় লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকার জন্য এক রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৫১ থেকে ১৯৫৪ চার বছর জেল খেটেছেন। ফিলিস্তিনি আন্দোলনের পুরোধা ইয়াসির আরাফাতের অনুপ্রেরণায় আফ্রো এশিয় লেখক সংঘের মুখপত্র লোটাস সম্পাদনা করতেন বৈরুত থেকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদে যোগ দিয়ে ১৯৪৭ সালে লেঃ কর্ণেল পদে থাকাকালীন চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। দৈনিক পাকিস্তান টাইমস সম্পাদনা করেন। লেনিন শান্তি পুরস্কার জয়ী ফয়েজ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। অবিভক্ত পাকিস্থানের শেষ সাধারণ নির্বাচনের আগে করাচি থেকে উর্দু সাপ্তাহিক লাইল-ও-নাহার বের করেন যার ঢাকা প্রতিনিধি ছিলেন বর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য উর্দু কবি আহমেদ ইলিয়াস। আহমেদ ইলিয়াসের ভাষায় ‘পত্রিকাটি বের করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঠিক চিত্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সামনে তুলে ধরা। এই সাপ্তাহিকেই ফয়েজ ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, যদি ১৯৭১, ৩ মার্চের ন্যাশনাল এসেম্বলী ব্যর্থ হয় তবে পাকিস্তানের ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।’ ১৯৮৪ সালের ১০ নভেম্বর তিনি লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।
বাংলাদেশের অনুবাদ সাহিত্যে জাফর আলম পরিচিত নাম। বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাফর আলমের রচিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩০। তিনি উর্দু সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম বিশেষ করে মুন্সি প্রেমচন্দ, মুলক্ রাজ আনন্দ, সা’দত হাসান মান্টো প্রভৃতি প্রথিতযশাদের সাহিত্যকর্ম বাংলার পাঠকের সাথে পরিচিত করেছেন। ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের উপর বইটি সম্পাদনা ও ফয়েজের নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ করে তিনি আরেকবার বাঙালী পাঠকদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন । উল্লেখ্য, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের অনুপ্রেরণায় ১৯৬৯ সালে রণেশ দাশগুপ্ত ফয়েজের অনূদিত কবিতার সংকলন বের করেন যা বাংলা সাহিত্যে ফয়েজ চর্চার ভিত্তি।
বইটি মূলত দু’ভাগে বিভক্ত। এক অংশ ফয়েজের লেখা কবিতার প্রতিনিধিত্বশীল অনুবাদ। আর অন্য অংশে ফয়েজের ব্যক্তিজীবন ও তাঁর সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নিজের রচনাসহ সম্পাদকের আলোচনা, ফয়েজের লেখা অনুবাদ ও কয়েকজনের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।
ফয়েজ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে জাফর আলমের নিজের আলোচনা রক্তের চিৎকার শিরোনামে। রক্তের চিৎকার শব্দদ্বয় ফয়েজ তাঁর কবিতায় কয়েকবার ব্যবহার করেছেন যা শিরোনামটি অর্থবহ হয়েছে। এ নিবন্ধে ফয়েজের ব্যক্তিজীবন ও কাব্যপ্রতিভার সাথে পাঠককে সংক্ষেপে পরিচায় করানো হয়েছে। পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল সাজ্জাদ জহির তাঁর অকৃত্তিম বন্ধু ছিলেন। বামপন্থী হওয়ার কারণে শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের পুরোধা ফয়েজ পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ফলে ১৯৫১ সালে গ্রেফতারের সময় লন্ডন টাইমস ফয়েজকে পাকিস্তানের ‘সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রভাবশালী বামপন্থী’ হিসেবে চিহ্নিত করে।
ফয়েজের কৈশোর ও যৌবন নামের নিবন্ধটি ফয়েজের নিজের বয়ান এবং লেনিন শান্তি পুরস্কার উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণের অনুবাদ শান্তির সপক্ষে লড়াই, দুটোই অনুবাদ করেছেন জাফর আলম। শান্তির সপক্ষে লড়াই ভাষণে ফয়েজ শান্তি ও স্বাধীনতার বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে, ‘শান্তি বলতে আমাদের সবার কল্পনার জগতে ভেসে উঠে গমের ক্ষেত, সফেদার গাছ, নববধুর আঁচল, শিশুর আনন্দিত দোলায়মান হাত, কবির কলম এবং শিল্পীর হাতের তুলি। স্বাধীনতা হলো সেসব অসাধারণ গুণাবলীকে রক্ষা করার আধার।’ ফয়েজের কৈশোর ও যৌবন নিবন্ধে ফয়েজ তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলো দিক তুলে ধরেছেন। বন্ধু খুরশীদ আনোয়ারের অনুপ্রেরণায় ফয়েজ কৈশোর থেকেই সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। খুরশিদের বাড়িতে ওস্তাদ তোয়াকুল হোসেন খান, ওস্তাদ আবদুল ওয়াহেদ খান, ওস্তাদ আশিক আলি খান, ওস্তাদ ছোটে গোলাম আলি খান প্রমুখের গানের আসরে যোগ দেন। আবার দশম শ্রেণির ছাত্র অবস্থা থেকেই ফয়েজ বিভিন্ন মোশায়েরায় অংশ নিয়ে নিজের কবিতা পাঠ করা শুরু করেন। লাহোর রেডিওতে যাতায়াতের সুবাদে ড. তাসির, আলি সরদার জাফরি, জান নিসার আখতার, মঈন আহসান জাজবি, মখদুম মহিউদ্দিন প্রমুখের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে।
সূর্যদগ্ধ পথে একঝলক শীতল মেঘ নিবন্ধটি লিখেছেন ফয়েজের স্নেহধন্য শিল্পী মুর্তজা বশীর। দীর্ঘ এ প্রবন্ধে তিনি তার ব্যক্তি জীবনে শিল্পী হওয়ার স্মৃতি আওড়েছেন যার অনেক অংশ জুড়ে তৎকালীন পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক পরিবেশের সন্ধান মিলে আর তার পরতে পরতে পাওয়া যায় ফয়েজের সাথে তাঁর টুকরো টুকরো স্মৃতির স্ফুলন। এরপর রয়েছে সাংবাদিক ও কবি হাসান ফেরদৌসের ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ: জন্মশত বার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। এ প্রবন্ধে ফয়েজের ব্যক্তি জীবনের নানা দিক থেকে শুরু করে তাঁর সাহিত্য ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জাভেদ হুসেনের ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ: অদৃষ্টের ভাষার খোঁজে কবি প্রবন্ধটিতে মূলত: আধুনিকতা ও উর্দু সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে ফয়েজের কবিতা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া, রয়েছে জাফর আলমের অনুবাদে আসিফ আসলাম ফার্রুকীর মুসাফিরের ঘরে ফেরা যা ফয়েজের সাক্ষাৎকার। প্রবন্ধগুলি ও সাক্ষাৎকারটি ফয়েজ সম্পর্কে যারা জানতে চান তাদের খোরাক মেটাবে। প্রবন্ধ ও নিবন্ধগুলি যেহেতু বিভিন্ন জনের বিভিন্ন সময়ে ও প্রেক্ষাপটে লেখা তাই অনেক সময় ফয়েজের জীবন ও সাহিত্য চর্চার বিভিন্ন দিক ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে।
অনূদিত কবিতার তিনটি বাংলাদেশ ও একটি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে নিয়ে। আলোচিত রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় সোহরাওয়ার্দি ফয়েজের পক্ষে আইনী লড়াই পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ নিয়ে দুটি কবিতা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও অন্যটি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সফর শেষে রচনা করেন। স্বাধীনতার পর ফয়েজ ঢাকা সফরে এলে তাঁর অনেক বন্ধু তাঁর সাথে দেখা করেননি। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন শওকত ওসমান। ফিরে গিয়ে তিনি লিখলেন ঢাকা থেকে ফেরার পর (ঢাকা সে ওয়াপসি)। কবিতাটিতে তাঁর আক্ষেপের সুর তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে:
এত অন্তরঙ্গ হয়েও আমরা পরস্পর
এখনো অপরিচিত
আর কতবার দেখা সাক্ষাতের পর
আবার গড়ে উঠবে বন্ধুত্ব।
বাংলাদেশের মানুষের ওপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে ফয়েজ মার্চ মাসে তাঁর আমার শরীর থেকে দূরে থাক কবিতায় লেখেন:
সাজাব তবে কীভাবে সাজাব গণহত্যার শোভাযাত্রা
আমার রক্তের চিৎকারে কাকে আকর্ষণ করব?
বাংলাদেশকে নিয়ে আরেকটি কবিতা বাংলাদেশ ২ কবিতার কয়েকটি পংক্তি:
প্রত্যেক গাছ রক্তের মিনারের মত
প্রতিটি ফুলও রক্ত মাখা
প্রতিটি চাহনি যেন রক্তের বর্শার তীর
উপরে উল্লিখিত চারটি বাদে আরো ৩৪টি কবিতা অনুবাদ স্থান পেয়েছে যার মাধ্যমে ফয়েজ সম্পর্কে বাঙালী পাঠক কিছুটা ধারণা পাবে।
সম্ভবত উর্দু কবিতার বৈশিষ্টের কারণে ও আজন্ম মাকর্সবাদী হওয়ায় ফয়েজের কবিতায় একদিকে ব্যক্তিজীবনের প্রতিচ্ছবি ও তা থেকে ভবিষ্যতের পথ খোঁজার নিরন্তর প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় যা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমষ্টির মাঝে লীন হয়ে যায়। আবার বিপরীত দিকে, তাঁর কবিতায় সার্বজনীনতার মিলনের আকুতি, মানুষের মুক্তির কথা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। এর এর মাঝেই ব্যক্তি নিজেকে খুঁজে পায়। মনে রাখা দরকার, উর্দু কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট হলো রচিত কবিতার জীবন্ত বয়ান। একজন উর্দু কবি সচরাচর নিভৃতচারী হতে পারেন না। তাঁকে তাঁর কবিতা নিয়ে সুধীমহলে আবৃত্তি করতে হয়। মুশায়েরায় পাঠ করে বাহবা পেতে হয়। আবার তা যদি গজল হয় তবে পরবর্তীতে সুর দিয়ে গান আকারে গীত হয়। তাই কবিতার আঙ্গিক, ছন্দ, কাব্যময়তা, কাঠামো ও পরিশেষে উপস্থাপনা এমন হতে হয় শ্রোতার আসরে তা যেন বাজিমাত করতে পারে। ফয়েজের কবিতা বিশেষ করে গজল এই বৈশিষ্টের বাইরে না। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উর্দু কবিতার যে ডিকশন, রচনাভঙ্গি, ছন্দের প্রকরণ, বাক্যবিন্যাস তা বাংলার থেকে নিতান্তই আলাদা। নিজস্ব। ফলে ফয়েজের মত কবির কবিতা বাংলায় অনূদিত হলে তার পুরোপুরি স্বাদ পাওয়া কঠিন।
ফয়েজের অত্যন্ত বিখ্যাত একটি কবিতা আমার কাছে প্রথম প্রেম চেয়ো না (মুঝসে পেহলি সি মুহাব্বত মেরি মেহবুব না মাং)। কবিতাটির প্রথম পংক্তিই আধুনিক কবিতার সকল বৈশিষ্ট ধারণ করে কবি প্রেয়সির কাছে প্রেম নিবেদন করছেন একেবারে বাস্তবতার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে:
প্রথম প্রেমের মত প্রেম
চেয়ো না আমার কাছে
হে প্রিয়তমা
প্রেয়সীর প্রতি টান তিনি অস্বীকার করছেন না। চিরকাম্য প্রেমাস্পদের প্রতি কামনার জন্যই তো কবির প্রেয়সী:
জগতের যত বসন্ত সব তোমার মুখেরই মুখাপেক্ষী
তোমার দুটি চোখ ছাড়া দুনিয়ার আছেটা কী।
তারপরও কেন কবি আগের মত প্রেম নিবেদন করতে পারছেন না। কবি নিজেই তার সুরাহা করছেন:
অগণন শতকের অন্ধকার অমানবিক সম্মোহক
সিল্ক-সাটিন আর কিংখাবে বোনা জীবনের পাশাপাশি
অলিগলি আর হাট বাজারে মনুষ্যের শরীর বিকোয়
কর্দমে লদপদ রক্তে স্নাত দেহ
যেন আধি ব্যথির ফুটন্ত তন্দুর থেকে নির্গত
এ রকম একটা রাজনৈতিক আর্থসামাজিক পরিবেশে জীবনের জঙ্গমতা, গ্লানি, স্বেদ সবকিছু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এ যেন তাবৎ প্রেমিক প্রেমিকাদের উদ্দেশ্যে কবির নিবেদন বাস্তবতা বোঝার। এখানেই ফয়েজের আধুনিকতা। উর্দু কবিতার বুলবুল, প্রিয়র গলি, ফুল বাগান প্রভৃতি চিরাচরিত উপমার পরিবর্তে সমাজের বাস্তব চিত্র এভাবেই তুলে ধরেছেন। তেমনটি দেখতে পায় আমরা জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। তিনি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বনলতা সেনের কাছে শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন। আবার তিনিই অন্য কবিতায় বর্তমান সময়কে বলছেন ‘অদ্ভুত আঁধার’ কারণ এখন:
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই – প্রীতি নেই- করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যে রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশে ফয়েজকে সাহিত্যচর্চা করতে হয়েছে তাতে কমিউনিস্ট ফয়েজকে বারবার উপমা, উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করতে হয়েছে। আর তা উর্দু সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু ফয়েজ বুলবুল, প্রিয়র গলি, ফুলবাগান প্রভৃতি উর্দু সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল উপমার বদলে সমকালীন রাজনৈতিক উপমা ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন। এখানেই ফয়েজের আধুনিকতা, যুগোপযোগীতা। তাই তো তিনি গালিব ও ইকবালের পর উর্দু কবিতায় গজলের ধারা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে নতুন ধারার প্রবর্তক। তার কবিতায় রোমান্টিকতার সাথে রাজনৈতিক চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ, মেহনতি মানুষের প্রতি দরদ ও তাদের মুক্তির বাণী বারবার উচ্চারিত হয়েছে। লেনিন শান্তি পুরস্কার উপলক্ষে ভাষণে ফয়েজ সাম্যের কথা, সমতার কথা, স্বাধীনতার কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বলেন, ‘এখন মানব সমাজের জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ, বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি এমন স্তরে উন্নীত হয়েছে, যা থেকে প্রত্যেক মানুষই ভালভাবে জীবনধারণ করতে পারে। প্রকৃতির এই অসামান্য খাজাঞ্চিখানা, উৎপাদনের এই অফুরন্ত ভান্ডার মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইজারাদার এবং বিশেষ শ্রেণির ভোগের জন্য নয়। সমগ্র মানবজাতির এই ধন সম্পদ ব্যবহৃত হতে পারে।’ তাই তো তিনি তোমার ভালবাসায় কবিতায় বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন:
এ পৃথিবী তোমার স্মৃতি মুছে ফেলেছে আমার হৃদয় থেকে
রোজগারের বেদনা তোমার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়
সমকালীন রাজনৈতিক ইঙ্গিতময়তার উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। যেমন জেলে জেলে কোলাহল কবিতাটিতে গোলাপ ফুলের কথা বলা হয়েছে যার সাথে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্বাচনী প্রতীকের সাথে একাকার হয়ে গেছে:
জামার কিনারায় গোলাপের সমারোহ
আঁচলে আঁচলে চোখের অশ্রু
গ্রামে গ্রামে রাজকীয় উৎসব
আর শহরে শহরে চলছে আহাজারি।
ফয়েজের কবিতায় আগেই বলা হয়েছে গালিবের প্রভাব লক্ষণীয়। গালিব চেয়েছিলেন, বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে কিন্তু ফয়েজ মনে করতেন কবি-সাহিত্যিকের কাজ শুধু বারি বিন্দুতে দরিয়া দেখা নয়, দেখানোও বটে। তাই ফয়েজের মতে কবির বার্তা শুধু দিব্য দৃষ্টি নয়, সংগ্রামও। পা থেকে রক্ত মুছে ফেল কবিতা চরম আশাবাদ নিয়ে তাই তো কবি ঘোষণা করছেনঃ
পা থেকে রক্ত মুছে ফেল
নরম রক্তাক্ত এই পথ আবার শক্ত হবে
এখান থেকে শত শত নতুন পথ বেরিয়ে আসবে
গ্রন্থ আলোচনায় রণেশ দাশগুপ্তের ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।
ফয়েজ আহমদ ফয়েজ
সম্পাদনা ও অনুবাদ: জাফর আলম
প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রচ্ছদ: আবুল বারক আলভী
লেখাটি ২০১৫ সালের একটি অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল। গুগল করে তা খুঁজে না পেয়ে এখানে প্রকাশ করা হলো জাফর আলমের প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে।
Mazhar Ziban
সম্পাদক, লেখালেখির উঠান । কলেজ জীবন থেকে রূপান্তরবাদী রাজনীতির সাথে জড়িত। সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। একটি বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলেন। অনূদিত কবিতার বই আমিরি বারাকা'র কেউ আমেরিকা উড়িয়ে দিয়েছে। হাওয়ার্ড জিনের নাটক এমা, সম্পাদক: মাঠের পারের দূরের দেশ: দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছোটগল্প সংকলন, সহলেখক: • বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়: বৈষম্য, বঞ্চনা ও অস্পৃশ্যতা মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা বরেন্দ্রী আদিবাসীদের চালচিত্র Colonialism Casteism and Development: South South Cooperation as a 'New' Development paradigm