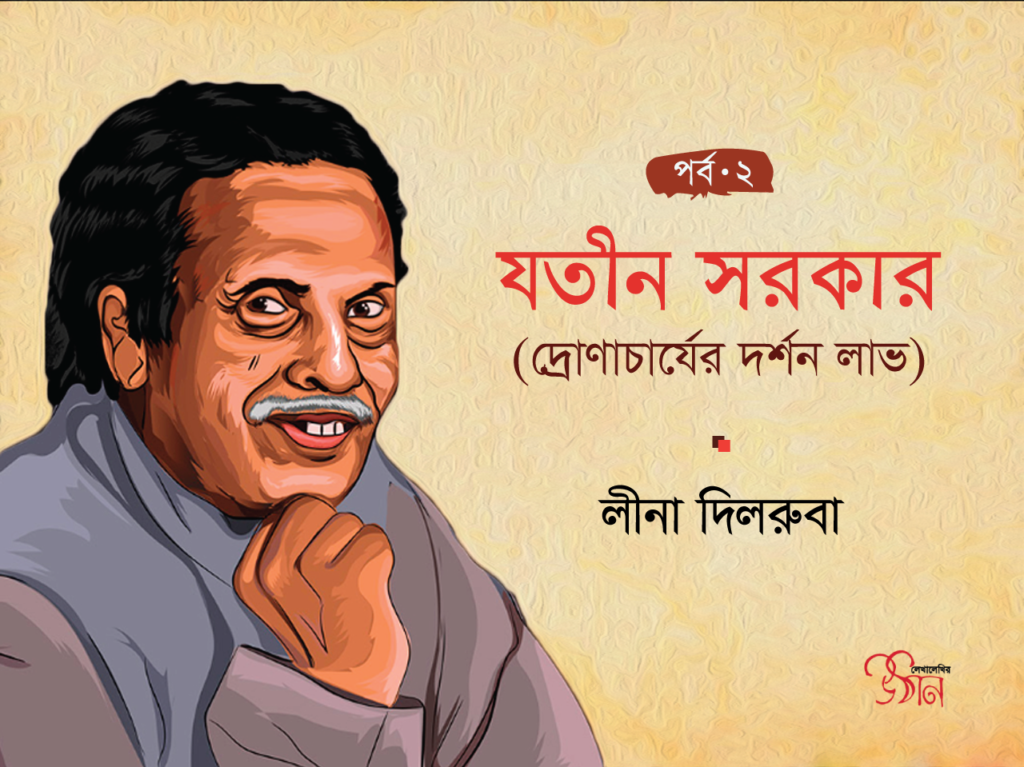তিন.
কথায় কথায় চলে এল নেত্রকোনার কবি গোলাম ফারুক খান এবং পাশের ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার কৃতী সন্তান সুব্রত শংকর ধরের কথা। যুগপৎভাবে এই দুই ব্যক্তি জ্ঞানের তুঙ্গস্থান স্পর্শ করেছেন। দুজনই যতীন স্যারের স্নেহধন্য।
একবার ‘স্থিতধী’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোলাম ফারুক খান প্রথমেই স্মরণ করেন দিব্যজ্ঞানের সেই মহান বাণী- দুঃখেষু অনুদবিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ। অর্থাৎ, দুঃখে যিনি অনুদবিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা হয়।
এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো গোলাম ফারুক খানের সামনে বসে শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি এ-ও বলছিলেন, কেন মানুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে। স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া সহজ কথা নয়। সেদিনের আলোচনার পর আমার শুধু এ-কথাই মনে হয়েছিল, জীবনকে তাৎপর্যময় করতে এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হতে যার এমন অখণ্ড মনোযোগ তিনি কতোই না ব্যতিক্রম! গোলাম ফারুক খান এবং সুব্রত শংকর ধর দুজনই স্থিতধী।
প্রসঙ্গত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী ‘তরী হতে তীর’-এ ভারতের এক সময়ের রাষ্ট্রপ্রধান এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞায় আকাশ স্পর্শ করা গুণী ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, রাধাকৃষ্ণণের সবই ছিল, তবে ইনি ঠিক ‘স্থিতধী’ নন। তাই এই দুই ব্যক্তিকে স্থিতধী আখ্যা দেবার সময় আমাকে সতর্ক দৃষ্টিতে আবারও পেছনে ঘুরে আসতে হল। আমার অনুধাবনে কোনো ভুল নেই তো! নাহ! নেই। যাহোক।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, দেশ-বিদেশে দু’বার পিএইচডি এবং তিনবার এম.এ করা সুব্রত শংকর ধরের পিতা শহীদ মধুসুদন ধর সম্পর্কে স্যার বললেন, ‘গৌরীপুর স্কুলে স্বল্পকালের চাকরি জীবনে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন, সেই সূত্রে সুব্রত আমার সন্তানের মতো।’ যদিও বহুবছর ধরে পুত্রসম এই বিদ্বানের সঙ্গে স্যারের যোগাযোগ নেই বলে তিনি আক্ষেপ করলেন।
অপরজন, কবি গোলাম ফারুক খানের পিতা কবি খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম এবং পিতামহ বিশিষ্ট বাউলসাধক জালাল উদ্দীন খাঁ যতীন সরকারের আকরগ্রন্থ- ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন’ বইয়ের মূল নায়ক।
‘হ্যায় যে কত বই পড়ছে! তার লেখাপড়া খুবই ভালো ছিল, কিন্তু হলে কী হবে, জ্ঞানকে কাজে লাগাল না, কোনো বইপত্র লেখল না’, গোলাম ফারুক খানের কথা বলতে বলতে স্যারকে মাথা নাড়াতে দেখা গেল।
কবি গোলাম ফারুক খান এবং স্যারের আরেক ছাত্র, যিনি আবার গোলাম ফারুক খানেরও শিক্ষক, কবি নূরুল হক- এই দু’জন ব্যক্তি নিজেদের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেননি বলে স্যারকে বেশ হতাশ মনে হল। রাজীব সরকার পাশ থেকে ফোড়ন কাটলেন-‘ফারুক ভাই প্রতিভার অপচয় করলেন; প্রায় কিছুই লিখলেন না!’
স্বপন ধর সম্পাদিত ‘বিদ্যাব্রতী যতীন সরকার’ গ্রন্থের ‘যতীন সরকারের চিন্তাবিশ্ব: একটি চকিত ভ্রমণ’ প্রবন্ধে গোলাম ফারুক খান যতীন সরকারের দর্শন এবং চিন্তা নিয়ে একটি গভীর বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উত্থাপন করেছিলেন, স্যারকে লেখাটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি বললেন, ‘হ্যায় যদি এই লেখাটারও একটা বিস্তৃত আলোচনা করত তবেই তো একটা বই হইয়া যায়। কত কইছি, একদম কথা শুনে না।’
কবি নূরুল হকের কবিতা নিয়েও তিনি বেশ কিছু কথা বললেন। নূরুল হক সম্পর্কে কথাগুলোর সার হল: নীরবে-নিভৃতে থেকে নূরুল হক কবি হিসেবে তেমন নাম করলেন না, অথচ নূরুল হকের কবিতা নির্মলেন্দু গুণের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।
আগেই বলেছি, জরা তাঁর শরীর স্পর্শ করেছে। হলে কী হবে, চোখে যে আশ্চর্য দীপ্তি! লক্ষ করলাম, তিনি খুব হাসেন, তবে হাসিটা হঠাৎ করে আরম্ভ হয়। তাঁর হাসি দেখে আমার চকিতে মনে পড়ে গেল জীবনানন্দের কথা। জীবনানন্দও এমন হঠাৎ করেই উচ্চস্বরে হেসে উঠতেন।
জীবনে চলার পথে ‘বিবেক’ তাঁকে চালিত করেছে। প্রান্তিক এলাকায় বসবাস করেও দেশের একজন প্রধান চিন্তকে পরিণত হওয়া যতীন সরকার সারাজীবন নীতির প্রশ্নে যেমন অটল থেকেছেন, তেমনি জ্ঞানসাধনায়ও ছিলেন গভীরভাবে ব্রতী। সারাজীবন কেবল পড়েছেনই। লেখালেখি আরম্ভ করেছেন পঞ্চাশ বছর বয়সে।
তিনি আপসকামী নন, প্রতি ক্ষেত্রে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে অবিচল থেকেছেন। আমাদের খুব কম প্রাবন্ধিকই যুগ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যতীন সরকার যুগস্রষ্টাদের একজন। সামাজিক ইতিহাসের নতুন ধারা প্রবর্তন করে তিনি ইতিহাস-চর্চায় যেমন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন, সেই-সঙ্গে নানান ধরনের মননশীল গ্রন্থ রচনায়ও ছিলেন উদ্যমী।
‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন’ কেবল মননশীলতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণই নয়, এরসঙ্গে জড়িয়ে আছে সামাজিক ইতিহাসের সুবৃহৎ ক্ষেত্র। বইটির শেষপ্রান্তে তিনি স্মরণ করেছেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের মৃত্যুর মাধ্যমে সৃষ্ট বাংলাদেশের জন্মমুহূর্তের কথা, যেদিন তিনি কল্পনা করতে পারেননি অচিরেই তাঁকে এই দেশে আবার পাকিস্তানের ভূত দেখতে হবে।
এদেশে মৃত পাকিস্তানের প্রেতাত্মাকে অবলোকন করে লেখা সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘পাকিস্তানের ভূত দর্শন’ নিয়ে স্যারের মনোভাব জানতে চাইলাম। তিনি জানালেন, এই বইটি তাঁর নিজের খুব প্রিয় কিন্তু পাঠকরা কেন যেন এটি তেমনভাবে গ্রহণ করেনি। স্যার আমার কাছে প্রশ্ন করলেন, বইটা আমার কাছে কেমন লেগেছে। অকপটে মনের কথাটা বললাম, খুব ভাল লেগেছে।
চার.
সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। একসময় স্যার নিজের ডান-হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শীর্ণ আঙুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দেখলাম তর্জনীর একপাশটা শক্ত হয়ে আছে। জানা গেল ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন’ লিখতে গিয়ে আঙুলের এ-দশা।
পাণ্ডলিপি তৈরিতে বার-বার ভুল-শুদ্ধ যাচাই করা এবং প্রচুর কাটাকাটি করা তাঁর স্বভাব। এই করতে করতে লেখা তৈরিতে অনেক সময় লেগে যায়। যতক্ষণ না পর্যন্ত লেখাটি তাঁর মন জয় করেছে ততক্ষণ তিনি এর উপর কলম চালাতেই থাকেন। আঙুল নিস্তার পাবে কেন!
অবশ্য এসব অতীতের কথা। আশি বছর বয়সে তিনি কলম থামিয়ে দিয়েছেন। এখন আর লেখেন না। কেবল পড়েন। তাও খুব নিয়মিত নয়।
তাঁর প্রিয় বিষয় ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ নিয়ে কথা আরম্ভ হল। স্যার যখন বিএ ক্লাসের ছাত্র তখন তাঁর আত্মোপলব্ধি হয়, জ্ঞানের ভুবনে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্তে না আনলে কারো পান্ডিত্য পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব না। এটি জগৎ ও জীবনকে অবলোকনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
আমার প্রিয় অসমীয়া লেখক হোমেন বোরগোহাঞির এক লেখায় দেখেছিলাম, ‘প্রতিটি মানুষ না হলেও অন্ততঃ কিছু মানুষ জীবনে একজন গুরুর প্রয়োজন অনুভব করে এবং মনে মনে সব সময় একজন গুরুর সন্ধানে থাকে।’ ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ভিত্তিক পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে চারদিকের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আবহ বর্ণনা করতে যতীন সরকার যাঁকে গুরুর স্থানে বসিয়েছেন – ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হচ্ছেন সেই লোক। যিনি যতীন সরকারের মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন।
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শুধু পাভলভপন্থী মনোচিকিৎসক ছিলেন তা নয়, বিজ্ঞান আন্দোলনে তিনি ছিলেন এক পুরোধাপুরুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ‘মানবমন’ পত্রিকা নিয়ে স্যার নানা কথা বললেন। এই পত্রিকায় ছাপানো লেখাগুলোর নিচে ফুটনোটের ব্যবস্থা ছিল। ধীরেন্দ্রনাথ যে-লেখায় ঐকমত্য পোষণ করতেন না, সেটির নিচেই কেবল ফুটনোট জুড়ে দিতেন। যতীন সরকার বাংলাদেশের একমাত্র লেখক যার লেখা ‘মানবমনে’ কোনো ফুটনোট ছাড়াই ছাপা হয়েছিল। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে স্যারের প্রবন্ধ পছন্দ করতেন। যাঁরা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে জানেন তাঁদের কাছে নিশ্চয় এ কথাটা বোধগম্য যে, বিষয়টা কতটা ব্যতিক্রমধর্মী। ধীরেন্দ্রনাথের প্রশ্রয় এবং মনোযোগ পাওয়া অনায়াস ছিল না।
বসার ঘরের দেয়ালের একপাশে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের দুটো ছবি পাশাপাশি ঝুলতে দেখলাম। ‘আমার রবীন্দ্র অবলোকন’ এবং ‘আমার নজরুল অবলোকন’ – দুই নক্ষত্রকে নিয়ে লেখা স্যারের দুটো গ্রন্থের নাম। ধীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যার প্রাসঙ্গিক করলেন রবীন্দ্রনাথকে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সস্পর্কে বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ‘বেঁচে’ ছিলেন।’ স্যার বললেন, খুব কম লোক সম্পর্কেই একথা বলা যায়। একইসঙ্গে স্যার বিশ্লেষণ করলেন ‘বেঁচে’ থাকা শব্দটিকে। আমরা অনেকেই দীর্ঘ আয়ু পাই, তার মাধ্যমে আমরা আসলে জীবন্ত থাকি, ‘বেঁচে’ থাকি না। তাঁর মতে, কেবল রবীন্দ্রনাথই সেই অর্থে দীর্ঘ আয়ু পেয়ে ‘বেঁচে’ ছিলেন। যতীন সরকারের গুরু ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মূল্যায়ন করেছেন বলে তাঁকে সন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গেল।
স্যারের অটোগ্রাফ নেবার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে নিজের সংগ্রহের ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন’ বইটি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেটা ব্যাগ থেকে বের করে স্যারের দিকে বাড়িয়ে দিতেই তিনি একগাল হাসলেন। বইতে লিখলেন, ‘নিজের টাকা দিয়ে লীনা দিলরুবা আমার এই বইটি কিনেছে। আমি তাকে কোনো বই উপহার দিতে পারিনি। এ-জন্যে আমি খুবই দুঃখিত।’ স্যারের দুঃখবোধ নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়েছে, কারণ নজরুল প্রসঙ্গে আলাপচারিতার পর তিনি আমাকে তাঁর লেখা ‘আমার নজরুল অবলোকন’ বইটি উপহার দিয়েছিলেন।
‘বিদ্রোহী’ কবি কাজী নজরুল ইসলাম যতীন সরকারের পছন্দের কবি এবং ব্যক্তিত্ব। প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি গড়গড় করে নজরুলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে লাগলেন।
একজন মার্কসবাদী চিন্তকের নজরুলপ্রীতি আমাকে বিস্মিত করলেও তেমন কিছু বললাম না।
‘আমার নজরুল অবলোকন’ বইতে স্যার লিখে দিলেন–‘আমি যে-দৃষ্টিতে নজরুলকে অবলোকন করেছি, জানি না লীনা দিলরুবা সে-দৃষ্টিতে নজরুলকে দেখবে কিনা।’
জোর দিয়ে বললেন, বইটা যেন আমি পড়ি এবং তাঁকে মতামত জানাই। কথা দিলাম, ‘আমার নজরুল অবলোকন’ দ্রুত পড়ে ফেলব এবং স্যারকে নিজের মতামত জানাব।
প্রসঙ্গক্রমে তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, উত্তরে জানালাম, এসব লেখা এখনো পড়ে উঠতে পারিনি, অচিরেই লেখাগুলো পড়ে ফেলব এবং নিজের মতামত সবিস্তারে তাঁকে জানাব।
কী মনে করে কৌতূহল থেকেই স্যারের কাছে জানতে চাইলাম, দস্তইয়েভস্কি নাকি তলস্তয় কাকে এগিয়ে রাখবেন? স্যার হেসে উঠলেন। ‘এসবের তুলনা হয় না।’
সামলে নিলাম। আবার প্রশ্ন করলাম, তুলনা বিচার নয়, এমনিতেই বলুন, কাকে বেশি ভালো লাগে?
তলস্তয়। তিনি বেশি বিস্তৃত।
বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে কাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?
সত্যেন সেন।
স্যার হাসান আজিজুল হকের কথাও বললেন, হাসানের লেখা তাঁর খুবই পছন্দ।
দুপুর গড়িয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে স্যারের কন্যা সুদীপ্তা সরকার আমাদের মিষ্টি, আম, চা ইত্যাদি পরিবেশন করেছেন। আমি সবই খেলাম, স্যার শুধু আম খেলেন।
—
চলবে… আরো এক পর্বে লেখাটি সমাপ্ত হবে…