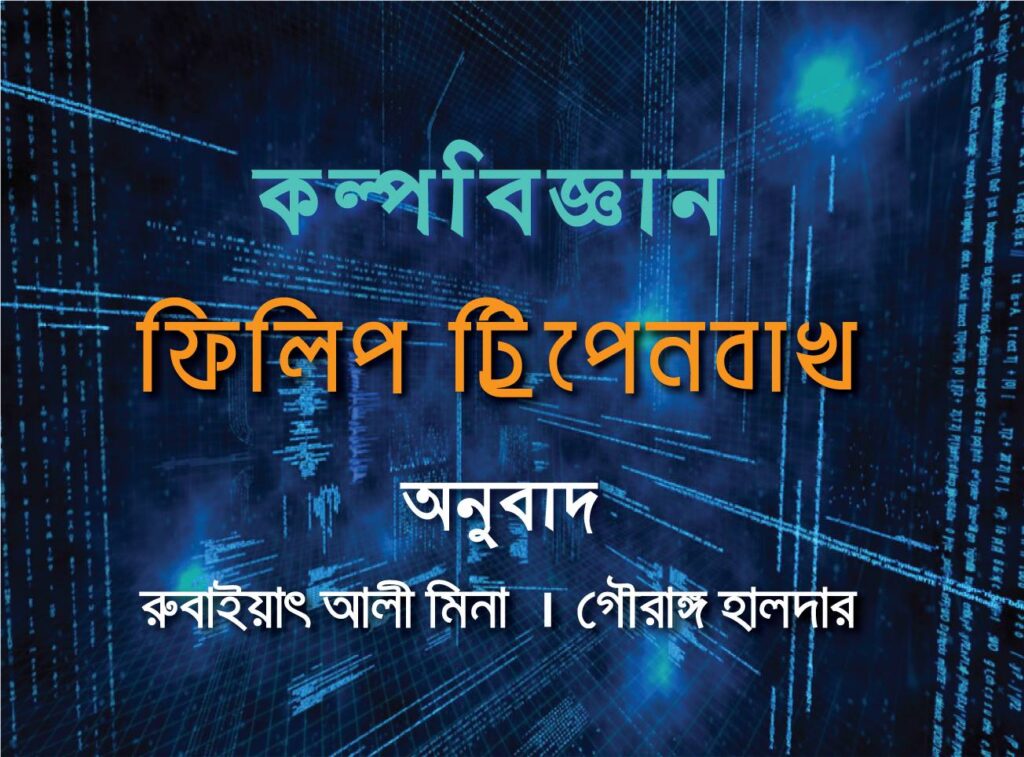[ জিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি (১৮৯৫-১৯৮৬) একজন ভারতীয় দার্শনিক এবং আধ্যাত্ম বিষয়ের উপর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ও বক্তা। তিনি ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডক্টর অ্যানি বেসান্ত এর সান্নিধ্যেই বেড়ে উঠেন। কার্যকর ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক বিপ্লবের চেয়ে মানসিক বিপ্লব এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পাশ্চাত্যে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই প্রবন্ধটি তাঁর The First and the last freedom বইয়ের Individual and Society প্রবন্ধটির অনুবাদ। ]

আরো বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন
যে প্রশ্নটির সম্মুখীন আমরা অনেকেই হই তা হল, ব্যক্তি কি সমাজের তুচ্ছ যন্ত্র মাত্র নাকি সমাজের লক্ষ্য? তুমি আর আমি কি ব্যক্তি হিসেবে সমাজ এবং সরকার দ্বারা শিক্ষিত-নিয়ন্ত্রিত-ব্যবহৃত-নির্দেশিত হই নির্দিষ্ট আকারে গঠিত হওয়ার জন্য, নাকি সমাজ-রাষ্ট্রের অস্তিত্বই ব্যক্তির জন্য? ব্যক্তি কি সমাজের লক্ষ্য, নাকি সে তুচ্ছ পুতুলমাত্র যাকে শেখানো হবে, শোষণ করা হবে, যুদ্ধের যন্ত্র হিসেবে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে? আমরা অধিকাংশই এই সমস্যাটির সম্মুখীন হই। বিশ্বব্যাপীই এটি একটি প্রধান সমস্যা।
কিভাবে তুমি এই প্রশ্নের উত্তর পাবে? সমস্যাটি গুরুতর, তাই নয় কি? যদি ব্যক্তি সমাজ গঠনের ক্ষুদ্র একটি উপাদান হয়ে থাকে, তবে সমাজ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি সত্যি হলে আমাদের ব্যক্তিসত্তা পরিত্যাগ করে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে, সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা পূর্ণগঠিত করতে হবে এবং প্রয়জনে নিঃশেষিত হবার জন্য মানুষকে পরিণত হতে হবে যন্ত্র; কিন্তু যদি সমাজের অস্তিত্ব কেব ব্যক্তির জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে সমাজের কার্যক্রম হবে ব্যক্তিকে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোর উপযোগী না করে তাকে স্বাধীনতার অনুভূতি দেয়া ও স্বাধীনতার প্রতি অনুপ্রাণিত করা। কাজে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল।
সমস্যাটিকে বিশ্লেষন করার কোনো উপায় তোমারে আছে কি? বিষয়টি কোনো অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল নয়, তা বামপন্থীই হোক বা ডানপন্থী, এবং এটি যদি কোনো অধিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল হয়েই থাকে, তাহলে তা শুধুই সাদারণ ধারণা বা বিশ্বাসের ব্যাপার। মতবাদগুলি কেবলি ঘৃণা, বিভ্রান্তি এবং বিদ্বেষের জন্ম দেয়। যদি তুমি বামপন্থী, ডানপন্থী বা পবিত্রগ্রন্থের উপর নির্ভর কর, তবে তোমার নির্ভরতা হবে কেবলই মতবাদকেন্দ্রীক-হতে পারে সেটা ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বৌদ্ধ, খৃস্টান বা অন্য কিছু। এগুলো কেবলই মতবাদ মাত্র, সত্য নয়। সত্য এমনই যা কখনো অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য সত্য সংক্রান্ত মতবাদসমূহ অস্বীকৃত হতেই পারে। যদি আমরা কোনো বিষয়ের সত্যতা আবিষ্কার করতে পারি, তবে মতনিরপেক্ষ কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। কাজেই অন্যরা যা বলছে তা প্রত্যাখ্যান করা কি গুরুত্বপূর্ণ নয়? বামপন্থী অথবা অন্যান্য নেতাদের মতবাদ তাদের আপেখিক অবস্থার ফলাফল। যদি তুমি শুধু বইয়ে পাওয়া ধারণার উপর নির্ভর কর, তাহলে তোমাকে শুধুমাত্র মতামত দ্বারাই পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে হবে, যা মোটেও জ্ঞানসংক্রান্ত বিষয় নয়।
এই বিষয়ে সত্যতা তবে কিভাবে উন্মোচিত হবে? আমরা আপাতত এর ওপরেই আলোকয়াপ্ত করব। বিষয়টির সত্যতা উন্মোচনে সংঘবদ্ধ প্রচারনা হতে মুক্ত থাকতে হবে, অর্থাৎ তোমাকে যেকোনো সমস্যা মতনিরপেক্ষ ভাবে বিচার করতে সমর্থ হতে হবে। শিক্ষার প্রধান কাজ হলো ব্যক্তিসত্তাকে জাগ্রত করা। স্বাভাবিকভাবেই তোমাকে এক্ষেত্রে স্বচ্ছ হতে হবে। অর্থাৎ তুমি কোনো নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল হতে পারবে না। তুমি তোমার বিভ্রান্তি থেকেই নেতা নির্বাচন কর এবং তোমার সকল নেতারাও একইরূপ বিভ্রান্ত। বিশ্বব্যাপী এই চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কাজেই নেতার কাছে দিক নির্দেশনা চাওয়াই ব্যর্থতারই নামান্তর।

কেউ যদি একটি সমস্যার গভীরে যেতে চায়, তাহলে সমস্যাটিকে পরিপূর্ণভাবে বুঝলেই চলে না বরং সেটিকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করতে হয়, যেহেতু বিষয়টি কখনই স্থবির নয়। সমস্যা সর্বদাই নতুন-হোক সেটি ক্ষুধা সংক্রান্ত অথবা মানসিক অথবা অন্য যেকোনো সমস্যা। কাজেই বিষয়টি বুঝতে হলে মনকে সজীব, স্বচ্ছ ও গতিশীল হতে হবে। আমি মনে করি, বিশিরভাগ মানুষই অভ্যন্তরীন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তাড়না অনুভব করে থাকি, যা কিনা একই ভাবে সমাজের বাহ্যিক কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই সমস্যা নিয়েই আমি এবং অন্যান সকল চিন্তাশীল মানুষ উদ্বিগ্ন। অর্থাৎ কিভাবে মৌলিক এবং গতিশীল পরিবর্তন আনা সম্ভব এটিই সমস্যা, কেননা আভ্যন্তরীন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ব্যতীত বাহ্যিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেহেতু সমাজ সর্বদাই স্থবির, তাই অভ্যন্তরীন পরিবর্তন ছাড়া যেকোনো পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া সমপরিমানে নিশ্চল হয়ে পড়ে। তাই তাৎক্ষণিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ব্যতীত কোনো আশাই অবশিষত নেই, কারণ এটি ছাড়া বাহ্যিক কার্যাবলী শুধুমাত্র অভ্যাসগত পুনরাবৃত্তি হয়ে পড়ে। তোমার এবং অন্যের, তোমার এবং আমার মধ্যকার ক্রিয়ার সম্পর্কই হচ্ছে সমাজ। সেই সমাজ গতিহীন হয়ে পড়ে যদি তার কোনো প্রাণসঞ্চারী ক্ষমতা না থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেখানে কোনো আভ্যন্তরীণ ধ্রুব বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সৃষ্টিশীল মানসিক পরিবর্তন না ঘটে। এই ধ্রুব আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের অভাবেই সমাজ নিরন্তর গতিহীন হতে হতে কেলাসিত রূপ ধারণ করে চলছে এবং ফলস্বরূপ ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে। তোমার ভেতরে ও বাইরে যে দুঃখ-দুর্দশা ও বিভ্রান্তি রয়েছে তার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা কোনো ফ্যাসিবাদী সমাজ নয়, বরং তুমি এবং আমিই এর সৃষ্টিকর্তা। তুমি এবং আমি আমাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এর জন্ম দিয়েছি। তোমার স্বরূপ যেমন, অর্থাৎ যেমনটা তুমি চিন্তা কর এবং অনুভব কর, তা বাইরের জগতে প্রতিফলিত হয়েই বাহ্যিক জগৎ গঠন করে। আমরা নিজেরা যদি বিভ্রান্ত-বিশৃঙ্খল হই তার প্রভাব পড়ে সমাজে, যেহেতু তোমার আর আমার সম্পর্কের ফসলই হচ্ছে সমাজ।
তুমি যা জগতও তাই। কাজেই তোমার সমস্যা জগতের সমস্যা। বিষয়টা খুব স্বাভাবিক নয় কি? আমাদের সম্পর্কের এই বিষয়টি দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যায়। আমরা পরিবর্তন আনতে চাই পদ্ধতিগত উপায়ে অথবা মতবাদ এবং মূল্যবোধের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, যদিও সমাজ তৈরি হয় আমাদের হাতেই এবং আমরাই বিভ্রান্তি বা শান্তিময় পরিবেশ তৈরি করি আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতির মাধ্যমে। কাজেই আমাদের সচেতন হতে হবে আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি, কার্যাবলী তথা আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব সম্পর্কে, যেগুলি আমাদের জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাসের সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এগুলিই আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব, তাই নয় কি? আমরা আমাদের জীবিকা, পরিবার এবং স্বজনদের সাথে সম্পর্ক এবং ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাসের মত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তিত। এখন যদি তুমি আমাদের পেশাগত দিকটিকে পরীক্ষা কর, দেখবে এটি মূলত ঈর্ষা আর বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত, এটি শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের মাধ্যম নয়। আমাদের সমাজ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে এটি ক্রমাগত বিরোধ ও লালসা উদগীরণ করে। এর মূল প্রোথিত লোভ, বিদ্বেষ আর ঈর্ষার ভিতর। একজন ক্লার্কের চোখ থাকে সর্বদা ম্যানেজারের পদের দিকে, যেটি প্রমাণ করে যে তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনই নয় বরং সামাজিক অবস্থানে বং সম্মান অর্জন। এ ধরনের আচরণ সাধারণত সামাজিক সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি তুমি এবং আমি শুধু জীবিকা নির্বাহ নিয়েই ভাবতাম তাহলে উপার্জনের এমন এক সঠিক পন্থা খুঁজে বের করতাম যা ঈর্ষাভিত্তিক নয়। সম্পর্কের ভেতর ঈর্ষা সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলোর একটী, যা নির্দেশ করে ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আকাঙ্ক্ষা, এবং যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রাজনীতির দিকে ধাবিত হয়। কেরানী যখন ম্যানেজার হতে চায়, তখন সে শক্তির রাজনীতির বিষয় হয়ে পড়ে, যা কিনা একটি বৃহৎ যুদ্ধ সৃষ্টির সুপ্ত কারণ। তাই সে সরাসরিভাবে যুদ্ধের জন্য দায়ী। আমাদের সম্পর্ক কিসের ওপর নির্ভরশীল? তোমার সাথে আমার, আমার সাথে অন্যের সম্পর্ক যা কিনা সমাজ গঠন করে তার ভিত্তি কিসের ওপর প্রোথিত? নিশ্চিতভাবেই তা ভালবাসা নয়। যদি ভালবাসা থাকত তাহলে শৃঙ্খলা থাকত, শান্তি থাকত, তোমার আমার মাঝে সুখ থাকত। কিন্তু তোমার আমার সম্পর্কের মাঝে অনেক বেশি পরিমাণে বিদ্বেষ রয়েছে যা পরিবর্তিত হয়ে শ্রদ্ধায় রূপ নিয়েছে। যদি আমরা উভয়েই চিন্তায় এবং অনুভূতিতে সমান হতাম, তাহলে শ্রদ্ধাও থাকতো না, বিদ্বেষও থাকতো না। কারণ আমরা তখন মিলিত হতাম দুজন ব্যক্তি হিসেবে, শিষ্য এবং গুরু হিসেবে নয়, কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামী বা স্ত্রী হিসেবেও নয়। যেখানে বিদ্বেষ থাকে, সেখানে শাসনের আকাঙ্ক্ষা থাকে যা হিংসা-রাগ-ক্রোধের উদ্রেক করে দ্বন্দের সৃষ্টি করে। এসব থেকে আমরা পালাতে চেষ্টা করি, যদিও তা আরও বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে।

ধারণা বা মতবাদ, যা কিনা আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের একটি অংশ, আমাদের মানসিকতাকে কি বিকৃত করছে না? আমাদের অধিকাংশ মতবাদই কি তাদের স্বরূপ বিসর্জন দিয়ে ভুল গুরুত্ব বহন করে চলছে না? অতএব যখন আমরা মতবাদের ক্ষেত্রে ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনপ্রণালীতে বিশ্বাসী হই, এমনকি যখন আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হই, তখন তা একটি সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ হতে মানুষকে আলাদা করে মাত্র, যেমন জাতীয়তাবাদ। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা বিশ্বাসের প্রতি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে চলেছি, যা নির্বুদ্ধিতাকেই নির্দেশ করে। বিশ্বাস মানুষকে বিভক্ত করে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে এটি অক্ষম।
যুগপৎ এমন সমাজ কি পাওয়া সম্ভব যা স্থবির কিন্তু সেই সমাজেরই প্রত্যেকের মাঝে বিরামহীনভাবে সংঘটিত হচ্ছে বিপ্লব? সামাজিক বিপ্লব অবশ্যই হতে আভ্যন্তরীণ এবং মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আমরা অনেকেই সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন দেখতে চাই। এটাই সেই যুদ্ধ যা সমাজতন্ত্রবাদ বা অন্য যেকোনো উপায়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে বিশ্বব্যাপী চলছে। এখন যদি কোনো সামাজিক বিপ্লব ঘটে থাকে, যা কিনা সমাজের বাহ্যিক কাঠামোতেই শুধু সংঘটিত হয়েছে, সেই সামাজিক বিপ্লব যত মৌলিক হোক না কেন এর মূল প্রকৃতি খুবই স্থবির হবে, কারণ সেখানে ব্যক্তির আভ্যন্তরীন বিপ্লব এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটে না। কাজেই কার্যকর একটি সমাজ গঠনের দরকার প্রাণবন্ত একটি সমাজ যা স্থবির এবং খন্ডিত নয়। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ: বিপ্লব অবশ্যই ব্যক্তির মানসিক কাঠামোতে হতে হবে কারণ আভ্যন্তরীণ মানসিক বিপ্লব ছাড়া তুচ্ছ বাহ্যিক পরিবর্তনের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। যত বেশি পরিমাণে আর যত দক্ষতার সাথেই আইন প্রণয়ন করা হোক না কেন, যেখানে ভেতরে বিপ্লব না ঘটিয়ে শুধু বাইরের আবরণেই পরিবর্তন আনা হয়, সমাজ সর্বদাই সেখানে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। আমি মনে করি, এর নিন্দা না করে বরং একে বোঝাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্যিক কার্যাবলী সংঘটিত হওয়ার পরেই শেষ হয়ে যায়, স্থবির হয়ে পড়ে। যদি সমাজ আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলাফল না হয়ে থাকে, তবে এটি ব্যক্তিকে নিঃশেষ করে দেয় এবং সমপরিমাণে স্থবির এবং গতানুগতিক করে ফেলে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করলে এ বিষয়ে মতৈক্য বা মতবিরোধের প্রশ্নই আসে না। এটি সত্য যে সমাজ সর্বদা ব্যক্তিকে নিঃশেষিত করছে এবং বিরতিহীন ও সৃষ্টিশীল বিপ্লব শুধুমাত্র ব্যক্তিতেই ঘটা সম্ভব, সমাজ বা বাহ্যিক কিছুতে নয়।আমরা দেখতে পাই, বর্তমানে সমাজ ভারত ও ইউরোপ-আমেরিকাতে অর্থাৎ প্রত্যেক অংশে কিভাবে দ্রুততার সাথে খন্ডিত হচ্ছে। বিষয়টি অবশ্য আমরা আমাদের নিজেদের জীবন থেকেই অনুবাধন করতে পারি। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ই এটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সমাজ যে টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে এটি বলার জন্য কোনো বড় ইতিহাসবিদের প্রয়োজন নেই। সমাজ গড়তে নতুন স্থপতির প্রয়োজন আর প্রয়োজন আবিষ্কৃত সত্য এবং মূল্যবোধের। কিন্তু এ ধরণের স্থপতির আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই। আমরাই সমাজকে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়তে, খন্ডিত হতে দেখি ফলত আমাদের অর্থাৎ তোমাকে এবং আমাকেই হতে হবে স্থপতি। মূল্যবোধগুলো পুনরায় আবিষ্কার করতে হবে আরও মৌলিক স্থিতিশীল ভিত্তির উপর; কারণ আমরা যদি পেশাগত স্থপতি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নির্মাতার উপর নির্ভর করি, আমরা ঠিক আগের জায়গাতেই থাকব, যেখানে আগে থেকেই ছিলাম।
প্রবন্ধটি ইংরেজিতে পড়তে ক্লিক করুন
তুমি বা আমি সৃজনশীল নই, আমরাই সমাজকে এই বিশৃঙ্খলা ঠেলে দিয়েছি, কাজেই এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের অবশ্যই সৃজনশীল হতে হবে এবং সমাজের অকার্যকর অবস্থার কারণগুলি খুঁজে বের করে নতুন ভিত্তি স্থাপন করতে হবে, এই ভিত্তি হবে সৃজনশীল উপায়ে, অনুকরণশীলতা দিয়ে নয়। এর জন্য প্রয়োজন নেতিবাচক বা নঞর্থক চিন্তাধারা। নঞর্থক চিন্তা হল বোধগমত্যতার জগতে সর্বোচ্চ পর্যায়। সৃজনশীল চেতনাকে বুঝতে হলে আমাদের সমস্যাটির গভীরে যেতে হবে নঞর্থক উপায়ে। ইতিবাচক মানসিকতায় অগ্রসর হলে নতুন করে অনুকরণশীলতারই উদাহরণ তৈরি হবে। সমস্যার প্রকৃতি বোঝার জন্য আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে নঞর্থক উপায়ে; ইতিবাচক পদ্ধতি, ইতিবাচক প্রণালী বা ইতিবাচক উপসংহারে নয়।
সমাজ কেন ভেঙ্গে পড়ছে? অনেকগুলো মৌলিক কারণের একটি হচ্ছে ব্যক্তি, অর্থাৎ তুমি নিজেকে সৃজনশীল হওয়া থেকে বিরত রেখেছো। তুমি এবং আমি অনুকরণপ্রিয় হয়ে উঠছি; আমরা অনুকরণ করছি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে। বাহ্যিকভাবে আমি যখন কিছু শিখছি স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কিছু অনুকরণশীলতা চলে আসবে। আমি ভাষা অনুকরণ করি, আমি যন্ত্রকৌশল অনুকরণ করি। প্রথমে কৌশন শিখার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুকরণশীলতা আবশ্যক। কিন্তু যখন আমরা মনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আসি, তখন মানসিক অনুকরণশীলতার দরুন সৃজনশীলতা বর্জন করি। আমাদের শিক্ষা, সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় জীবন সবই অনুকরণের উপর নির্ভরশীল; অর্থাৎ আমি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অথবা ধর্মীয় রীতির আওতাধীন। আমি সত্যিকার অর্থ একজন ব্যক্তি হয়ে ওঠা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছি; মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমি নির্দিষ্ট কিছু শর্তশাপেক্ষে বরাবর একই প্রতিক্রিয়া প্রদানের তুচ্ছ যন্ত্রে পরিণত হয়েছি- হোক সেটা হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, জার্মান অথবা ইংরেজ। আমাদের প্রতিক্রিয়াগুলো সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী আপেক্ষিক, সেটি প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যই হোক আর ধর্মীয় অথবা বস্তুবাদীই হোক। সুতরাং সমাজের খন্ড খন্ড হওয়ার মৌলিক কারণগুলোর একটি হল অনুকরণ।
বিভক্ত হতে থাকা সমাজের প্রকৃতি বোঝার জন্য তুমি ও আমি সৃষ্টিশীল হতে সক্ষম কিনা তা অনুসন্ধান করাটা কি গুরুত্বপূর্ণ নয়? আমরা দেখতে পাই যে, যেখানেই অনুকরণ সেখানেই বিভক্তিকরণ; আর যেখানেই কতৃত্ব সেখানেই অনুসরণ। প্রকৃতরূপে সৃষ্টিশীল হতে গেলে সকল প্রকার কর্তৃত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। তুমি কি লক্ষ্য করনি সৃষ্টিশীলতার মুহূর্তগুলিতে, যেমন-গভীর আগ্রহ বিষয়ক কিছু আনন্দের মুহূর্তের কোন পুনরাবৃত্তি নেই? এরকম মুহূর্তগুলি সবসময়ই নতুন, সহজ, সৃষ্টিশীল ও আনন্দময়। সুতরাং আমরা দেখছি যে সামাজিক বিভক্তিকরণের মূল কারণ হলো অনুকরণ, অর্থাৎ ক্ষমতার উপাসনা।