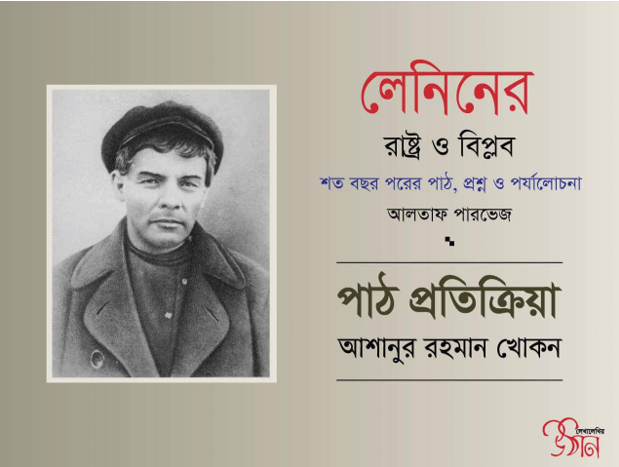মানুষ সাধারণ থেকে বিশেষ হয়ে ওঠে তার কাজের মাধ্যমে। সেই কাজের প্রতি থাকতে হয় নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা আর কঠোর পরিশ্রম। এবং অবশ্যই স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পূরণের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এসবের মিশেল ঘটলে সাফল্য এসে কড়া নাড়ে দোরগোড়ায়। তখন ইতিহাস কোল পেতে দেয় সেই বিশেষ হয়ে ওঠা মানুষটির জন্য। সম্রাট বাবুর(এই নামটিই বই এ ব্যবহার হয়েছে)এমনই একটি নাম যাকে ইতিহাস ঠাঁই দিয়েছে পরম মমতায় এবং অশেষ গৌরবে। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে গেঁথে যাওয়া এই নামটি ইতিহাসের পাতা থেকে হীরকের ন্যায় দ্যুতি ছড়াচ্ছে…
ফারগানা(বর্তমানে উজবেকিস্তান)একটি ছোট্ট দেশ যার উত্তর-পশ্চিমে শাইহুন নদী আর অবশিষ্ট অংশ বালুকাময় পার্বত্যভূমি দিয়ে ঘেরা। এই পাহাড়ি উপত্যকার সাতটি নগর ছিল। যার একটি আন্দিজান। বসন্ত ঋতুতে মনোহর রূপ ধারণকারী এই আন্দিজান ফারগানার রাজধানী। এর সড়কের কিনারে কিনারে আনার ও খুবানির বাগিচা, ক্ষেতে আঙুর, নাশপাতি, তরমুজের মতো রসালো ফল আর দিঘিতে নীল ফুল, টিউলিপ, গোলাপের বিপুল সমারোহ। এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময়তায় ঘেরা পরিবেশে ১৪৮৩ সনের ১৪ ফেব্রুয়ারি জহির-উদ-দিন মুহম্মদ বাবুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফারগানার শাসক উমর শেখ মির্জার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মায়ের নাম কুতলক নিগার খানম। নিজেকে মঙ্গোল বা মোগল বলে অভিহিত করতেন বাবুর। কারণ “পিতার দিক দিয়ে বাবুর মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত বিজেতা এবং ভারত জয়ী বীর আমির তাইমুরের চতুর্থতম অধঃস্তন এবং মায়ের দিক দিয়ে মোগল বীর চেঙ্গিস খানের চতুর্দশ অধঃস্তন ছিলেন।” বাবুরের মাতৃভাষা ছিল চুগতাই বা চুগতাই তুর্কি। এছাড়া তিনি সংস্কৃতিবানদের প্রধান ভাষা ফার্সিও জানতেন। তবে চুগতাই তুর্কিতেই বাবুর তাঁর আত্মজীবনী ‘তুজুক-ই-বাবরী’ লিখেন। পরে এটি ফার্সিতে অনূদিত হয়ে সুবিখ্যাত হয়ে ওঠে। “চুগতাই তুর্কির ভাষা ফার্সির মতোই আরবি লিপিতে লেখা হয় এবং সে ভাষা তার গঠনশৈলী, যেমন শব্দগঠন, বাক্যগঠন, ব্যাকরণ প্রায় সবটাই ফার্সির অনুসারী।” সুন্দর চেহারার আন্দিজানিরা সবাই তুর্কি ছিলেন। বাবুর ফার্সি জানলেও তাঁর আত্মজীবনীতে চুগতাই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন হয়তো মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষার প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা থেকে। কেননা, পরবর্তীকালে মাতৃভূমির প্রতি নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার অব্যাহত প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।
১৪৯৪ সনে মাত্র এগারো বছর বয়সে বাবুর পিতৃরাজ্য ফারগানার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে কিছুদিনের মধ্যেই সিংহাসন হারিয়ে যাযাবর হয়ে পড়েন। তখন কিছু বন্ধু আর কৃষকশ্রেণির লোকের সাথেই যোগাযোগ ছিল। এমন অসহায় অবস্থায় একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। রাজ্য হারালেও তা ফিরে পাবার স্বপ্নকে অতি যত্নে বুকে লালন করে রেখেছিলেন। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় মাত্র বারো-তেরো বছরের একটা বালক পথ চলছেন। অতঃপর পিতার আমলের কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সহায়তাত ১৪৯৭ ঈসায়ী সনে সমরখন্দের উজবেক নগরে আক্রমণ চালান। সাতমাস পর সমরখন্দ জয় করেন। এরপর ফারগানা জয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলে কাছের জনরা তাঁকে ছেড়ে যান এবং বাবুর ফারগানা ও সমরখন্দ দুইই হারিয়ে ফেলেন। সব হারিয়ে ১৫০৪ ঈসায়ী সনে বাবুর খুরাসান যাত্রা করলেও পরে মত বদলে কাবুলের পথে যান। বুদ্ধিমত্তা আর বুদ্ধিদীপ্ত ও অভিনব রণনীতি প্রয়োগে বাবুর কাবুল ও গজনী জয় করেন।
“কাবুলে বিজয়াভিযান, বাবুরের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তার বলে প্রমাণ হয়েছিল। কেননা, কাবুল অভিযানই তাঁর জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের নতুন দ্বার খুলে দেয়। তিনি যদি কাবুল জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করে নিজের মনোযোগ সমরখন্দ, বুখারা, ফারগানা ও সেখানকার আশেপাশের গোত্রগুলোর উপর নিবদ্ধ করতেন তাহলে হার আর জিতের মধ্যেই তাঁর জীবন কেটে যেত। তিনি তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য এক বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে পারতেন না।”
বাবুর কাবুল জয় করে হিঁদুস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন ১৫০৫ এর জানুয়ারিতে। বলছেন, “কাবুল হিঁদুস্তানের সীমান্ত ক্ষেত্র ছিল নিংগনহর। আমরা ওই পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম। এখন আমার সামনে এক নতুন দুনিয়া দেখার সুযোগ ছিল। সেখানকার তৃণভূমি, সেখানকার গাছপালা, পশুপাখি সবকিছু আমার দেখা দুনিয়া থেকে আলাদা ছিল।” বাবুরের ভাষায় বিস্ময়কর ভূমির এই দেশকে জয় করার উদ্দেশ্যে চারবার রওনা হয়েও ফিরে আসেন। কিছুটা প্রাকৃতিক আর কিছুটা রাজনৈতিক কারণ ছিল এর পেছনে। অবশেষে পঞ্চমবার বাবুরের ভারতজয় সম্পন্ন হয়। ২১ এপ্রিল ১৫২৬ পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদিকে পরাজিত করে পুত্র হুমায়ূনকে নিয়ে দিল্লি ও আগ্রা জয় করেন। অবশ্য সম্পূর্ণ দিল্লি সালতানাত বাবুরের অধিকারে আসে ১০ মে ১৫২৬ ঈসায়ী সনে। তিনি দিল্লি জয়ের পূর্বে তাঁর সৈন্যদের এই বলে উৎসাহিত করতেন যে, “আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের বিজিত ভূমি পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমরা হক (ন্যায়ধর্ম)-এর উপরে আছি। ধর্মের জয় সর্বত্রই।” ইসলামি সুন্নি মতের অনুসারী বাবুরের নিজ স্রষ্টা আর নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর বেশ আস্থা ছিল। তিনি ভারতকে নিজের পূর্বপুরুষদের অধিকৃত ভূমি মনে করতেন কারণ তাইমুর ভারত জয় করেছিলেন। বাবুর এই যুদ্ধে ‘তুলুগামা’ নীতি প্রয়োগ করেন। এটাকে ইংরেজিতে Ottoman Fashion বলা হয়। অর্থাৎ এটা তুর্কিদের যুদ্ধনীতির সাথে সম্পর্কিত। এখানে ডানে-বামে শত্রুসেনাকে ধাওয়া করা হতো আর সামনে অবরোধ থাকতো এবং পিছনে কামান বসানো থাকতো। এখানে বাবুর কামান ব্যবহার করেন যেটা ভারতবর্ষে নতুন ছিল। বাবুরের প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিনশ বছরের অধিককাল শাসন করে। বাবুর, হুমায়ূন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহাঁ, ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারের ধারা অব্যাহত থাকে। “ঔরঙ্গজেবের পর সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়ে যায় এবং অবশেষে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ‘জাফর’ পর্যন্ত এসে তা নিঃশ্বেস হয়ে যায়।” তিনি ইংরেজদের অধীনে নামেমাত্র বাদশাহ ছিলেন।
বাবুর বিশ্বাস করতেন “যুদ্ধ অস্ত্রবলে নয়, বুদ্ধিবলে জিততে হয়।” যুদ্ধবাজ এই মানুষটি তাঁর প্রিয় সমরখন্দ জয় করেন ১৫১১ ঈসায়ী সনে। তাঁর হাতছাড়া হওয়া রাজ্যগুলোকে জয় করতে তাঁকে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। একজন প্রকৃত বীর এবং প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতার মতো তিনি সময় আর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছেন। বারবার হারিয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন কিন্তু কখনো নিজের অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে থাকেননি। এটা তাঁর সফলতার অন্যতম রহস্য। তিনি কথা দিয়ে কথা রাখতেন বলে তাঁর প্রজাদের আস্থাভাজন হতে পারতেন দ্রুত। ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে তিনি অনেক ছোট ছোট রাজ্য জয় করেন। আফগান উপজাতিদের অধীনে থাকা অনেক এলাকা তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তিনি এসব জায়গায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে প্রধান নির্বাচন করে তাদের হাতে শাসনভার তুলে দিতেন। তিনি তাঁর বিজিত রাজ্যের সংস্কৃতি তথা রীতি-রেওয়াজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এটা তাঁর বিশেষ গুণ ছিল। এমনকি তিনি তাঁর সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দেশের এবং গোত্রের লোক নিতেন।
আল-সুলতান-এ-আজম, ওয়ালি-এ-সকম; আল মুকাররম, বাদশাহ-এ-গাজী, জহির-উদ-দিন মুহম্মদ বাবুর মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ১৫৩০ ঈসায়ীর ২৬ ডিসেম্বর আগ্রায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে দিল্লিতে দাফন করা হয়। পরে তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যুর নয় বছর পর শেরশাহ সূরী তাঁকে কাবুলে দাফন করেন। নিজের জন্মভূমি থেকে একদা বিতাড়িত বাবুর তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নির্দিষ্ট আবাস্থল রেখে যান। দিল্লি জয়ের পর পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর নয়জন পত্নী ও সাতজন সন্তানের কথা জানা যায়। ফারগানা থেকে দিল্লির পথে বাবুরের সফল যাত্রা। মধ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির অঙ্গনে এক সফল শাসকের দৃপ্ত পদচারণার কথা ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে।
বাবুর পারস্যের শব্দ। ইংরেজিতে একে Leopard বলে। সত্যিকার অর্থেই তিনি বাঘের মতো সাহসী ছিলেন। শারীরিকভাবেও ভীষণ শক্তিশালী ছিলেন। আর তাঁর মানসিক শক্তি তথা দৃঢ়তার কথা তো কিংবদন্তিতূল্য। মাত্র এগারো( কোথায় বারো বছর বলা হয়েছে) বয়সে ক্ষমতায় বসেন। সেটা হারিয়েও ফেলেন। কিন্তু স্বপ্ন আর মনোবলকে হারাননি এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বালক। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখা যায় পুত্র হুমায়ূনকে তিনি যুদ্ধবিদ্যা তথা রণকৌশল শেখাচ্ছেন। কিন্তু বাবুরকে শেখাবার কেউ ছিল না। বলা হয়ে থাকে যে পথ চলতে চলতে বাবুর শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের পথ পেরিয়েছেন। পথই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে। বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে জীবন আর জগৎকে চিনেছেন এই অকুতোভয় মানুষটি। জীবনের অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তাঁর হাতে ধরা পড়েছে। তাই কিছুটা প্রকৃতি তাঁর শিক্ষক আর কিছুটা নিজেই অর্থাৎ যাকে বলে স্বশিক্ষিত।
“বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন বাবর। তিনি এক হাতে অসি ও আরেক হাতে মসি নিয়ে বিশ্বজয়ের পথে বেরিয়েছিলেন। অসি দিয়ে তিনি ভুবন জয় করেছেন। তাঁর অসির খ্যাতি ভারত বিজয় ও তার ইতিহাস, মসীর[মসি] খ্যাতি বিশ্ববিখ্যাত ‘বাবরনামা’ তাঁর আত্মকথা রূপে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বাবর চুগতাই তুর্কি সাহিত্যের ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর অনেক কবিতা ও অন্যান্য রচনা রয়েছে। বর্তমানে উজবেকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাবর একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রূপে বরণীয়। সে দেশের পাঠ্য পুস্তকে তাঁর রচনা ওই দেশের প্রামাণ্য রচনা হিসেবে পাঠ্য। তিনি ভাষাবিদ পণ্ডিত, লিপি বিশারদ। তাঁর রচনাশৈলী অত্যন্ত মার্জিত এবং সুখপাঠ্য।”
বাবুর সম্পর্কে সমালোচকের এই মত প্রণিধানযোগ্য। যা-ই হোক, ‘বাবরনামা’ তো একজন যুদ্ধবাজ শাসকের বীরত্বের কাহিনি তারপরেও কেন এর বিশ্বব্যাপী এত জনপ্রিয়তা? এটি আর দশটা সাধারণ যুদ্ধজয়ের আখ্যান নয়। এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একজন শিল্পীর স্পর্শ। এখানে বাবুরের শত্রুর মস্তক ছেদন করার গল্প যেমন আছে তেমন আছে একজন ভাবুক মনের মানুষের কল্পনার প্রকাশ। আছে অভাবিত রণকৌশলের কথা, আছে জয়ী হওয়ার দৃঢ় সংকল্পের কথা, আছে পরাজয় বরণের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা, আছে কাছের মানুষদের বিশ্বাসভঙ্গের কথা, আছে সাম্রাজ্য জয়ের পর নতুন দেশের মানুষের আনুগত্য প্রদর্শনের কথা। শৌর্যবীর্য নিয়ে বাগাড়ম্বর নয়, আছে কুসংস্কারমুক্ত, দায়িত্ব ও নীতিবান, প্রজাহিতৈষী একজন আধুনিকমনস্ক মানুষের কথা। আর এখানেই এই লেখাটা দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে সকলকালের পাঠকের আগ্রহের জায়গা দখল করে নেয়। আজকের মানুষের লড়াইয়ের গল্পটা অনেকাংশে মিলে যায়। রাজ্য জয়কে যদি স্বপ্ন জয়ের সাথে তুলনা করি তবে। কেননা, আধুনিক মানুষকেও শত প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে যেতে হয় প্রতিনিয়ত। মধ্যযুগের একটা মানুষের লড়ায়টা তাই কালের সীমানা পেরিয়ে বর্তমানেও প্রাসঙ্গিকতা পেয়ে যায় অনায়াসে। আমাদের জানার অনেককিছু আছে এখান থেকে আছে শেখার এবং উপভোগ করারও। এ তো গেল দেশজয়ের প্রসঙ্গ। তবে এই গ্রন্থটির আরও অনন্যতা রয়েছে। এটা একজন সম্রাটের নিজের হাতে লেখা আত্মজীবনী যাতে রয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর ভাষার কারুকাজ। অর্থাৎ এর শৈল্পিক তথা নান্দনিক দিকটি। বাবুর যখন যেখানে যুদ্ধযাত্রা করেছেন তখন সেখানকার প্রকৃতি, মানুষ আর তাদের রীতি-রেওয়াজ নিয়ে কথা বলেছেন। যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতা নিয়ে তথা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সে জায়গা জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। তাঁর দেখার ভঙ্গি, সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি আর ভাষার লালিত্য বিষয়কে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর লেখা থেকে যেখানে কাবুলের একটা জায়গার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে—
“এখানকার পাহাড়ি উপত্যকা-ঘেরা পথকে হাঁটা-পথ বলে। . . .
এই হাঁটা-পথে(টিউলিপ-নলিনী, চমকদার ফুলের গাছ) রঙ-বেরঙের নলিনী ফুলের বাহার দেখার মতো। এখানে এরকমই বহু-রঙের ফুল দেখা যায়। এই স্থান অতিক্রম করার সময় আমি ৩২-৩৩ পর্যন্ত রঙের ফুল গুনতে পেরেছিলাম। আমি এক রকমের নলিনী ফুলের নাম দিলাম ‘গোলাপি সুগন্ধীযুক্ত’। . . . ওই ফুল দেখতে ছিল লাল গোলাপের মতো, তা থেকে লাল গোলাপের মতো সুঘ্রাণ ভেসে আসত। এখানে নলিনী ফুলের চাষ করা হয় না। দাস্তে-শেখের সমভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে হয়, দূর-দূরান্ত পর্যন্ত রঙ-বেরঙের ছটা বিচ্ছুরিত হয়।
. . . নলিনী ফুলের বাহারের কারণেই ঘুরবন্দের পাহাড়ি এলাকাটি পর্যটকদের কাছে বড়ই আকর্ষণীয় হয়ে রয়ে গেছে।”
কিংবা,
“এখানে কঠিন বরফাকৃত পাহাড় বারো মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। . . .
এখানকার মানুষদের জীবনযাত্রা দ্রুতগতিসম্পন্ন। এখানকার প্রধান নদী হরমন্দ্, সিন্ধু, কন্দালের দুঘাব এবং বলখ্-আব—এই চার নদী দূর-দূরান্ত অবধি বয়ে যায় না। এই চারটির মধ্যে দূরত্ব এতটুকুই যে, কোনো ব্যক্তি সাফরে[সফরে] বেরোলে একদিনের সফরেই এই চার নদীর পানির স্বাদ নিতে পারবে।”
এভাবে বাবুর তাঁর লেখায় সময়, স্থান আর ব্যক্তিমানুষকে অমর করে রেখেছেন। তবে এসব বেশিরভাগই ফারগানা, আফগান, কাবুলের কথা। ভারতবর্ষ নিয়ে বিশেষকিছু বলা নেই তার এই লেখায়। কারণ হয়তো রাজনৈতিক হতে পারে। কেননা, দিল্লি অধিকার করলেও অন্যান্য অংশের উপর আধিপত্য বিস্তারের লড়ায় চলছিল। এসময় লাগাতার যুদ্ধে রত থাকায় বাবুর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এছাড়া গ্রন্থটির শেষের দিকের কিছু পাতাও বিনষ্ট হয়। আর কয়েক জায়গায় ধারাবাহিকতার অসমঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। এটা হয়তো বাবুরের বন্ধুর পথে অসহনীয় দূর্বিপাকের জীবন অতিবাহিত করার জন্য হয়ে থাকবে। তবে কাবুল থেকে ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন সেই পথের আর চার ঋতুর দেশ কাবুলের বেশ সুবিন্যস্ত বিবরণ এখানে পাওয়া যায়। যা মনোরম এবং মনোহরও।
বাবুরের আত্মজীবনী ‘তুজুক-ই-বাবুরী’ তাঁর পৌত্র সম্রাট আকবরের নির্দেশে খান-ই-খানান আবদুর রহিম ফার্সিতে অনুবাদ করেন। ফার্সি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মিসেস বেভারিজ ‘মেমোরিজ অব বাবুর’ নামে। এই নামে গ্রন্থটি সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। “ভারতীয় লেখক সৈয়দ আমীর রিজভি এ গ্রন্থের উর্দু ও ইংরেজি অনুবাদ থেকে একটি হিন্দি সংস্করণ প্রস্তুত করেন।” এই গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ ‘বাবরনামা’ নামে করেন মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস। তাঁর বেশকিছু অনুবাদকর্ম রয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা বেশ। আর নিজে একজন কবি হওয়ার ফলে তাঁর ভাষার সাবলীলতা এই গ্রন্থের পাঠকে সুখকর করেছে। ২৫৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ৭১ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ ভূমিকা রয়েছে। যেখানে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের বাবুরের পূর্বের ৩২০ বছরের ইতিহাসের বিবরণ আছে। খলিফা উমর (রা) এর শাসনামলে হিঁদুস্তানে রাজনৈতিক মিশন প্রেরণের পরিকল্পনা হয়। কিন্তু সেটার বাস্তবায়ন হয় না। অনেককাল পরে সপ্তদশবর্ষীয় আরব তরুণ মুহম্মদ বিন কাশিম ভারত জয় করেন। তার ধারাবাহিকতায় ১২০৬ থেকে ১৫২৬ এই ৩২০ বছরের মুসলিম শাসন চলে বাবুরের পূর্বে। যেখানে কুতুবউদ্দীন আইবক থেকে ইব্রাহীম লোদি মোট ২৯ জন শাসক রাজত্ব করেছেন। এদের বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনুবাদক উপস্থাপন করেছেন। কাজটি বেশ শ্রমসাধ্য। আছে বাবুরের বিবরণও। এই ভূমিকা গ্রন্থটিকে পাঠকের ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের কাল এবং কার্যাবলীর একটা স্পষ্ট ধারণা দেবে। কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া এই অনুবাদকর্মটি বেশ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়—ভারতবর্ষ দীর্ঘ প্রায় ছয়-সাতশ বছর মুসলমানের অধীনে রয়ে গেল। কীভাবে? রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা হয়তো বলবেন তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি আর ধর-পাকড়ের রাজনীতি। সমাজতাত্ত্বিকরা বলবেন তাদের সহবস্থানের নীতি। আসলে মুসলিম ধর্মের উদার ঔদার্য কিছুটা সেক্যুলার মনোভাব এসবের পেছনে কাজ করে থাকবে। মুসলিম শাসকরা লুট করে নিয়ে যায়নি বরং এখানকার অধিবাসীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চেয়েছে। মোগলদের এমন অনেক নজির খুঁজে পাওয়া যাবে। ফলে এই জনপদের সংস্কৃতি হয়েছে সমৃদ্ধ। খানা-পিনা, সাজ-সজ্জা, শিল্পচর্চা সবতাতেই নান্দনিকতার ছোঁয়া পরিলক্ষিত হয়। স্থাপত্যশৈলীর কথা তো সর্বজনবিদিত। মন্দির আর মসজিদের উপরিকাঠামো তথা বাহ্যিক আকৃতির স্থাপত্যশৈলীর মিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেওয়া আর নেওয়ার ব্যাপারটায় হয়তো ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনের অন্তর্গূঢ় রহস্য।
‘বাবরনামা’য় এক জায়গায় অমূল্য সেই কোহিনূরের হীরের কথা বলা হয়েছে। আগ্রা অধিকারের পর বিক্রমজিতের পরিজনদের কাছ থেকে সেটি এনে হুমায়ূন বাবুরকে দেয়। বাবুর সেটি আবার হুমায়ূনকে উপহারস্বরূপ দিয়ে দেন। এটি সম্পর্কে বাবুর বলেন, “যার মূল্য দিয়ে পুরো দুনিয়াবাসীর আড়াই দিনের আহার মিলতে পারত।” এই মণিটি এখন ইংল্যান্ডের রাজদরবারের শোভা বর্ধন করছে।
“আমার হাত থেকে সমরখন্দও বেরিয়ে গেল এবং ফারগানাও।” সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরছেন এক কিশোর। যার হাতে পৃথিবীর অন্যতম বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে বলে ভবিতব্য পরিকল্পনা করে রেখেছিল। সেই নিরাকার পরিকল্পনাকে কীভাবে সাকার করলেন অর্থাৎ নিজের স্বপ্নের পথে হাঁটার এক আপাত কঠিন সংগ্রামমুখর জীবনের আখ্যান ‘বাবরনামা’। আর এসবের সাথে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের বন্ধুর পথে হেঁটে চলা এক যুদ্ধবাজের কবিমনের শৈল্পিক প্রকাশ এই গ্রন্থের পাঠকের জন্য বাড়তি পাওয়া। নজরুলের কবিতার মতো ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি আর হাতে রণতূর্য’ ছিল বাবুরের। তিনি যে হাতে শত্রুর মস্তক ছেদন করে নিজের সালতানাত নিরাপদ রেখেছেন সেই হাতেই কলম ধরে জগৎবাসীর চিত্তে প্রফুল্লতা এনেছেন। “তাঁর রচনাবলী, তাঁকে ভূগোলবিদ, ইতিহাসবিদ, কাব্য ও সাহিত্যবিদ, সংঙ্গীতজ্ঞ ও লিপিবিশারদ বলে প্রতিষ্ঠা দেয়। এ এক বিস্ময়কর মনীষা।” তাই ইতিহাস একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পাশাপাশি একজন মহান শিল্পীকেও স্মরণ করে। বাবুর ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে আলোকিত মানুষ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই। বাবুরের চাচাতো ভাই তাঁর সম্পর্কে বলেন, “চেঙ্গিস খাঁ-র পর চুগতাই বংশের লোকেরা শুষ্ক স্বভাব ও অসভ্য ছিলেন। তাঁদের জন্য বাজারি শব্দের প্রয়োগ করা হতো। এই বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি জহির-উদ্-দীন মুহম্মদের জন্য লোকে ‘বুজুর্গ’ বলে সম্বোধন করত।” তাই শুধু চেঙ্গিস বংশ নয় বাবুর তাঁর অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা মধ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার এক বিরাট অংশের মানুষের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। আর তাঁর সম্রাট ও শিল্পীমনের অনন্যসাধারণ প্রকাশ ‘বাবরনামা’ বিশ্বসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজন হয়ে আছে। এ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম ব্যক্তিমানুষের জ্যোতির্ময় জীবনালেখ্য।

নূর সালমা জুলি
নূর সালমা জুলি প্রাবন্ধিক এবং গল্পকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : কথাশিল্পে মুক্তিযুদ্ধ, যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের । তিনি রাজশাহীতে থাকেন।