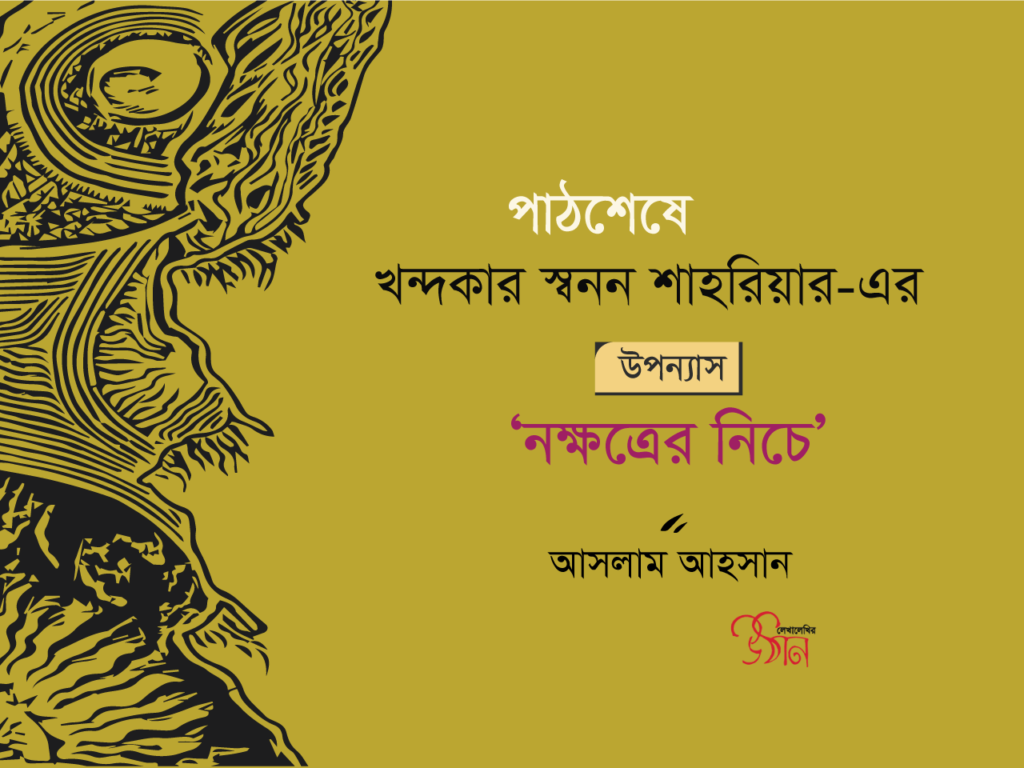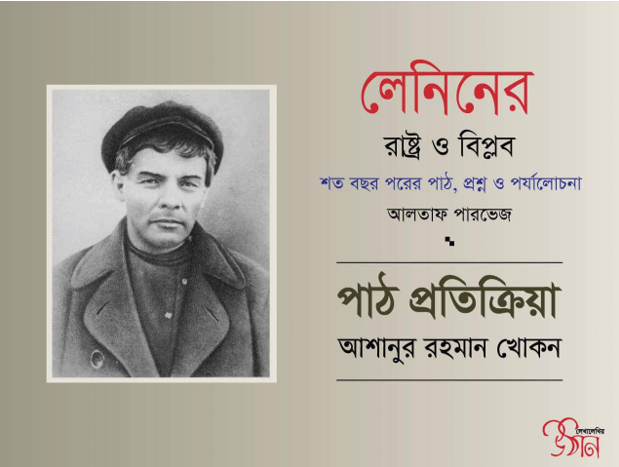উপন্যাসের শুরুটা অভিনব। জীবনের মাঝ পর্যায়ে এসে, অবসরে কায়সার কবির বসেছে এ্যালবাম খুলে। নানা বয়সের নানা রকম ছবি। একেকটা ছবি দেখে চোখে ভেসে উঠতে থাকে ফেলে আসা নানা রঙের দিনগুলো। ধারাবাহিকভাবে কাহিনি এগিয়ে চলে এ্যালবামের ছবির সূত্র ধরে। কায়সার শুধু পৃষ্ঠা ওল্টায়, ছবিগুলোই যেন পাঠকের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। কত রকম কথা, বদলে যাওয়া জীবনের কত রকম আবর্ত।
ভিন্ন ভিন্ন উপশিরোনামে অধ্যায়গুলো বিন্যস্ত : প্রথম চারটি ছবি, রাজনীতির প্রথম পাঠ, নিষিদ্ধ ফল, একদিন উৎসবে, যেখানে সীমান্ত তোমার, আলোর ফেরিওয়ালা, আলো-অন্ধকারে যাই, উপল উপকূলে… ইত্যাদি। ৩৫৮ পৃষ্ঠার বৃহৎ উপন্যাস। কিন্তু অধ্যায়গুলো স্বল্পদৈর্ঘ্য। পড়তে গিয়ে ক্লান্তি আসার সুযোগ কম।
আমরা দেখেছি পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য জনপ্রিয় লেখকেরা বিভিন্ন ‘কায়দা’ অবলম্বন করেন। খন্দকার স্বনন শাহরিয়ার অনুরূপ কোনো পথে যাননি। তাঁর গদ্য স্মার্ট। ভাষা প্রাঞ্জল। লেখায় বাড়তি কোনো রঙ না চড়িয়ে সহজ স্বাভাবিক আবেদনে পাঠককে সহযাত্রী করে গল্পের কাহিনিকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন পরিণতির দিকে। পুরো বই জুড়ে মমত্বের ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। বোঝা যায়, হুট করে স্বনন লেখায় হাত দেননি। বিস্তৃত পঠন-পাঠনের ছাপ আছে তাঁর লেখায়। পর্যাপ্ত পড়াশোনা না-থাকলে বইয়ের কিছু অংশ মিস করবেন পাঠক, ভুল বুঝবেন কিংবা এড়িয়ে যাবেন। ‘শ্যামলী তোমার মুখ’ নামে একটি অধ্যায় আছে এ বইয়ে। উক্ত শিরোনামে জীবনানন্দ দাশের কবিতাটি যদি কোনো পাঠকের পড়া না থাকে, তিনি কি বুঝবেন, কেন এই অধ্যায়ের নাম ‘শ্যামলী তোমার মুখ’ দেয়া হলো?
উপন্যাসের কাল পরিধি ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। নব্বই দশকের ছেলেমেয়েরা কোন বোধ বিশ্বাস নিয়ে কীভাবে বেড়ে উঠেছে, এর একটি দলিল হতে পারে এই বই। সমকালীন ইতিহাসের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু বাঁক বদলের চিত্র আছে এতে। গ্রামীণ ব্যাংকের পূর্ণ বিকাশ, মোবাইল ফোনের প্রচলন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উত্থান, কোচিং সেন্টারের তুঙ্গস্পর্শী চাহিদা, নতুন পত্রিকা হিসেবে ‘প্রথম আলো’র আত্মপ্রকাশ। ‘আলোর ফেরিওয়ালা’ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও উপস্থিত আছেন তাঁর চিরচেনা হাস্যোজ্জ্বল মুখ আর স্বপ্নময় চোখ নিয়ে। লেখকের সজীব বর্ণনা :
“আমার এ্যালবামের প্রিয় একটি ছবি স্বনন তুলে দিয়েছিল। অদ্রি, অপু আর আমি দাঁড়িয়ে আছি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে ঘিরে। ছবিতে তিনজনের বয়স ষোল-সতের, একজনের বয়স ছাপান্ন। চারজনই হাসছি, তবে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে চোখ এবং সবচেয়ে তারুণোজ্জ্বল হাসিটি সায়ীদ স্যারের।”
গল্পের গাঁথুনি বেশ গোছানো। দৃষ্টান্তসহ চরিত্রগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা গেলে ভালো হত। আপাতত, মোটা দাগেই যদি বলি— আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত ঢাকা শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, মৃত্যু থেকে পুনর্জন্মের গল্প, অপশক্তির সঙ্গে শুভবোধের অসম লড়াই। কায়সার চরিত্রটি আমাদের খুব পরিচিত। কায়সারের বাবা, চাচা এবং নানাকে খুব আপন মনে হয়। অদ্রির বাবার প্রতিও সমান টান অনুভব করি। নায়িকা অপরাজিতা/অপুর চেয়ে ইসাবেল চরিত্রটি কোনো অংশে কম উজ্জ্বল নয়।
কিশোরী বেলোয় ‘ছিচকে চোর’ আসাদকে গণপিটুনির হাত থেকে বাঁচিয়েছিল অপু। আসাদকে পাঠক ভুলেই গিয়েছিল ততক্ষণে, লেখক ভোলেননি। ঠিকই উপযুক্ত জায়গায় যথাসময়ে তাকে উপস্থিত করেছেন। কাহিনির তুঙ্গ পর্যায়ে ‘তারকা’ অপু একবার চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। সেই মুহূর্তে আসাদকে অপুর বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর ভূমিকায় দেখে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি।
বইয়ের প্রথম ফ্ল্যাপে কায়সার জীবনানন্দের মতোই ‘অচল মানুষ’ কিনা, এমন ইঙ্গিত থেকে মনে হতে চায়- কাহিনি বুঝি বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে আগাবে। তাছাড়া, পলিটিক্স ও মিডিয়া জগতের দুজন ক্ষমতাধর ব্যক্তির সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ে কায়সার জড়িয়ে পড়ে। ঘটনা গড়ায় খোদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত। জটিল ক্লাইমেক্স। অবশেষে লেখক অবশ্য জয় দেখিয়েছেন মানুষের শুভবোধেরই। দেশপ্রেমের বার্তা আছে বইয়ের শেষাংশে অপুর বাবার মৃত্যু-পরবর্তী একটি ঘটনায়। অপুর মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে সমাহিত করা হচ্ছে মিরপুর গোরস্থানে। অপু তার বাবার কাফনের ওপর একটি লাল-সবুজ পতাকা রেখে দেয়। এটা দেখে ক্ষেপে ওঠেন স্থানীয় এক প্রভাবশালী লোক। পতাকা ছুড়ে ফেলে দেন তিনি। সামনে এগিয়ে যায় অপু। একদম মুখোমুখি। অতঃপর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় :
– পতাকা কি আল্লাহর কাছে যাবে?
– পতাকা আল্লাহর কাছে যাবে না। মাটি দেয়ার সময়ে পতাকা তুলে নেব। তবে এখনই পতাকা তুলে নিয়ে না এলে আপনি আল্লাহর কাছে যাবেন। নগদে।
-তুমি জানো আমি কে? আমি কোন্ দল করি জানো?
– জাতীয় পতাকার সঙ্গে বেয়াদবি করলে তোমার দলসুদ্ধ মাটিচাপা পড়ে যাবে!
অবস্থা বেগতিক দেখে পিছু হটতে বাধ্য হয় ‘কোন্-দল-করা’ ব্যক্তি। দেশপ্রেমিকের সন্তানের দাঁড়ানো যে কোনো শক্তির পক্ষে কঠিন বুঝিয়ে দিলেন লেখক।
স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক-গীতিকারদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উদ্ধৃতি আছে এ উপন্যাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্বতঃস্ফূর্ত। লেখকের রবীন্দ্র-অনুরাগ স্পষ্ট। হুমায়ূন আহমেদ তিনি পড়েছেন মুগ্ধতার সঙ্গে, টের পাওয়া যায়। বাক্য বিন্যাসে দুয়েক জায়গায় হুমায়ূন আহমেদের প্রভাব লক্ষ করা গেছে প্রত্যক্ষভাবেই। এটা অস্বাভাবিক নয়। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যের মান নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে যতই সংশয় থাকুক, তাঁর মায়াজড়ানো সহজিয়া বর্ণনাভঙ্গির মোহ এড়াতে সমকালীন নবীন লেখকের আরও একটু সময় লাগবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’(১৯৩৬)-এ শশী ও কুসুমের কথাপকথনে একটি স্মরণীয় সংলাপ ছিল নায়ক শশীর মুখে :
‘শরীর শরীর। তোমার মন নাই কুসুম!’
এ উক্তির প্রতিধ্বনি শুনি ‘নক্ষত্রের নিচে’র নায়ক কায়সারের মুখে। এই একই কথা সে বলছে ঠিক উল্টো করে:
‘মন মন। তোমার শরীর নাই অপু!’
পূর্বসূরি মহান লেখকেরা নতুন লেখকের রচনায় এভাবেই বার বার ফিরে আসেন। উদ্ধৃতিতে দুয়েক জায়গায় বিচ্যুতি ঘটেছে। চ-ীদাস আর কায়কোবাদের লাইন একাকার হয়ে গেছে এক জায়গায়। এগুলো অবশ্য গৌন বিষয়।
লেখকের রসবোধ মুগ্ধ করার মতো। এক জায়গায় কায়সার বলছে:
“পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু নেই। তরমুজের বিচি আছে। ফলুই মাছের কাটা আছে। ছুটিছাটায় বাড়ির কাজ আছে। আর বান্ধবীর আছে বড় ভাই।” আমরা দেখেছি জটিল পরিস্থিতি বর্ণনাতেও লেখকের সূক্ষ্ম রসবোধ অক্ষুণ থেকেছে।
উত্তম পুরুষে লেখা এ বইটি কি স্বনন শাহরিয়ারের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস? সে রকমই মনে হয়। তবে লেখক এখানে একটি চিত্তাকর্ষক হেঁয়ালি তৈরি করেছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম কায়সার। গোল বাঁধায় স্বনন নামের চরিত্রটি যার বাবা একজন লেখক। আমাদের মনে হতে থাকে ‘কায়সার তো বোধহয় স্বয়ং লেখকই। এদিকে, স্বনন আবার লেখকেরই নামের অংশ। বাস্তবে স্বনন শাহরিয়ারের বাবাও একজন লেখক ছিলেন। তাহলে…?’।
প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে কায়সারের মুখ দিয়ে লেখক উপলব্ধিমূলক কিছু কথা বলেছেন। কথাগুলো সুন্দর, উদ্ধৃতিযোগ্য :
“সত্যিকারের সাহস আসে মানুষের জন্য গভীর মমতা থেকে। ছেলে হোক, আর মেয়েই হোকÑ যার মমতা বেশি, সে-ই বেশি সাহসী।”
“অপু আমাকে বলল, “মেয়েটার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে।”
তার চোখে পানি টলমল করতে লাগল। চেহারায় কোনো মিল না থাকা সত্ত্বেও আমি তার মুখে রাজিয়ার মুখ দেখতে পেলাম।
সেই প্রথম জানলাম, ভালোবাসার মুখগুলো দেখতে একইরকম। ভালোবাসার সুখগুলোও।
আর ভালোবাসার সোনালি দুঃখগুলোও।”
“…কায়া খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, “কী করছ বাবা? ছাড়ো। আমার ছবি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!”
কায়া জানে না, দুই হাত দিয়ে আমি শুধু তাকেই না, জড়িয়ে রেখেছি আমার ছোটবেলাকেও।”
এমন উক্তি আরও আছে। এর কোথাও কোথাও লেখক যেন ‘বিবেকের’ ভুমিকায় অবতীর্ণ। আদর্শবাদ লেখায় থাকতেই পারে। কিন্তু তা যদি উপদেশের ভঙ্গিতে অধ্যায়ের শেষে না থেকে গল্পের ভেতরেই প্রচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে জড়িয়ে থাকত (কোনো কোনো অধ্যায়ে আছেও), বেশি ভালো হত।
উৎসর্গপত্রের শেষ অংশটা তাৎপর্যপূর্ণ :
“বাবা হিসেবে নয়, এই উপন্যাস তাঁকে উৎসর্গ করছি তিনি আমার চোখ, কান এবং মন তৈরি করেছেন বলে। আমার দ্বিতীয় জন্মের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে।”
এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা : ‘দ্বিতীয় জন্ম’। সাহিত্য অঙ্গনের এমন খরাকবলিত দিনে স্বনন শাহরিয়ারের আত্মপ্রকাশ আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। চার ফর্মায় বই শেষ করতে হবে- এই অচলায়তন ভাঙার জন্যেও স্বনন ধন্যবাদ পেতে পারেন। বৃহৎ পরিসরে উঠে আসুক জীবনের বিচিত্র দিক, নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেরই এমন প্রত্যাশা। এই সুবাদে ‘নক্ষত্রের নিচে’র প্রকাশক-লেখক উভয়কে অভিনন্দন। প্রথম বইয়ের মাধ্যমে পাঠকের যে মনোযোগ তিনি আকর্ষণ করেছেন- এর যথার্থ মূল্য তিনি পরবর্তী বইগুলোতে দেবেন আশা করা যায়।