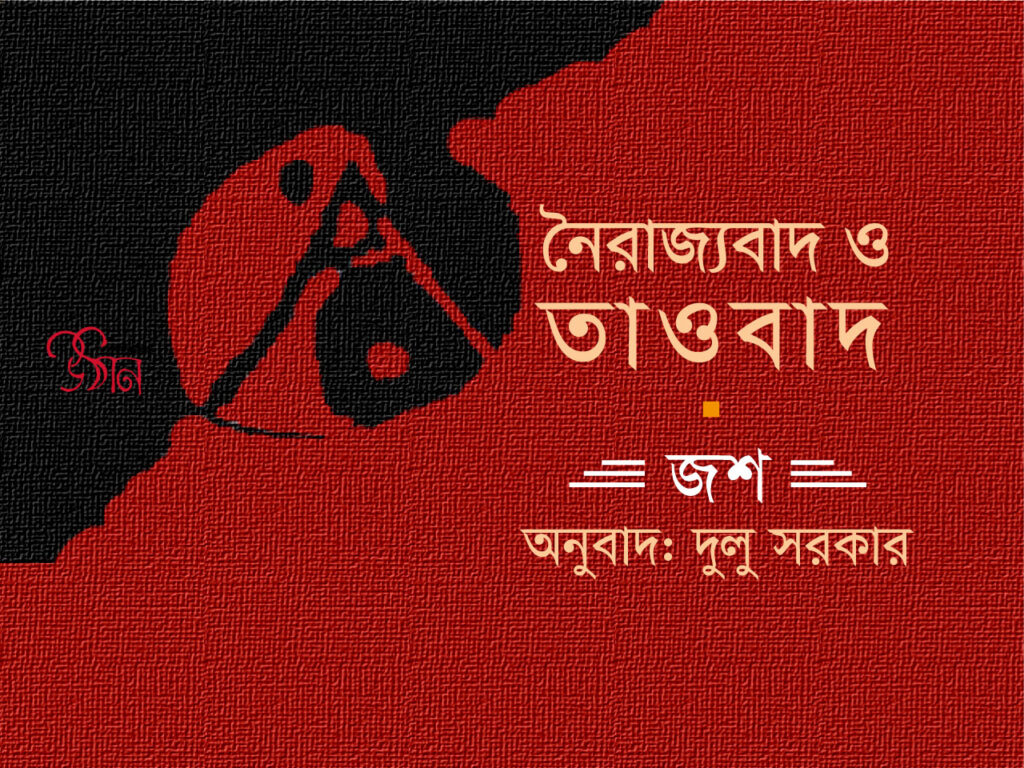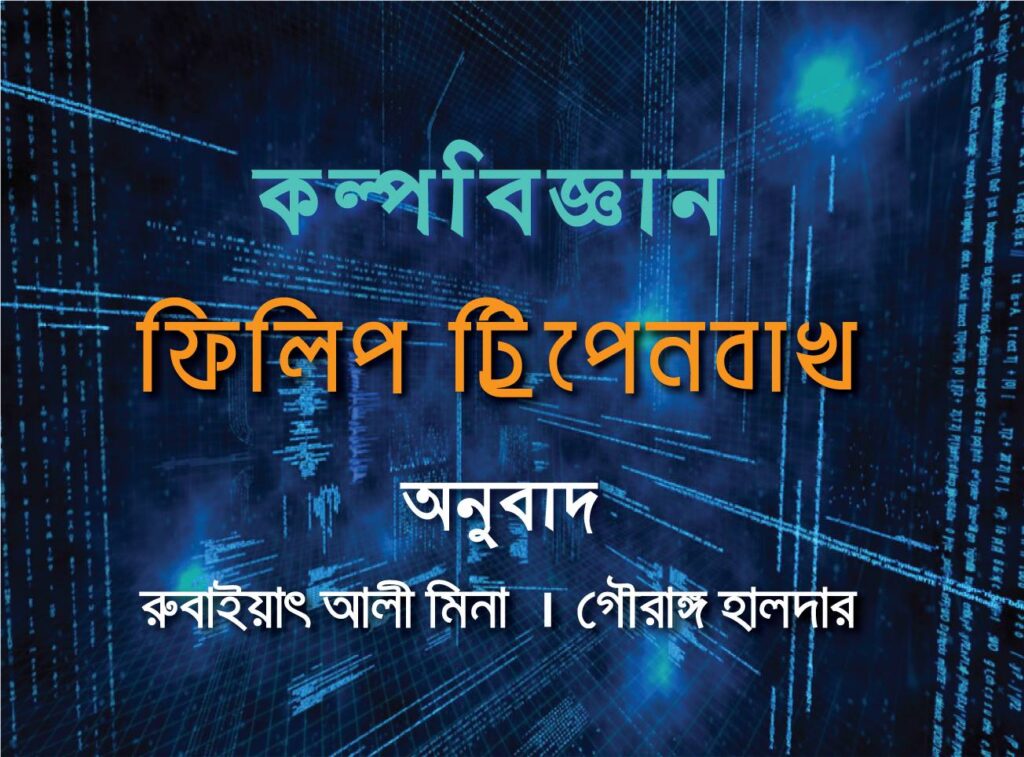নৈরাজ্যবাদকে সাধারণত একটি সাম্প্রতিক পশ্চিমা প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতাগুলির গভীরে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দিকে চীনের তাও মতবাদে নৈরাজ্যবাদী চেতনার প্রথম স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। বস্তুত, তাওবাদের প্রধান কেতাব তাও তে চিং’কে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নৈরাজ্যবাদী রচনাগুলির মধ্যে প্রধানতম বিবেচনা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।
সে সময় তাওবাদীরা এমন এক সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বসবাস করতো যেখানে আইন সংবিধিবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি সরকারব্যবস্থা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠছিলো। এই কার্যক্রমগুলির বৈধতা দান ও সমর্থনকারী গোষ্ঠীর প্রধান মুখপাত্র ছিলেন কনফুসিয়াস। তিনি এমন এক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের আহ্বান জানিয়েছিলেন যেখানে প্রত্যেক নাগরিককে তার নিজস্ব অবস্থানের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হতো৷ এদিকে তাওবাদীরা সরকারব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং তারা বিশ্বাস করতো যে সবাই প্রাকৃতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রীতিতেই জীবন যাপন করতে পারে। সেই থেকে, যারা হস্তক্ষেপ করতে চায় এবং যারা মনে করে যে হস্তক্ষেপ না করলেই বরং কোনো কিছুর সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে, উভয় দলের মধ্যে এক চিরকালীন দ্বন্দ্ব শুরু হয়।
তাওবাদী ও কনফুসীয়বাদী উভয় ধারাই প্রাচীন চীনা সংস্কৃতিতে অনুবিদ্ধ ছিলো। প্রকৃতির ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গতি পরিলক্ষিত হলেও নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা প্রবলভাবে পৃথক। উভয়েরই মানব স্বভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব ছিলো; আদি পাপের মতো খ্রিস্টীয় ধারণা ছিলো তাদের চিন্তাপ্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। উভয়েই বিশ্বাস করতো যে সদগুণের প্রতি মানুষের সহজাত প্রবণতা রয়েছে; কোনো শিশুকে কূপে পড়ে যেতে দেখলে যে কারো স্বভাবজ প্রতিক্রিয়াতেই তা প্রকাশিত হয়। উভয়েই তাও বা প্রাজ্ঞদের পথ রক্ষার দাবি করতো এবং স্বেচ্ছাসেবী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতো।
তাওবাদীরা যেখানে প্রকৃতির প্রতি আগ্রহী ছিলো এবং তার পরিচয়েই পরিচিত হতো, সেখানে কনফুসীয়বাদীরা ছিলো অতি পার্থিব-মনোভাবাপন্ন এবং সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। কনফুসীয়বাদীরা কর্তব্য, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের মতো ‘পুরুষধর্মী’ মূল্যবোধের গুণকীর্তন করতো, অন্যদিকে তাওবাদীরা প্রচার করতো গ্রহণক্ষমতা ও নিষ্ক্রিয়তার মতো ‘নারীধর্মী’ মূল্যবোধের।
চীনা সংস্কৃতির বিকাশে বৌদ্ধ ও কনফুসীয় মতবাদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও স্বভাবতই তাওবাদ কখনো সরকারি ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয়নি। এটি চীনা চিন্তাধারায় এক চিরন্তন প্রবাহ হয়ে রয়েছে। চীনা সভ্যতার প্রভাতকালীন লোকায়ত সংস্কৃতিতে এর শেকড় প্রোথিত থাকলেও খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দর্শন, ধর্ম, আদি-বিজ্ঞান এবং মায়াবিদ্যার চমকপ্রদ সংমিশ্রণ হিসেবে তাওবাদ আত্মপ্রকাশ করে।
তাওবাদের প্রধান ব্যাখ্যাকার ধরা হয় লাওৎসে’কে, যার অর্থ ‘প্রবীণ দ্রষ্টা’। খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ সালের দিকে তিনি হুনান প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। একজন অভিজাত হিসেবে তিনি তাঁর বংশগত অবস্থান প্রত্যাখ্যান করেন এবং লোহ’র রাজকীয় গ্রন্থাগারে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যোগদান করেন। সারাজীবন তিনি নীরবতার পথেই চলেছেন। তিনি শেখাতেন, ‘যে তাও নিয়ে কথা বলা যায়, শাশ্বত তাও সেটি নয়।’ (১) জনশ্রুতি অনুসারে, মৃত্যুবরণের উদ্দেশ্যে তিনি যখন মরুভূমির দিকে যাত্রা করেছিলেন তখন চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক সীমান্তদ্বাররক্ষী পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাঁকে তাঁর শিক্ষা লিখে যেতে রাজী করান।
লাওৎসে’র তাও তে চিং খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক অবধি রচিত হয়নি বলে কেউ কেউ মনে করেন। চীনা পণ্ডিত জোসেফ নীধাম গ্রন্থটিকে ‘কোনোরকম ব্যতিক্রম ছাড়াই চীনা ভাষার সবচেয়ে গভীর জ্ঞানপূর্ণ ও সুন্দর রচনা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাঠ্যটি কাব্যিক ঢঙে রচিত ৮১টি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় নিয়ে গঠিত। প্রায়শই অস্পষ্ট ও আপাতবিরোধী মনে হলেও এটি নৈরাজ্যবাদী নীতিগুলির শুধু সর্বপ্রথমই নয়, সবচেয়ে আলংকারিক প্রকাশও বটে।
তাওবাদী প্রকৃতি-দর্শন না বুঝে এর নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাও তে চিং প্রকৃতির পথ বা তাও-এর গুণকীর্তনের পাশাপাশি প্রাজ্ঞজনেরা এটি কীভাবে অনুসরণ করবে তা বর্ণনা করে। প্রকৃতির ব্যাপারে তাওবাদী ধারণা প্রাচীন চীনা তত্ত্ব ইন ও ইয়্যাং-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইন ও ইয়্যাং হলো বিপরীতমুখী অথচ পরিপূরক দুটি মহাজাগতিক শক্তি যা চি’র(বস্তু–শক্তি) সৃষ্টি করে। চি থেকে সকল সত্তা ও প্রপঞ্চের উদ্ভব ঘটে। ইন হলো অন্ধকার, শীতলতা ও গ্রহণক্ষমতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক সর্বোচ্চ নারীধর্মী শক্তি যা চাঁদের সাথে সম্পর্কিত। আর ইয়্যাং হলো উজ্জ্বলতা, উষ্ণতা ও সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পুরুষধর্মী শক্তি যা সূর্যের দ্বারা প্রতীকায়িত। উভয় শক্তিই পুরুষ ও নারীর পাশাপাশি সবকিছুতেই ক্রিয়ারত।
তাওকে কোনোভাবেই সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এটি নামহীন ও নিরাকার। লাওৎসে অনির্বচনীয়কে ব্যাখ্যা করার এক বৃথা প্রয়াস হিসেবে এটিকে কখনো খালি পাত্র, কখনো সাগরপানে বহমান নদী, আবার কখনো খোদাইবিহীন ফলকের উপমা দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, তাও প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। এটি এমন পথ যে পথে মহাবিশ্ব ক্রিয়ারত, এটি এমন প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা যা সবকিছুকে অস্তিত্ববান করে এবং বাঁচিয়ে রাখে।
বাম–ডান উভয়দিকেই পরম তাও বহমান৷ সবকিছু এর উপর নির্ভরশীল; এটি কিছুই অধিকার করে না। তাও কোনো দাবি না রেখে নীরবে এর উদ্দেশ্য পূরণ করে। (৩৪)
নীধাম এটিকে যতটা না শক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার চেয়ে বেশি ‘সময় ও স্থানের মধ্যকার এক প্রাকৃতিক বক্রতা’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
পরবর্তীকালের অধিকাংশ নৈরাজ্যবাদীর মতোই তাওবাদীরা মহাবিশ্বকে নিরন্তর পরিবর্তনশীল এক প্রবহমান অবস্থা হিসেবে দেখেছে। বাস্তবতা এক নিরন্তর প্রক্রিয়ার অবস্থা; সবকিছুই পরিবর্তনশীল, কিছুই নিত্য বা ধ্রুব নয়। বিপরীত শক্তিগুলির মধ্যে প্রগতিশীল পারস্পরিক ক্রিয়া হিসেবে পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার একটি দ্বন্দ্বমূলক ধারণাও তাদের রয়েছে। ইন ও ইয়্যাং-এর মেরু দু’টির মধ্যে অবিরামভাবে শক্তি প্রবহমান। একই সঙ্গে তারা প্রকৃতির ঐক্য এবং সম্প্রীতির উপর জোর দেয়। প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অসৃষ্ট; সচেতন স্রষ্টার অস্তিত্বে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা শুধু গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না, বরং আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান কর্তৃক উপস্থাপিত মহাবিশ্বের ব্যাখ্যার সাথেও মিলে যায়। আধুনিক সামাজিক বাস্তুশাস্ত্রও বৈচিত্র্য, জৈবিক বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার একাত্মতার প্রতি জোর দিয়ে তাওবাদী বিশ্ব-দর্শনকেই প্রতিবিম্বিত করে।
লাওৎসে এবং তাওবাদীদের দ্বারা প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক পন্থা হলো গ্রহনক্ষমতার ঐক্য। কনফুসীয়বাদীরা যেখানে প্রকৃতিকে জয় ও শোষণ করতে চায় তাওবাদীরা সেখানে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একে বুঝতে চায়। তাওবাদীদের প্রথাগত ‘নারীধর্মী’ দৃষ্টিভঙ্গি ইঙ্গিত দেয় যে তাদের চিন্তাপদ্ধতি প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিকশিত হতে পারে। প্রথম দর্শনে এটিকে ধর্মীয় মতবাদ বলে মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এই চিন্তাপদ্ধতি তাওবাদীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের অনুপ্রেরণা যোগায়। কারো উপর পূর্বকল্পিত ধারণা চাপিয়ে না দিয়ে তারা প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো। তাই তারা কল্যাণজনকভাবে প্রকৃতি-শক্তি ব্যবহার করতে শেখে।
তাওবাদীরা প্রাথমিকভাবে প্রকৃতির প্রতি আগ্রহী ছিলো, তবে তাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্ত রয়েছে। তাওবাদী চিন্তাধারা থেকে নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। তাওবাদীদের কোনো পরম মূল্যবোধ নেই; ভালো ও মন্দ ইন ও ইয়্যাং-এর মতোই পরস্পর-সম্পর্কিত। এদের পারস্পরিক ক্রিয়া বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। কিছু অর্জনের জন্য উল্টোদিক থেকে শুরু করা প্রায়শই সবচেয়ে ভালো ফল নিয়ে আসে। যাই হোক, তাওবাদী শিক্ষায় এমন এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে যিনি নিরহংকারী, অকপট, স্বতঃস্ফূর্ত, উদার এবং উদাসীন। তাওবাদীদের কাছে সরলতা, নিরাকাঙ্ক্ষা এবং সৃজনশীল ক্রীড়াই জীবন যাপনের শিল্প।
তাও মতবাদ মূলত উ-উয়ি নামক একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রায়শই নিছক অ-ক্রিয়া হিসেবে এর অনুবাদ করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ‘নৈরাজ্যবাদ’ এবং ‘উ-উয়ি’র মধ্যে লক্ষনীয় শব্দতাত্ত্বিক সাদৃশ্য রয়েছে। গ্রীক শব্দ ‘an-archos’-এর অর্থ হলো শাসকের অনুপস্থিতি, তেমনি ‘উ-উয়ি’র অর্থ হলো উয়ির অনুপস্থিতি, যেখানে উয়ি বলতে বোঝায় ‘কৃত্রিম ও মতলববাজি কার্যকলাপ যা প্রাকৃতিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে হস্তক্ষেপ করে’। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উয়ি বলতে বোঝায় ‘কর্তৃপক্ষের আরোপন’। তাই উ-উয়ি’র সাথে সঙ্গতি রেখে কিছু করা প্রাকৃতিক হিসেবে বিবেচিত হয়; কারণ এটি প্রাকৃতিক ও স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার দিকে চালনা করে। কোনো ধরণের আরোপিত কর্তৃত্বের সাথে এর যোগসূত্র নেই।
তাও তে চিং বলপ্রয়োগের প্রকৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা দেয়। আমরা নিজেদের বা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কায়িক বা নৈতিক যে বলই প্রয়োগ করি না কেন, আমরা কেবল শক্তির অপচয়ই করি এবং নিজেদের দুর্বল করি : ‘বলপ্রয়োগের দ্বারা শক্তিহ্রাস হয়।’ (৩০) তার মানে যারা যুদ্ধ বাধায় তারাই তার পরিণতি ভোগ করে : ‘একজন হিংসাত্মক মানুষের মৃত্যুও সহিংস হয়।’ (৪২) অন্যদিকে, পথ ছেড়ে দেয়াই জয় করার সর্বোত্তম উপায় : ‘আকাশের নিচে পানির চেয়ে কোমল আর উৎপাদনশীল কিছু নেই, তবু কঠিন ও শক্তিশালীকে আক্রমণের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম কিছু নেই, এর কোনো জুরিও নেই। দুর্বলই সবলকে জয় করতে পারে; কোমলই কঠোরকে করতে পারে পরাস্ত।’ (৭৮) তাওবাদীদের দ্বারা প্রস্তাবিত অমায়িক শান্তিপূর্ণতা পরাজয়বাদীদের নতি স্বীকার নয় বরং শক্তির সৃজনশীল ও কার্যকর ব্যবহারের আহ্বান।
লাওৎসের পরামর্শ হলো, ‘অ-ক্রিয়ার অভ্যাস করো। কর্ম করো কিছু না করেই।’ (৬৩) উ-উয়ির ধারণা অনুযায়ী তাওবাদীরা অ-ক্রিয়া বলতে নিছক নিষ্ক্রিয়তার প্রেরণা দেয় না, বরং প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপের নিন্দা করে। তারা অলসতার গুণকীর্তন করে না; বরং প্রয়াস, উদ্বেগ ও কোনো জটিলতা ছাড়াই কর্ম সমাধা করে। এ ধরনের কর্ম কোনোকিছুর পক্ষাবলম্বন ও বিরুদ্ধাচারণ কোনোটাই করে না। লোকেরা যদি সৎভাবে উ-উয়ি’র চর্চা করে, তবে কর্ম তার জবরদস্তিমূলক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত হবে। কার্যকর ফলের জন্য নয় বরং কর্ম গৃহীত হবে তার স্বকীয় মানের জন্য। প্লেগের মতো পরিহার্য হওয়ার পরিবর্তে কর্ম পরিণত হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং অর্থপূর্ণ ক্রীড়ায় : ‘যখন অযথা কথা না বলে কর্ম সম্পাদন করা হয় তখন লোকেরা বলে, “আমরাই এটি করেছি!”’ (১৭)
কেউ যদি উপদেশ নিতে চায় তবে তাওবাদীদের পরামর্শ হলো, মানুষ জীবন যাপন করুক এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বাস্থ্যবান হোক। তাদের মৌলিক বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটি হলো, ‘যা কিছু তাও-এর বিপরীত তা দীর্ঘস্থায়ী নয়।’ (৫৫) আর, যে পুণ্যবান সে যেন এক নবজাতক। আয়ু দীর্ঘ করার জন্য তাওবাদীরা যোগ-কৌশল এমনকি আলকেমির চর্চাও করতো।
তাদের মৌলিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি ছিলো এই বিশ্বাস যে, ‘সবকিছু যেমন চলছে তেমন চলতে দিয়েই জগৎ শাসিত হয়, হস্তক্ষেপ করে এটি শাসন করা যায় না।’ (৪৮) সম্ভবত প্রাচীন চীনের শুরুর দিকের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উ-উয়ি’র তাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গির শেকড়গুলি গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে। তাওবাদী আদর্শ হলো কৃষিজীবি-সমষ্টিবাদ যা প্রকৃতির সাথে আন্তরিক ঐক্যকে পুনরুদ্ধার করতে চায়, যা কিনা মানুষ কৃত্রিম ও শ্রেণিকরণ সংস্কৃতির বিকাশের ফলে হারিয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেই কৃষকেরা নানা দিক দিয়ে বিচক্ষণ। নানা কঠিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে শিখেছে এবং উপলব্ধি করেছে যে চাষাবাদের জন্য তাদেরকে অবশ্যই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি বুঝতে হবে এবং প্রকৃতিকে সহযোগিতা করতে হবে। ‘ফসল যেমন তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় যখন তাদের স্বভাবমাফিক বাড়তে দেয়া হয়, তেমনি মানব সম্প্রদায়ও হস্তক্ষেপ না করলেই উন্নতিলাভ করে।’ (৬) এই অন্তর্দৃষ্টিই সব ধরনের আরোপনবাদী কর্তৃপক্ষ, সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে তাওবাদীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এটিই তাদের আধুনিক নৈরাজ্যবাদ এবং সামাজিক বাস্তুশাস্ত্রের পূর্বসুরীতে পরিণত করেছে।
একটি বিতর্ক আছে এমন যে, তাওবাদীরা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কৃত্রিম কাঠামো হিসেবে নয় বরং পরিবারসদৃশ একটি প্রাকৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছে। যদিও তাও তে চিং নিঃসন্দেহে কর্তৃত্ববাদী শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে, আবার এমনও মনে হয় যে এটি শাসকদের শাসনের ক্ষেত্রে আরো ভালো হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে :
গুরুকে যদি লোকেদের পথপ্রদর্শন করতে হয়, তবে তিনি নম্রতার সাথেই তা করেন। যদি তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হয়, তবে তিনি থাকেন সবার পশ্চাতে। কেউ যদি এভাবে শাসন করেন তবে লোকেরা নিজেদের নিপীড়িত বোধ করে না। (৬৬)
বুকচিন এতদূর দাবি করেছেন যে, আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়ে কৃষকদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা গড়ে তোলার জন্য কোনো এক অভিজাত কর্তৃক তাওবাদের প্রয়োগ করা হয়েছিলো।
নিশ্চিতভাবেই লাওৎসে নেতৃত্বের সমস্যাবলী নির্দেশ করেছেন এবং জনগনের উপরে না থেকে তাদের সাথে কাজ করার জন্য সত্যিকারের গুরুকে চেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ শাসক তাঁর লোকেদের শান্তিপূর্ণ ও উৎপাদনশীল চরিত্রের অনুসরণ করতে দেন। তাঁকে অবশ্যই তাদের উপর আস্থা রাখতে হয়, কারণ, ‘তিনি যদি পর্যাপ্ত আস্থা না রাখেন তবে তিনিও কারো আস্থাভাজন হতে পারেন না।’ (১৭) কোনো শাসক যদি তার লোকদেরকে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চলতে না দিয়ে কর্তৃত্বপরায়ণ হয় তাহলে বিশৃঙ্খলা হবেই : ‘দেশ যখন বিভ্রান্ত ও বিশৃঙ্খল হয়, তখনই কেবল কর্তব্যনিষ্ঠ দেশপ্রেমী মন্ত্রীদের আবির্ভাব ঘটে।’ (১৮) একটি সুশৃঙ্খল সমাজে :
মানুষ পৃথিবীকে অনুসরণ করে,
পৃথিবী অনুসরণ করে নিয়তিকে,
নিয়তি তাওকে অনুসরণ করে,
তাও অনুসরণ করে প্রকৃতিকে। (২৫)
তবে গভীর অধ্যয়ন থেকে বোঝা যায় যে তাও তে চিং শাসকদের ম্যাকিয়াভেলীয় পরামর্শ দেওয়া এমনকি ‘সরকার পরিচালনার শিল্প’ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন নয়। যে কেউ যদি সত্যিই তাও’কে বোঝে এবং তা শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগ করে তবে সে এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, শ্রেষ্ঠ শাসক কখনোই শাসন করেন না। লাওৎসে সরকারব্যবস্থার কুপ্রভাব ছাড়া কিছুই দেখেননি৷ বস্তুতই, লাওৎসের প্রস্তাবনাকে ইতিহাসের প্রথম নৈরাজ্যবাদী ইশতেহার বলা যেতে পারে।
দেশে যত বেশি আইন ও বিধিনিষেধ
ততো বেশি দরিদ্র হয় মানুষ,
লোকেদের অস্ত্র হয় যতো বেশি ধারালো
দেশে ততো বেশি হয় ঝামেলা,
লোকে যতো বেশি হয় চালাক চতুর
ততো বেশি ঘটে অদ্ভূত ঘটনা,
যেখানে যতো বেশি নিয়ম-কানুন
সেখানে ততো বেশি চোর-ডাকাত।
তাই গুরু বলেন :
আমি কোনো পদক্ষেপ নেই না
তাই সংশোধিত হয় জনগণ,
আমি শান্তি উপভোগ করি
তাই জনগণ হয় সৎ,
আমি কোনো কাজ করি না
তাই জনগণ হয় ধনবান,
আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই
তাই লোকে ফিরে আসে সৎ ও সরল জীবনে। (৫৭)
তাও তে চিং-এর অদ্ভূত কাব্যগুলির মধ্যে সমাজ সম্পর্কিত কিছু বাস্তব পর্যালোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থে সামন্তবাদী ব্যবস্থার আমলাতান্ত্রিক, সামরিক এবং বাণিজ্যিক চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। লাওৎসে সম্পদকে দেখতেন দস্যুতার বিশেষ রূপ হিসেবে: ‘যখন জাঁকজমকপূর্ণ করে সাজানো হয় রাজসভা, তখন শস্যক্ষেত্র ভরে যায় আগাছায়, আর শস্যাগার পড়ে থাকে ফাঁকা।’ (৫৩) অসম বন্টণব্যবস্থাকে তিনি যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন : ‘যদি সম্পদ জমাও আর উপাধি বাগাও, তবে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।’ (৯) সামন্তবাদী ব্যবস্থার শ্রেণিবৈষম্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমালোচনা করে তিনি পিতৃতন্ত্র ও সরকারব্যবস্থা-মুক্ত এমন এক শ্রেণিহীন সামাজের আদর্শ উপস্থাপন করেছেন যেখানে মানুষ প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সরল ও অকপট জীবন যাপন করবে। এটি হবে এমন এক বিকেন্দ্রীভূত সমাজ যেখানে উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করে জনসাধারণ ভাগাভাগি করে নেবে। জনতা হবে শক্তিশালী, তবে তাদের শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে না; তারা প্রাজ্ঞ হবে, তবে কোনো শিক্ষা ছাড়াই; তারা উৎপাদনশীল হবে, তবে অহেতুক পরিশ্রমের সাথে জড়াবে না। এমনকি তারা খতিয়ান লেখার চেয়ে দড়িতে গিঁট দিয়ে গণনা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে :
একটি ছোটো দেশে থাকে অল্প জনগণ।
সে দেশে দশ থেকে একশত লোকের চেয়ে
দ্রুতগামী যন্ত্র থাকলেও সেগুলি ব্যবহারের
কোনো প্রয়োজন হয় না।
লোকে মৃত্যুকে গুরুত্ব সহকারে দেখে
তাই দূরবর্তী কোথাও ভ্রমণ করে না,
তাদের নৌকা এবং গাড়ি থাকলেও
কেউ সেসব ব্যবহার করে না,
তাদের অস্ত্রশস্ত্র থাকলেও
কেউ সেসব প্রদর্শন করে না,
লোকে লেখার পরিবর্তে
গণনাকার্যে ব্যবহার করে দড়ির গিঁট।
তাদের খাবার সাধারণ ও স্বাস্থ্যকর,
তাদের পোশাক অনাড়ম্বর ও সুন্দর,
আর তাদের আবাসস্থল সুরক্ষিত,
তারা সুখী নিজেদের মতো ক’রে।
যদিও তারা বাস করে প্রতিবেশীর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই,
মোরগ আর কুকুরের ডাকাডাকিও শুনতে পায়,
তবু তারা একে অপরকে শান্তিতে থাকতে দেয়,
যেহেতু তারা বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। (৮০)
তাওবাদীদের নৈরাজ্যিক প্রবণতা আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে দার্শনিক চুয়াংৎসের রচনার মাধ্যমে, যিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৯–২৮৬ সালে জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত অনুগল্প এবং কাহিনীগুলিতে ছড়িয়ে থাকা মতবাদ মূলত অন্বেষণ করে তাও-এর প্রকৃতি, যা আসলে এক মহাজৈবিক প্রক্রিয়া, মানুষও যে প্রক্রিয়ার অংশ। তাঁর রচনা কোনো নির্দিষ্ট শাসকের কথা বলে না। তাও তে চিং-এর মতোই এটি সকল প্রকার সরকারব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের অবাধ বিচরণের গুণকীর্তন করে। ঘোড়া সম্পর্কিত একটি ছোটো গল্পে চুয়াংৎসের এই স্বরটি শোনা যায় :
ঘোড়া বাস করে শুকনো জায়গায়, ঘাস খায় আর জল পান করে। যখন তৃপ্ত থাকে, তখন নিজেদের ঘাড় রগড়ায়। রাগ হলে ঘুরে দাঁড়ায় আর গোড়ালি দিয়ে গোড়ালিতে সজোরে আঘাত করে। এই পর্যন্ত তাদের প্রাকৃতিক স্বভাব। কিন্তু কপালে ধাতব ফলক দিয়ে লাগাম পরিয়ে নিয়ন্ত্রণ করলে তারা বদমেজাজী রূপ প্রদর্শন করতে শেখে, কামড়ানোর জন্য মাথা ঘোরাতে শেখে, প্রতিহত করতে শেখে, মুখ থেকে বল্গা বের করে ফেলতে চেষ্টা করে। আর এভাবেই তাদের স্বভাব নষ্ট হয়।
ঘোড়ার সাথে যেমন হয়, মানুষের সাথেও তেমনই হয়। নিজেদের মতো ছেড়ে দিলে তারা বাস করে প্রাকৃতিক সম্প্রীতিতে আর স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলায়। কিন্তু যখন তাদের বাধ্য করে শাসন করা হয়, তাদের স্বভাব হয়ে ওঠে বিদ্বেষপূর্ণ। এটি বোঝায় যে, রাজা বা শাসকদের জনগণকে মনুষ্যনির্মিত আইন মেনে চলতে বাধ্য করা উচিৎ নয় বরং তাদের প্রাকৃতিক স্বভাব মোতাবেক চলার অবকাশ দেয়া উচিৎ। মনুষ্যনির্মিত আইন ও বিধিবিধান দ্বারা জনতাকে শাসন করার প্রচেষ্টা অবাস্তব এবং অসম্ভব : ‘এ যেন সাগরের জলের উপর দিয়ে হাঁটার প্রচেষ্টা, নদীর মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করা, অথবা পাহাড় কাঁধে নিয়ে মশার উড়ে চলা!’ বস্তুত, আমাদের অস্তিত্বের প্রাকৃতিক অবস্থা কোনো কৃত্রিম সহায়তার দাবি করে না। নিজেদের মতো চলতে দেয়া লোকেরা শান্তিপূর্ণ ও উৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকে এবং প্রকৃতি ও একে অপরের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে জীবন যাপন করে।
খ্রিস্টের জন্মের তিনশত বছর পূর্বে চুয়াংৎসে’র ‘অন লেটিং এলোন’ নামক একটি নিবন্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে মৌলিক নৈরাজ্যবাদী প্রস্তাবনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে :
‘মানবজাতিকে একা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপার আগেও ছিলো; কিন্তু তাদের শাসন করার ব্যাপার কখনো ছিলো না। পাছে মানুষের প্রাকৃতিক স্বভাব বিকৃত হয় আর তাদের সদগুণাবলী চলে যায়, তাই একা ছেড়ে দেয়াটা ভয়ের উদ্রেক করে। কিন্তু যদি তাদের প্রাকৃতিক স্বভাব বিকৃত না হয় বা সদগুণাবলী চলে না যায়, তবে সরকারের আর কাজ কী?’
তাওবাদীরা তাই একটি মুক্ত সমাজের সুপারিশ করেছে। সরকারব্যবস্থাহীন সেই সমাজে লোকজনকে নিজেদের মতো করে ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে অন্যের স্বার্থকে ভুলে যাবে না। প্রস্তাবিত স্বার্থপরতা কোনো ক্ষতিকর স্বার্থপরতা নয়। ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধারণ কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত : ‘যতো বেশি কেউ পরের জন্য করে, তার লাভ হয় ততো বেশি; যতোই সে অন্যদের দান করে, ততো তার প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায়।’ (৮১) তাওবাদী পাঠ্য হুয়াই নান ৎজু (Huai Nan Tzu) অনুযায়ী ‘সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া’ মানে হলো ‘আত্ম-উপলব্ধি’। ‘আমি যদি নিজেকে বুঝি তবে সাম্রাজ্যও আমাকে বুঝবে। আমি আর সাম্রাজ্য যদি একে অপরকে বুঝি তবে আমরা সর্বদাই একে অপরের অধিকারী হবো।’
মানুষ চূড়ান্তভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হলেও সে সামাজিক জীবও বটে, অংশ সে সমগ্রতার। আধুনিক বাস্তুশাস্ত্রের পূর্বসুরী হিসেবে তাওবাদীরা বিশ্বাস করতো যে যেখানে যতো বেশি স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য রয়েছে সেখানে সামগ্রিক সম্প্রীতিও ততো বেশি। সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা দ্বন্দ্বকে ছাঁটাই করে না বরং বিরোধী শক্তিসমূহের প্রগতিশীল পারস্পরিক ক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে। চুয়াংৎসের বর্ণনানুযায়ী সমাজ হলো : নির্দিষ্ট কিছু রীতিনীতি মেনে চলার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার এবং ব্যক্তির মধ্যকার একটি চুক্তি, যেখানে সামগ্রিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিবদমান উপাদানগুলি একত্র করা হয়। এই ঐক্যকে কেড়ে নাও, দেখবে প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য রয়েছে… প্রতিটি আলাদা কণার কারণেই পাহাড় এত উঁচু। প্রতিটি পৃথক বিন্দুর কারণেই নদী এত বিশাল। আর, তিনিই প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ যিনি প্রতিটি অংশকে সমগ্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন।
এইভাবে তাওবাদ নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রথম ও প্রধানতম অনুপ্রেরণামূলক ভাবের প্রকাশ করেছিলো। এর নৈতিক এবং রাজনৈতিক ধারণাগুলি বৈজ্ঞানিক বিশ্বদর্শনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যদিও তাওবাদী দর্শনে (Tao Chia) আধ্যাত্মিক এবং অতিন্দ্রীয়বাদী উপাদান রয়েছে, তবে প্রকৃতির প্রতি আদি তাওবাদীদের গ্রহণক্ষম পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও গণতান্ত্রিক অনুভূতিকেও অনুপ্রাণিত করেছিলো। তারা প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের ঐক্য এবং রূপান্তরের বিশ্বজনীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাওবাদী নীতিশাস্ত্রে তারা প্রকৃতির বৃহত্তর অনুষঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ এবং আত্ম-বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে : অধিকার ছাড়াই উৎপাদন, আত্ম-দাবি ছাড়াই কর্ম আর আধিপত্য ছাড়াই বিকাশ। তাদের রাজনীতিশাস্ত্রে তারা শুধু শাসকদেরকে প্রজাদের একা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শই দেয়নি বরং কনফুসীয়বাদের আমলাতান্ত্রিক ও আইনি শিক্ষার বিরোধিতাও করেছে, তবে তারা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকারব্যবস্থাহীন সমবায়ী ও মুক্ত সমাজের আদর্শও প্রবর্তন করেছে।
কৃষকদের আরো অনুগত ও আজ্ঞাবহ করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কোনো অভিজাত কর্তৃক তাওবাদ ব্যবহৃত হয়নি। তাওবাদীদের সামাজিক পটভূমি গড়ে উঠেছে সামন্ত প্রভূগণ এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যবর্তী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। তাওবাদীরা শক্তিশালী লোকেদের কাছে সমর্পিত হয়ে, অনতিউচ্চ প্রোফাইল বজায় রেখে এবং ‘নিজের চরকায় তেল দিয়ে’ ঝামেলাপূর্ণ সময়ে টিকে থাকার পরামর্শ দেয়নি। পক্ষান্তরে, তাওবাদ হলো তাদের দর্শন যারা ক্ষমতা, সম্পদ এবং পদমর্যাদার ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতিকে বুঝতে পেরেছে, যেগুলি থাকার চেয়ে না থাকাই যথেষ্ট ভালো। সত্তার সামগ্রিক ঐকতানের বিকাশ ঘটানোর অভিপ্রায় যাদের রয়েছে তাদের জন্য ব্যর্থতা বা স্থৈর্যের দর্শন থেকে দূরবর্তী তাওবাদ এক গভীর ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আকড়।
————
মূল : Anarchism and Taoism by Josh
উৎস : theanarchistlibrary.org
দুলু সরকার
জন্ম— ১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩রা কার্তিক। পড়াশোনা— জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর। বিশেষ অনুরাগ— দার্শনিক ধারার সাহিত্য পাঠ, অনুবাদ; অল্পবিস্তর কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা।