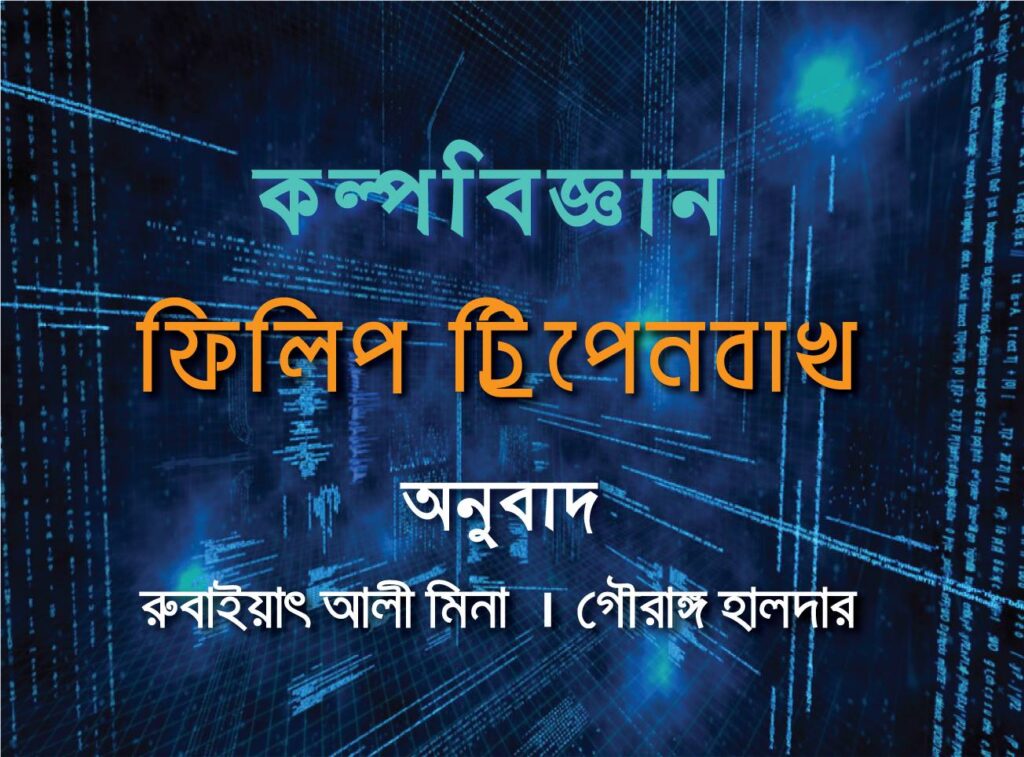বৃটিশ সামাজিক-নৃবিজ্ঞানে সাংস্কৃতিক-অনুবাদের ধারণা // তালাল আসাদ, অনুবাদঃ মোহাম্মদ সাঈদ হাসান খান
[বর্ষীয়ান নৃতত্ত্ববিদ তালাল আসাদ গত প্রায় পাঁচ দশক ধরে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি বিষদ গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সাংস্কৃতিক-নৃবিজ্ঞান, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ, মধ্যপ্রাচ্য, ধর্মতত্ত্ব, ইসলাম, সেকুলারিজম, মানবাধিকার ইত্যাদি তার গবেষণার বিষয়বস্তু। সৌদি আরবের মদিনায় ১৯৩২ সালে তালাল আসদের জন্ম আর বেড়ে ওঠা পাকিস্তানে। এরপর ১৮ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে যান। যুক্ত্রাজ্যের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৯ সালে তিনি নৃবিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করেন। তিনি তার পিএইচডি সম্পন্ন করেন ১৯৬৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর সেখানে তিনি বিশিষ্ট সামাজিক-নৃবিজ্ঞানী ইভান্স-প্রিটচার্ডের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি শিক্ষকতা করেছেন সুদানের খারতুম ইউনিভার্সিটি, ইংল্যান্ডের হাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্রের জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটিসহ আরো বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে। বর্তমানে তিনি নিউ ইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটিতে নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তালাল আসাদ রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে জিনিয়ালজিস অব রিলিজিয়ন (১৯৯৩), ফরমেশনস অব দ্যা সেকুলার (২০০৩) এবং অন সুইসাইড বোম্বিং (২০০৭)।]
সূচনা
ই, বি টেইলর প্রদত্ত সংস্কৃতির এই বিখ্যাত সংজ্ঞাটির সাথে সকল নৃবিজ্ঞানীই পরিচিত: “জাতিতত্ত্বের বৃহৎ পরিসরে সংস্কৃতি অথবা সভ্যতা হলো সেই জটিল বিষয় যার মধ্যে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নৈতিকতা, আইন ও প্রথা সহ সমাজের একজন সদস্য হিসেবে একজন মানুষের অর্জিত অন্য যে কোন সক্ষমতা ও অভ্যাস অন্তর্ভুক্ত”। মানুষের “সক্ষমতা ও অভ্যাসের” হিসেবই হলো সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতির এমন ধারণায়, লিন্টন যাকে বলছেন সামাজিক-উত্তরাধিকার (সক্ষমতা ও অভ্যাস সম্পর্কে শিক্ষা লাভের উপায় হিসেবে), তার ওপরই জোর দেয়া হতো সবচেয়ে বেশি, সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের এমন ধারণা কখন ও কিভাবে যে একটি টেক্সটের ধারণা অর্থাৎ অন্তর্লিখিত-ডিসকোর্সের অনুরূপ ধারণায় রূপান্তরিত হলো তা খুঁজে বের করা বেশ আকর্ষণীয় একটি কাজ হতে পারে। ইতিহাসের অগ্রগতি ও সামাজিক শিক্ষার (চর্চা) ক্ষেত্রে ভাষার ধারণা হলো পূর্বশর্ত, সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে এই ধারণার আধিপত্যই সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণার এমন পরিবর্তনের অন্যতম সুস্পষ্ট কারণ হিসেবে নির্দেশ করা যেতে পারে। অবশ্য সাধারণভাবে বলতে গেলে, ভাষার প্রতি এমন আগ্রহ টেইলরের সময়কালের অনেক আগে থেকেই লক্ষণীয়, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এই বিষয়টিই মানব-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় না হলেও বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সাহিত্য-তত্ত্ব ও শিক্ষার মূল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। কখন ও কিভাবে বিষয়টি বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল? আমি সেই ইতিহাস এখানে আওড়াতে চাই না, কিন্তু শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৫০ পরবর্তী সময় থেকে সামাজিক-নৃবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্রসূচক কাজ হিসেবে গড়পড়তা ভাবে “সংস্কৃতিসমূহের অনুবাদ” এই কথাটি ব্যবহার করা হলেও এই সময় কালের আগে এই ধারণার ব্যবহার তেমন একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আপাত পরিবর্তনের এই ঘটনাটিকে সেই পুরনো প্রাক-ফাংশনালিজম/ ফাংশনালিজমের কাল বিভাগের সাথে তুলনা করলে চলবে না। কিংবা ব্যাপারটি শুধুমাত্র ভাষা ও তার অর্থের প্রতি নতুন করে তৈরী হওয়া কোন বিশেষ আকর্ষণও নয় যা আগে ছিল না। ফাংশনালিস্ট ঘরানার অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা ব্রনিসলঅ ম্যালিনোস্কি “আদিম ভাষা” বিষয়ে অনেক লিখেছেন এবং নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য প্রচুর পরিমানে ভাষাসংক্রান্ত উপাদান (প্রবাদ, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পরিভাষা, জাদু মন্ত্র ও অন্যান্য) সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তিনি কখনই তার নিজ কাজকে সংস্কৃতিসমূহের অনুবাদের প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করেননি।
গডফ্রে লিয়েনহার্ডটের এর “মুডস অব থট” (১৯৫৪) প্রবন্ধটিই এই বিষয়ে সম্ভবত একদম প্রথম দিককার অন্যতম প্রবন্ধ এবং নিশ্চিত ভাবেই সেই সকল কৌশলী উদাহরণগুলোর একটি যেখানে সামাজিক-নৃবিজ্ঞানের একটি মূল কাজ বর্ণনা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবেই অনুবাদের এই ধারণার ব্যবহার করা হয়েছে। “অপরিচিত একটি জাতি কিভাবে চিন্তা করে সেই বিষয়টি অন্য কারো নিকট ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যে বিপত্তি তা মূলত অনুবাদের বিপত্তি অর্থাৎ অপরিচিত ঐ ভাষাটিতে চিন্তার যে প্রাথমিক সঙ্গতি রয়েছে তাকে আমদের নিজস্ব ভাষায় অমনই স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার বিপত্তি”। পরবর্তী অংশে আমি আর্নেস্ট গেলনারের যে প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রবন্ধটিতে উপরোক্ত বাক্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে আর এর সমালোচনা করা হয়েছে। গেলনারের যুক্তির প্রেক্ষিতে উপরোক্ত বাক্য সংক্রান্ত আলোচনায় আমি কিছুক্ষণ পরে যাচ্ছি। তার আগে এখানে আমি খুবই স্বল্প পরিসরের মধ্যে লিয়েনহার্ডটের “অনুবাদ” শব্দটির ব্যাবহারের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এখানে অনুবাদ বলতে কেবল ভাষান্তরের কথা বলা হয়নি বরং অনুবাদের মধ্যে “চিন্তার বিভিন্নতার” বিষয়টি যে অঙ্গীভূত হয়ে আছে তার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে এই তথ্যটিও হয়তো অগুরুত্বপূর্ণ নয় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড লিয়েনহার্ডটের রয়েছে,অক্সফোর্ডে ই,ই রিচার্ড-প্রিটচার্ডের একজন শিষ্য ও সহকর্মী হিসেবে কাজ করার পূর্বে তিনি ক্যামব্রিজে এফ,আর, লেভিসের শিষ্য ছিলেন।
বৃটেনে নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে অক্সফোর্ডের সুনাম অনেক আর “সংস্কৃতি সমূহের অনুবাদ” এর প্রতি প্রদেয় মনযোগের বিষয়ে তারা বেশ আত্মসচেতন। সেখান থেকে প্রকাশিত জন বিয়েটির আদার কালচারস (১৯৬৪) নামের পরিচিতিমূলক পাঠ্যবইটি বহুল পরিচিতি পেয়েছিল । বইটিতে সামাজিক-নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে “অনুবাদের সমস্যার” ওপর জোর দেয়া হয়েছে এবং “সংস্কৃতি” ও “ভাষার” মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে (কিন্তু তাদেরকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি)। “সংস্কৃতি” ও “ভাষার” মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশের এই ধারণাটি তখন নৃবিজ্ঞানীদের কাছেও বেশ সুপরিচিত হয়ে উঠতে থাকে—তবে তার মানে এই নয় যে এদের মধ্যকার পার্থক্যের এই ধারণাটি খুব স্পষ্ট ছিল। (পৃষ্ঠা ৮৯-৯০)
মজার ব্যাপার হলো এরো প্রায় এক দশক পরে, এডমুন্ড লিচ, যার কিনা অক্সফোর্ডের সাথে কোনই সম্পৃক্ততা নেই, তার সামাজিক-নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসের পরিলেখর উপসংহারে এই একই রকম ধারণা প্রদান করেন:
এবার সার কথাটি বলি। প্রথমে আমরা জোর দিয়ে বলেছিলাম অন্যরা আমাদের থেকে কতোটাই না আলাদা—আর বলেছিলাম ওরা আমাদের থেকে শুধু ভিন্নই না বরং আমাদের থেকে ওদের দূরত্ব অনেক আর ওরা নিম্ন বর্ণের। এরপর আবেগ প্রবণ হয়ে আমরা ঠিক বিপরীত পথটা বেছে নিয়েছিলাম আর বলেছিলাম সব মানুষ আসলে একই রকম; ট্রবিয়ান্ডার আর ব্যরোটসদের আমরা বুঝতে পারি, কারণ, ওদের চাওয়া-পাওয়াগুলো সাথে আমাদের চাওয়া-পাওয়াগুলোর কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু এ চিন্তাও কাজে লাগেনি, “পর” গোঁয়ারের মত পরই থেকে গেছে। তবে, এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, মূল সমস্যাটি হলো আসলে অনুবাদের সমস্যা। ভাষাবিদরা আমাদের দেখিয়েছেন যে সব অনুবাদই কঠিন, আর যথাযথ অনুবাদ আসলে প্রায় অসম্ভবই। আর আমরা এও জানি যে মূল লেখাটি যত ভয়ানক রকমের দূর্বোধ্যই হোক না কেন ব্যবহারিক কাজের জন্য সহনীয় মাত্রার সন্তোষজনক অনুবাদ করা সবসময়ই সম্ভব। সব ভাষাই একে অপরের থেকে ভিন্ন তবে এতটাও ভিন্ন তারা নয় যে তাদের কোন ভাষান্তরই সম্ভব হবে না। পুরো বিষয়টির প্রতি এমনই একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সামাজিক-নৃবিজ্ঞানীরা সাংস্কৃতিক-ভাষার অনুবাদের একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন”। (লিচ ১৯৭৩, ৭৭২)
লিচের এমন বক্তব্যের অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ম্যাক্স গ্লুকম্যানও (১৯৭৩, ৯০৫) “সাংস্কৃতিক-অনুবাদের” কেন্দ্রীয়তার কথা স্বীকার করে নেন যদিও নৃবিজ্ঞানের অমন চর্চার জন্য তিনি খুব ভিন্ন রকমের একটি ধারা প্রস্তাব করেছিলেন।
সাংস্কৃতিক-অনুবাদের এই ধারণাটি বৃটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের আত্মপরিচয় হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত হলেও, সামাজিক-নৃবিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে নিয়মানুগ নিরীক্ষা খুব বেশি হয়নি। এক্ষেত্রে, রডনি নিধহামের বিলিফ, ল্যংগুয়েজ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স (১৯৭২) কিছুটা ব্যতিক্রম। এমন জটিল আর পান্ডিত্যপূর্ণ কাজ নিয়ে আলোচনা করতে আরো বড় পরিসরের প্রয়োজন হবে। আমি অবশ্য এখানে আরো ছোট রচনার প্রতি মনোনিবেশ করতে চাই, আর তা হলো আর্নেস্ট গেলনারের “কনসেপ্টস অ্যান্ড সোসাইটি”। টেক্সটটি বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আন্ডারগ্রাজুয়েট কোর্সগুলোতে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এখনো বেশ কিছু জনপ্রিয় সংকলনে টেক্সটটি পাওয়া যায়। তাই, আমার লেখার এই অংশটি এই প্রবন্ধটি নিয়ে একটি বিষদ নিরীক্ষায় নিবিষ্ট থাকবে আর এই প্রবন্ধটি নিয়ে আমার এই আলোচনায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বেরিয়ে আসবে সেগুলো আলোচিত হবে তার পরবর্তী অংশে।