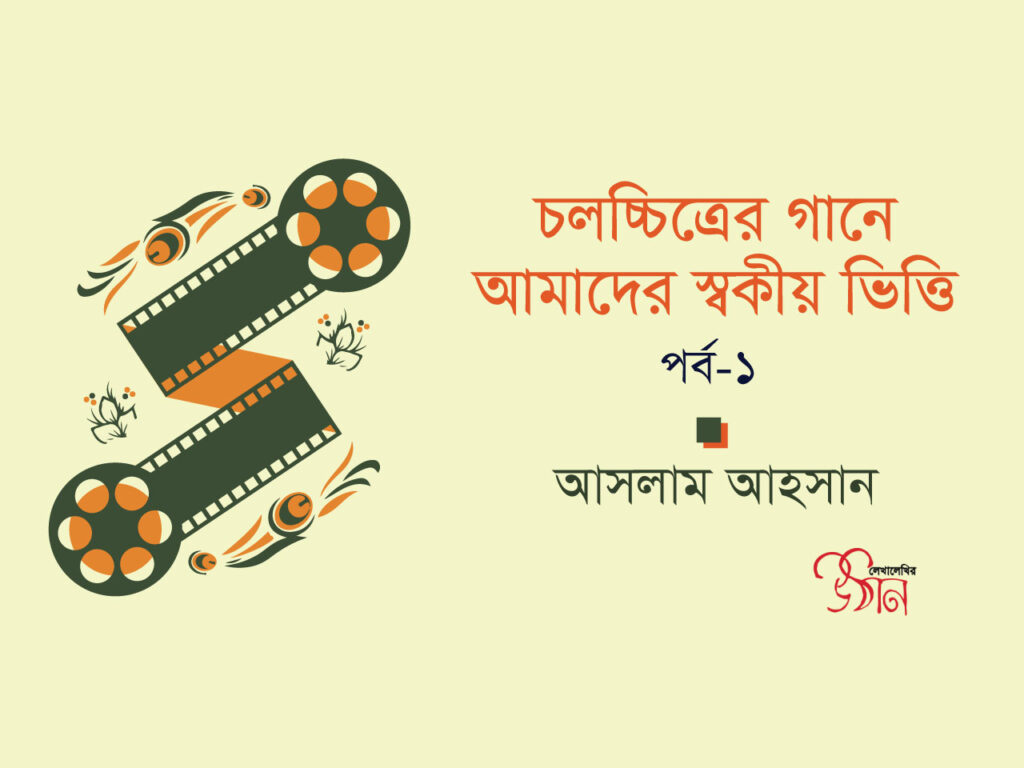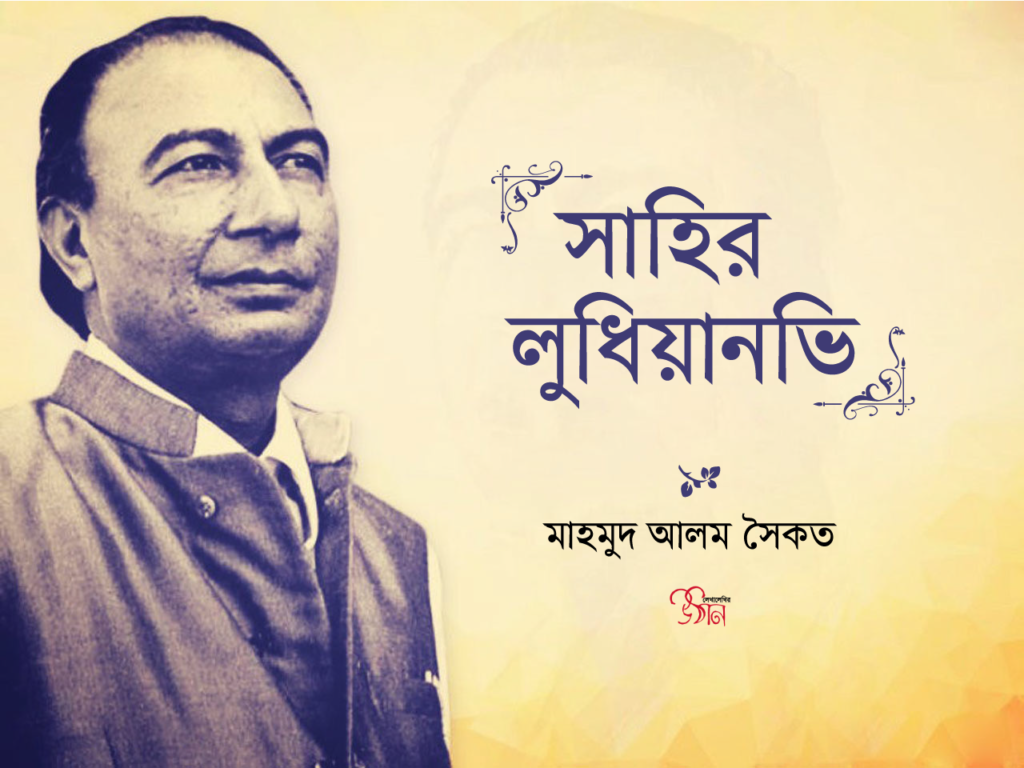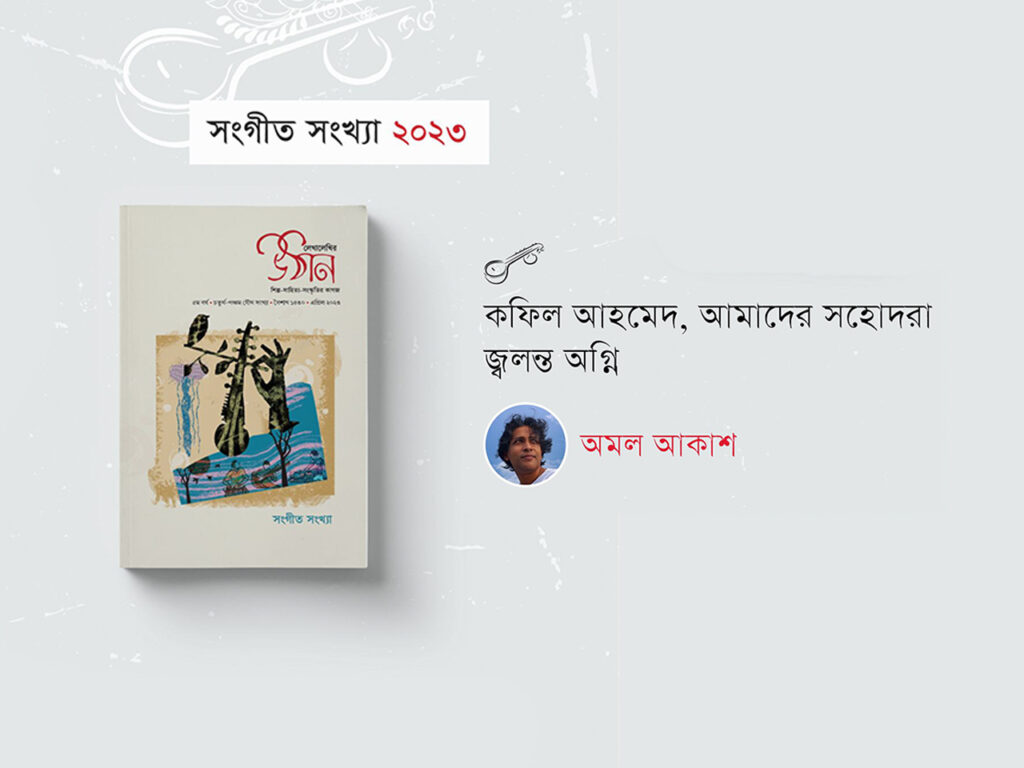৪
পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক গানের সমান্তরালে আমাদের এই ভুখ-ে আবু বকর খান, আনোয়ার উদ্দীন খান, আসাফউদদৌলা পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি আধুনিক গানের যে ধারাটা সৃষ্টি করেছিলেন, তা যদি বহমান থাকতো এবং সে সময়ে সৃষ্ট অসাধারণ গানগুলো যদি রেকর্ডে ধরে রাখা যেত, তাহলে আমাদের নিজস্ব আধুনিক গানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লেখার কাজটি সহজতর হতে পারত। সেটি হয়নি। এ সময়ে যারা ফার্স্ট বিটে গান করে ‘ক্রেজ’ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন, তারা যদি বেতারে প্রচারিত আবু হেনা মোস্তফা কামালের কথায় আনোয়ার উদ্দীন খানের নিজস্ব সুরে গাওয়া ‘পথে যেতে দেখি আমি যারে’ গানটি শোনেন, উপলব্ধি করবেন-সত্যিকার অর্থে তারা এখনও নতুন কিছু ‘আবিষ্কার’ করতে পারেননি; পুনরাবিষ্কারই করে চলেছেন কেবল।
পথে যেতে দেখি গানটি শুনতে ক্লিক করুন
যাবার বেলায়-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
পথের ক্লান্তি ভুলে-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ প্রেমের গানেও আমরা এমন অসাধারণ বাণী বিন্যাস দেখেছি, মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ‘অদ্বিতীয়া’ (১৯৬৮) ছবিতে মুকুল দত্তের লিরিক-
‘যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে
কেন বলো কাঁদালে আমায় / আমার এ মন বুঝি মন নয় ॥’
আর, মোহিনী চৌধুরীর লেখা কমল দাশগুপ্তের সুরে ১৯৪৫ সালে সত্য চৌধুরীর রেকর্ডের গান: ‘পৃথিবী আমারে চায় / রেখো না বেঁধে আমায় / খুলে দাও প্রিয়া, খুলে দাও বাহুডোর’- সে তো একই সাথে প্রেমের গান এবং দুর্দান্ত গণসংগীত।
‘পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলে তব / মা গো বলো কবে শীতল হবো’-‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ (১৯৫৯) ছবিতে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা গান। ‘[…] বলো তার কী অপরাধ জন্ম হয়েছে যার পাঁকে / তোমার ক্ষমা দিয়ে তুমি ফোটাও পদ্ম করে তাকে’- একই গীতিকারের রচনা ‘প্রতিদান’ (১৯৮৩) ছবির গান। চলচ্চিত্রর গানের বাণীও এতটা অতলস্পর্শী হতে পারে! তাহলে আমাদের চলচ্চিত্রর গানে স্বকীয় ভিত্তির ভরকেন্দ্র কোথায়?
সেটা আমাদের লোকজ গানে। লোকসংগীতের ধারা অন্যান্য দেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বহমান। কিন্তু বাংলাদেশি লোকসুরের যে চিরায়ত আবেদন, ওখানকার গানে তা দুর্লভ। মানবন্দ্রে মুখোপাধ্যায়ের এক টিভি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, প্লেব্যাক জীবনের শুুরুতে তিনি ভাটিয়ালী টাইপ গান বেশি গাইতেন। ‘নবজন্ম’ (১৯৫৮) চলচ্চিত্রয় তাঁর গাওয়া ‘ওরে মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে’ তখন সে জনপ্রিয়। সে সময়ের কথা। কলকাতার বেলেঘাটার এক গানের জলসায় গাইতে গিয়েছেন তিনি। আচমকা মাইক্রোফোন বিভ্রাট। সামনে বসে পাঁচ হাজারের মতো দর্শক শ্রোতা তখন স্থবির। সেই মুহূর্তে আয়োজকদের কাছ থেকে এক রকম জোর করে অনুমতিনিয়ে মঞ্চে উঠে পড়েন গ্রাম্য যুবক। যুবক জানালেন- ‘আমার কোন মাইক-মুইক লাগে না।’ কথা শুুনে আমন্ত্রিত শিল্পীরা মুচকি হাসেন। নামধাম কিছু উল্লেখ না করেই দোতরা হাতে সরাসরি গান শুরু: ‘মাঝি রে…।’ পাঁচ হাজার দর্শকের বুকে যেন বর্শার ফলক বিঁধে গেল! পরে জানা গেল, যুবকের নাম নির্মলেন্দু চৌধুরী, এসেছে সিলেট থেকে। খালি গলায় নির্মলেন্দু চৌধুরীর উদাত্ত কণ্ঠের গান শুনে সেই দিন থেকেই ভাটিয়ালী গাওয়া ছেড়ে দেন মানবেন্দ্র, চিরদিনের জন্য।
ওরে মন মাঝি-গানটি শুনতে ক্লিক করু
নির্মলেন্দু চৌধুরীর গান শুনতে ক্লিক করুন
শুধু সুর নয়; আমাদের লোকগানের বাণীও বেশ সমৃদ্ধ। ইদানিং দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরা বাংলাদেশের লোকআঙ্গিকের গানগুলো নতুন সংগীতায়োজনে গাইতে শুরু করেছেন, অবশ্য তাদের মতো করে। যে কারণে ওরা যখন লালনগীতি গান, আমাদের কানে সেটা আধুনিক গান বলেই মনে হয়। সুরের মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণে পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব চেহারা ও চরিত্র হারাচ্ছে আমাদের লোকগান।
৫
ষাটের দশকের শুরুর দিকে উর্দু ছবির প্রবল বিপ্রতীপ স্রােতের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের নির্মাতাগণ বাংলা ছবি নির্মাণে ব্রতী হন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত উর্দু ছবির রমরমা বাজার ছিল। জহির রায়হানের মতো সৃষ্টিশীল মৌলিক প্রতিভাও উর্দু ছবি নির্মাণের দিকে ঝুঁকেছিলেন এক পর্যায়ে। পরে অবশ্য তিনি এবং অন্যরাও এ বলয় থেকে বেরিয়ে আসেন।
বাংলা ছবির বাজার ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় লোককাহিনীভিত্তিক ছবি ‘রূপবান’ (১৯৬৫) নিয়ে কান্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সালাহউদ্দীন। দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ে হলগুলোতে। বাণিজ্যিকভাবে দারুণ সাফল্য অর্জন করে ছবিটি। এরপর থেকে ছবি তৈরির ধারাই বদলে গেল। ‘রূপবান’-এর মধ্য দিয়ে নতুন এক যুগের সূচনা হলো।
‘রূপবান’-এর পর স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে লোককাহিনী ভিত্তিক প্রচুর ছবি নির্মিত হয়েছে যার বেশীর ভাগই স্মরণীয় হয়ে আছে লোকআঙ্গিকের গানের বদৌলতে। কিন্তু ‘রূপবান’-এর জনপ্রিয়তা এক্ষেত্রে একটি ট্রেন্ড। এরপর এ জাতীয় ছবি তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। ‘এ কালের রূপকথা’ (১৯৬৬), ‘গুনাই বিবি’ (১৯৬৬), ‘মহুয়া’ (১৯৬৬), ‘আপন দুলাল’ (১৯৬৬), ‘জরিনা সুন্দরী’ (১৯৬৬), ‘কাঞ্চনমালা’ (১৯৬৭), ‘সাইফুলমুলক বদিউজ্জামান’ (১৯৬৭), ‘মধুমালা’ (১৯৬৮), ‘রাখাল বন্ধু’ (১৯৬৮), ‘সাত ভাই চম্পা’ (১৯৬৮), ‘অরুণ বরুণ কিরণ মালা’ (১৯৬৮), ‘পাতালপুরীর রাজকন্যা’ (১৯৬৯), ‘বেদের মেয়ে’ (১৯৬৯), ‘লালন ফকির’ (১৯৭২), ‘নিমাই সন্ন্যাসী’ (১৯৭২), ‘কাজলরেখা’ (১৯৭৬), ‘মহুয়া সুন্দরী’ (১৯৮৭), ‘বেদের মেয়ে জোস্না’ (১৯৮৯), ‘গাড়িয়াল ভাই’ (১৯৯২), ‘খায়রুন সুন্দরী’ (২০০৪)। প্রভৃতি লোককাহিনীভিত্তিক ছবির গানগুলো মানুষের মনে যেভাবে গেঁথে আছে, অন্য কোন ধারার গানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। লক্ষ করার মতো বিষয়, এ ধারার ছবির কেন্দ্রে প্রায়শই নারী চরিত্রের প্রাধান্য দেখা গেছে। আমাদের চলচ্চিত্রয় লোকগান ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি ধারায় :
১. সরাসরি লোকসঙ্গীত ও পল্লিগীতি
২. লোক আঙ্গিকের গান
৩. লোকসুর মিশ্রিত আধুনিক গান (‘ফোন ফিউশন’ নামে বহুল পরিচিত)।
চলচ্চিত্রে লালন ফকির, হাসন রাজা, দুর্বীন শাহ, সৈয়দ শাহনূর শাহ, উকিল মুনশী, রশিদ উদ্দিন প্রমুখ মরমী সাধক ও লোককবিদের গান যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি তাঁদের কথা ও সুরের ধারা অনুসরণে রচিত লোক আঙ্গিকের প্রচুর গান আমাদের চলচ্চিত্রসংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। লালনের জীবন ও দর্শন নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। হাসন রাজার জীবনী নিয়েও হয়েছে চলচ্চিত্র।
বেতারের জনপ্রিয় ও স্মরণীয় আধুনিক গানগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পল্লীসুরে রচিত। কিছু গান তো এমন যে, গানগুলো আধুনিক, না পল্লিগীতি; শ্রেণি নির্ণয় করাই কঠিন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় এমনি কিছু গানের প্রথম লাইন:
‘বাঁশি বাজে ঐ দূরে’ (কথা-সুর-শিল্পী: মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী), ‘কলসি কাঁখে ঘাটে যায় কোন রূপসী’ (কথা: ফজল-এ-খোদা, সুর: ধীর আলী মিয়া, শিল্পী: মোহাম্মদ আবদুল জব্বার), ‘বাসন্তী রঙ শাড়ি পরে’ (কথা: ফজল-এ-খোদা, সুর: ধীর আলী মিয়া, শিল্পী: খন্দকার ফারুক আহমেদ), ‘লোকে বলে প্রেম আর আমি বলি জ্বালা’ (কথা-সুর-শিল্পী: আনোয়ার উদ্দিন খান), ‘মন রে, ভবের নাট্যশালায় মানুষ চেনা দায়’ (কথা: আজিজুর রহমান, সুর ও শিল্পী: মোহাম্মদ আবদুল জব্বার), ‘রেল লাইন বহে সমান্তরাল’ (কথা: নজরুল ইসলাম বাবু, সুর: শাহনেওয়াজ, শিল্পী: দিলরুবা খান)।
বাঁশি বাজে ঐ দূরে-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
কলসী কাঁখে- গানটি শুনতে ক্লিক করুন
বাসন্তী রঙ শাড়ী- গানটি শুনতে ক্লিক করুন
ভবের নাট্যশালায়-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
রেল লাইন বহে -গানটি শুনতে ক্লিক করুন
ইদানিং জনপ্রিয় ব্যান্ড সংগীতকেও বার বার পল্লীঘরানার কথা ও সুরের দ্বারস্থ হতে দেখা গেছে। হাবিবের কম্পোজিশনে বরাবরই লোকসুরের প্রাধান্য। চলচ্চিত্রর গানে যে গানটি দিয়ে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে হাবিবের উত্থান এবং জনপ্রিয়তা; (ভালোবাসব বাসব রে বন্ধু, হৃদয়ে কথা-২০০৬)- তাতেও লোকসুরের আমেজ। হাবিবের প্রথম অডিও এলবাম কৃষ্ণ (২০০৩) সরাসরি লোকসুরভিত্তিক। ওই এ্যালবামের কিছু গান সংগৃহীত, কিছু শাহ আব্দুল করিম (১৯১৬-২০০৯), দীনহীন (১৮৯৩-১৯৫৮) প্রমুখের রচনা।
লোক আঙ্গিকের গানে উপমা অলঙ্কার কি ংবা অন্ত্যমিলের বাহাদুরি থাকে না, ভাষার মারপ্যাঁচ থাকে না। সহজ সরল ভাষায় এখানে মানুষের মনে কথা তুলে ধরা হয়। তবে ‘বেদের মেয়ে’ (১৯৬৯) ছবির একটি গানে জসীম উদ্দীন যে উপমার খেলা দেখিয়েছেন, তা স্বতঃস্ফূর্ত, অথচ শৈল্পিক:
‘যারে ছেড়ে এলাম অবহেলে রে
সে কি আবার আসবে ফিরে
[… …]
সে ছিল মোর বুকের মণি রে
এখন জ্বলে সাপের শিরে / (সে কি আবার আসবে ফিরে) ॥’
গানটি শুনতে ক্লিক করুন
বুকের মণি এখন সাপের মাথার মণি হয়ে শোভা পাচ্ছে! সে সুন্দর, একই সঙ্গে ভয়ঙ্করও। তাকে ছোঁয়া যায় না; নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে দেখতে হয়। একান্ত কাছের মানুষ সময়ের ব্যবধানে দুর্লভ-দূরের মানুষ হয়ে যাওয়ার প্রগাঢ় বেদনা এই কথাগুলোতে যে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত, তার তুলনা হয় না। প্রচলিত অর্থে লোককাহিনীভিত্তিক ছবি নয়; কিন্তু লোকআঙ্গিকের গান ব্যবহৃত হয়েছে অন্য ধারা ছবিতেও এবং সে গান ঐ ছবির জনপ্রিয়তায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে- এমন দৃষ্টান্তও অল্প নয়। প্রদত্ত তালিকা থেকে লোকসুরাশ্রিত গানের জনপ্রিয়তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।
আমি ভিন গেরামের নাইয়া- শুনতে ক্লিক করুন
পথে পথে দিলাম-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
নিশি জাগা চাঁদ-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
শোনেন শোনেন জাহাপনা-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
ওরে সাম্পান ওয়ালা-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
সবাই বলে বয়স বাড়ে-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
আমি না জানিলাম-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
ওরে কর্ণফুলীরে-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
তুমি দেখা দাও দরদী-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
ঢাকায় যারা চাকরী-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
বাঁশি বারণ মানে না-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
মাটির কোলে খাঁটি-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
কিছু গান সংগৃহীত, কিছু ছবির জন্যই রচিত, কিছু গানে আধুনিকতার ছোঁয়া, কোনটায় আবার বৈষ্ণবভাব… কিন্তু সবটাতে লেগে আছে সোঁদা মাটির গন্ধ। লোকগানের আঙিনায় এই যে বার বার বিভিন্ন রঙে, বিভিন্ন ঢঙে প্রত্যাবর্তন- সেটা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে, লোকসংগীতই আমাদের শেকড়। শুধু এই একটিমাত্র ধারাতেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত এবং অন্যান্য দেশের সংগীত থেকে কথা ও সুরে স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারি। এইসব গানের কথা ও সুর আমাদের চিরায়ত বাঙালি জীবনকে ধারণ করে। চিরচেনা বাঙালি জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাব। প্রথম গানটির কথাই ধরা যাক: ‘আমি ভিন গেরামের নাইয়া।’ এই গানটি আমাদের মাঝি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সাথে নৌকায় নৌকায় যারা এক সময় বাণিজ্যের বেসাতী নিয়ে ঘুরে বেড়াত, তাদের কথাও আছে এ গানে। ‘পথে পথে দিলাম ছড়াইয়া’; এই গানেও মাঝি। মাঝি এখানে জীবন নদীর কূলে দিশাহারা এক শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি। তারপরের গানটি এক ক্রন্দসী রমণীর অভিমান- আকাশে চাঁদ হাসছে, সে কেন হাসতে পারছে না? তালিকায় উক্ত ‘সাত ভাই চম্পা’ ছবির উক্ত গানটিকে (শোনেন শোনেন জাহাঁপনা) বলা যায় ঐ ছবির সারাংশ। ছবিটি রূপকথাভিত্তিক, গানের ভাষাতেও তারই সহজ উদ্ভাস। একটু তলিয়ে দেখলে আমরা টের পাই; এই ছবিতে, এই গানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমাদের জাতীয় ঐক্যের কথা, সংঘবদ্ধ শক্তির কথা।
‘নিমাই সন্ন্যাসী’ (১৯৭২) ছবিতে মৌসুমী কবিরের গাওয়া ‘নিমাই দাঁড়া রে’ গানের এক দিকে বাৎসল্যপ্রেম, অন্যদিকে ঈশ্বরপ্রেম।
(গানটির মূল শিল্পী অনন্তবালা বৈষ্ণবী।)
নিমাই দাঁড়ারে-গানটি শুনতে ক্লিক করুন
‘ফকির মজনু শাহ’ (১৯৮৩) ছবিতে গাজী মাজহারুল আনোয়ার রচিত গানে বিধৃত হয়েছে মানবজীবনের চরম সত্য :
‘সবাই বলে বয়স বাড়ে আমি বলি কমে
এই) মাটির ঘরটা খাইল ঘুণে প্রতি দমে দমে ॥’
‘আরাধনা’ (১৯৭৯) ছবির ‘আমি না জানিলাম না চিনিলাম রে’ গানটিতে দ্ব্যর্থকতা আছে। পথে যেতে যেতে বাউল গাইছে: …‘সে যে ঘরের পাশে ঘর বানাইয়া আছে লুকাইয়া।’ গানটি আধ্যাত্মিক। বিধাতা মানুষের খুব কাছেই থাকেন, মানব-হৃদয়েই তাঁর বসবাস। কিন্তু মানুষ তা টের পায় না। বাউলের আক্ষেপে গানের উদ্দীষ্ট অর্থ এটাই। আবার, এ গানের আরেকটি অর্থ সরাসরি ছবির গল্পের সাথে সম্পর্কিত। নায়িকা (কবরী) জানে না যে, তার প্রিয় মানুষটি (বুলবুল আহমেদ) আর ইহজগতে নেই। তার এই অপেক্ষা অর্থহীন, অন্তহীন। ঘরের পাশে ঘর বানিয়ে যে লুকিয়ে আছে, সে আর কোনদিনই ফিরতে পারবে না। প্রিয় মানুষটির কবরের পাশে বসেই সে অপেক্ষা করে তার মনের মানুষ একদিন আসবেই: ‘সেই সান্ত¡নাতে বুকটি আজও রাইখাছি বান্ধিয়া।’ বাণীর এই দ্ব্যর্থক ব্যঞ্জনা,নিগুঢ় বেদনা গানটিকে ক্লাসিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে।
নিজের কষ্টার্জিত ফসল সোনার তরীতে তুলে দিয়ে কৃষক যখন অনুরোধ করে-‘এবার আমারে লহো করে’, জবাব আসে নেতিবাচক: ‘ঠাঁই না ঠাঁই ছোটো সে তরী/আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।’ রবীন্দ্রনাথের এই দর্শনটুকুই কি আমরা পেয়ে যাই না ‘রূপবান’ (১৯৬৫) ছবিতে ব্যবহৃত কোন এক লোককবির এই গানে?-
কারে ডেকে বলছো মাঝি, ‘আমার নায়ে আয়’
আমায় দেখে বলছো মাঝি-
‘আমার নায়ে তো জাগা নাই।’
‘আকাশ আর মাটি’ (১৯৫৯) ছবিতে মমতাজ আলী খানের গাওয়া ‘মুর্শিদ দাও দেখা দরদী’ কিংবা ‘আরশীনগর’ (১৯৭৮) ছবিতে সৈয়দ আব্দুল হাদীর গাওয়া ‘তুমি দাও দেখা দরদী’ গানে পাই বঙ্গভূমির সহজ সরল ধর্মভীরু মানুষের প্রতিচ্ছবি। তারা দর্শনের কুটতর্ক বোঝে না, বুঝতে চায় না। ¯্রষ্টার সান্নিধ্য চায় নিঃশর্ত আত্মনিবেদনে, আটপৌরে ভাষায়-
‘তুমি দাও দেখা দরদী
তোমায়) না দেখিলে প্রাণ আমার বাঁচে না রে ॥
[…]
দয়াল আমারে করিয়া দীন
তুমি হইলা জলের মীন রে
তোমায়) অঞ্চলে বান্ধিয়া রে রাখব ॥’
তোমায় পিঞ্জিরায় ভরিয়া রাখব, গলেতে গাঁথিয়া রাখব; অধরাকে ধরার বাঁধনে বাঁধার এমনি আরও কত আকুতি। চলচ্চিত্রর গান না হলেও এই প্রসঙ্গে পরান ফকির রচিত একটি গানের কথা এসে যায়: ‘তুমি কোন দ্যাশে রইলা রে দয়াল’-
‘দয়াল তোমার লাগিয়া দেশে না বৈদেশে
আমি পাইতাছি পিরিতির ফান্দ
তুমি কোন বা দ্যাশে রইলা রে দয়াল চান ॥’
এই গানের কথায় যে আকুতি, সুরের যে আর্তি; মনে হয়-অমন করে ডাকলে পিরিতের ফাঁদে ‘তিনি’ ধরা না দিয়ে থাকতে পারেন? গুরুভক্তি এদেশের মানুষের স্বভাবজাত। লৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে মুর্শিদকেই তারা মনে করে নির্ভরতার পরম আশ্রয়। তাই তারা নিঃসংশয়ে বলতে পারে-
‘আছেন আমার মোক্তার
আছেন আমার বারিস্টার
শেষ বিচারের হাই কোটেতে
তিনি আমায় করবেন পার
আমি পাপী তিনি জামিনদার ॥’
কথা : গাজী মাজহারুল আনোয়ার, সুর: আলাউদ্দীন আলী, ছবি: গোলাপী এখন ট্রেনে (১৯৭৮)
৬
‘রূপবান’ (১৯৬৫) থেকে লোকজ ধারার ছবি ও গানের যে ধারাটি বইতে শুরু করে, সত্তর দশকে এসে বেগবান হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে চিত্র পরিচালক আমজাদ হোসেন একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর পরিচালিত ‘নয়নমণি’ (১৯৭৬), ‘গোলাপী এখন ট্রেনে’ (১৯৭৮), ‘সুন্দরী’ (১৯৭৯), ‘দুই পয়সার আলতা’ (১৯৮২), ‘ভাত দে’ (১৯৮৪) ইত্যাদি ছবির প্রায় প্রতিটি গান এখন মানুষের মুখে মুখে। এর কারণ, গানের কথাগুলো সাধারণ মানুষেরই মনের কথা। এসব ছবির অধিকাংশ জনপ্রিয় গানই আমজাদ হোসেনের লেখা। লক্ষণীয়, সৈয়দ আব্দুল হাদী ও সাবিনা ইয়াসমিন, রথীন্দ্রনাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী; এই ক’জন কণ্ঠশিল্পীই মূলত ঘুরে ফিরে এসেছেন এ ধারার গানে।
লোকজ ধারার চলচ্চিত্রের কাহিনি ও গানে নিখাদ ধর্মবোধ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও রয়েছে তীব্র প্রতিবাদ। ‘নয়নমনি’ (১৯৭৬) ছবিতে সৈয়দ আব্দুল হাদী ও ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর গাওয়া গান ‘কোন কিতাবে লিখা আছে গো হারাম বাজনা গান’ তো সংগীতের প্রতি অহেতুক নিষেধাজ্ঞারই জবাব।
গানটি শুনতে ক্লিক করুন
‘কোন কিতাবে লেখা আছে গো/ হারাম বাজনা গান/… সুর যদি হারাম হতো / বেলালে কি আজান দিতো / পড়ত কি কেউ মধুর তানে পবিত্র কোরান ॥’ পাপ-পুণ্যের বিচার অত্যাচারী মানুষ নিজের হাতে তুলে নিয়ে মানুষেরই অবমাননা করে। তারই প্রতিবাদ শুনি ‘নালিশ’ (১৯৮২) ছবির গানে-
‘খোদার ঘরে নালিশ করতে দিল না আমারে
পাপপুণ্যের বিচার এখন মানুষে করে ॥’
গানটি শুনতে ক্লিক করুন
সমকালের চিত্রজগতের গ্রাফের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়— গ্রামীণ জীবন নিয়ে নির্মিত ছবিগুলো বরাবরই জনপ্রিয়তার শীর্ষে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ছয় দশক পার করেছে। ছয় দশকের নিরিখে, সর্বাধিক দশর্কনন্দিত ৪টি মাত্র চলচ্চিত্রের নাম যদি নিতে বলা হয়, সেখানে অবশ্যই স্থান করে নেবে:
১. রূপবান (১৯৬৫)
২. ময়নামতি (১৯৭০)
৩. বেদের মেয়ে জোস্না (১৯৮৯)
৪. কেয়ামত থেকে কেয়ামত (১৯৯৩)
কেয়ামত থেকে কেয়ামত (১৯৯৩) নিয়ে পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের সর্বকালের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে ‘বেদের মেয়ে জোস্না’ (১৯৮৯)। ‘বেদের মেয়ে জোস্না’র এই বিপুল জনপ্রিয়তা যে নিছক হুজুগ নয়, বিস্তৃত এক আলোচনায় ফরহাদ মাজহার সেটি দেখিয়েছেন। ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ (২০০০) ছবিতে হুমায়ূন আহমেদ ব্যবহার করেছেন রশিদউদ্দীন (১৮৮৯-১৯৬৪), উকিল মুনশি (১৮৮৫-১৯৭৮)-এর গান। এ ছবিতে বারী সিদ্দিকীর কণ্ঠবাহিত সেসব গান জনপ্রিয়তার সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছে। এই ছবির শেষ দৃশ্যে দেখা যায়: বিষখাওয়া মুমূর্ষু কুসুমকে চিকিৎসার জন্য নৌকায় করে শহরে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় পাগলের মতো বৈঠা চালাচ্ছে গায়ক মতি (জাহিদ হাসান), আর কুসুমের হবু বর (মাহফুজ)। হঠাৎ কুসুম নিথর হয়ে পড়ে। হাত থেকে বৈঠা পড়ে যায় হবু বরের।নিয়ন্ত্রণহীন নৌকা, স্থবির কুসুমের জননী। সর্বস্বান্ত মতির মনের ভাব ফুটে ওঠে উকিল মুনশির গানে: ‘শুয়াচান পাখি / আমি ডাকিতাছি তুমি ঘুমাইছ নাকি!’ বুলবুলি, তোতা, ময়না কত নামে ডাকা হয়, কুসুমের মরণঘুম আর ভাঙে না। জীবনের বৃন্ত থেকে বড় অসময়ে ঝরে পড়ে কুসুম। সমাগত সন্ধ্যায় নিঃসীম হাহাকারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ছবি। কিন্তু দর্শক-শ্রোতার অন্তর জুড়ে অনুরণিত হতে থাকে মতির সেই কাতর জিজ্ঞাসা: ‘…তুমি ঘুমাইছ নাকি?’হুমায়ূন আহমেদের জীবনের সর্বশেষ ছবি ‘ঘেটুপুত্র কমলা’ (২০১২)। স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে নির্মিত এ ছবিটিকে গতানুগতিক বাণিজ্যিক ধারার একটি চলচ্চিত্র হিসেবেই গণ্য করা যেতো। ধারণা করা যেত যে, বাজার ধরার কৌশল হিসেবেনির্মাতা জুতসই একটি প্লট বাছাই করেছেন। কিন্তু সব হিসেব পাল্টে যায়, কিংবা বলা যায় সব হিসেব পাল্টে দেন কাহিনীকার-পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ ছবির শেষাংশ, শেষ দৃশ্য ও শেষ গানটি দিয়ে। সপরিবারে দেখা যাবে কি-না; এ দ্বিধা নিয়ে হলে ঢুকে দর্শক হল থেকে বেরিয়েছেন চোখ মুছতে মুছতে; শিশুকণ্ঠে [প্রান্তি] গাওয়া একটি গানের রেশ নিয়ে যার রচয়িতা শীতালং শাহ (১৮০০-১৮৮৯): ‘শুয়া উড়িল উড়িল জীবের জীবন / শুয়া উড়িল রে।’ শুধু গ্রামগঞ্জের মানুষ নয়; শহুরে মানুষেরাও এসব চলচ্চিত্র উপভোগ করছেন।
অতএব, চলচ্চিত্রের গানে আমরা যদি স্বকীয়তার, মৌলিকতার কথা সোচ্চার কণ্ঠে বলতে চাই, তাহলে লোকগানের শরণই আমাদের নিতে হবে। বোধ-বিশ্বাস-ভালোবাসা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, ইতিহাস-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আমাদের লোকগানের যে অফুরন্ত ভা-ার, তা নিয়ে আমরা গর্ব করতেই পারি। আমরা পাইনি অনুপম ঘটকের মতো সুরস্রষ্টা, প্রণব রায় বা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের মানের গীতিকবি। কিন্তু আমরা তো পেয়েছি আবদুল আহাদ, রবিন ঘোষ, আলতাফ মাহমুদ, সমর দাস, খোন্দকার নূরুল আলম, সত্য সাহার মতো দিকপাল কম্পোজার। সুবল দাসগুপ্তের সাথে সুবল দাসের, কিংবা সুধীন দাসগুপ্তের সাথে সুধীন দাসের তুলনামূলক আলোচনার কোন সার্থকতা নেই। আমরা পেয়েছি আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, কেজি মোস্তফার মতো শক্তিমান গীতিকবি। সময় এসেছে তাঁদের এবং তাঁদের সৃষ্টির যথাযথ মূল্যায়ন ও চর্চার।