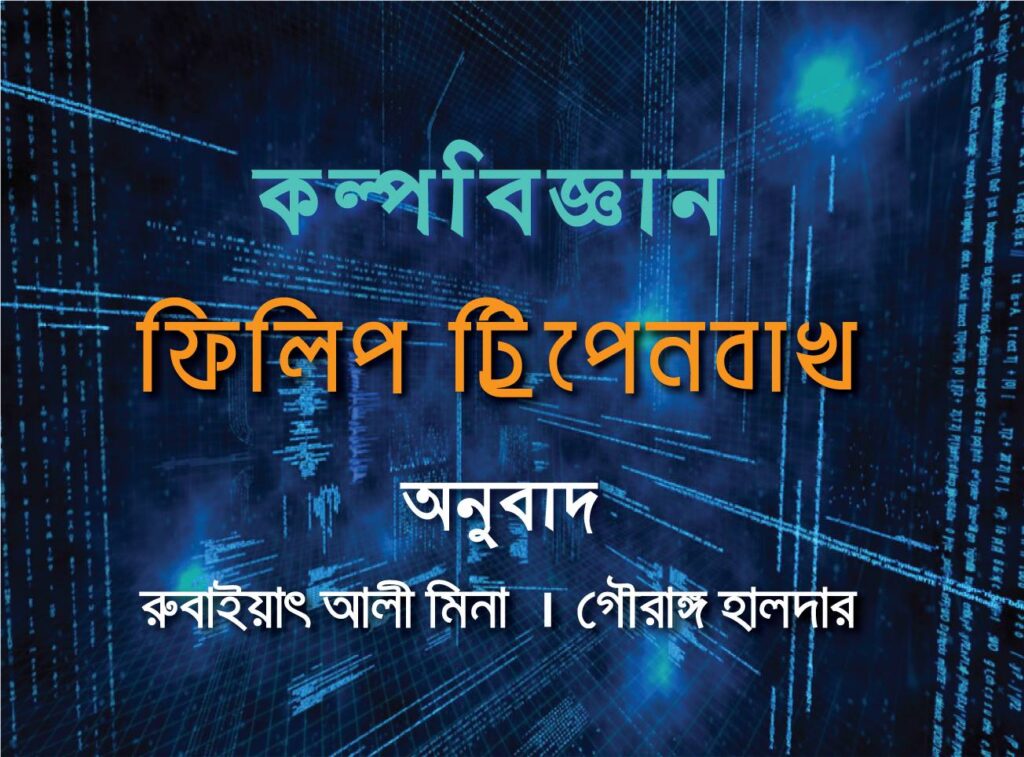[ তাসনীফ হায়দারের এই গদ্যটি প্রায় দেড় বছর আগে পাকিস্তানের বিখ্যাত ওয়েব জার্নাল ‘হাম সব’-এ প্রকাশিত হলে খুব জপ্রিয়তা পায়, পাশাপাশি বিতর্কিতও হয়। ভারতের উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাহিত্যের পাঠকপ্রিয় অনলাইন লিটল ম্যাগাজিন ‘সদানীড়া’র অনলাইন পত্রিকার জন্য উর্দু থেকে লেখাটির হিন্দি অনুবাদ লেখক নিজেই করেছেন। সদানীড়া লেখাটির শেষে একটি ছোট্ট ভূমিকা সহকারে লিখেছে, লেখকের বর্ণনায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু সাহিত্য বিভাগের অবস্থা দেখে বোঝা যায়, হিন্দি সাহিত্য বিভাগের মতো এই বিভাগটিরও প্রায় একই দুর্দশা । বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাহিত্য বিভাগে আমরা যদি তাসনিফের মতোই কিছু যোগ্য, সাহসী এবং স্পষ্টভাষী যুবক খুঁজে পাই, তাহলে আমরা সমস্ত ভারতীয় ভাষার (প্রকৃত বিভাগীয়) অবস্থান সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে পারব। ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর আত্মজীবনী এর তৃতীয় খণ্ডে সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত, সচেতন এবং সৃজনশীল হওয়ার জন্য যে জায়গাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অবস্থান ছিল না। ]
✿
মাত্র কয়েকদিন হলো, আমার এক বন্ধু যখন প্রশ্ন করল তাসনিফ, তুমি যত্রতত্র লেখালেখি না করে বরং এম.ফিল-টা সম্পূর্ণ করে জমা দিয়ে দিতে সেটাও ভাল ছিল। এই যে ঘুরে বেড়াও, বন্ধুদের কাছ থেকে ধার-কর্য কর,বন্ধুদের অনুগ্রহে জীবন কাটাও এটা আর কতদিন সম্ভব। সর্বোপরি, জীবন কিছু গুরুতর আর্থিক নিশ্চয়তা চায়। একদিকে শীতের রোদে আরামে বসে বই পড়তে হবে, অন্যদিকে দুনিয়াকেও চালু রাখতে হবে। তোমাকে বই লিখতে হবে, কবিতা করতে হবে এবং আরও অনেক কিছু তোমার করার আছে যা দিয়ে তোমার জীবনকে সুন্দর করতে চাও।
বন্ধুর কথাটা ভুল ছিল না। এই সময়ে এসে যে কোনো বন্ধুই এইরকম ভাববে এটা স্বাভাবিক। এবং তারও এভাবে চিন্তা করা উচিত। অনেক সময় আমি নিজেও ভাবি, এম.ফিল এর পেপারটা আরও পঁচিশ পৃষ্ঠা লিখতে বাকি আছে, তা পূরণ করে জমা দিয়ে দিতে সমস্যা কী? সম্ভবত আমার জীবন আমাকে এমন কিছু জাদু দেখাবে যে, হয়তো আমাকে কোট-টাই পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো উর্দু বিভাগে বসে থাকতে দেখা যাবে, কিন্তু এই জাদুটি এমন কালো জাদু হবে, যা এই মুহূর্তে আমার আসলে পছন্দ নয়। এর কারণ হল, গত দুই-তিন বছরে আমি নিজের মধ্যে এমন অদ্ভুত পরিবর্তন দেখেছি যার কারণে আমি উর্দুতে এম ফিল করতে আসলে চাই না।
সবাইকে যে আমার মতো করেই ভাবতে হবে তা নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও আপনি খালিদ জাভেদ, তারিক ছেত্রী এবং আরও কিছু ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাবেন যারা এখনও এই পূর্ণিমায় চাঁদের আলো। অধ্যাপকদের নাম উল্লেখ করার পেছনে অবশ্যই সচেতনভাবে তাদের নিয়ে কাঁদা ছোড়াছুড়ি করার কোনো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছেও আমার নেই।
লক্ষ্য করবেন, এখানে সবকিছুর একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়, যেটা খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং তারপর তা আমাদের শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে।বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী করে, কী করতে পারে? তারা শুধু শিক্ষা বিস্তারের ঘোষণা দিতে পারে, শিক্ষা কি শুধু দশম শ্রেনীর পর আর আগের মতো সীমাবদ্ধ কাঠামোতে থাকে? আমার মতে, তার আগে থেকেই বিকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, যা আমাদের চিন্তা করার এবং বোঝার ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যায় তখনই যখন আমাদের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এমনই শিক্ষকদের যুক্ত করেন, যারা নিজেরাই এই আদর্শিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন… যাদের একাডেমিক পড়াশোনার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। এবং তারা ছিলেন একেকজন সমালোচনার মোটা শব্দকোষ, যাদের অবস্থান সৃজনশীলতা থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে।
আমি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগে গত দুই বছরে হয়তো দু-তিনবার গিয়েছি, সেখানে গেলে আমার মধ্যে একটা অন্যরকম কৈফিয়ত তৈরি হয়। অদ্ভুত অনুভূতি জাগে। অথচ সেখানকার ছাত্রদের দেখি কি অদ্ভুদ ভাষায় কথা বলতে। ডিপার্টমেন্টে সব কিছু আছে, সবাই যার যার চেয়ারে বসে আছে, তবুও যেনো কোথাও এর জাঁকজমক শেষ হয় না। কিন্তু সেখানে নতুনত্বের অনুভূতি, নতুন জিনিসের উজ্জ্বলতা বা নতুন কোনো বিষয় নেই। নেই কোনো রকম তর্ক-বিতর্ক। না সৃষ্টির কোনো আলো দেখা যায়।
আমি দেখেছি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রভাষক হওয়ার জন্য লোকেদের এইরকম কিছু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়,যেখানে প্রশ্ন করা হয়, মোল্লা ওয়াজহি বা ফুলন আফসানার লেখা মসনভির নাম কী? অথবা এই চারটি আফসানা-নিগারের মধ্যে কোনটি উনার রচিত? এটা একরকম কৌতুকই আর তামাশা,স্যার। একজন মানুষ যদি এমন একশত মূর্খ ও হাস্যকর প্রশ্নের মধ্যে আশিটির সঠিক উত্তর দিয়ে লেকচারার হওয়ার যোগ্য হন, তাহলে আমাকে নিজের জন্য দাঁড়িয়ে হাততালি দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।
ভাবতাম ইউনিভার্সিটিতে যাবো, মায়ের খুব ইচ্ছে তার ছেলেকে লোকজন প্রফেসর সাহেব বলে ডাকবে। কিন্তু এই মুক্তমনা এবং একচোখা মূর্খতা দেখে আমি না হেসে পারি না। যে ছাত্ররা সমালোচনামূলক নিবন্ধের দশ কপি বই ছাপিয়ে ইন্টারভিউতে নিয়ে যায় কারণ সেই বইয়ের উপর পাঁচ থেকে দশ নম্বর যোগ করা হয়। অথচ দেখা গেল যে একটি সৃজনশীল প্রকাশনার কোনো মানেই রাখে না এইসব ইন্টারভিউতে। প্রফেসর, ডিন, ইন্টারভিউয়াররা তাকে সম্পূর্ণ আবর্জনার মতো ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তারা বলবে ও আচ্ছা তুমি কবি, গল্পকার, ভাল। এইটুকুই। ইন্টারভিউতে আপনার সৃজনশীল কর্মের আসলে কোনো মূল্য নেই। আপনি সেজন্য কোনো নাম্বার পাবেন না। অর্থাৎ সৃজনশীলতা এই জগতের বাইরের কিছু তাদের কাছে।
একজন তরুন প্রার্থী যদি এই ধরনের বই নিয়ে সাক্ষাৎকারে আসেন,তাহলে তিনি উপহাসের লক্ষ্যবস্তু হবেন। শুধু তাই নয় আপনার সৃষ্টিশীল কাজের জন্য, মানে এই গুরুতর কাজের জন্য সমস্ত গাম্ভীর্য নিয়ে আপনাকে উপহাস করা হবে যেন, আপনি সৃষ্টিশীল কাজ করতে আর উৎসাহ না পান। একাডেমিক এই সাহিত্যিক এবং অদম্য অধ্যাপকরা যেন আকার ইঙ্গিতে বলেই দিতে চান, না জনাব! সৃজনশীল কাজ এখানে চলবে না। শুধু পুরাতন বিষয়ের উপর লেখা মোটা মোটা সমালোচনা নিয়ে আসবেন।
গালিবের গজল ও উর্দু ভাষার সমৃদ্ধি, ইকবালের কালামে উপস্থিত ঐতিহাসিক ঘটনা, মান্টোর গল্প ভাবনা, সামাজিক বাস্তবতার সন্ধান… ইত্যাদি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখে বই তৈরি করা আমার পক্ষে মোটেও কঠিন কাজ নয়, আমি চাইলেই তা করতে পারি। এক রাতে, জনাব, হ্যাঁ, আমি স্বজ্ঞানে বলছি, আমি এক রাতে এমন একটি বই লিখে ফেলতে পারি যা দিয়ে ইন্টারভিউতে পাঁচ বা দশ নম্বর পাওয়া যাবে। যা এই সময়ের পরীক্ষার্থীরা খুব পরিশ্রমী আর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখে সুখী হয়।
কিন্তু এই দীর্ঘ তর্ক-বিতর্কের মানে কি, এমন একটা মূর্খ উদ্দেশ্যের জন্য আমার জীবনের একটি সুন্দর রাত নষ্ট করা উচিত? আমি একমত যে বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে প্রতি মাসে একটি মোটা অংকের বেতন দিবে যা দিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তে আমার ছোট বাচ্চাকে গল্প শুনাতে পারবো, কবিতা শুনাতে পারবো কিন্তু সেজন্য আমাকে দিনের পর দিন নিজেকে ধ্বংস করতে হবে। এই বিভাগের গৌরব শুনে, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামের এমন অদ্ভুত গন্ধ আমার নাকের মধ্যে এসে লাগে যে আমার বমি বমি ভাব করে, কোন তাজা হাওয়া যেন আর কাছে আসে না। এইখানে এমন নতুন কিছু, চমকপ্রদ কিছু নেই যে আমাকে আশ্বাস দিবে! সেজন্য বরাবর চিন্তা করা উচিত।
প্রতিদিন একজন অধ্যাপক এসে বিভিন্ন সাহিত্যের ঘরানার বিপরীতে ব্যাখ্যা করে এবং তিনি খুব করে বুঝাত চান তিনি দুর্দান্ত কাজ করেছেন। যে ছাত্ররা উর্দুকে ভাষা ও আদাব প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নিয়েছিল তাদের খারাপ অবস্থার জন্য আমি কখনই চোখের জল ফেলিনি, তবে এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যন্ত তাদের কেবল গজলই শেখানো হয়েছিল। গজল মানেই হলো, নারীদের সঙ্গে কথা বলা বা মেহবুবা, মেহবুবা করে থাকা।
এখানে আমি একটি অদ্ভুত এবং প্রায় অনুপযুক্ত ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, আমি এমন একটি পরিবারে বড় হয়েছি যেখানে তাবিজ, নামাজ, ফাতিহা-খোয়ানি, মিলাদ এবং মাজার জিয়ারতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা রয়েছে। আমাদের এলাকায় ভাসাই গ্রামে (মহারাষ্ট্র) এক বাবা থাকতেন, তার নাম জানি না, বয়স বাহাত্তর, তবে সবসময় তার পিঠে বইয়ের বস্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, এই কারণে পুরো এলাকায় লোকজন তাকে কিতাবওয়ালা বাবা নামে চিনতেন। নামায কোনদিন কাজা করতেন না। আমার প্রায়ই মসজিদে তার সঙ্গে দেখা হতো। গোটা গ্রাম তাঁকে ওলি মনে করত, তাই আমাদের হৃদয়েও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল। একদিন তার কাছে গিয়ে কিছু তাবিজ চাইতেই সে হাসতে লাগলো, বলল বাছা! কোনো মুসলমানের কি তাবিজের প্রয়োজন আছে? সে তো নিজেই একটা জ্যান্ত তাবিজ। বিসমিল্লাহ বলে যেকোনো ভালো কাজ শুরু করলেই হলো।
আজ আমার মনে হয় আমরা একই রকম তাবিজের উপর ভরসা করে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভুল করেছি। এই তাবিজগুলো আমাদের কোনো কাজে আসে না। এখন আবার বিসমিল্লাহ পড়ে এ ময়দানে প্রবেশ করতে হবে। তার আগে আমাদের এই অবস্থা নিয়ে হাসতে হাসতে কথা বলা দরকার, যা কিনা আমার আগে আমার প্রজন্মকে এবং আমার সমসাময়িক প্রজন্মকে সচেতনভাবে কঙ্কাল করে দিয়েছে।
সর্বোপরি, উর্দু সাহিত্য পড়ান এমন একজন অধ্যাপক কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে গালিবের একেকটা শের সৃজনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যখন তাঁর রচনা থেকে তিনি বহু বহু দূরে। এমনকি সেসব বিষয়ে তিনি কখনো ভাল নম্বর পাননি। তিনি অধ্যাপক হয়ে মোটা মোটা সমালোচনা ও বিশ্লেষণের বই পড়ে অথবা কয়েকটা বইয়ের সাহায্য নিয়ে কথা কথায় গালিবের শের বলে বিখ্যাত, লোক নন্দিত হয়ে যাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
কর্মসংস্থানের উত্স খুঁজে পাওয়া একটি ভাল জিনিস, সেটিকে গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ দেওয়া আরও ভাল। যে উপায়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়, সেগুলোর উন্নতি করতে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের একটু থেমে ভাবা উচিত, টাকা রোজগারের এই বহু বিচিত্র ফেরের মধ্যে পড়ে আমরা আসলে কী হারাচ্ছি।
মন ডুবে যাচ্ছে, শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। মুখে নেই কোনো আশার কথা, মঙ্গলের কথা। মগজে নেই কোনো পরিশ্রুত, সুন্দর পরিকল্পনা। ঠিক একই কালশিটে, ফুসকুড়ি, পচা শব্দের টুকরো বছরের পর বছর চিবিয়ে খাওয়া হচ্ছে… আমার সামনেও সেই একই জিনিস পরিবেশন করা হবে। আমি জানি, যদি এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমি পড়াতে যাই, তাহলে আমার পদ্ধতি দিয়ে আপনি কাউকে শেখানোর সুযোগ দিবেন না। ছাত্ররা নিজেরাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, বলবে এই লোকটা কী বলে আমরা বুঝি না। উনি ভাল শেখাতে পারে না। কী ভুল-ভাল, উলট পালট বকে যান। উর্দু বিভাগে এসে জীবন সম্পর্কে কথা বলেন। উর্দু বিভাগে যে বিষয়ের উপর কোনো নাম্বার দেওয়া হয় না।
—
তাসনিফ হায়দারের জন্ম ১৯৮৪ সালে, ভারতের দিল্লীতে। তিনি সমসাময়িক উর্দু কবিতার সেই নামগুলির মধ্যে একটি যার অনুপ্রেরণা ও সহচার্যে ভবিষ্যতের কঠিন পথ সহজ হয়ে ওঠে। ‘মহব্বত কি নাজমিন’ (২০১৮) তার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। তিনি বর্তমানে দিল্লীতে থাকেন।