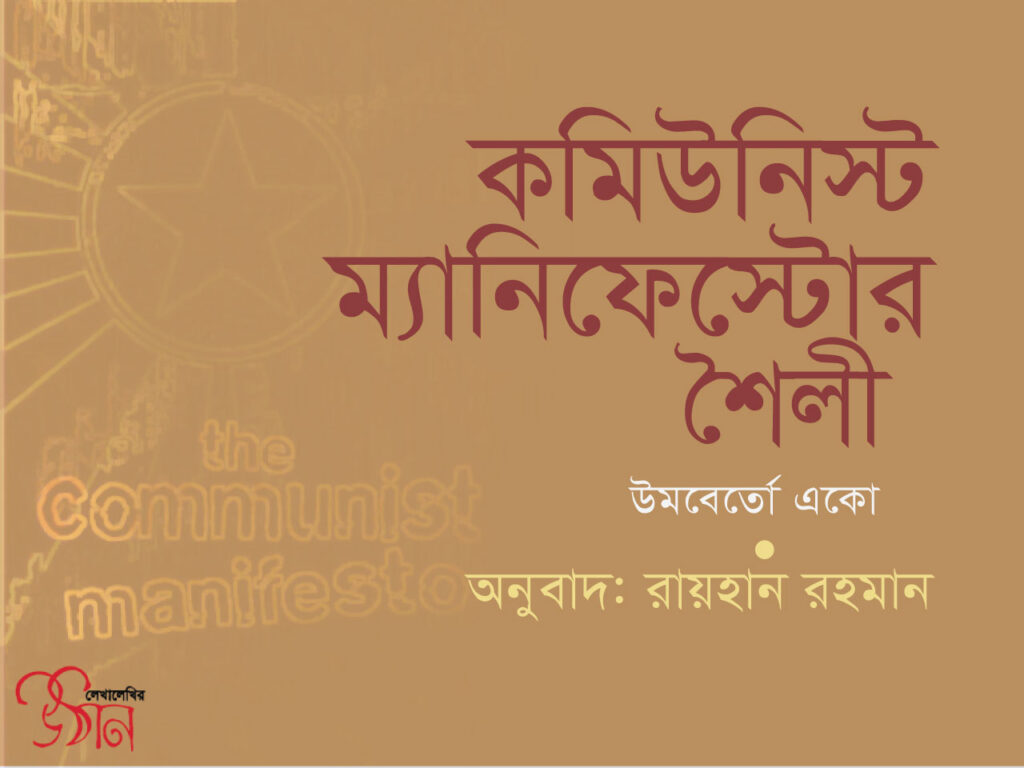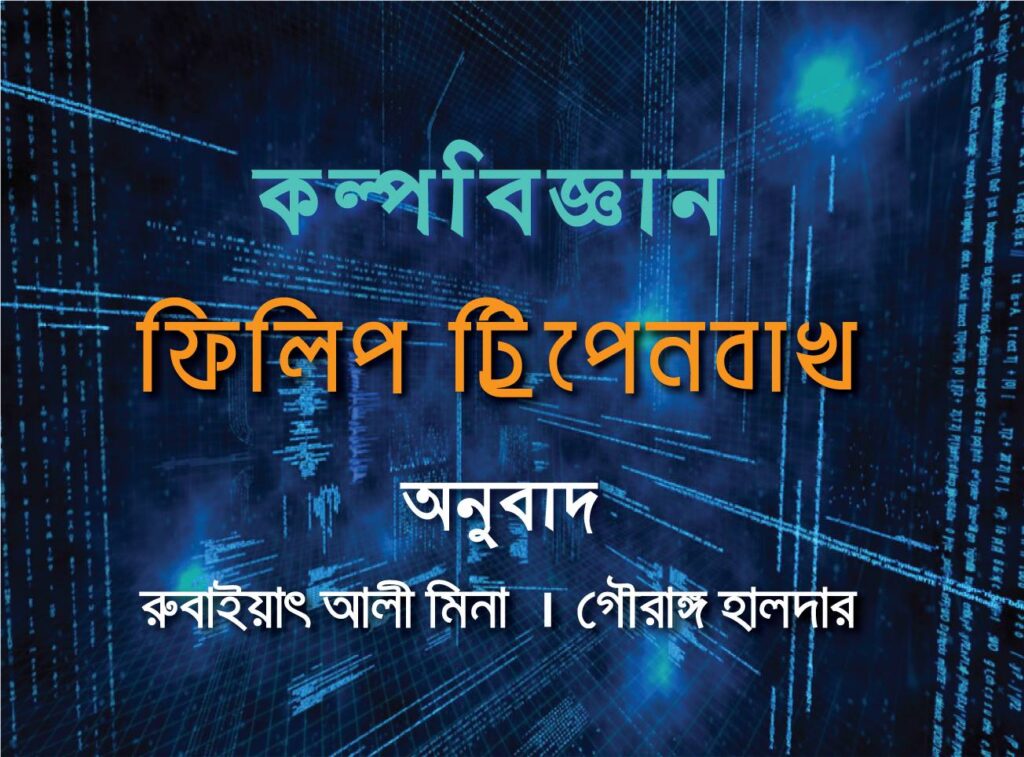এটা কল্পনা করা কঠিন যে সামান্য কয়েকটি বইয়ের পাতা একাই পুরো পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। দান্তের গোটা সমগ্র কিন্তু শেষপর্যন্ত আর ইতালির নগর-রাষ্ট্রে হোলি রোমান সাম্রাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। কিন্তু যখন ১৮৪৮ এ প্রকাশিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার-এর কথা ভাবি, যে বইটি পরবর্তী দুই শতাব্দীর ইতিহাসে অসামান্য প্রভাব ফেলেছে, আমার মনে হয় তাকে এর সাহিত্য মানের দৃষ্টিকোণ থেকেও অবশ্যই পাঠ করা প্রয়োজন। আর কিছু না হলেও অন্তত এর অসাধারণ অলংকারশাস্ত্র এবং যুক্তির কাঠামোকে পাঠ করা উচিৎ। এমনকি যদি মূল জার্মানে পাঠ নাও করা হয়, এর মাহাত্ম্য অনুধাবন করা কঠিন কিছু হবে না।
১৯৭১ সালে ভেনিজুয়েলার লেখক লুদোভিকো সিলভার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির নাম মার্ক্সের সাহিত্যিক শৈলী (Marx’s Literary Style)। ইতালীয় ভাষায় বইটি ১৯৭৩ সালে অনূদিত হয়েছিল। আমার ধারণা বইটি আর পাওয়া যায় না, তবে এটি পুনর্মুদ্রন করা একটা কাজের কাজ হবে। সিলভা বইটিতে মার্ক্সের সাহিত্য শিক্ষার ক্রমবিকাশের একটা গতিরেখা নিরূপণের চেষ্টা করেন (খুব কম মানুষই জানে যে মার্ক্স কবিতাও লিখতেন, যদিও যারা পড়েছে তারা বলে কবিতাগুলো নাকি ভয়াবহ!) এবং মার্ক্সের গোটা রচনাসমগ্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেন। আশ্চর্যজনকভাবে সিলভাইশতেহার -এর উপর সামান্য কয়েকটি লাইন উৎসর্গ করেন মাত্র। এটি পুরোপুরি মার্ক্সের ব্যক্তিগত কাজ নয়, একারনে হয়তো তিনি এমনটি করে থাকবেন। বিষয়টি দুঃখজনক, কারণ এটি একটি বিস্ময়কর রচনা। এটি খুব সুচারুভাবে এর সুর বদলাতে পারে; এর সুর কখনো মহাপ্রলয়ের তমসাচ্ছন্ন রহস্যের, কখনোবা পরিহাসের, কখনো দেখা যায় প্রবল তেজস্বী শক্তিশালী স্লোগান, কখনো পরিষ্কার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এবং এই কটা পাতা যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিশোধ যদি পুঁজিবাদী সমাজ নিতে চায়, এমনকি আজও একটি পবিত্র শাস্ত্র হিসেবে বইটি বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোতে পাঠ্য হতে পারে।
প্রবল এক ঢাকনিনাদ দিয়ে রচনাটি শুরু হয়, অনেকটা বিটোফেনের পঞ্চম সিম্ফোনির মতঃ “ইউরোপকে তাড়া করছে একটি প্রেত” (আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে তখনো প্রাক-রোমান্টিক ও রোমান্টিক যুগের গথিক উপন্যাসের প্লাবন চলছিলো এবং প্রেতকে বেশ গুরুত্ব সহকারেই নিতে হবে)। এর পরে আছে শ্রেণি-সংগ্রামের একটি উপরিগত ইতিহাস, প্রাচীন রোম থেকে শুরু করে বুর্জোয়াদের উৎপত্তি ও বিকাশ পর্যন্ত। পরের পাতাগুলোতে আছে এই নতুন “বৈপ্লবিক শ্রেণির” বিজয়-গাঁথা এবং সেই বিজয় যে মহাকাব্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে যেটি কিনা আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থকদের জন্যেও বহাল আছে তার গুণগান। পাঠক এই অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে দেখতে পারে (আমি অনেকটা সিনেমায় দেখার মত করেই ‘দেখা’ বোঝাচ্ছি), যে শক্তি পণ্যের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টির তাগাদা দেয়, স্থল ও জলপথে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে যায় (আমার মনে হয় এখানে ইহুদী-খৃস্টীয় মার্ক্স জেনেসিস এর সূচনা অংশের কথা ভাবছিলেন)। এই শক্তি দূরের দেশগুলোকে খোলনলচে পালটে দেয় কারণ পণ্যের স্বল্পমূল্যই কামানের তোপের হয়ে কাজ করে যা কিনা নিমেষেই চীনের মহাপ্রাচীর গুঁড়িয়ে দেয় এবং যেসব বর্বররা বিদেশীদের প্রতি ঘৃণায় কঠোর ও অনমনীয় হয়ে আছে, তাদেরকেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। নিজের ক্ষমতার প্রতীক ও বুনিয়াদ হিসেবে এটি নগরের পর নগর গড়ে তোলে। এটি পরিণত হয় বহুজাতিক, বিশ্বায়িত একটি শক্তিতে এবং এমনকি সৃষ্টি করে একটি আখ্যানের, একটি সাহিত্যের যা আর জাতীয় গণ্ডিতে সীমিত নয়, বরং পুরোপুরি আন্তর্জাতিক।(১)
এই স্তুতির পরে (যা আসলেই বিশ্বাসযোগ্য এবং আন্তরিক প্রশংসার উপরে দাঁড়িয়ে) হঠাৎ করেই আমরা একটি নাটকীয় বাঁকবদল দেখতে পাইঃ যে তান্ত্রিক মাটির তলে চাপা থাকা এই অভাবনীয় শক্তিকে তলব করেছে, সে আবিষ্কার করে এই শক্তিকে আর সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। অতি-উৎপাদন এই বিজয়ী বীরের গলা চেপে ধরে এবং সে নিজেই নিজের সমাধিখনককে জন্ম দেয় – প্রলেতারিয়েত শ্রেণিকে।
এই নতুন শক্তি তখন দৃশ্যপটে প্রবেশ করেঃ প্রথমদিকে বিভাজিত ও বিভ্রান্ত এই শ্রেণিকে পুরনো উৎপাদন যন্ত্রের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পিটিয়ে তৈরি করা হয় এবং এদের শত্রুর শত্রুর বিরুদ্ধে (একচ্ছত্র রাজতন্ত্র, জমির মালিক, পেটি-বুর্জোয়া) লড়াই করতে বুর্জোয়াদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় যতদিন না কারিগর, দোকানদার, গেরস্থ কৃষককে (যারা একসময় তাদের শত্রু ছিল) বুর্জোয়ারা প্রলেতারিয়েত বানাতে পারে। হাঙ্গামা একসময় সংগ্রাম হয়ে যায় যেহেতু শ্রমিকরা নিজেদের সংগঠিত হতে থাকে, যার জন্য বুর্জোয়াদের নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বিকশিত আরেকটি ক্ষমতা ধন্যবাদ পেতে পারেঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা। এবং এই ইশতেহার এখানে রেলের উদাহরণ দেয় কিন্তু লেখকদ্বয় এখানে নতুন গণমাধ্যমের কথাও ভাবছিলেন (আমরা যেন ভুলে না যাই যে দ্য হলি ফ্যামিলি-তে মার্ক্স ও এঙ্গেলস সমষ্টিগত কল্পনার একটি মডেল হিসেবে কাজ করা তাদের যুগের টেলিভিশনকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন – সিরিয়াল নভেল – এবং তারা এর ভাবাদর্শের সমালোচনা করেছেন ঠিক সেই ভাষা এবং পরিস্থিতি ব্যবহার করে যেগুলো এই সিরিয়ালকে জনপ্রিয় করেছে)।
এই মুহূর্তে কমিউনিস্টরা মঞ্চে আসে। তারা কারা এবং তারা কি চায়, নির্দিষ্টভাবে সেটি বলার আগে (দারুণ একটি বাগ্মী কৌশল হিসেবে) ইশতেহার তাদেরকে বুর্জোয়াদের অবস্থানে রাখে যারা তাদেরকে ভয় পায় এবং কিছু ভয়াবহ প্রশ্ন তুলে ধরেঃ তোমরা কি সম্পদ বিলোপ করতে চাও? তোমরা কি নারীদের সম-অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিতে চাও? তোমরা কি ধর্ম, জাতি ও পরিবার নির্মূল করে দিতে চাও?
এখানে বিষয়গুলো আরেকটু সূক্ষ্মতার দিকে যায়, কারণ এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর ইশতেহার এমন নিশ্চিন্তভাবে দিচ্ছে যেন মনে হয় ইশতেহার তার বিরোধীদের শান্ত করার চেষ্টা করছে। তারপরে হঠাৎ করেই এটি যেন তাদের পেটের ঠিক মাঝখানে ঘুষি দিয়ে প্রলেতারিয়েত জনগণের হর্ষধ্বনি জয় করে নেয়… আমরা কি সম্পদের বিলোপ চাই? অবশ্যই না। কিন্তু সম্পদ-সম্পর্ক সবসময়েই কি পরিবর্তনীয় ছিল নাঃ ফরাসি বিপ্লব কি সামন্তবাদী সম্পদকে বিলোপ করে পুঁজিবাদী সম্পদকে পথ করে দেয় নি? আমরা কি ব্যক্তিসম্পদ বিলোপ করতে চাই? কি সব পাগলামি কথাবার্তা! এটার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ এই সম্পদ তো সবার সম্পদ না, এই সম্পদের দখল কেবল এক-দশমাংশ জনগণের হাতে। এখন তোমরা কি তাহলে “তোমাদের” সম্পদ বিলোপ করতে চাওয়ার জন্য আমাদের ভর্ৎসনা করছো? ভাল তো, আমরা ঠিক এটাই চাই।
নারীর সম-অংশগ্রহণ? সমাজকে নারীদের সমাজ বানিয়ে দেবো? কি যে বলো! তোমরা নারীদেরকে যে কেবল উৎপাদন যন্ত্রের স্থানে অবনমিত করেছো, এবং তোমাদের কাছে উৎপাদন যন্ত্র মানেই হল তাকে শোষণ করতে হবে। আমরা তো তাদেরকে সেই উৎপাদন যন্ত্রের ভূমিকা থেকে অব্যহতি দিতে চাই। নারীদেরকে কুক্ষিগত করে রাখাটা তোমাদের আবিষ্কার, যেহেতু তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের ব্যবহার করার পরে তোমরা শ্রমিকদের স্ত্রীদের থেকে সুবিধা নিয়েছো, এবং পরম আনন্দযজ্ঞ হিসেবে নিজেদের সমকক্ষদের স্ত্রীদের প্রলুব্ধ করার শিল্প চর্চা করেছো। জাতি নির্মূল করে দেয়া? কিন্তু তোমরা শ্রমিকদের থেকে এমন কিছু কিভাবে নেবে যা তাদের কখনো ছিলই না। আমরা শ্রমিকরা বরং নিজেদেরকেই একটি জাতিতে রূপ দিতে চাই…
ধর্মের প্রশ্নের উত্তরেও মৃতভাষীতার এই মাস্টারপিসে একই রকমের কৌশল দেখা যায়। আমরা ভাবতে পারি যে উত্তরটি হবে, “আমরা ধর্মকে ধ্বংস করতে চাই” তবে রচনাটি কিন্তু এমন কিছু বলে না। যখনই এধরণের সংবেদনশীল বিষয় আসে, এটি এর উপর দিয়ে চলে যায় এবং আমাদের অনুধাবন করতে দেয় যে সব পরিবর্তনই একটা মূল্যের বিনিময়ে আসে, কিন্তু দোহাই লাগে, আমরা এমন সংবেদনশীল বিষয়গুলো এখনই হাতে তুলে না নেই।
তারপরে আসে মতবাদ-সংক্রান্ত বিষয়গুলো, আন্দোলনের কর্মসূচী, বিভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রের সমালোচনা, কিন্তু এর মধ্যেই পাঠকেরা আগের পৃষ্ঠাগুলোতে মজে গেছে। এবং এই কর্মসূচী বিষয়ক পৃষ্ঠাগুলো যদি বেশি কঠিন লাগে, সেজন্য আমরা শেষের দিকে এসে চূড়ান্ত ছোবলটি দেখতে পাই, দুটি শ্বাসরুদ্ধকর স্লোগান, সহজ, মনে রাখার মত এবং অসামান্য ভবিষ্যতের পথে নির্ধারিত (আমার কাছে তাই মনে হয়)ঃ “শ্রমিকদের কেবল নিজেদের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু হারানোর নেই” ও “দুনিয়ার মজদুর, একহও!”
স্মরণীয় রূপক উদ্ভাবনের মৌলিক কাব্যিক ক্ষমতার বাইরেও ইশতেহার রাজনৈতিক (যদিও শুধু রাজনৈতিকই নয়) বাগ্মীতার একটি মাস্টারপিস হয়ে থাকবে, এবং সিসেরোর ইনভেক্টিভস এগেইনস্ট ক্যাটিলিন এবং শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার এ সিজারের মরদেহ সামনে রেখে মার্ক এন্টনির সেই ভাষণের পাশাপাশি এটিও পাঠক্রমে অবশ্য পাঠ্য করা উচিৎ। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতির সাথে মার্কসের ঘনিষ্ঠতার কথা চিন্তা করলে বলা যায় যে ইশতেহার লেখার সময় ঠিক এই রচনাগুলোর কথা মাথায় আনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।
টীকাঃ
(১) আমি যখন এই নিবন্ধটি লিখি, তখন ইতোমধ্যে “বিশ্বায়ন” বা “globalization” শব্দটি প্রচলিত এবং “আন্তর্জাতিক” শব্দটি আমি দৈবাৎ ব্যবহার করি নি। কিন্তু আজ যখন আমরা প্রায় সবাই এ ধরণের সমস্যা নিয়ে বেশ সংবেদনশীল হয়ে পড়েছি, তখন পেছনে ফিরে এই পাতাগুলোর পুনর্পাঠ করাটা খারাপ হবে না। বিস্ময়করভাবে ইশতেহার বিশ্বায়নের যুগেরও প্রায় দেড়শো বছর আগে এর জন্ম এবং বিকল্প যেসব শক্তিকে এটি লেলিয়ে দিয়েছে সেটি প্রত্যক্ষ করে গেছে। এটি বলার চেষ্টা করে যে বিশ্বায়ন আসলে পুঁজিবাদের প্রসারণের পথে ঘটা একটি দুর্ঘটনা নয় (দেয়াল ভেঙে গেছে এবং ইন্টারনেট এসে গেছে বলেই নয়) বরং এটি একটি অবশ্যম্ভাবী ছক যা উদীয়মান শ্রেণি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় নি, যদিও সেসময়ে, বাজারের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এর সবচেয়ে সুবিধাজনক (এবং সবচেয়ে নিষ্ঠুর) উপায়টি ছিল উপনিবেশবাদ। একই সাথে এই সতর্কবাণী জানিয়ে রাখা ভাল যে (এবং এটি কেবল বুর্জোয়াদের জন্যই প্রযোজ্য নয়, সব শ্রেণির জন্য) বিশ্বায়নের অগ্রযাত্রাকে বাধা দেয়া প্রতিটি শক্তিই প্রথমদিকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত থাকে। এবং এরা লুডিজম-এর দিকে ধাবিত হয় এবং তখন এদের শত্রুরা নিজেদের লড়াই লড়ার জন্য এদেরকে ব্যবহার করে থাকে।
(উৎসঃ Umberto Eco. On Literature. Vintage, 2006)
উমবের্তো একো
ইতালীয় দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক। জন্ম ১৯৩২ সালে। একাডেমিক পরিসরে সেমিওটিকস ও মধ্যযুগীয় নন্দনতত্ত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। ১৯৮০ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস The Name of the Rose প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। উত্তরাধুনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই ঔপন্যাসিকের মোট সাতটি উপন্যাস ও অসংখ্য তাত্ত্বিক বই প্রকাশিত হয়। ২০১৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি উবমের্তো একোর জীবনাবসান ঘটে।