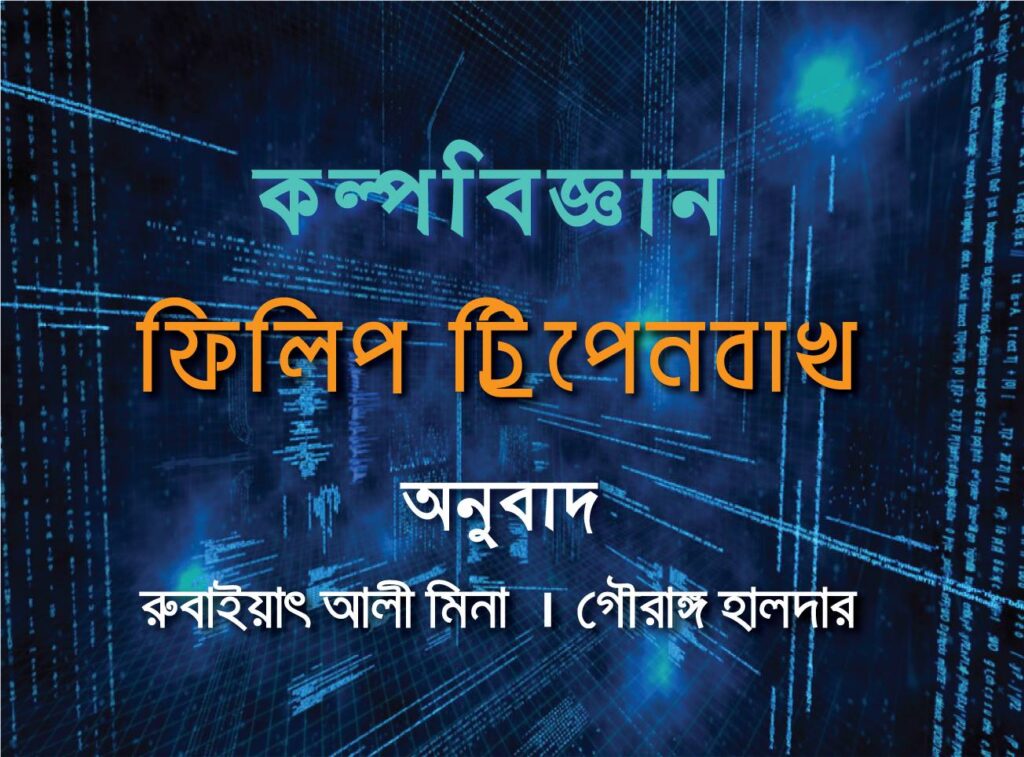উপন্যাসের ক্ষেত্র, তার বিষয়ের দিক থেকে, অন্যান্য শিল্পকলা থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। ওয়াল্টার বেসেন্ট এ বিষয়ে নিজের বিবেচনা প্রকাশ করেছেন এরকম ভাষায়:
‘উপন্যাসের বিষয় এর বিস্তার মানব চরিত্র থেকে কোনো দিক দিয়ে কম নয়। এর সম্পর্ক চরিত্রসমূহের কর্ম এবং বিবেচনা, দেবত্ব এবং পশুত্ব, উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের সঙ্গে। মনোভঙ্গির বিভিন্ন রূপ এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এদের (চরিত্রগুলোর) বিকাশ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়।’
এই বিষয়বিস্তারে উপন্যাসকে সংসার-সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ করে তুলেছে। যদি আপনার ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ থাকে, তবে আপনি আপনার উপন্যাসে গভীর থেকে গভীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ করতে পারেন। আপনার রুচি যদি হয় দর্শনে তাহলে উপন্যাসে মহৎ দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন। যদি আপনার মধ্যে কবিত্বশক্তি থাকে তাহলে উপন্যাসে তার জন্য সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর। সমাজনীতি বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়ের জন্য স্থান রয়েছে উপন্যাসে। এখানে (উপন্যাসে) লেখকের জন্য কলমের ক্ষমতা দেখানোর যতটা সুযোগ রয়েছে ততটা সাহিত্যের আর কোনো অঙ্গে মেলা মুশকিল। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ঔপন্যাসিকের জন্য কোন বাধা-বন্ধন নেই। উপন্যাসের বিষয় বিস্তারই ঔপন্যাসিককে বন্ধনে আবদ্ধ করে। সরু গলিতে চলা পথিকের জন্যে লক্ষ্যে পৌঁছানো ততটা কঠিন নয়, যতটা কঠিন হয় এক লম্বা-চওড়া পথহীন ময়দানে চলা পথিকের জন্য।
ঔপন্যাসিকের প্রধান গুণ তার সৃজনী শক্তি। যদি তাঁর মধ্যে এই ক্ষমতার অভাব থাকে, তবে তিনি নিজের কাজে কখনোই সফল হতে পারেন না। তাঁর মধ্যে যতো কিছুরই অভাব থাকুক কল্পনাশক্তির প্রখরতা অনিবার্য। যদি তাঁর মধ্যে এই ক্ষমতা থাকে তবে তিনি এমন অনেক দৃশ্য, অবস্থা বা মনোভঙ্গির চিত্রণ করতে পারেন, যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। যদি সেই শক্তির ঘাটতি থাকে, তাহলে তিনি যত দেশই পর্যটন করে থাকুন না কেন, তিনি যতই বিদ্বান হন না কেন, তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হোক না কেন, তাঁর রচনায় সরসতা আসতে পারে না। এমন অনেক লেখক রয়েছেন যাঁদের মধ্যে মানবচরিত্রের রহস্যকে মনোজ্ঞ, সূক্ষ্ম এবং প্রভাববিস্তারী শৈলীতে বয়ান করার শক্তি রয়েছে; কিন্তু কল্পনাশক্তির অভাবে তিনি তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারেন না, জীবন্ত ছবি আঁকতে পারেন না। তাঁর রচনা পাঠ করে আমাদের এই কথা মনে হয় না যে আমরা কোনো সত্যি ঘটনা দেখছি।
এতে সন্দেহ নেই যে উপন্যাসের রচনাশৈলী সজীব এবং প্রভাববিস্তারী হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমরা শব্দের গোলকধাঁধা তৈরি করে পাঠককে এমন প্রমাদের মধ্যে ফেলে দেব যে এর মধ্যে অবশ্যই কোনো গূঢ় অর্থ আছে। যেমন আমরা কোনো মানুষের ঠাটবাট দেখে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, তেমনি উপন্যাসের শব্দগত আড়ম্বর দেখেও আমরা ধরে নিই যে এর মধ্যে কোনো মহৎ বিষয় লুকিয়ে রয়েছে। হতে পারে, এধরনের লেখক কিছুদিনের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু মানুষ সেই উপন্যাসকে সম্মান দেয় যার বিশেষত্ব তার গূঢ়তায় নয় সরলতায়।
কাহিনীকে ঘটনাবৈচিত্র্য দ্বারা আকর্ষণীয় করে তোলার অধিকার ঔপন্যাসিকের আছে, কিন্তু মূল কাঠামোর সঙ্গে প্রত্যেক ঘটনার সম্পর্ক থাকা জরুরি। কেবল তাই নয়, বরং সব কিছু মিলেমিশে একাকার হওয়া চাই, নইলে উপন্যাসের দশা সেই ঘরের মতো হবে যেখানে সব কিছু স্বতন্ত্র হয়ে আছে। যখন লেখক মুখ্য বিষয় থেকে সরে গিয়ে অন্য কোনো বিষয়ে তর্ক করতে শুরু করেন, তখন পাঠক কাহিনী থেকে যে আনন্দ পাচ্ছিলো তাতে বাধা সৃষ্টি হয়। উপন্যাসের সেই সব ঘটনা, সেই সব বিবেচনা উপস্থাপন করা উচিত, যাতে কাহিনীর মাধুর্য বাড়ে, যা প্লট-বিকাশে সহায়ক হয় অথবা চরিত্রের লুকানো মনোভঙ্গি প্রকাশ করে। পুরনো কাহিনীসমূহে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ঘটনা বৈচিত্র্য দেখানো; তাই তাঁরা এক কাহিনীর মধ্যে অজস্র উপকাহিনী যুক্ত করে নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণ করতেন। সাম্প্রতিক উপন্যাসে লেখকের উদ্দেশ্য মনোভঙ্গি এবং চরিত্র রহস্য উদ্ঘাটন; তাই চরিত্রকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে হয়, যাতে তার চরিত্রের কোনো অংশ দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। এ ধরনের উপন্যাসে উপকাহিনীর সুযোগ বেশি থাকে না।
এ কথা সত্য, দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুই উপন্যাসের উপযুক্ত বিষয় হতে পারে। প্রকৃতির সকল রহস্য, মানব জীবনের সকল প্রসঙ্গ যখন কোন সুযোগ্য লেখকের কলম থেকে বেরোয়, তা সাহিত্যের রত্ন হয়ে যায়, কিন্তু তার সাথে সাথে বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং তার গভীরতা উপন্যাসের সাফল্যের জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। নায়ক চরিত্রের উচ্চশ্রেণীর হওয়া জরুরী নয়। হর্ষ এবং শোক, প্রেম এবং অনুরাগ, ঈর্ষা এবং দেশ মানুষমাত্রের ভেতরেই ব্যাপক পরিমাণে থাকে। আমাদের কেবল হৃদয়ের সেই তারে আঘাত করা প্রয়োজন যার ঝংকারে পাঠকের হৃদয়ে সে রকম প্রভাব হয়। সফল ঔপন্যাসিক এর সবচেয়ে বড় লক্ষণ, তিনি পাঠকের হৃদয়ে সেই ভাব জাগরিত করেন যা তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। পাঠক যেন ভুলে যায় যে সে কোনো উপন্যাস পড়ছে—তার এবং উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে যেন আত্মীয়তা স্থাপিত হয়।
মানুষের সহানুভূতি সাধারণ অবস্থায় ততক্ষণ অব্দি জাগৃত হয় না যতক্ষণ এর জন্য তার ওপর বিশেষ ভাবে আঘাত না করা হয়। আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম ভাব সাধারণ অবস্থায় আন্দোলিত হয় না। তার জন্য এমন ঘটনার কল্পনা করা প্রয়োজন হয় যা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়, যা আমাদের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে যায়। যদি কোনো অবলাকে নিজের পরাধীন অবস্থা অনুভব করাতে হয় তবে এর থেকে প্রভাববিস্তারী আর কোনো ঘটনা হতে পারে যাতে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের দরবারে এসে হাজির হয় এবং দুষ্মন্ত তাকে না চিনে উপেক্ষা করে? দুঃখের বিষয় হলো, আজকালকার উপন্যাসে গভীরভাবে স্পর্শ করবার মতো অনেক মসলা থাকে। অধিকাংশ উপন্যাস গভীর এবং তীব্র ভাবের প্রদর্শন করে না। আমরা প্রতিদিনের সাধারণ কথার ঝঞ্ঝাটে পড়ে থাকি।
এ বিষয়ে এখনো মতভেদ আছে যে, উপন্যাসে মানবীয় দুর্বলতা, কুবাসনা, কমজোরি এবং অপকীর্তির বিশদ বিবরণ বাঞ্ছনীয় কিনা; কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যে লেখক নিজেকে এসকল বিষয়ের মধ্যে বেঁধে ফেলেন, তিনি কখনও সেই শিল্পীর মহত্ত্ব অর্জন করেন না যিনি জীবন সংগ্রামে একজন মানুষের আন্তরিক চেষ্টা, সৎ-অসতের সংঘর্ষ এবং অন্তে সত্যের বিজয়কে ধর্মীয় ভাবে দেখান। যথার্থবাদের অর্থ এই নয় যে আমরা নিজের দৃষ্টিকে অন্ধকারের দিকে কেন্দ্রিত করে ফেলি। অন্ধকারে মানুষ অন্ধকার ছাড়া আর কিই বা দেখতে পারে? নিঃসন্দেহে, ঠাট্টা করা, এমনকি কাটাছেঁড়া করাও কখনো কখনো অনাবশ্যক হয়। দৈহিক ব্যথা অস্ত্রোপাচারে দূর হয়ে গেলেও মানসিক ব্যথা সহানুভূতি এবং উদারতার সাহাজ্যেই দূর করা সম্ভব। কাউকে নীচু মনে করে আমরা তাকে উঁচুতে তুলতে পারি না বরং আরো নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি। ভীতু এ কথা বলাতে সাহসী হয়ে যাবে না যে ‘তুমি ভীতু’। আমাদের এটা দেখাতে হবে যে তার মধ্যে সাহস, শক্তি এবং ধৈর্য—সবকিছুই আছে, কেবল এদের জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। সাহিত্যের সম্পর্ক সত্য এবং সুন্দরের সাথে, এ কথা আমাদের ভোলা উচিত নয়।
কিন্তু আজকাল কুকর্ম, হত্যা, চুরি, ডাকাতিভরা উপন্যাসের যেন বন্যা বয়ে চলেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কোনো সময় ছিলো না যখন এরকম কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসের আধিক্য ছিলো। রহস্যোপন্যাসে কেন এত আনন্দ? এর কারণ কি এই যে আগের চেয়ে মানুষ এখন বেশি পাপাসক্ত হয়ে গেছে? যে সময় মানুষের দাবি এই যে মানব সমাজ নৈতিক এবং বৌদ্ধিক উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, তখন এ কথা কে স্বীকার করবে যে আমাদের সমাজ পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে? সম্ভবত এর কারণ এই যে এই ব্যবসায়িক শান্তির যুগে এমন ঘটনার অভাব রয়েছে যা মানুষের কৌতূহলকে সন্তুষ্ট করতে পারে—যা তার মধ্যে রোমাঞ্চ নিয়ে আসতে পারে। অথবা এর কারণ এটা হতে পারে যে মানুষের ধনলিপ্সা উপন্যাসের চরিত্রকে সম্পদের লোভে কুকর্ম করতে দেখে প্রসন্ন হয়। এ ধরনের উপন্যাসে এই তো হয় যে কোনো ব্যক্তি লোভের বশে কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে, অথবা তাকে কোনো সংকটে ফেলে মোটা অংকের অর্থ আদায় করে। তারপর গোয়েন্দা আসে, উকিল আসে এবং অপরাধী গ্রেফতার হয়, সে শাস্তি পায়। এমন রুচি ভালোবাসা, অনুরাগ অথবা উৎসর্গের কাহিনীতে আনন্দ পেতে পারে না। ভারতবর্ষে ব্যবসায়িক উন্নতি তো হয়নি কিন্তু এ ধরনের উপন্যাসের প্রাধান্য শুরু হয়ে গেছে। যদি আমার অনুমান ভুল না হয় তাহলে এ ধরনের উপন্যাসের কাটতি এদেশেও অনেক বেশি। এই কুরুচির পরিণাম, রুশ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায়, এমন পরিবেশ সৃষ্টি যা কুকর্ম এবং প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করে। এতে এ বিষয় তো স্পষ্ট হয়ে যায়, মানুষের মধ্যে পাশবিক বৃত্তিসমূহ এতোটা প্রবল হয়ে যাচ্ছে যে এখন তার হৃদয়ে কোমল ভাবের জন্য জায়গাই নেই।
উপন্যাসের চরিত্র চিত্রন যতটা স্পষ্ট, গভীর এবং বিকাশমান হবে পাঠকের উপর এর প্রভাব ততটাই বেশি পড়বে, আর এটা লেখক এর রচনা শক্তির ওপর নির্ভর করে। যেমন কোনো মানুষকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাই না, তার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্টতা যতটা বাড়ে তার মন ও রহস্য ততটাই প্রকাশিত হয়, ঠিক সেইরকম উপন্যাসের চরিত্রও লেখক এর কল্পনায় পূর্ণরূপে চলে আসে না বরং তাতে ক্রমশ বিকশিত হয়। এই বিকাশ এতটা গোপন, অস্পষ্ট রূপে হয় যে পাঠক কোনো পরিবর্তনের ধারণাও পায়না। যদি চরিত্রের মধ্যে কারো বিকাশ থেমে যায় তাহলে সেই চরিত্রকে উপন্যাস থেকে বাদ দেয়া উচিত। কেননা চরিত্রের বিকাশই উপন্যাস। যদি তার মধ্যে বিকাশ-ত্রুটি থাকে তাহলে সে উপন্যাস দুর্বল হয়ে পড়ে। কোনো চরিত্র যদি উপন্যাসের শেষে সে রকমই থাকে প্রথমে সে যে রকম ছিলো— তার শক্তি, বুদ্ধি, ভাবের কোনরকম বিকাশ না ঘটে, তবে সেটা অসফল চরিত্র।
এই দৃষ্টিতে যখন আমরা বর্তমান হিন্দী উপন্যাসকে দেখি তখন নিরাশ হতে হয়। অধিকাংশ চরিত্র এমন পাওয়া যাবে যারা কাজ অনেক করে, কিন্তু যে কাজ যেমন ভাবে আদিতে করেছে, সে কাজ সেরকম ভাবে শেষেও করে।
কোনো উপন্যাস শুরু করবার জন্য যদি আমরা তার চরিত্র গুলোর একটা মানসিক চিত্র অঙ্কন করে নিই তবে তাদের বিকাশ দেখানো আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে বিকাশ পরিস্থিতি অনুসারে স্বাভাবিক হওয়া চাই। অর্থাৎ পাঠক এবং লেখক যেন এ বিষয়ে সহমত হন। যদি পাঠকের এরকম মনে হয় যে এই অবস্থায় এমন হওয়া উচিত ছিল না তবে এর অর্থ হতে পারে লেখক চরিত্র চিত্রণে অসফল। চরিত্রগুলোর ভেতরে কিছু না কিছু বিশেষত্বও থাকা প্রয়োজন। যেমন পৃথিবীতে দুজন ব্যক্তি এক রকম হয় না, তেমনি উপন্যাসেও রকম হওয়া উচিত নয়। কিছু মানুষ তো কথাবার্তা এবং চেহারাসুরতেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। কিন্তু আসল ব্যতিক্রম তো তাই যা চরিত্রের অভ্যন্তরে থাকে।
উপন্যাসের সংলাপ যত বেশি হয় এবং লেখকের কলম থেকে যত কম লেখা যায় উপন্যাস ততই সুন্দর হয়ে উঠবে। কথাবার্তা যেন কেবল সংযোগসূত্র না হয়। প্রত্যেক বাক্য—যা কোনো চরিত্রের মুখ থেকে বের হয়—তার চরিত্র এবং মনোভঙ্গির ওপর যেন কোনো না কোনো আলো ফেলে। সংলাপ স্বাভাবিক, পরিবেশের অনুকূল, সরল এবং সূক্ষ্ম হওয়া চাই। আমাদের উপন্যাসে সচরাচর চরিত্রদের সে ভাষাতেই কথা বলানো হয় যেন লেখক নিজের ভাষা চরিত্রের মুখে দিচ্ছেন। শিক্ষিত সমাজের ভাষা তো সর্বত্রই এক। তবে হ্যাঁ ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মুখে তার রূপ কিছু না কিছু বদলে যায় (যখন তারা হিন্দি বলেন–অনুবাদক)। বাঙালি, মাড়োয়ারি কিংবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানকেও কখনো কখনো শুদ্ধ (মান হিন্দী–অনুবাদক) হিন্দী বলতে শোনা যায়। কিন্তু এটা ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। গ্রামীণ সংলাপ আমাদেরকে দ্বিধায় ফেলে দেয়। বিহারের গ্রামীণ ভাষা দিল্লির আশেপাশের লোক সম্ভবত বুঝতেই পারবে না।
বাস্তবে কোনো রচনার রচয়িতার মনোভাবের, তার চরিত্রের, তার জীবনাদর্শের, তার দর্শনের আয়না। যার হৃদয়ে প্রদর্শন-প্রেম রয়েছে সেই লেখকের চরিত্র, ঘটনাবলী এবং পরিস্থিতি সবই সেই রঙে রাঙানো হবে। নিছক আনন্দের অভিসারী লেখকের চরিত্রের অধিকাংশই এমন হবে যাদেরকে জগতের অন্য কোনো বিষয় প্রভাবিত করতে পারে না। তারা রহস্যোপন্যাস, অলৌকিক কাহিনী রচনা করেন। যদি লেখক আশাবাদী হন তাহলে তার রচনায় আশাবাদ ঝলকে উঠবে, যদি তিনি দুঃখবাদী হন তাহলে অনেক চেষ্টা করেও তিনি তার চরিত্রদের হাসিখুশি স্বভাবের করতে পারবেন না। ‘আযাদ-কথা’র উদাহরণ নিতে পারেন। পাঠক খুব দ্রুতই জেনে যাবে যে এই লেখক হাসা এবং হাসানোর প্রাণী যিনি জীবনকে গভীর বিবেচনার বিষয় মনে করেন না। যেখানে তিনি সমাজের প্রশ্ন তুলেছেন, সেখানেই রচনাশৈলী শিথিল হয়ে গেছে।
যে উপন্যাস সমাপ্ত করবার পর পাঠক নিজের ভেতরে উৎকর্ষ অনুভব করে, তার সদ্ভাব জাগ্রত হয় তাইতো সফল উপন্যাস। যার ভাব গভীর, প্রখর—যে জীবনের বোঝা হয়ে নয় বরং বাহন হয়ে চলে, যে উদ্যোগী হয় এবং বিফল হয়, ওঠার চেষ্টা করে এবং পড়ে যায়, যে সত্যি জীবনের গভীরতার মধ্যে ডুবে রয়েছে, যে জীবনের চড়াই-উৎরাই দেখেছে, সম্পদ এবং বিপদের মুখোমুখি হয়েছে, যার জীবন মখমলের গদির ওপর কাটে না সেই লেখকই উপন্যাস লিখতে পারেন যে উপন্যাসে আলো, জীবন এবং আনন্দ প্রদান করবার ক্ষমতা থাকে।
উপন্যাস-পাঠকের রুচিও এখন বদলে যাচ্ছে। এখন তারা কেবল লেখকের কল্পনায় সন্তুষ্ট হয় না। কল্পনা যেমনই হোক কল্পনাই। তা বাস্তবতার স্থান দখল করতে পারে না। ভবিষ্যৎ সেই উপন্যাসের অধিকারে যাবে যা অনুভূতির ওপর দাঁড়িয়ে।
এর অর্থ এই যে ভবিষ্যতে উপন্যাসে কল্পনা কম সত্য বেশি হবে।আমাদের চরিত্র কাল্পনিক হবে না বরং ব্যক্তির জীবনের ওপর ভিত্তি করে হবে। কতকটা তো এখনও সেরকম হয়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা পরিস্থিতির ক্রম এমনভাবে সাজাই যে পরিণতি স্বাভাবিক হয়েও তাই হয় যা আমরা চাই। আমরা স্বাভাবিকতার সঙ যত সুন্দর ভাবে সাজাতে পারি ততটাই সফল হই। কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠক এই সঙে সন্তুষ্ট হবে না।
বলতে হয় যে ভবিষ্যতের উপন্যাসে জীবন-চরিত্র হবে, তা সে বড় মানুষের হোক কিংবা ছোট মানুষের। তার ক্ষুদ্রতা কিংবা বৃহত্তের ফয়সালা সেই লড়াইয়ের ওপর করা হবে যাতে সে জয় পেয়েছে। হ্যাঁ, সে চরিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত হবে যাতে উপন্যাস মনে হয়। এখন আমরা মিথ্যাকে সত্য বলে দেখাতে চাই, ভবিষ্যতে সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দেখাতে হবে। কোনো কৃষকের চরিত্র হোক কিংবা কোনো দেশ-প্রেমিকের চরিত্র, বা কোনো বড় মানুষের চরিত্র তার ভিত্তি বাস্তবের ওপর হবে। তখন এই কাজ এখনকার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হবে। কেননা এমন মানুষ খুব কমই আছেন যিনি অনেক মানুষের ভেতরটা জানবার গৌরব অর্জন করেছেন।

সফিকুন্নবী সামাদী
সফিকুন্নবী সামাদী (জন্ম: ১৯৬৩)।অধ্যয়ন: স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর (বাংলা), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। হিন্দী-উর্দু সাহিত্যে আগ্রহী। পিএইচ.ডি গবেষণায় তুলনামূলক আলোচনা করেছেন উর্দু-হিন্দী ঔপন্যাসিক মুন্সি প্রেমচাঁদ এবং বাংলা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের। তাঁর কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ বেরিয়েছে উর্দু এবং হিন্দী থেকে।